০৪. ভারতে ব্রিটিশ শাসন : হিন্দু ও মুসলিম
মানসিকতার এই পরিবর্তন তো একদিনে হয়নি। সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সলতে পাকানো হয়েছে আরও অনেক আগে থেকেই। এই মানসিকতা তৈরির মূল কারিগর হল হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগঠন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগ প্রভৃতি। ঐতিহাসিকভাবে আদিতে ভারত ভূখণ্ডে প্রথম ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করেছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। তাঁরা চেয়েছিল রাজশক্তি ব্রিটিশদের সাহায্যে ভারত থেকে মুসলিমদের ঝেটিয়ে বিদায় করতে। তাঁরা স্বপ্ন দেখত মুসলিম শূন্য একটি হিন্দু রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হবে সম্পূর্ণ গেরুয়া রঙের।
তবে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘই প্রথম সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক মানসিকতা বহু প্রাচীন। তখনও ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রবেশ ঘটেনি। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের নিশ্চিহ্ন হওয়ার পিছনের ব্রাহ্মণ্যবাদীদের (সে সময়ে হিন্দু বলে কোনো ধর্মের ধারণা ছিল না। বর্তমানে হিন্দু বললে তার ব্যাপ্তি অনেক। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলাটাই যুক্তিযুক্ত। কারণ সব ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু হলেও, সব হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী নয়) ভূমিকা ইতিহাস ভুলে যায়নি। গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অকথ্য নিপীড়নের বিরুদ্ধে কথা বলে গেছেন। তবুও প্রাচীন ইতিহাসের নৃশংসতম এক হত্যাযজ্ঞের পরে হিন্দুরাজা অশোকের ২৩৬ পূর্বাব্দে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে পর্যন্ত বৌদ্ধদের ভারতবর্ষের রাষ্ট্রযন্ত্রে কোনো রকম প্রভাব ছিল না বললেই চলে। অশোকের শাসনকালে বৌদ্ধধর্ম ভারত ছেড়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। পঞ্চম শতাব্দীর চিনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ও তীর্থযাত্রী ফেক্সিয়ান ভারত সফরের সময় স্থানীয় মহায়ন বৌদ্ধতত্ত্বে মৌলিক দুর্বলতা দেখতে পান। সেখানে অনেক ঈশ্বররূপী বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বরা মহাবিশ্বের অগণিত স্তরগুলোতে বসবাসরত। ওই বৌদ্ধতত্ত্ব হিন্দুধর্মের এতটাই কাছাকাছি ছিল যে, অনেকেই এই দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেতেন না। উঁচু বর্ণের ব্রাহ্মণরা ধর্ম বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতেন। তাঁরা বুদ্ধের দার্শনিক ভাবশিক্ষার বিরুদ্ধে ততটা সোচ্চার ছিলেন না। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদের ভিত্তিপ্রস্তর অর্থাৎ, প্রাচীনকাল থেকে রক্ষা করে আসা বেদে দেওয়া ব্রাহ্মণদের দৈবত্ব, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বকে যখন বৌদ্ধবাদে প্রশ্নবিদ্ধ করা হল, তখন তাঁরা তার সর্বাঙ্গীন বিরোধিতা শুরু করলেন।
ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এক দীর্ঘমেয়াদি ষড়যন্ত্রের ফসল ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের বিনাশ (অবশ্য শেষের দিকে বৌদ্ধ বিতারণে মুসলিমদেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেকে মনে করেন)। কারণ সে সময়ে বৌদ্ধধর্মই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে প্রধান ও একমাত্র হুমকিস্বরূপ। উঁচুবর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছ থেকে ধারাবাহিকভাবে অকথ্য অত্যাচারে নীচু শ্রেণির মানুষরা দলে দলে বৌদ্ধধর্মে চলে আসছিল। এটা ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মেনে নিতে পারেনি। তবে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হওয়ার কারণ নিয়ে গবেষণা করা শ্রীনরেশ কুমার মনে করেন, বৌদ্ধবাদের বিরোধিতা ও একইসঙ্গে ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদের পুনঃস্থাপনের জন্যে ব্রাহ্মণ পুনর্জাগরণীরা তিন ধাপের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছিলেন। প্রথম ধাপে তাঁরা বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে ঘৃণা আর অত্যাচারের অভিযান শুরু করেন। এরপরে তাঁরা বৌদ্ধধর্মের ভালো দিকগুলো আত্মস্থ করে নেয়, যাতে করে নীচু জাতের বৌদ্ধদের মন জয় করা যায়। কিন্তু বাছাইকৃত আত্মীকরণের এই ধাপে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য যাতে কোনোভাবেই ক্ষুগ্ন না হয় তা নিশ্চিত রাখা হয়। বৌদ্ধবাদ ধ্বংস প্রকল্পের শেষধাপে গৌতম বুদ্ধকে বিষ্ণুর দশাবতারের একজন হিসাবে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর বৌদ্ধধর্ম যে পৃথক ধর্ম নয় সেটা বুঝিয়ে দেওয়া গেল। অতএব বুদ্ধ বিষ্ণুর আর-একটি অবতার ছাড়া আর কিছুই নয়। হিন্দুধর্মের শরীরের ভিতর বৌদ্ধধর্মকে বিলীন করে দেওয়ার প্রয়াস। অবশেষে বৌদ্ধরা মূলত শূদ্র আর অচ্ছুত হিসেবে জাতপ্রথায় আত্মীকৃত হলেন –আর এভাবেই নিজ জন্মভূমিতেই বৌদ্ধরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে লাগলেন।
বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ঘৃণা মনুসংহিতা, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতেও স্পষ্টত উল্লেখ আছে। গবেষক নীলেশ কুমার বলেন, “বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে চলা এই নির্মূলাভিযানকে বৈধতা দিতে ব্রাহ্মণ্য লেখাগুলোতে বৌদ্ধদের প্রচণ্ডভাবে তিরস্কার করা হয়। মনুসংহিতায় মনু বলছেন— “কেউ যদি বুদ্ধকে স্পর্শ করে … তবে সে স্নান করে নিজেকে শুচি-শুদ্ধ করে নেবে।” অপরাকা তাঁর গ্রন্থে একই ধরনের আদেশ দেন। ব্রাদ্ধ হরিত ঘোষণা করেন যে, বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ করাই পাপ, যা কেবল আচারিক স্নানের মাধ্যমে স্খলিত হতে পারে। এমনকি সাধারণ জনগণের জন্যে লেখা নাটিকা কিংবা পুথিগুলোতেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বুদ্ধের বিরুদ্ধে ঘৃণার বিষ ছড়িয়েছেন। প্রাচীন নাটিকা ‘মৃচ্ছকটিক’-এ নায়ক চারুদত্ত এক বৌদ্ধ সন্তকে হেঁটে আসতে দেখে, বন্ধু মৈত্রীয়কে ক্রোধক্তিতে বলেন –“আহ্! কী অশুভ দৃশ্য– এক বৌদ্ধ সন্ত দেখছি আমাদের দিকেই আসছে।” অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থের কৌটিল্য বলেছে— “যদি কেউ শক্য (বৌদ্ধ), অজিবিকাশ, শুদ্র বা নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তিদের ঈশ্বর বা পূর্বপুরুষদের পূণ্যার্থে উৎসর্গিত ভোজসভায় যোগদান করে, তাহলে তাঁর উপর একশো পণ অর্থদণ্ড আরোপিত হবে।” ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবনের পুরোধা শঙ্করাচার্য বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড নিন্দামূলক কথার মাধ্যমে বৌদ্ধদের মনে সীমাহীন ভীতির সঞ্চার করেন। পুরাণের অনেক রচয়িতাও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক, তস্কর, অপবাদ, চরিত্রহরণের মাধ্যমে ঘৃণার এই পরম্পরা অব্যাহত রাখেন। এমনকি বিপন্ন সময়েও কোনো বৌদ্ধের বাড়িতে প্রবেশ করাকে ব্রাহ্মণদের জন্যে মহাপাপ হিসাবে তাদের ধর্মগ্রন্থ নারদীয় পুরাণে উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর দশাবতারে যে বুদ্ধকে একজন হিসাবে সংযোজন করেছে, সেই বিষ্ণুপুরাণে বৌদ্ধদের ‘মহামোহ হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানে বৌদ্ধদের সঙ্গে কথা বললে পাপ”-কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে— “যারা, এমনকি বৌদ্ধ শ্ৰমণদের সঙ্গে কথা বলবে, তাঁদের নরকে যেতে হবে।”
কুশিনগরে গৌতম বুদ্ধ মারা যান। সেই কারণে এটি বৌদ্ধদের কাছে একটি তাৎপর্যপূর্ণ স্থান। এই নামকরা শহরের চাকচিক্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্রাহ্মণরা এই কুৎসা রটায় যে, এই শহরে মৃত্যু হলে সে সরাসরি নরকে চলে যাবে কিংবা পরজন্মে গাধা হয়ে জন্মাবে। কিন্তু ব্রাহ্মণীয় পবিত্র নগর কাশিতে মৃত্যু হলে সে সরাসরি স্বর্গে চলে যাবে। নরেশ কুমার বলেন, “বুদ্ধের নাম কলুষিত করার পাশাপাশি এহেন ব্রাহ্মণ্য পুনর্জাগরণবাদীরা নিরপরাধ বৌদ্ধদের নিপীড়ন কিংবা এমনকি মেরে ফেলার তাগিদ হিন্দুরাজাদের দিতে থাকেন। বাংলার শৈব ব্রাহ্মণরাজা শশাঙ্ক শেষ বৌদ্ধ সম্রাট হর্ষবর্ধনের বড়ো ভাই রাজ্যবর্ধনকে ৬০৫ সালে হত্যা করেন। শশাঙ্ক বোধিগয়াতে গিয়ে পবিত্র বোধিবৃক্ষকে উপড়ে ফেলেন। এই বোধিবৃক্ষ বৌদ্ধদের কাছে পবিত্র স্থান। কারণ এই বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করে গৌতম বোধি প্রাপ্ত হন, বুদ্ধ হন। পাশের বৌদ্ধবিহারে থাকা বুদ্ধের প্রতিকৃতি সরিয়ে ফেলে তার জায়গাতে শিবের প্রতিকৃতি ঝুলিয়ে দেয় শৈবরাজা শশাঙ্ক। শশাঙ্ক কুশিনগরের সব বৌদ্ধভিক্ষুদের নির্বিচারে হত্যা করেন। আর-এক শৈবরাজা মিহিরকুল (মিহিরকুল ছিলেন হুন জাতি। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উসকানিতে কাজটি করেন। পরে কি শিবের উপাসক হয়েছিলেন?) ১৫০০ বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেন। শৈবরাজা তরামন কৌসম্বিতে থাকা বৌদ্ধ মঠ ঘোষিতরাম ধ্বংস করেন বলে জানা যায়। অষ্টম শতকের বিখ্যাত হিন্দু দার্শনিক শঙ্কর বুদ্ধকে ‘জনতার শত্রু’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। শঙ্করাচার্যকে হিন্দু সাহিত্যে বৌদ্ধবাদের পরাজয়ের কারণ হিসাবেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গণহারে বৌদ্ধ, বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্মের নিমূল হওয়াকে ত্বরান্বিত করেছে। বহু বৌদ্ধমন্দির গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে হিন্দুমন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু লিখেছেন— “বোধগয়ার মহাবোধি বিহারকে জোর করে শিব মন্দিরে পরিণত করা হয়েছে। কুশিনগরের বুদ্ধের স্তূপ-প্যাগোড়াকে রমহর ভবানী নামের এক অখ্যাত হিন্দু দেবতার মন্দিরে পরিবর্তিত করা হয়। জানা যায় যে, আদি শঙ্কর অধিকৃত বৌদ্ধ আশ্রমের জায়গাতে হিন্দু শ্রীঙ্গেরী মঠ বানিয়েছিলেন। অযোধ্যার অনেক হিন্দু তীর্থস্থান, যেমন সবরীমালা, বদ্রীনাথ কিংবা পুরীর মতো প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মন্দির আদতে একসময় বৌদ্ধমন্দির ছিল।” স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দও এই ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন– “জগন্নাথ মন্দির একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির। আমরা ওইটিকে এবং অন্যান্য বৌদ্ধ মন্দিরকে হিন্দু মন্দির করিয়া লইয়াছি।”
‘A History of Indian Buddhism’ গ্রন্থের লেখক ইতিহাসবিদ এস, আর, গোয়েল লিখেছেন— ব্রাহ্মণবাদীদের শত্রুতার জন্যেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধবাদের অবলুপ্তি ঘটেছে। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (১৮৫-১৫১ পূর্বাব্দ) বৌদ্ধদের প্রতি প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন। তিনি ধর্মীয় সূত্র লেখনিগুলোসহ বৌদ্ধ প্রার্থনালয় জ্বালিয়ে দেওয়া ছাড়াও অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুকে গণহারে হত্যা করেন। প্রথম সহস্রাব্দীর দ্বিতীয় অংশে বৌদ্ধদের অবস্থা সম্পর্কে আমরা যা জানি তা মূলত এসেছে সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে। যদিও কিছু জায়গাতে বৌদ্ধদের সমৃদ্ধ হতে দেখেছেন, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধবাদকে দেখেছেন জৈন ও ব্রাহ্মণ শক্তির কাছে পরাভূত মৃতপ্রায় সত্তা হিসাবে। চালুক্যদের রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, চালুক্যদের শাসনামলে অন্ধ্র আর পল্লব শাসকদের অনুকূল্যে গড়ে ওঠা অনেক বৌদ্ধ স্তূপ মন্দির পরিত্যক্ত কিংবা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলগুলো বৈষ্ণব-পূর্ব চালুক্যদের শাসনাধীনে আসে, যাঁরা বৌদ্ধদের প্রতি প্রচণ্ড বৈরী ছিলেন। তিনি শশাঙ্ককে একজন ‘বিষাক্ত গৌড় সাপ’ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন, যিনি বাংলায় বৌদ্ধ স্তূপ-মন্দিরগুলো ধ্বংস করেন, আর তাঁর রাজ্যের বৌদ্ধ শ্ৰমণদের মাথার জন্যে একশো স্বর্ণমুদ্রা করে পুরস্কার ঘোষণা করেন। হিউয়েন সাঙ সহ অনেক বৌদ্ধসূত্রগুলোতে থানেশ্বরের বৌদ্ধরাজা রাজ্যবর্ধনের হত্যার জন্যে শশাঙ্ককেই দায়ী করা হয়। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, বোধিগগায়ার বোধিবৃক্ষ কাটা ছাড়াও ওখানকার বুদ্ধের মূর্তিগুলোকে শিবলিঙ্গ দ্বারা প্রতিস্থাপন করেন। লোহারা সাম্রাজ্যের শেষ হিন্দুরাজা হর্ষ (১০৮৯-১১০১) আর একটি ধর্মীয় নিবর্তনমূলক নিয়ম চালু করেন। তিনি একাধারে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠগুলো ধ্বংস করা শুরু করেন। দ্বিতীয় লোহারা সাম্রাজ্যের সময় (১১০১-১১৭১) অবশ্য রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় দুটি ধর্মই পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। “The Decline and Fall of Buddhism” বইতে ডক্টর কে, জামানদাস জানিয়েছেন যে, দুটো বুদ্ধের মূর্তি হর্ষের ধ্বংসাভিযানের হাত থেকে বেঁচে যায়, তা রাজা জয়সিংহের (রাজত্ব ১১২৮-১১৪৯) আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তা ছাড়াও শ্রীনগরের কাছে আরিগোনের বৌদ্ধবিহার আগুনে ভস্ম করে দেওয়া হয়।
সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতকে যখন ইসলাম দক্ষিণ এশিয়ায় আগমন করে তখন থেকেই এটি হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মকেই উদার ও বিশ্বজনীন ধর্ম হিসাবে প্রতিস্থাপন করে ফেলে। আগে যেভাবে বলা হল, মধ্য এয়োদশ শতকে বাগদাদে হুলাগু খানের গণহত্যা ও ধ্বংসলীলার কারণে অনেক মুসলিমই তুলনামূলক ঝামেলাবিহীন জায়গাগুলোতে আশ্রয় খুঁজছিল। অনেকেই ভারতবর্ষকেই পছন্দ করে নেন। খালি হাতে আসেননি কেউ। সঙ্গে নিয়ে এসেছিল উন্নততর নৈতিক শিক্ষা ও তার প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে সুফি শিক্ষা ভারতীয় জনগণকে ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে প্রণোদিত করে। সুফি সাধকদের প্রভাব, বর্ণপ্রথার চাপ এবং সেইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনকে রুখে দেওয়ার মতো রাজনৈতিক শক্তির অভাবে বাংলাতে সবচাইতে বেশি লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য।
যাঁদের আমরা হিন্দুবাদী বলি তাঁরা আসলে নির্দিষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদী। যবনদের ঘৃণা করার অভ্যাস এঁদের অনেক পুরোনো অভ্যাস। মুসলিম শাসনের ৮০০ বছরে তাঁরা এঁটে উঠতে পারেনি। মুসলিমদের এক হাতও নিতে সক্ষম হয়নি। রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য পেতেই তাঁরা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়।
৮০০ বছরের মুসলিম শাসকদের মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ওই ৮০০ বছরে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কিন্তু শূদ্র, অন্ত্যজ, দলিতদের উপর ধারাবাহিক অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে গেছে। কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে কখনোই দ্বন্দ্বে জড়ায়নি। বরং মুসলিম শাসকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে থেকেছে। হয়তো শক্তিহীনতার কারণেই। এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই ভারতকে সেইরূপে পেতে চায়– যে ভারতে শূদ্র থাকবে না, দলিত থাকবে না, বৌদ্ধ থাকবে না, জৈন থাকবে না, শিখ থাকবে না, মুসলিম থাকবে না, এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক হিন্দুরাও থাকতে পারবে না। এই উপমহাদেশে থাকবে কেবল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। এই সংগঠন যে ‘হিন্দুরাষ্ট্র’ চায়, তা আসলে ব্রাহ্মণবাদীদের রাষ্ট্র, সে রাষ্ট্রে উচ্চবর্ণ ছাড়া আর কেউ থাকতে পারবে না।
১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পর থেকেই ব্রিটিশরা উপলব্ধি করতে পেরেছিল হিন্দু-মুসলিমকে একে অপরের জন্মশত্রু বানিয়ে ফেলতে পারলেই এ দেশে নিরঙ্কুর শাসন করা সম্ভব। ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরবে, আমরা তখন নির্বিঘ্নে এ দেশ থেকে সব লুঠ করে ব্রিটেনে নিয়ে যেতে পারব। সেজন্য চাই ‘Divide & Rule’। এই কৌশলটা প্রথম মাথায় এলো লর্ড এলগিন স্টোনের, ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে। এরপর ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত সচিব উড ভারতের বড়োলাট লর্ড এলগিনকে এক চিঠিতে লিখছেন –“এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লড়িয়ে ভারতে ক্ষমতা কায়েম রাখতে হবে।… সুতরাং সকলের সম্মিলিত চেতনা জেগে ওঠার পথে বাধা সৃষ্টির জন্য যা পারেন দ্রুত করুন।” ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের এই রাজনৈতিক প্রয়োজনটা মেটানোর জন্য হাজির হয়ে গেল উগ্র হিন্দুবাদী গোষ্ঠী। সেই গন্ধটা ব্রিটিশরা ভারতেই ঢুকেই বোধহয় পেরে গিয়েছিল। ১৮৭৩ সালে অমৃতসরে ‘শ্রীগুরু সিং সভা’ এবং ১৮৭৫ সালে বোম্বে (অধুনা মুম্বাই) শহরে ‘আর্য সমাজ’ নামে দুটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটল। হ্যাঁ, এই দুটি সংগঠন প্রথমে হিন্দু মহাসভা ও পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার জ্বণ হিসাবে কাজ করেছিল। সে সময় কোহট, বানু, মদলতাল, নাগপুর, কানপুর সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় নিজেরাই আজকের দিনের মতোই কৌশল অবলম্বন করে দাঙ্গা সংঘটিত করত। লুঠতরাজ ও মানুষ হত্যা করত। এর ফলে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দুদেরও মৃত্যু হত। লুঠতরাজ, হত্যাকাণ্ড চালিয়ে সেই দায় শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হত, এখনকার মতোই। এই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নিজস্ব প্রচার মাধ্যমে তাঁদের অন্যতম জন্মদাতা হেডগেওয়ারকে উদ্ধৃতি করে বলা হচ্ছে– “.. এগুলি হিন্দু-মুসলিমের দাঙ্গা নয়। তিনি (হেডগেওয়ার) বলতেন, এগুলি মুসলিমদের দাঙ্গা। কারণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারাই দাঙ্গা করে এবং আক্রমণ করে।”
ইতিহাসকে বিকৃতি করা এদের মজ্জাগত অসুখ, সৃষ্টির জন্মলগ্ন থেকেই। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও হিন্দুদের পক্ষে ইতিহাসের বিকৃতি করা এঁদের ফ্যাসিস্ট পলিসি। অর্থাৎ মুসলিম শাসক মানেই অত্যাচারী, খুনী এবং হিন্দুশাসকরা সকলেই মহান, দয়ালু। বিকৃতি শুরু হয়েছিল মুসলিমদের মোপলা বিদ্রোহ দিয়ে। অত্যাচারী ব্রিটিশদের পক্ষে বয়ান দিল এঁরা, যা মুসলিম বিদ্রোহীদের বিপক্ষে গেল। এই বিদ্রোহ নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বক্তব্য কী ছিল? রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বলেছিল বিদ্রোহ নয়, ওটা দাঙ্গা ছিল –“এই দাঙ্গার পরিণতি মোপলাদের নৃশংস অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ, লুঠ, হত্যা, ধর্ষণ এবং জোর করে ধর্মান্তরিত করা।” মুসলিমদের যে মোপলা বিদ্রোহ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, সেই বিদ্রোহ কেন হয়েছিল? মোপলা শব্দের অর্থ রায়ত। রায়ত হল রাষ্ট্রের প্রজাসাধারণ ও শাসকশ্রেণির অধীনস্থদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হত। মোগল ও ব্রিটিশ শাসনকালে প্রথাগত ও আইনসম্মতভাবে কৃষককুলকে বলা হত। রায়ত মূলত একটি আরবি শব্দ ‘রঈয়াৎ’ থেকে উদ্ভব হয়েছে। মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় রায়ত ছিল একজন চাষি। মালায়লাম ভাষায় মাপ্পিলা লাহালা বা মোপলা।
সুদূর অতীতে আরব দেশ থেকে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলে মোপলারা বসতি স্থাপন করে। তাঁদের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষিকাজ। জমিদারদের কাছে বর্গাভিত্তিক চাষাবাদ করত মোপলারা। মহিশুর সুলতানদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধেও মোপলাদের সংগ্রামের কথা ‘ডিউক অফ ওয়েলিংটন’-এর জীবনী থেকে জানা যায়। কেরল রাজ্যের অধিবাসী দরিদ্র মোপলাদের উপর শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার ও আক্রমণই এই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। মোপলারা মূলত সমুদ্র উপকূলবর্তী মালাবার অঞ্চলের কৃষিজীবী। জমিদারের খাজনা, মহাজনের ঋণের অত্যাচার সব মিলিয়ে তীব্র অসন্তোষ দীর্ঘস্থায়ী মোপলা বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছিল একাধিক সময়ে (১৮৭৩-১৮৯৬)। মালাবারের ওয়ালুভানাদ ও এরনাদ তালুক জুড়ে দশ লক্ষ মোপলা চাষি সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে মোপলারা প্রাথমিকভাবে পরাজিত হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেও বিভিন্ন সময় চোরাগোপ্তা আক্রমণ ও গেরিলা যুদ্ধে আঘাত হানতে থাকে। ১৮৮৫ সাল নাগাদ দ্বিতীয় মোপলা বিদ্রোহ হয়, যা দমন করতে ব্রিটিশ সরকার ৩০০০ সৈন্য ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিযুক্ত করে। দ্বিতীয় বিদ্রোহ দেড় বছর স্থায়ী হয়। আবারও বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটে। তাঁদের নির্মম ভাবে দমন করা হয় পিটুনি কর’ বসিয়ে ও দ্বীপান্তর পাঠিয়ে। ১৮৯৪ সালে তৃতীয় মোপলা বিদ্রোহ এবং ১৮৯৬ সালে চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহ ঘটে। সবকটি বিদ্রোহই কঠোর ও নির্মম হাতে দমন করা হয়। চতুর্থ মোপলা বিদ্রোহে ভীত শাসকগোষ্ঠী জমিদারদের বর্ধিত খাজনা ও মহাজনদের সুদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, যদিও সামন্ত শ্রেণি তাঁদের বহু উপারে শাসন শোষণ অব্যাহত রেখেছিল।
১৯২১ সালে মোপলারা মালাবারকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন এবং স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়ে দেন। ব্রিটিশ সরকার মালাবারে অসংখ্য সৈন্য, ছোটোবড়ো ট্যাংক, কামান, বোমা, কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ পাঠায়। প্রথমদিকে কয়েকজন অত্যাচারী জমিদার মহাজন জনরোষে প্রাণ হারায়। ব্রিটিশ সরকার কৌশলগতভাবে একে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে এবং সফলও হয়। ব্রিটিশ অ্যানি বেসান্ত (এই ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ অ্যানি বেসান্ত পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পদ ছিলেন) বয়ান দিলেন –“মুসলিম মোপলারা অনেক হিন্দুকে জোর করে ধর্মান্তরিত করে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করে। অনেক হিন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, এদের মোট সংখ্যা ১০০,০০০।” দেশের এলিট বুদ্ধিজীবী মহলের বৃহৎ অংশ মোপলাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার প্রসঙ্গে নীরব থাকলেন। বিদ্রোহীরা একমাস যুদ্ধ চালালেও ব্রিটিশ সরকার মোপলা এলাকার উপর আকাশ থেকে বোমা, রণতরী ও কামান থেকে নির্বিচারে গোলাবর্ষণ করে প্রায় ১০,০০০ সাধারণ মানুষ হত্যা করে, তাঁদের বাড়িঘর, দোকান-পাট ও ক্ষেতখামার ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। ধরপাকড়, পৈশাচিক অত্যাচার ও নির্যাতনের ফলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রায় ১০০ মোপলা প্রজাকে গ্রেফতার করে একটি মালগাড়িতে বোঝাই করা হয় এবং দরজা বন্ধ করে তাঁদেরকে কালিকট প্রেরণ করার সময় হয় ৬০ জনের মৃত্যু হয়।
মোপলা বিপ্লবীদের একশো ভাগই ছিল মুসলমান। যেহেতু সেখানকার রাজা-মহারাজা-জমিদাররা বারেবারে ব্রিটিশদের পক্ষে সাহায্য করে এসেছেন, তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বিপ্লবী মোপলা বাহিনী হিন্দু বিত্তবানদেরও শত্রু মনে করতে দ্বিধা করেনি। উপেক্ষিত শোষিত অনুন্নত নিম্নশ্রেণির অ-মুসলমানরা প্রতিবারেই মোপলাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা করলেও নেতৃস্থানীয় ধনী মধ্যবিত্তদের কৌশলময় প্রচারে তাঁদের বোঝানো সম্ভব হয়েছিল যে ওটা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই। তাই অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের অপব্যবহারের ফলে নীল বিদ্রোহের মতো মিলিত হিন্দু-মুসলমান একত্রিত সংগ্রাম হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন এবং মাওলানা মোহাম্মদ আলিদের খেলাফত আন্দোলনেও ওই মোপলা বাহিনী সাড়া দিতে ভোলেনি। ব্রিটিশ সরকার সারা ভারতে যা করেনি তা করেছে মোপলাদের বিরুদ্ধে।
এটা ইতিহাস। যেটা বিকৃতি ইতিহাস, তা হল হিন্দুদের জোর করে ধর্মান্তরিত করা। এই মোপলা বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়দের এইভাবে নৃশংস হত্যাকে যেভাবে ভাবাতে চেয়েছিল, সেভাবেই ভাবতে সাহায্য করেছিল হেডগেওয়ার ও আরএসএস। এঁরা কেউই ব্রিটিশদের এহেন হত্যাকাণ্ডের তীব্র বিরোধিতা করা তো দূরের কথা, উলটে ভারতীয় মুসলিমদেরই কাঠগোড়ায় তুলে দিল। হেডগেওয়ার ও আরএসএসদের অনুপ্রেরণায় ১৮৮৭ সালে ভারত সচিব লর্ড ক্রুস লিখলেন –“ধর্মের ক্ষেত্রে এই বিভেদের মনোভাব আমাদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে খুবই অনুকূল।” ১৯২৫ সালে ভারত সচিব বার্কেন হেড বডোলাট লিখলেন– “সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চিরস্থায়ী হোক, সবসময়ে সর্বান্তকরণে আমি এই আশা করছি।”
নাগপুরে আরএসএসের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন হেডগেওয়ার, এ বি এস মুঞ্জে, ড. এল ভি পরাঞ্জপে, ড. বি বি পলকর এবং বাবুরাও সাভারকর (বিনায়ক দামোদর সাভারকরের ভাই)। হেডগেওয়ার ছাড়া বাকি চারজনেরই হিন্দু মহাসভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল। হিন্দু মহাসভা ছাড়াও আরএসএসের জন্মলগ্নে আমাদের দেশে আরও বেশ কয়েকটি হিন্দু সম্প্রদায়ের সংগঠন ছিল। যেমন –হিন্দু স্বয়ংসেবক সমিতি, হিন্দু সংরক্ষণ সমিতি ইত্যাদি। এই সংগঠনগুলির সঙ্গে এ বি এস মুঞ্জে, ড. এল ভি পরাঞ্জপেদের বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁরা ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির ক্রিয়াকর্মের ব্যাপক সমর্থক ছিল। ফ্যাসিস্ট মুসোলিনির ক্রিয়াকর্মের একেবারে সূচনাপর্ব থেকেই মূলত মহারাষ্ট্রকে (দেশভাগের আগে এবং অনেক পরে মহারাষ্ট্র নামে কোনো প্রদেশ ছিল না। ১৯৬০ সালে বোম্বে দু-টুকরো হয়ে দক্ষিণাংশ মহারাষ্ট্র ও পশ্চিমাংশ গুজরাট প্রদেশ সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র করে যাঁদের হিন্দু জাতীয়তাবাদী চিন্তাচেতনার জন্ম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে মুসোলিনিকে ঘিরে একটা বড়ো রকমের আগ্রহ লক্ষ করা যায়। আরএসএসে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এ বি এস মুঞ্জের সঙ্গে মুসোলিনির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ১৯৩১ সালে মুঞ্জে ইটালিতে সফর করেন এবং ইটালির বেশকিছু সামরিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। যুবসম্প্রদায়ের মগজ কীভাবে বৈজ্ঞানিকভাবে ধোলাই করতে হবে এখান থেকেই শিখে নেন। আরএসএসের জন্মের আগের বছর থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত কেশরী’ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে ইতালির ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনির সম্পর্কে ইতিহাস প্রবন্ধ লেখা হত। ১৯৩৫ সালের পর ফ্যাসিবাদ এবং মুসোলিনির সম্পর্কে কেন আর ইতিবাচক প্রবন্ধ লেখা হল না? কারণ তখন বিশ্বের পরিস্থিতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তের থমথমে, আরএসএসের পরম বন্ধু ব্রিটিশের শত্রুপক্ষ ইতালি এবং অক্ষশক্তির দেশগুলি। বন্ধুর শত্রু হলে কি আমার বন্ধু হতে পারে?
পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত ‘পাঞ্জাবি’ পত্রিকায় হিন্দুদের কীভাবে দেশ গড়তে হবে, সে বিষয়ে জনৈক ব্যবসায়ী aloin se pot facena– “This can only be achieved by asserting-purely Hindu interest, and not by an Indian Propaganda. The consciousness must arise in the mind of each Hindu that he is a Hindu, and not merely an Indian and when it does arise the newly awakened force is bound to bring its result.” (এটি কেবল নির্ভেজালভাবে হিন্দুস্বার্থের দাবিতে অর্জন করা সম্ভব, কোনও ভারতীয় প্রচারের দ্বারা নয়। প্রতিটি হিন্দুর মনে এই চেতনা জাগ্রত হতে হবে যে, তিনি কেবল ভারতীয় নন, তিনি একজন হিন্দু এবং যখন উত্থিত হবে সদ্য জাগ্রত শক্তি, তার ফলাফল আনতে বাধ্য।)
আরএসএস সংগঠনের ‘বিদ্যাভারতী’ এই ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলির ভাবাদর্শেই তৈরি করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট এই সংগঠনগুলিতে ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি শিশু-কিশোরদের নেওয়া হয়। তাঁদের নানা প্রকারের শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আধা-সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের কুচকাওয়াজ ছিল বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ আরএসএসের প্রশিক্ষণে যে সমস্ত রীতিনীতি অবলম্বন করা হয়, সেগুলি মূলত ফ্যাসিস্ট সংগঠনগুলি থেকেই ধার করা। ১৯২২-২৪ সালে রামচন্দ্র রাদুর নেতৃত্বে অন্ধ্রের কয়া উপজাতির মানুষরা ঔপনিবেশিক সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। ব্রিটিশ শাসকদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করে দিয়েছিল তাঁরা। আইনসভার ভিতরে ঔপনিবেশিক ভিত প্রায় টলিয়েই দিয়েছিল। ১৯২৩ সালে পাঞ্জাবের আকালিরা ও সত্যাগ্রহীরা জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার জন্য নাগপুরে সমবেত হয়েছিল। এই সমাবেশও ঔপনিবেশিক প্রভুদের হৃদয়ে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা হেডগেওয়ারকে নাগপুরেই আরএসএসের জন্মদানের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করল। ১৯২৭ সালে আরএসএস স্বয়ংসেবকদের জন্য একটা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করল। লাঠি, তরবারি, বর্শা চালানোর প্রশিক্ষণ। না, আরএসএসের এই সশস্ত্র প্রশিক্ষণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে নয়, এই প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বিরোধী স্বদেশি ও মুসলিমদের হত্যা করা। একই সঙ্গে ব্রিটিশদের তোয়াজ করা। প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯২৭ সালেই একটি দাঙ্গা সংঘটিত হল। ১৯২৭ সালে এই নাগপুরের দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে আরএসএসের ভারতীয় সমাজজীবনে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, প্রাদেশিকতার বিষবৃক্ষ রোপণের সূচনা। এই দাঙ্গায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়ে মুসলিম নিধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে নাগপুর এবং তার সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এই সংগঠনটির যাত্রা শুরু। গোটা দেশে তখন ঝড়ের পূর্বাভাস স্পষ্ট। এই পূর্বাভাসের লক্ষণ দেখেই জাতীয়তাবাদকে হিন্দুত্বের মোড়ক দিয়ে দেশের নানা প্রান্তে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক মিত্রেরা কাজ শুরু করে দিল।
কখনো ব্রিটিশরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আরএসএসের দিকে, কখনো আরএসএস সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রিটিশদের দিকে। ক্রমশ একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রথম পর্বের ব্রিটিশ বিরোধী কৃষক আন্দোলনগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদ লক্ষ করা যায়নি। এমনকি ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই মহাবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহ নির্মূল করতে শুধুমাত্র দিল্লি শহরেই ২৭,০০০ ভারতীয় মুসলিম বিপ্লবীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল (আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস –সিদ্ধার্থ গুহরায় ও সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৩০)। ইতোমধ্যে ব্রিটিশরা উপলব্ধি করল হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হলে এদেশে ব্রিটিশ শাসনের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। সেই কারণে ১৮৭০-এর দশক থেকে ব্রিটিশদের দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সম্ভাবনা দূর করতে ব্রিটিশ সরকার লোক দেখানো মুসলিম তোষণ করতে শুরু করে দেয়। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৃদ্ধি করার জন্য এটি একটি কৌশল ছিল। এর ফলে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের অতি দ্রুত ক্ষেপিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার আরএসএসের সক্রিয়তার আরও বলব পরে। তার আগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার ব্রিটিশপ্রভুদের অবদানের কথা জেনে নেব, যে বিষবৃক্ষের ফল উভয় সম্প্রদায় আজও সেবন করে চলেছি। স্যার জন স্ট্রাচে এসময় লিখছেন –“ভারতে পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে একটি দারুণ সুবিধা।” মাউন্টস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোন ব্রিটিশ সরকারকে পরামর্শ দেন– “প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের প্রধান নীতি ছিল ‘বিভাজন ও শাসন’, আমাদের এই নীতি গ্রহণ করা উচিত।” ১৯০১ সালে বড়োলাট লর্ড কার্জন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করলেন– “যতদিন আমরা ভারত শাসন করব, ততদিন পর্যন্ত আমরা হলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তি।” এই শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম রাখতেই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যকে নিরাপদ, নিরঙ্কুশ ও দীর্ঘস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার জাতিতে জাতিতে বিভেদ, ভাষায় ভাষায় বিভেদ এবং ধর্মে ধর্মে বিভেদ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়। এই অসুখগুলো ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী তথা উচ্চবর্গীয়দের আদি থেকেই ছিল, ব্রিট্রিশরা কেবল সুচারুভাবে সেই আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছিল।
ভারতের সমাজব্যবস্থায় কিছু কিছু হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় চেতনার এগিয়ে এসেছিল শুরুর দিকে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের মুসলিম ও অন্যান্য অ-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সরকার তাঁদের উৎসাহিত করে। এভাবে তাঁরা হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে, এমনকি বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বিরোধ ও বিভেদ বৃদ্ধি করে ব্রিটিশ বিরোধীকে দুর্বল করার চেষ্টা করে গেছে, সফলও হয়েছে অনেকক্ষেত্রে।
শুরু হয়ে গেল লোক-দেখানা তীব্র তোষণনীতি। ভারতের ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তাতে মূলত তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়– (১) ব্রিটিশরা প্রথমে মুসলিমদের আধিপত্য ধ্বংস করে ভারতে সাম্রাজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল। এছাড়া প্রথমদিকে ব্রিটিশ প্রশাসনের নিম্নস্তরের বিভিন্ন পদে কাজের জন্য শিক্ষিত হিন্দু-ব্রাহ্মণরা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই এই পর্যায়ে ব্রিটিশরা হিন্দুদের প্রতি সদয় ছিল। (২) প্রশাসনে হিন্দু ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের আধিপত্য কিছুদিনের মধ্যেই ব্রিটিশদের নজরে আসে। স্যার উইলিয়াম লি নামে জনৈক উচ্চপদস্থ ব্রিটিশকর্তা ১৯০০ সালে লক্ষ করেন ১৮৬৯ থেকে ১৮৯৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং ব্রিটিশ প্রশাসনে হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়েছে। এতটাই যে মনে হচ্ছে ব্রাহ্মণরাই দেশ পরিচালনা করছে, ব্রিটিশরা নয়। আবার ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ব্রাহ্মণরাই অগ্রভাগে থাকে, এটাও সরকারের নজরে আসে। দেখা গেল ব্রিটিশ বিরোধী কংগ্রেস দলে এবং অ্যানি বেসান্তের হোমরুল আন্দোলনেও ব্রাহ্মণরাই অগ্রভাগেই আছে। তাঁরাই সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্ররোচনা দিচ্ছে বলে ব্রিটিশরা মনে করতে থাকে। এই প্রেক্ষাপট থেকেই ব্রিটিশরা লোক-দেখানো মুসলিম তোষণ করতে শুরু করে দিল। এর ফলে ব্রিটিশ-ভারতীয়দের সংগ্রামের পথ ঘুরে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সংগ্রামে পরিণত হতে খুব বেশি সময় লাগল না। মুসলিমদের শিক্ষা প্রসঙ্গে স্যার ডব্লিউ এইচ গ্রেগরি ১৮৮৬ সালে লর্ড ডাফরিনকে লেখেন– “আমি নিশ্চিত যে, মুসলিমদের শিক্ষার প্রসার ব্রিটিশ সরকারের কাছে খুবই ফলদায়ক হবে। শিক্ষিত মুসলিমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বাবুদের আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে। মুসলিমদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতে মুসলিমরাই ছিল রাজশক্তি। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে হিন্দু সম্প্রদায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা। এটা বুঝিয়েই ব্রিটিশ সরকার মুসলিমদের তোষণ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁদের ব্যবহার করে। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা টোপ ফেলল। সেই টোপ গিলল আলিগড় আন্দোলনের নেতা ‘স্যার সৈয়দ আহমদ। এইসব ‘স্যার’ ‘প্রিন্স’, ‘রাজা’ উপাধি পাওয়া যেত সফলভাবে ব্রিটিশদের চামচাগিরি করলেই, ব্রিটিশরা আহ্লাদিত হয়ে দিত। সেই ‘স্যার’ উপাধি পেয়ে তাঁরা সমাজের ‘প্রভু’ হয়ে পড়তেন। সৈয়দ আহমদও ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৮৭৫ সালে আলিগড়ে ‘অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটা অবশ্যই একটা উত্তম কাজ। অধম কাজটিও শুরু হল এই কলেজ থেকেই। এই কলেজের আর্চিবোল্ড, থিওডোর, বেক, মরিসন প্রমুখ ব্রিটিশ-খ্রিস্টান অধ্যক্ষ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মুসলিমদের মনে বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতার মনের ভিতর বিষ ঢুকিয়ে দিতে থাকল। (৩) ব্রিটিশ সরকার হিন্দু উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের পাশাপাশি পিছিয়ে-পড়া হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোকেও তোষণ করতে শুরু করে।
বহিঃশক্তি ব্রিটিশদের হাতের কাছে পেয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, বি আর আম্বেদকরদের মতো মানুষরাও বাণী ছাড়তে শুরু করে দিলেন। দু-একটা নমুনা একটু দেখে নিতে পারি। জ্ঞানযোগে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন– “মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কী দেখা যাচ্ছে? কোনো অ-মুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তাঁর গলা কাটা যাবার সম্ভাবনা দেখা যাবে।” বাবা সাহেব আম্বেদকর লিখলেন– “ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাঁরা বাইরে তাঁদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।”(Pakistan or Partition of India, Government of Maharashtra Publication, 330) পাশাপাশি মুসলিম নেতারাও কী বলছেন জেনে রাখা প্রয়োজন এই পরিপ্রেক্ষিতে। পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক আনোয়ার শেখ লিখলেন –“মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালোবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অ-মসুলমানদের প্রতি ঘৃণা। অ মুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অ-মুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য।”(Islam : The Arab Imperialism) অনিরুদ্ধ জ্ঞানশিখা ওরফে আনোয়ার শেখ, যিনি তাঁর প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের বেশিরভাগ সময় যুক্তরাজ্যে কাটিয়েছেন। ওয়েল্ড কার্ডিফেই মারা যান ২০০৬ সালে। Practical Vedanta’ গ্রন্থে বিবেকানন্দ লিখছেন– “তাহাদের (মুসলিমদের) মূলমন্ত্র আল্লা এক এবং মোহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হবে; যে-কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে, যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে-কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকার দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।”
শুধু বিবেকানন্দ, আম্বেদকর, আনোয়ার শেখরাই নয়–ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী জুড়েই এ ধরনের বিষময় লেখালেখি চলছিলই। লেখক-মনিষীদের একমাত্র উপজীব্য হয়ে উঠছিল সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প তৈরি করা। উভয় সম্প্রদায়ের এলিট মানুষদের লাগাতার এই প্রয়াসের ফলে অবশেষে আমরা হাতে উঠে এলো ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’। আসব আমরা সে কথায়। তার আগে আরএসএস নিয়ে সামান্য কিছু বলা বাকি আছে, সেটুকু সেরে নিই। হিন্দু মহাসভার কথাও আসবে।
ভারতীয় রাজনীতির মঞ্চে প্রবেশ করলেন মারাঠি জাতি বিনায়ক দামোদর সাভারকর। সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন নিয়ে তিনি তখন মাঠ কাঁপিয়ে দিচ্ছেন। শুধু মাঠ কাঁপাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর প্রথম টার্গেট হিসাবে বেছে নিলেন নিজামশাসিত হায়দ্রাবাদকে। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গোটা ভারত উপমহাদেশে যখন ব্রিটিশ শাসন কায়েম করে ফেলেছে, শেষ পর্যন্ত দুটি অঞ্চলের শাসন শর্তসাপেক্ষে মুসলিম শাসকদের হাতেই ছিল। একটি হায়দ্রারাবাদ, অপরটি জুনাগড়। কাশ্মীরের মতো বেশকিছু অঞ্চল হিন্দু শাসকদের দখলেই ছিল দেশীয় রাজ্য হিসাবে। হায়দ্রাবাদ ও জুনাগড় ছিল হিন্দুসংখ্যাগরিষ্ট জনগণের অঞ্চল, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠের অঞ্চল ছিল কাশ্মীর। একে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল তায় মুসলিম শাসক, একি সহ্য হয় সাভারকরের মতো মুসলিম-বিদ্বেষী নেতাদের! হিন্দুদের শাসন করবে একজন মুসলিম! অতএব রাজনৈতিক মুখোশ পরে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার বিষকে সমাজজীবনে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হলেন সাভারকর।
“ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে, অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে”– রবীন্দ্রনাথের এই বাণী সেদিনের মতো আজকেও ততটাই সত্য। নিজামশাসিত হায়দ্রাবাদে সাভারকর সত্যাগ্রহের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানো কাজ শুরু করে দিল। কংগ্রেসের একাংশ সেই ফাঁদে পা গলিয়ে দিয়েছিল। কংগ্রেসের হায়দ্রাবাদ শাখা এই আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ভূমিকা পালন করল। কংগ্রেস সদস্যরা শোলাপুর, পান্ধারপুর, ধুলিয়া ইত্যাদি অঞ্চলে সভার আয়োজন পর্যন্ত করল। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ ক্যাম্প প্রকাশ্যেই সাভারকরের হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহ শিবির গঠনকে স্বাগত জানাল। হায়দ্রাবাদ হিন্দু সত্যাগ্রহ মণ্ডলের সর্বগ্রাসী প্রকোপ থেকে তাঁরা কেউই মুক্ত হতে পারল না। কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা কি বুঝতে পারেনি সাভারকরের উদ্দেশ্য? কংগ্রেসিরা কিন্তু মোটের উপর সাম্প্রদায়িক চরিত্রের বিরোধীই ছিলেন।
১৯৩৯ সালের ১০ সেপ্টেম্বর হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সমিতির জরুরি বৈঠক ডাকা হল। বৈঠকে ঠিক হল হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক এবং জেলস্তরের শাখাগুলির মাধ্যমে ‘হিন্দু মিলিটারি অ্যাসোসিয়েশন’ গড়ে তোলা হবে। এটা কোন্ সময়? যখন গোটা বিশ্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মুসোলিনির নির্দেশিত যে পথে আরএসএস ধীরে ধীরে এগোচ্ছিল। হিন্দু মহাসভাও ঠিক সেই একই পথে হাঁটতে শুরু করল। ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আগ্রাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। সাভারকরের এই সামরিকীকরণ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা একটা মাত্রা লাভ করে। ১৯৪০ সালে মাদুরাই হিন্দু মহাসভার এক বার্ষিক অধিবেশনে হিন্দুত্বের সামরিকীকরণের উপরে সাভারকর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। এই অধিবেশন আরএসএসের বহু নেতাও উপস্থিত ছিল। ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীর ভারতীয় হিন্দু যুবকরাও উৎসাহী পড়ে পড়ল। সাভারকর মনে করতেন ব্রিটিশরা পাকাপাকিভাবে এই দেশ থেকে চলে গেলেই ক্ষমতা দখলের জন্য হিন্দু-মুসলিমের সংঘাত সৃষ্টি হবে। তেমন হলে সেই সংঘাতের জন্য সবরকমভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে হিন্দুদের।
সে সময় হিন্দু মহাসভা ও আরএসএসের পক্ষ থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সাভারকরের সংবর্ধনার আয়োজন করা হত। সেইসব সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে যেমন গঠনমূলক বক্তৃতা দিত, পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম বিষয়েও বিস্ফোরক কথা বলত, যা সম্প্রীতি নষ্ট করার চূড়ান্ত বাহক ছিল। এ বিষয়ে ১৯৩৮ সালে হিন্দু মহাসভার নাগপুর অধিবেশনে তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশ তুলে দিলাম –“It could not be wished away or overcome by compromise. The only way to treat it was to recognise that all India was Hindusthan, the land of the Hindus, at once heir fatherland and holy land, that there was only one nation in India, the Hindu nation; and that the Moslems were only a minority community, and as such must their place in a single Indian state. They would be treated justly, for no distinction would be made on ground of race or faith. All citizens at the state would be equal : One man one vote would be the general rule; such matters as the national language would be settled as in other democratic countries by the will of the majority.” (সমঝোতা হয়ে এটি কাটিয়ে উঠতে বা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এটির চিকিৎসা করার একমাত্র উপায় ছিল এই স্বীকৃতি দেওয়া যে, সমস্ত ভারতবর্ষই হিন্দুস্থানের দেশ, একসঙ্গে উত্তরাধিকারী পিতৃভূমি এবং পবিত্র ভূমি, যে ভারতে একমাত্র জাতি ছিল হিন্দু জাতি; এবং মুসলিমরা কেবল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তাঁদের অবশ্যই একটি একক ভারতীয় রাজ্যে স্থানে থাকতে হবে। তাঁদের ন্যায্য আচরণ করা হবে, কারণ জাতি বা বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনো পার্থক্য করা হবে না। রাজ্যের সমস্ত নাগরিক সমান হবে : এক পুরুষের একটি ভোট সাধারণ নিয়ম হবে; জাতীয় ভাষার মতো বিষয়গুলিও অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছায় নিষ্পত্তি করা হবে।)
১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ১১ অক্টোবর পুনে শহরে ৪০০০ সমর্থকের জমায়েতে সাভারকর বললেন –“ভারতবর্ষে যদি একটা গণভোট নেওয়া হত তাহলে অতি অবশ্যই মুসলিমরা মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যাওয়া আর হিন্দুরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যাওয়াটাকেই পছন্দ হিসাবে মেনে নিত।” গণভোট হয়নি। এরকম গণভোট হলে ঠিক হত, মুসলিমরা মুসলিমদের সঙ্গে মিশে যেত কি না, হিন্দুরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে যেত কি না জানা যেত স্পষ্টভাবে। তাহলে নিশ্চয় হিন্দুশূন্য একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র হত, আর একটি মুসলিম শূন্য একটি স্বতন্ত্র হিন্দুরাষ্ট্র হত। মুসলিমদের জন্য একটি স্বতন্ত্র দেশ দিতেই হত ভারত ভেঙে। মোদ্দা কথা দেশটা ভাগ হতই। বিধ্বংসী চিন্তাধারা! তাহলে যে স্বাধীনোত্তর ভারত হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিটা হত না। বিজেপি নামক ‘রাজনৈতিক দলটার নাম কেউ চিনতেও পারত না। বাবরি মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়েই বিজেপির উত্থান হল। আরএসএসের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যেত কিংবা দলিতদের উপর হামলা করে প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখত। যাই হোক, ওটা বাস্তবিক ছিল না। তাই ও পথ কেউ মাড়ায়নি।
প্রায় ১৯০ বছর ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছিল। লাখো লাখো মানুষের উপর অত্যাচার, ৩০ কোটি মানুষকে গণহত্যা করেছিল। এক মহাবিদ্রোহেই ২৫,০০০ ভারতীয়কে ফাঁসি দিয়েছিল, যাঁরা ধর্ম-পরিচয়ে মুসলিম ছিল। এহেন ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে গোলওয়ালকার, হেডগেওয়ার, মুঞ্জে, সাভারকর তথা আরএসএস, হিন্দু মহাসভার হিন্দুদের ভূমিকা কী ছিল?
আমরা তো চেয়েছিলাম ব্রিটিশমুক্ত একটি নিজেদের দেশ। কিন্তু দাঙ্গায় রক্তস্নাত কেন আমরা? ব্রিটিশদের সুদক্ষ প্রশাসন কেন দাঙ্গা রুখে দিতে পারল না? কেন পূর্বপরিকল্পনা ছাড়াই তড়িঘড়ি ভারত ভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল? হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এত তীব্রতা পেল কীভাবে? কেন ব্রিটিশ প্রশাসন দমন করতে ব্যর্থ হল? হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সব দায় গোলওয়ালকার, হেডগেওয়ার, মুঞ্জে, সাভারকরদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে ভুল হবে। কমিউনিস্ট ছাড়া প্রায় সব সংগঠনই এই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিভোর ছিল। আরএসএসরা ছিল প্রত্যক্ষে, বাকিরা ছিল পরোক্ষে। ভয় একটাই, ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুসলিমরা যদি রাজদণ্ড হাতে নিয়ে নেয়! খুব ভয়ে ভয় ছিল জাতীয় কংগ্রেসও। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পাঁচ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন ‘আনন্দমঠ’, ১৮৮০ সালে। এই আনন্দমঠেই আমরা পেলাম ‘বন্দেমাতরম্’ শব্দটি। লক্ষ দেখুন এই ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনিটি আরএসএস ওরফে বিজেপি এবং জাতীয় কংগ্রেস উভয়রই দলীয় শ্লোগান ধ্বনি। অর্থাৎ একই ভাবনায় জারিত দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন। এই আনন্দমঠ বিপ্লবী আন্দোলনকে অবশ্যই অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে এবং সেইসঙ্গে হিন্দু পুনরুত্থানবাদের জন্মও হয়, যা পরবর্তী সময়ে হিন্দু মৌলবাদী শক্তির মূলমন্ত্র হয়েছিল এবং অবশ্যই সেখান থেকেই প্রেরণা পেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজেও অল্পবিস্তর সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁর প্রতিটি রচনাতেই সেই ছাপ স্পষ্টভাবে রেখেছেন। তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ আনন্দমঠ। এই গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের ক্ষোভ ও রোষকে প্রক্ষিপ্ত করা। তা করতে গিয়ে তিনি দেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে আহত ও ক্ষুব্ধ করে। এই গ্রন্থে মুসলিম প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো সম্পূর্ণ কাহিনি গড়ে ওঠেনি বা কোনো মুসলিম চরিত্র আঁকা হয়নি। কেবলমাত্র নবাব ও মুসলিমদের ধ্বংস করতে সন্তান-সেনাদের মুখ দিয়ে তাঁদের প্রতি বিক্ষোভ অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।
ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা সমাজ-সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়কে হিন্দু মৌলবাদী বলা চলে না। সেই রামমোহন রায় ব্রিটিশদের নিয়ে উঁচু মত পোষণ করতেন। তিনি ব্রিটিশদের ‘পিতা’ ও ‘রক্ষাকর্তা’ মনে করতেন। তিনি বলতেন –“বেনিয়ার এই শাসন ছিল বিধাতার আশীর্বাদ। ইংরেজ ছিল ধর্মের রক্ষক। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহারের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করার আগে, অর্থাৎ মুসলমান শাসনের আমলে মুসলমানদের অত্যাচারে ও নিপীড়নে হিন্দুর ধর্ম পদদলিত হয়েছে, বিশেষত দৈহিক দুর্বলতার কারণে বাঙালির রক্তপাত ঘটেছে বারবার, বাঙালির ধর্ম লাঞ্ছিত হয়েছে, তাঁদের সম্পত্তি লুষ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে বিধাতার অনুগ্রহে ইংরেজ জাতি বাঙালিকে এই অত্যাচারের জোয়াল থেকে মুক্ত করেছে। যদিও তিনি যে ‘রাজা’ উপাধিটা বহন করেছেন সেটা এক মুসলিম শাসকের দেওয়া, ১৮৩০ সালের ১৯ নভেম্বর। তিনি ছিলেন দিল্লির বাদশাহ দ্বিতীয় আকবরের প্রিয়পাত্র। এমনকি মোগলদের পয়সায় মোগল সাম্রাজ্যের দূত হিসাবে যুক্তরাজ্য ভ্রমণ করে আসেন, ফ্রান্সও পরিদর্শন করেন। রামমোহন রায় প্রাক-ব্রিটিশ যুগে, অর্থাৎ ১৮২৩ সালে ‘অসহায় হিন্দুর’ উপর মুসলিমদের অত্যাচারের ইতিহাস প্রচার করেন। বিচক্ষণ ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিমের বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য রামমোহনের এই ইতিহাসচর্চাকে সাদরে গ্রহণ করে নেয়। উনিশ শতকে হিন্দু আইডেন্টিটি’ বা রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদের প্রবেশ ঘটেছে এঁদেরই হাত ধরে। রামমোহনই এই চিন্তার জনক। বঙ্কিমচন্দ্রও একটা ঐক্যবদ্ধ, সুসংহত ও হিন্দু জাতীয়তাবাদভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জাতীয়তাবাদের প্রতিপক্ষ ব্রিটিশরা নয়, মুসলিম। তিনি মনে করতেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের কাছে পরাধীনতাই ভারতের প্রথম পরাধীনতা নয়। দ্বাদশ শতাব্দীতে বখতিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়ের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাহীনতার সূচনা। মুসলিমদের হাতে ৮০০ বছরের পরাধীনতার কলঙ্কমোচনের আকাঙ্ক্ষাই বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ। তাই আনন্দমঠের ভবানন্দ পরাজিত ক্যাপ্টেন টমাসের চুল ধরে বলছেন– “কাপ্তেন সাহেব, তোমায় মারিব না, ইংরেজ আমাদিকের শত্রু নহে।…ইংরেজের জয় হউক, আমরা তোমাদের সুহৃদ।” বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম’ উপন্যাসেও উগ্র হিন্দুয়ানির প্রকাশ পেয়েছে যথাযথভাবেই।
অতএব সাম্প্রদায়িকতার বীজ অনেক গভীরেই প্রোথিত ছিল। আরএসএস সেই বীজে জল-বাতাস দিয়ে বৃক্ষে পরিণত করেছে মাত্র। ধর্মনিরপেক্ষতা’-র পরাকাষ্ঠা যাঁদের ভাবি, সেই জাতীয় কংগ্রেসেও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বীজে জল সিঞ্চন করে গেছে সুচারুভাবে। শুরু করেছিলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা লালা লাজপত রায়, ১৯২৪ সালে। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাই হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরেই। অর্থাৎ কংগ্রেসের শরীরে ব্রিটিশের রক্ত বহমান। কংগ্রেসেও ছিল হিন্দুত্ববাদী সদস্য। তবে এ কংগ্রেস সেই কংগ্রেস নয়। আজকের কংগ্রেস ইন্দিরা কংগ্রেস, একটি রাজনৈতিক দল। ভারতীয় রাজনীতিতে এই আধুনিক উদারনীতিবাদী দলটিকে ‘হিন্দু-বাম’ বলে বিবেচনা করা হয়। ১৮৮৫ সালে থিওজোফিক্যাল সোসাইটির কিছু ‘অকাল্ট’ সদস্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা হলেন অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম, দাদাভাই নওরোজি, দিনেশ এদুলজি ওয়াচা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনমোহন ঘোষ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে ও উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন প্রমুখ। হিন্দু এবং মুসলমান দুই তরফেরই বিভেদ ও বিদ্বেষমূলক কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের ব্যবহার করা দেখে সতর্ক হয়ে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি ১৯৩৪ সালে একটি রেজোলিউশন পাস করে, যার মাধ্যমে কংগ্রেস সদস্যদের আরএসএস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লিগে যোগদান করা নিষিদ্ধ করা হয়। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় কংগ্রেস সংগঠনে এঁরা সদম্ভেই ছিল। আর ঘাপটি মেরে যাঁরা ছিল, তাঁরা কিন্তু রয়েই গিয়েছিল।
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আপাদমস্তক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব হলেও তাঁর দলের (স্বরাজ্য পার্টি) নেতৃত্বের একটা বড়ো অংশ আংশিক সাম্প্রদায়িকতার নিমজ্জিত ছিলেন। গান্ধির ডানা ছাঁটার পরে চিত্তরঞ্জন মুসলিমগরিষ্ঠ বাংলায় ক্ষমতায় আসার জন্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ নামক চুক্তি করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ ১৭ ডিসেম্বর কলকাতায় চিত্তরঞ্জনের ‘বেঙ্গল প্যাক্ট গৃহীত হয়। প্যাক্টে বলা হয়, প্রাদেশিক আইনসভায় সদস্য, পৃথক নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। এবং স্থানীয় প্রশাসনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব হবে যথাক্রমে ৬০ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ। এ ছাড়া সমস্ত সরকারি পদে মুসলমানদের জন্য ৫৫ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকবে। যদিও ওই বছরের ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত কোকনদ কংগ্রেসে এই প্যাক্টকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। পরবর্তীকালে এই প্যাক্টের প্রতিশ্রুতিগুলোকে কীভাবে কাঁচকলা দেখাবেন চিত্তরঞ্জন ও তাঁর অনুগামীরা, কীভাবে ছুরি মারা হবে মুসলমানদের বুকে তারই ছক কষা শুরু হয়ে গেল। বেঙ্গল প্যাক্টের সুবাদে কলকাতা কর্পোরেশন নির্বাচনে স্বরাজ্য দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। মেয়র হন চিত্তরঞ্জন, ডেপুটি মেয়র হন সোহরাওয়ার্দি।
এক শ্রেণির আবেগপ্রবণ বাঙালি যতই হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্র হিসাবে এই বেঙ্গল প্যাক্টকে তুলে ধরার চেষ্টা করুন না-কেন, এই চুক্তি শেষ অবধি মুসলমানগরিষ্ঠ বাংলায় ক্ষমতায় আসার জন্য মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নিছকই ক্ষমতা ভাগাভাগির চুক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে বাধ্য। ধর্মের ভিত্তিতে পদ সংরক্ষণের এই বিপজ্জনক সূচনা আদতে শুধুমাত্র শ্রুতিমধুর ছিল, বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন আদৌ দেখা যায়নি। প্রকৃতপক্ষে চিত্তরঞ্জন কর্পোরেশনের মেয়র হওয়ার পরে সুভাষচন্দ্র বসু সেই কর্পোরেশনে মাত্র ২৫ জন মুসলমানকে নিয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার অধিকাংশই ছিল নিম্নশ্রেণির পদ। যশোহর, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নদিয়া, মেদিনীপুরের পুরসভা ও জেলা বোর্ডগুলির নির্বাচনে স্বরাজ্য দল সাফল্য পেলেও প্যাক্টের শর্ত পালনে সেখানকার নির্বাচিত হিন্দু সদস্যরা কোনো উদ্যোগই গ্রহণ করেননি। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খান বাহাদুর মোশারফ হোসেন যতদিন সরকারি চাকরির প্রতিটি বিভাগে মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ না হয়, অন্তত ততদিন সরকারি পদে শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়োগ করার কথা বলেন। কিন্তু সেই আশা পূরণে ব্যর্থ চিত্তরঞ্জন। স্বরাজ অর্জনের পরে এই ‘প্যাক্ট’ কার্যকরী করার কথা বলে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান। চুক্তি অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে কেবলমাত্র শিক্ষিত মুসলমানদের সংরক্ষণের আওতায় এনে তুষ্ট করার চেষ্টা হলেও, বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকদের অবস্থার উন্নয়নের কথা আদৌ বিবেচিত হয়নি। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই চুক্তি সম্পর্কে মুসলমানদের মোহভঙ্গ হয়। তাঁরা যে একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী হিন্দু উচ্চবর্ণ নেতার নেহাতই ক্ষমতা দখলের ক্রীড়নক মাত্র, অচিরেই সে কথা তাঁরা সম্যক উপলব্ধি করেন।
সারা দেশে তখন বিরাজ করছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশ। সাইমন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯২২ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ১১২টি দাঙ্গায় প্রায় ৪৫০ জন মারা যান, আহত হন প্রায় ৫ হাজার মানুষ। ১৯২৪ সালে বাংলাতেও ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, রংপুর, যশোহর, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলের খবর পাওয়া যায়, যা স্বরাজ্য দলের হিন্দু সদস্যদের সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব বৃদ্ধির বিষয়টিকেই তুলে ধরে। ইতিহাসবিদ অমলেন্দু দে বেঙ্গল প্যাক্টের যথাযথ বিশ্লেষণ করে লিখেছেন, “স্বভাবতই হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে যথেষ্ট তৎপর হওয়া সত্ত্বেও স্বরাজ্য পার্টি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে বাংলা দেশের রাজনীতিকে মুক্ত রেখে কোনো নতুন পথ নির্দেশ করতে সক্ষম হয়নি।
চুক্তি অনুযায়ী কর্পোরেশনের মেয়র হন আবদুর রহমান সিদ্দিকি এবং অল্ডারম্যান সুভাষ। মাত্র দুই বছর আগেও যিনি ছিলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি, সেই সুভাষের সামান্য ‘অল্ডারম্যান পদের জন্য এই লালায়িত হওয়া আশ্চর্যের বটে। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের যে মন্ত্রিসভাকে সাম্প্রদায়িক’ বলে অভিযুক্ত করেছিলেন, সেই ফজলুল হকেরই ১৯৪১ সালের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য হন শরৎ বসু। চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাস বসু, শরৎ বসুরা কিন্তু কেউ আরএসএস বা হিন্দু মহাসভার সদস্য ছিলেন না।
ফিরে আসি কংগ্রেসের কথায়। কংগ্রেস’ আসলে একটি প্ল্যাটফর্মের নাম। কেন এই প্ল্যাটফর্মের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সে সময়? অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউমদের এই প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দুদের বিজাতীয়করণের দিকে ঠেলে দেওয়া। তাই কংগ্রেসকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ফেনায়িত জাতীয়বাদকে দমিয়ে রাখার জন্যই। সদ্যোজাত দৈত্যকে তমসাচ্ছন্ন করে রাখার ‘খেলনা হিসাবে কংগ্রেস প্ল্যাটফর্মের সৃষ্টি। লেডি ডাফরিন সেদিন বলেছিলেন— “কংগ্রেস সংকীর্ণ স্বার্থ চরিতার্থ করার রাজনীতিতে নিমগ্ন।” হিউম সম্পর্কে ডাফরিন যথেষ্ট সংশয়বাদী ছিলেন। ১৮৮৬ সালের পরেই ডাফরিন বাঙালি ও মারাঠি ব্রাহ্মণদের আক্রমণ করে বলেন, “এঁরা মতলববাজ এবং আইরিশদের অনুসরণে বিপ্লবের স্রষ্টা।” কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে যে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের সম্পর্ক, তা থেকে কংগ্রেস কোনোদিনই রেহাই পায়নি। পরবর্তীকালে কংগ্রেসের ভিতরের একটা অংশ অত্যন্ত সচেতনভাবেই এই ধারায় মদত জুগিয়ে এসেছে সাম্প্রদায়িকতাকে। সেইসময়কার কংগ্রেস আরএসএস ও হিন্দু মহাসভার সাম্প্রদায়িক কাজকর্মের বিরোধিতা করেছে বলে শুনিনি। বরং একথা বলাই যায়, কংগ্রেসও মনেপ্রাণে চেয়েছিল ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর মুসলিম বর্জিত একটি হিন্দুরাষ্ট্র, যা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের দ্বারাই পরিচালিত হবে। আর-একটু বললে— কংগ্রেস হল নরম হিন্দুত্ব মতবাদে বিশ্বাসী, সংঘীরা চরম হিন্দুত্ব মতবাদে বিশ্বাসী। এক পক্ষ ঘোমটার নিচে খ্যামটা নেচেছে, অপরপক্ষ নগ্ন হয়েই নাচে। ভুলে যাবেন না মুঞ্জের মতো সংঘীও কংগ্রেসে ছিলেন। ১৯২০ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন সংঘীদের আদিগুরু বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে।
কংগ্রেসের একটা ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশ ছিল বটে। ধর্মনিরপেক্ষতা কংগ্রেসের মুখ নয়, সেটা বোঝায় সেসময়কার সংগঠনে মুসলিম সদস্য প্রায় ছিল না বললেই চলে। যদি কংগ্রেসে মুসলিম নেতাদের গুরুত্বের সঙ্গে রাখত, তাহলে হয়তো দেশটা ভাগ করতে হত না। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে একটা মিত্রতা গড়ে উঠতে পারত। কংগ্রেসের চালচলন ভাবভঙ্গিতে এট ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ভবিষ্যতে ব্রিটিশরা ভারত ছেড়ে গেলে মূলত হিন্দুরাই ক্ষমতা কায়েম করবে। মুসলিম নেতারা উপেক্ষিত হবে। যাই হোক, তা সত্ত্বেও ১৯৩৯ সালে সংঘপ্রধান মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর তাঁর ‘We are our nationhood difined” গ্রন্থে লিখলেন –“কংগ্রেসের ধর্মনরপেক্ষ নীতি হল জাতীয়তাবাদের বিরোধিতারই নামান্তর। জাতীয়তাবাদী বলে যাঁরা নিজেদের দাবি করে এবং আমাদের অতীতদিনের হানাদার মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের কিছু কিছু বিষয়ে বৈসাদৃশ্য আছে– এই মতবাদের যাঁরা প্রচারক তাঁদের হাতেই হিন্দু জাতীয় চেতনা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের শত্রুকে মিত্র করেছি, যার জন্য আমাদের জাতি প্রকৃত জাতিসত্তাকে দুর্বল করেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতে কেবলমাত্র ভারতীয় আর ইংরেজদের মধ্যে লড়াই নেই। এটা আসলে একটা ত্রিকোণ লড়াই। হিন্দুরা একই সঙ্গে মুসলমানদের সঙ্গেও লড়াই করছে, তেমনই তারা লড়াই করছে ইংরেজদের সঙ্গেও।” অথচ ভাবতে অবাক লাগে প্রায় ৮০ বছর পর আরএসএসের বর্তমান চালক মোহন ভাগবত বলছেন –“হিন্দুত্বের মানে সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলা। মুসলিমদের গ্রহণ করাও এর অংশ। মুসলিমদের যদি গ্রহণ করতে না পারি, এটা হিন্দুত্ব নয়। ভারতীয়ত্বই ও একাত্মকরণই হল হিন্দুত্ব। সংঘ মানে বিশ্ব ব্রাদারহুড। এই ভ্রাতৃত্বের জোরেই বিভেদের মধ্যে রয়েছে ঐক্য। এজন্য আমরা হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুত্ব আমাদের একজোট করে রেখেছে। আমাদের কাছে হিন্দুত্বের মানে কাউকে ছোটো করা নয়।” বিশ্বাসযোগ্য নয়, তবুও মনে পড়ে গেল বলে উল্লেখ করলাম। বৃদ্ধ শিকারি বাঘ যখন বনের সমস্ত প্রাণীদের বলে, আমি এখন সাত্ত্বিক হয়েছি, মাছমাংস কিছুই ভোজন করি না’, তখন নিশ্চয় বনে প্রাণীরা সে কথা বিশ্বাস করে না।
আরএসএস-বিজেপির তাত্ত্বিক ভিত্তির অন্যতম নির্মাতা সাভারকর প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে ‘বিশ্বাস’ হিটলারের ইহুদি বিরোধী যাবতীয় অভিযান হত্যালীলাকে সমর্থন করেছিল। আমাদের দেশের মুসলিম সমস্যার সমাধান হিসাবে এই সাভারকর ১৯৩৮ সালের ১৪ অক্টোবর বলেছিলেন– “যে-কোনো দেশ গড়ে ওঠে তার নিজস্ব ভূখণ্ডে বসবাসকারী সংখ্যাগুরুদের নিয়েই।”
কংগ্রেস সৃষ্টির পর থেকেই চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ব্যক্তিরা যেমন মদত জোগাচ্ছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে, তেমনই হিন্দু সংস্কারবাদী আন্দোলন কার্যত ছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদকে জোরদার করারই প্রয়াস। এই দেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি ও বিকাশে হিন্দুধর্মে অবস্থানকারী মানুষদের স্বার্থ অভিন্ন এই বোধটি প্রথম থেকেই কাজ করেছে। হিন্দুদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক স্বার্থ অভিন্ন এই দ্যোতনাই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে পল্লবিত হতে সাহায্য করেছে। এই দর্শনের ভিত্তিতেই তাঁরা তাঁদের নেতিবাচক অবদান রেখেছে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। হিন্দু রাজনৈতিক নেতা, হিন্দু বুদ্ধিজীবী ইত্যাদিদের মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে দেখা গেছে জাতীয়, আঞ্চলিক বা শ্রেণিনেতা হিসাবে অভিনয় করত। সাম্প্রদায়িকতাকে মতাদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত করে আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চালিয়েছে, তেমনই তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মুসলিম লিগ গঠিত হল মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে সাম্প্রদায়িকতা। মুসলিম লিগের প্রসঙ্গে পরে আসছি।
আরএসএসের ‘ঘরের লোক’ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতো ঐতিহাসিক ছাড়া বহু ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদের ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। বাল গঙ্গাধর তিলকের গো-রক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা, গণপতি ও শিবাজী উৎসবের প্রচলন, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের আন্দোলনের ভাবধারায় কালী ও দুর্গার মাতৃমূর্তির প্রচার প্রভৃতি মুসলিম সম্প্রদায়রা ভালো চোখে দেখেনি। তদুপরি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত বলে লালা লাজপত রায় প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ এটাই এরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে, জাতীয়তাবাদের কেবলমাত্র দাবিদার হিন্দুরাই, মুসলিমরা নয়। ব্রিটিশ-শাসন অবসানের পর যে রাষ্ট্র নির্মাণ হবে তা হিন্দু জাতিদের, মুসলিম জাতিদের নয়। ব্রিটিশ মুক্ত ভারতে মুসলিমরা ব্রাত্য। ভারত ধর্মমণ্ডল’, ‘পাঞ্জাব হিন্দুসভা’, ‘হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দুত্ববাদের প্রচার করতে থাকে উপর্যপরি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর পর। হিন্দু মহাসভার নেতা লালচাঁদ ঘোষণা করেন –“আমি প্রথমে হিন্দু, পরে ভারতীয়”। অর্থাৎ এদের মতাদর্শে জাতি (nationalism) মানে ভারতীয়ত্ব নয়, হিন্দুত্ব। এই ধরনের উগ্র হিন্দুত্বের প্রচারই। মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুদের ব্যবধান সৃষ্টি করে।
ব্রিটিশ সরকারও সাম্প্রদায়িকতার ফসল তুলতে মাঠে নেমে পড়েছে। সে সময়ের অবিভক্ত বঙ্গ ছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পীঠস্থান। বৃহৎ বঙ্গের হিন্দু-মুসলিম শক্তি পৃথক করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ব্রিটিশবিরোধী শক্তিকে দুর্বল করে দেওয়ার জন্য মুসলিম তোষণের নাটক শুরু করলেন লর্ড কার্জন। বিভিন্ন ব্রিটিশ কর্তারা বাংলায় এসে সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝানোর করে পৃথক পূর্ববঙ্গ মুসলিম সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নতির সহায়ক হবে। মূলত বঙ্গদেশের পূর্বাংশ ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ, পশ্চিমাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। নব্যসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার বামফিল্ড ফুলার মুসলিমদের উসকানি দিতে পূর্ববঙ্গে সরকারি চাকরিতে হিন্দুদের বাতিল করে মুসলিমদের নিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেন। সে সময় মুসলিমরা ফুলার তথা ব্রিটিশদের কাছ থেকে সুয়োরানির আদর পেতে শুরু করে দিয়েছিল।
১৯০৩ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করা হয়। তখন বঙ্গপ্রদেশ থেকে চট্টগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদুটিকে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার একটি প্রস্তাবও ছিল। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে সরকারিভাবে এই পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারিতে লর্ড কার্জন বঙ্গের পূর্বাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এক সরকারি সফরের মাধ্যমে এই বিভক্তির ব্যাপারে জনমত যাচাইয়ের চেষ্টা করেন। তিনি বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে এই বিভক্তির বিষয়ে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা দেন। পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী (দার্জিলিং বাদে) বিভাগ এবং মালদা জেলা, আসাম প্রদেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে এই নতুন প্রদেশ গঠন করবে। এর ফলে বঙ্গপ্রদেশ শুধু তার বৃহৎ পূর্বাঞ্চলই হারাবে না, তাকে হিন্দিভাষী পাঁচটি রাজ্যও মধ্যপ্রদেশকে ছেড়ে দিতে হবে। অন্যদিকে পশ্চিমে সম্বলপুর এবং মধ্যপ্রদেশের পাঁচটি ওড়িয়া-ভাষী রাজ্যের সামান্য অংশ বঙ্গকে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ফলে বঙ্গের আয়তন দাঁড়ায় ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৫৪ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৪২ মিলিয়ন হিন্দু ও ৯ মিলিয়ন মুসলিম।
অপরদিকে নতুন প্রদেশটির নামকরণ করা হয় পূর্ববঙ্গ ও আসাম’, যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর হবে চট্টগ্রাম। এর আয়তন হবে ১,০৬,৫০৪ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা হবে ৩১ মিলিয়ন, যাদের মধ্যে ১৮ মিলিয়ন মুসলিম ও ১২ মিলিয়ন হিন্দু। সরকার নির্দেশ দেয় যে, পূর্ববঙ্গ ও আসামের পশ্চিম সীমানা স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট থাকবে, সঙ্গে এর ভৌগোলিক, জাতিক, ভাষিক ও সামাজিক বৈশিষ্টাবলিও নির্দিষ্ট থাকবে। সরকার তাঁদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯ জুলাই, ১৯০৫ সালে এবং বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় একই বছরের ১৬ অক্টোবর। পূর্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশে ৬টি বিভাগ করা হয়েছিল— (১)ঢাকা (রাজধানী) বিভাগে ছিল ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকেরগঞ্জ ও সুন্দরবন।(২) চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও নোয়াখালী। (৩) রাজশাহী বিভাগে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, মালদহ ও জলপাইগুড়ি। (৪) সুরমা উপত্যকা ও পার্বত্য বিভাগে সিলেট, কাছাড়, লুসাই পার্বত্য জেলা, নাগা পার্বত্য জেলা, খাসিয়া জয়ন্তিয়া পার্বত্য জেলা ও গারো পার্বত্য জেলা। (৫) আসাম উপত্যকা বিভাগে গোয়ালপাড়া, কামরূপ, দাররাং, নওগাও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলা। এবং (৬) দেশীয় রাজ্যে ছিল পার্বত্য ত্রিপুরা ও মণিপুর।
এই ঘটনায় এক প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের এই ধারণা হয় যে, নতুন প্রদেশের ফলে শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁদের সুযোগ বেড়ে যাবে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের জনগণ এই বিভক্তি মেনে নিতে পারল না এবং প্রচুর পরিমাণে জাতীয়তাবাদী লেখা এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বঙ্গভঙ্গ রদ করার আবেদন জানালেন প্রস্তাবকদের কাছে। এই সকল রাজনৈতিক প্রতিবাদের ফলশ্রুতিতে ১৯১১ সালে বঙ্গপ্রদেশ আবার একত্রিত হয়। ভাষাতাত্ত্বিক এক নতুন বিভক্তির মাধ্যমে হিন্দি, ওড়িয়া এবং অসমীয়া অঞ্চলগুলো বঙ্গপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় আনা হয়। একই সঙ্গে বাঙালি ঐক্যের ভয়ে ব্রিটিশরা ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে নতুন দিল্লিতে স্থানান্তর করে।
বঙ্গভঙ্গের পরের বছরেই, অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর মুসলিম নেতা আগা খাঁর নেতৃত্বে ৩৫ জন ধনী অভিজাত মুসলিদের একটি প্রতিনিধি দল সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করেন এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। এটি ‘সিমলা ডেপুটেশন’ বা ‘সিমলা দৌত্য’ নামে পরিচিত। কী দাবি ছিল সেই স্মারকলিপিতে– (১) চাকরিতে বেশি সংখ্যায় মুসলিমদের নিয়োগ, (২) পরীক্ষা ছাড়া উচ্চপদে মুসলিমদের নিয়োগ, (৩) আইনসভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, (৪) একটি পৃথক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গঠন প্রভৃতি। বডোলাট অবশ্য সুবিচারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলিম সম্প্রদায়ের এই দাবি কার্যকরী করা হয়। লর্ড মিন্টো কী চিন্তা করে আগা খাঁর দাবিগুলি মেনে নিয়েছিল, সেটা লর্ড মিন্টোই ভালো বলতে পারত। তবে আমার মনে হয় দাবিগুলি মেনে নিয়ে আসলে উগ্র হিন্দু সম্প্রদায়কেই লাফাতে সাহায্য করেছে।
সিমলায় অবস্থানকালে মুসলিম নেতারা উপলব্ধি করেন, মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুললে নিজ সম্প্রদায়ের সুবিধা-অসুবিধাসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরা সম্ভব। মুসলিম সম্প্রদায়ের অগ্রগতি ও সরকারের কাছে দাবি-দাওয়া জানানোর জন্য একটি সংগঠন গড়ে তুলতে বলেছিলেন স্বয়ং লর্ড মিন্টোই। সঙ্গ দিয়েছিলেন মিন্টোর একান্ত সচিব ডানলপ স্মিথ। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বরে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর ডাকে ঢাকায় একটি সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ৩০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা ভারত মুসলিম লিগ’ (All India Muslim League) প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলিম লিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল– (১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে, (২) মুসলিমদের অধিকার ও স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করবে, (৩) জাতীয় কংগ্রেস ও হিন্দুদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খর্ব করবে, (৪) কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করবে।
গোড়ার দিকে যাই। ১৯০৪ সালের ৬ এপ্রিল বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ ইউনিয়নের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখলেন। তাতে বললেন, আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে কীভাবে এই বিকাশমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা যায়? কীভাবে এই সুগঠিত ও সুষম বস্তুটিকে বিভক্ত হতে বাধ্য করা যায়? সমাধান একটাই– বঙ্গভঙ্গ। বাংলাকে কেটে দুই ভাগ করা হবে। পূর্বদিকে থাকবে মুসলিমদের জন্যে একটি প্রদেশ আর পশ্চিমদিকে থাকবে হিন্দুদের জন্যে অন্য একটি প্রদেশ। মুসলিমরা আহ্লাদে আটখানা। হল। কারণ সমাজের পরিচালনায় ছিলেন যে বর্ণহিন্দুরা, তাঁদের হাত থেকে এবার মুক্তি মিলবে। বর্ণহিন্দুরা রাগে ফেটে পড়ল। কারণ যে অনুন্নত বুর্জোয়া শ্রেণিটিকে তাঁরা এতদিন পদানত করে রেখেছিল, যাঁদের তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তাঁরা তাঁদের হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে। দুইদিক থেকেই শুরু হল ধর্মযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রক্তের বন্যা বয়ে গেল। লর্ড কার্জন বাংলাদেশ পরিভ্রমণে বের হলেন। বিভিন্ন এলাকার স্থানীয় মুসলিমদের সঙ্গে দেখা করে পুরো দোষটা হিন্দুদের উপর চাপিয়ে দিলেন। তিনি মুসলিমদের ইসলামি ভাবনায় উদ্বদ্ধ হতে বললেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মহারানির আশীর্বাদপুষ্ট একজন ইংরেজ গভর্নর ইসলামি জেহাদের ডাক দিলেন।
১৯১১ সালে অবশ্য বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়। হতে পারে হিন্দুদের অসন্তোষের ঢেউয়ের ব্রিটিশরা পিছু হটেছিল। আবার এমনও হতে পারে যে, এই অসন্তোষ সৃষ্টি করাই ছিল ব্রিটিশদের মূল লক্ষ্য। লক্ষ্য একবার অর্জিত হয়ে গেলে বাংলা ঐক্যবদ্ধ হল নাকি দু-ভাগ হল, তাতে ব্রিটিশদের কিছু যায় আসে না। লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হয়ে গিয়েছিল। কারণ ততদিনে বিকাশমান ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। জাতীয়তাবাদের ভ্রুণ রূপান্তরিত হয়েছিল জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ। বাংলা জোড়া লেগেছিল। কিন্তু বাঙালিরা দু-ভাগ হয়ে গেল। বাংলা ভাগ হয়নি, কিন্তু ব্রিটিশদের সক্রিয় আনুকূল্যে দানবীয় এক বস্তুর জন্ম হয়েছিল। অস্বাভাবিক, প্রকৃতি-বিরোধী, জন্মগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল এই বস্তুটির নাম ‘ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ’। (Bernard-Henry Levy)
পাশাপাশি এই বাংলা প্রদেশে জন্ম নিল মুসলিম লিগ। মুসলিম লিগের জন্ম নেওয়ার তিনটি কারণ অনুসন্ধান করা যায়– (১) উগ্র হিন্দুত্ববাদের উত্থান, (২) ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায়ের অসন্তোষ এবং (৩) ঔপনিবেশিক শক্তির হিসাব-নিকাশ। মুসলিম অভিজাত সম্প্রদায় নিজেদের সংখ্যালঘু বলে মনে করতে শুরু করল। এই অজুহাতে তাঁরা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শক্তির কাছে মধ্যস্থতার আর্জি নিয়ে হাজির হয়ে গেল। মুসলিমদের আদর্শগত অবস্থান হঠাৎ করে রাতারাতি বদলে গেল। তাঁরা পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ প্রাধান্যভিত্তিক যে ক্ষমতানুক্রমিক কাঠামো ছিল, তার প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য দেখাতে শুরু করল। অভিজাত মুসলিমদের এই পরিবর্তিত মানসিকতা থেকে কিছুদিন পর ১৯০৬ সালে যে মুসলিম লিগের জন্ম হয়েছিল তাকে জন্মগতভাবে প্রতিক্রিয়াশীল, জনবিরোধী এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসকগোষ্ঠীর ধামাধরা সহায়তাকারী বলা যেতে পারে। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী কিছুকালের মধ্যে মুসলিম লিগ মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। ১৯০৮ সালের মধ্যেই গোটা ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশে লিগের শাখা ছড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক দল হিসাবে মুসলিম লিগ ১৯০৯ সালেই তাঁদের জন্য আইনসভায় পৃথক নির্বাচনের দাবি জানায়। সেই অনুসারে ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন চালু করে সরকার আইনসভায় মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ শুধু মুসলিমদের দ্বারাই আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ আরও বৃদ্ধি পায়।
বস্তুত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে উনিশ শতকের শেষের দিকে এই ভূমি ব্যবস্থার ভিতরে একটা বড়ো রকমের বাঁক এসে গেল। বিবর্তিত পরিস্থিতিতে সামাজিক ভিত্তি তৈরি করা তখন বেশ বড়ো রকমের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল জায়গিরদারি গোষ্ঠীর কাছে। সামাজিক পরিকাঠামোর ভাঙনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক পরিকাঠামোরও সংকট এসে পড়েছিল। তবে এই জায়গির গোষ্ঠীগুলি কোনোদিনই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী অবস্থান নেয়নি। কী হিন্দু, কী মুসলিম, কী অন্য কোনো সম্প্রদায়। ফলে যে নতুন সামাজিক পরিকাঠামো ক্রমশ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করেছিল, সেই পরিকাঠামোর সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল। জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীদের আধুনিক যে মধ্যশ্রেণি ইতোমধ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যস্থল হয়ে উঠল।
এমতাবস্থায় স্যার সৈয়দ আহমদ এগিয়ে এলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতরে যে জায়গিরদার গোষ্ঠীগুলো আছে তাঁদের সংগঠিত করতে। স্যার সৈয়দ আহমদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেল তাঁদের শ্রেণি স্বার্থরক্ষা। প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল জায়গিরদারদের বেশিরভাগই ছিল জন্মসূত্রে মুসলিম। আধুনিক মধ্যশ্রেণির সঙ্গে জায়গিরদারদের যে সংঘাত তৈরি হল, তা পরবর্তী সময়ে জাতীয় আন্দোলনে মুসলিম বিরোধিতা হিসাবে দেখতে শুরু করলেন জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা। সেদিক থেকে বলা যায় জাতীয় আন্দোলনের প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই অভিজাত মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেণিস্বার্থ রক্ষার তাগিদের মাশুল গোটা মুসলিম সমাজকেই গুণতে হল। বস্তুত হিন্দু ও মুসলিমদের ভবিষ্যতে ভাগ্যনির্ধারণের দায়িত্ব সমাজের অভিজাত শ্রেণির মানুষদের হাতে ন্যস্ত হল। গ্রাসরুটের অভাব-অভিযোগ, হাসি-কান্না যাঁদের কাছে পৌঁছোয় না। জাতীয় কংগ্রেসের প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই ভারতের রাজনীতিতে ছিল মূলত উচ্চবর্ণ, ধনী-ভূস্বামী, অভিজাত শ্রেণি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জাতীয় পরিষদের ৫০৩ জন সদস্যের মধ্যে মুসলিম লিগের ১৯৩ জনই ছিল অভিজাত জমিদার সম্প্রদায়ভুক্ত। আরএসএস, হিন্দু মহাসভাতেও একই চিত্র। অভিজাত ও ধণিক শ্রেণিক শ্রেণিক আধিক্য।
ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি সে সময়ে যে কৃষি ও কৃষকদের কথা ভেবেছিল, কংগ্রেস সেই ভাবনাকে সমর্থন করেনি। তাঁরা হিন্দু জমিদাররা কৃষক প্রজা পার্টির কৃষি আইনকে হিন্দু স্বার্থের উপর আক্রমণ হিসাবেই দেখেছিল। কংগ্রেসের ভিতর হিন্দু জমিদারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল অবিসংবাদিত। তাই তাঁরা সেই কৃষি আইনের বিরোধিতায় নামে। জমিদার বিরোধী যে-কোনো আন্দোলনে কী মুসলিম লিগ কী হিন্দু মহাসভা কী কংগ্রেস সকলেই একই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে। তা ছাড়া ভারতের জমিদাররা তো ছিল ব্রিটিশদের কেনা গোলাম। ব্রিটিশদের এত নাচন-কোঁদন এইসব তো জমিদারদের ভরসাতেই। বিনিময়ে জমিদাররা পেত পুরস্কার, উপাধি ইত্যাদি। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কোনো সংঘাতেই যায়নি উভয় সম্প্রদায়ের জমিদার শ্রেণি। এই সংঘাতে না-যাওয়ার কারণ থেকেই তাঁদের সমর্থন ছিল সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর প্রতি। বরং নিম্নবর্গীয়দের যে উত্থান সমসাময়িক ভারতে দেখা দিয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তি বিরোধিতা করে গেছে। দেশভাগে এত রক্তপাত হয়েছিল এই উচ্চবর্গীয় হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তির অনুপ্ররণাতেই।
আন্দোলনের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অবসান পর্যন্ত ভারতে মুসলিম নেতৃত্ব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু সম্প্রদায় থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করা। হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেসের বিরোধিতা করতে গিয়ে ব্রিটিশদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে বসল। অবশ্য আনুগত্য প্রদর্শনে কেউই পিছিয়ে ছিল না। আরএসএস, হিন্দু মহাসভা, কংগ্রেস সব সংগঠনই ব্রিটিশদের হাত থেকে তামুক খেতে ব্যস্ত ছিল। মুসলিম সম্প্রদায় সেই তুষ্টির উপহার হিসাবে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ লাভ করেছিল, যে প্রদেশে মুসলিমরা হল সংখ্যাগুরু, আর হিন্দুরা হয়ে গেল সংখ্যালঘু। এই অনুপাত মুসলিম সম্প্রদায়কে যারপরনাই খুশি হলেও হিন্দু সম্প্রদায় ততোধিক অখুশি হল। ব্রিটিশরা যে মুসলিমদের সঙ্গে খাতির করতে আলাদা প্রদেশ দেয়নি, এটা বুঝতে হল ১৯১১ সালে এসে। ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পুনরায় বঙ্গপ্রদেশ একত্র হয়ে গেল। এই কারণে মুসলিম সম্প্রদায় ব্রিটিশদের প্রতি বেজায় রুষ্ট হয়। বঙ্গপ্রদেশ একত্র হওয়ার ফলে ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম আধিপত্যের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। স্বভাবতই বঙ্গপ্রদেশ একত্রিত হোক এটা মুসলিদের একটা অংশ চাননি। কিন্তু কী আর করা! কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম। মুখোশধারী ব্রিটিশরা আদতে যা চেয়েছিল, তা হতে একদম দেরি হল না। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকল, যা শেষ হয়েছিল ৪৬ ছুঁয়ে ৪৭-এ। এই পরিণতিতে ইন্ধন জোগানো লোকেরও অভাব ছিল না সে সময়ে।
এতদিন মুসলিম লিগে আলিগড়ের নেতাদের আধিপত্য ছিল। কিন্তু এই সময়ে মৌলানা মোহম্মদ আলি, মৌলানা শওকত আলি, মোহম্মদ আলি জিন্নাহ, হাকিম আজমল খান, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, হজরত মোহানি প্রমুখ প্রগতিশীল তরুণ মুসলিম লিগে যোগ দিলে আলিগড় নেতাদের আধিপত্য হ্রাস পায়। নতুন মুসলিম যুবনেতারা ঘোষণা করেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে শামিল হয়ে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মুসলিম লিগের তরুণ-তুর্কি নেতাদের উদ্যোগে সাম্প্রদায়িক অশান্তি অনেকটা হ্রাস পেলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়। এর ফলে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে লখনউ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই চুক্তির মাধ্যমে– (১) কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ যৌথভাবে সরকারের কাছে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবি পেশ করতে রাজি হয়, (২) মুসলিম লিগও কংগ্রেসের ‘স্বরাজ’ আদর্শকে মেনে নেয়, (৩) মুসলিম লিগের প্রস্তাবিত পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়, (৪) প্রতিটি প্রাদেশিক আইনসভায় মুসলিম সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয় এবং (৫) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের এক তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলিম থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লখনউ চুক্তি কেন হল? এর পিছনের রহস্য কী? আমি কিছু বলব না। ভিন্ন মেরুর দুজন ব্যক্তির মতামত জানিয়ে দিই। গান্ধিজি বললেন— “এই চুক্তি ছিল শিক্ষিত ও ধনী হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটি বোঝাঁপড়া মাত্র। এর সঙ্গে সাধারণ হিন্দু ও মুসলিমদের কোনো যোগ ছিল না।” আরএসএস ঘনিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বললেন– “রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক সূত্রকে মেনে নিয়ে প্রবল অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন এবং এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।”
মুসলিম লিগ নিয়ে আলোচনা আপাতত স্থগিত রেখে আমরা আবার ফিরে আরএসএসের প্রসঙ্গে। মুসলিম লিগ নিয়ে আলোচনা শেষ হয়নি। পরবর্তী আলোচনায় আসব। স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের ভূমিকা কী লিখব? একজন হিন্দুর সন্তান হিসাবে লিখতে বড়ো লজ্জা হয়। গোটা ভারত যখন ব্রিটিশ মুক্ত স্বাধীন ভারতের জন্য রক্ত ঝরাচ্ছে, তখন তাঁরা নিষ্ক্রিয়। তদুপরি ব্রিটিশদের সহযোগীর ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো সময়কাল ধরেই আরএসএসের ইতিহাস ছিল মূলত ব্রিটিশের পদলেহন। কারণ এই সংগঠনের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের কোনোরকম জন-আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার অনুমতি ছিল না। সে কথা আরএসএসের বর্তমান কর্তা মোহন ভাগবতও মনে করিয়ে দিলেন। তাঁর কথায় –“জন্ম থেকেই রাজনীতি থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আরএসএস। নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে না, এমনকি কোনো নির্বাচনী প্রক্রিয়াতেও যোগ দেয় সঙ্ঘ। কোনো রাজনৈতিক দলের পদাধিকারী হতে পারেন না আরএসএস কর্মীরা।” যদিও আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে একথা সর্বৈব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আসলে হিন্দুত্ব সংগঠনগুলো এই মোড়কটিকে খুব মূল্যবান সম্পত্তির মতো ধারণ করে থাকে। ধারণ করতেই হবে। না-হলে তাঁদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কারণ তাঁরা মনে করে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতা চালিয়ে যাওয়ার পর স্বাধীন ভারতে ওদের হাতে এখন শুধুই পেনসিল। যে ‘লজ্জাজনক ইতিহাস তাঁদের কাঁধ কামড়ে বসে আছে, সেই ইতিহাস এই মেকি জাতীয়তাবাদের রঙিন মোড়ক দিয়ে তাঁরা খুব সহজেই ঢেকে দিতে পারবে। এটা মোটেই ওদের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়, এটা হিন্দু জাতীয়তাবাদ। এই স্ব-আরোপিত মোড়কটি আরএসএস নিজেদের নতুনভাবে পুনঃস্থাপন করার কাজে ব্যবহার করে, এমন ভাব করে যেন তাঁরাই একমাত্র দেশপ্রেমিকের দল, বাকি সব দেশদ্রোহী।
বস্তুত স্বাধীনতা-পূর্ব ভারতে আরএসএসের রাজনৈতিক ভূমিকাকে ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের ভিত্তিভূমি হিসাবে দেখানোর প্রচেষ্টা করে বর্তমান রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি। এঁরা হেগড়েওয়ার, সাভারকর প্রমুখদের ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ বলে তকমা দিতে উঠেপড়ে লেগেছে। যদিও আসলে আরএসএস কোনোদিনই সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে কোনো রকমের সংগ্রামে যায়নি। সংগ্রামে যায়নি এটা কিঞ্চিৎ ভুল কথা। গিয়েছিল। তবে একেবারে শুরুর দিকে। তারপর ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের প্রেমে পড়ে গেল।
হেগড়েওয়ার আরএসএস গঠনের আগে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন এবং খিলাফত আন্দোলনে (১৯১৯-১৯২৪) যোগ দেওয়ার অপরাধে তাঁর এক বছরের কারাদণ্ড হয়– সেটাই ছিল তাঁর শেষ স্বাধীনতা সম্পর্কিত কোনো আন্দোলনে যোগদান। জেলের ভাত আর পিটানি খেয়ে উনি ‘গুড বয়’ হয়ে গেলেন। সাভারকরের হিন্দুত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হেগড়েওয়ার মুক্তি পাওয়ার পরেই, অর্থাৎ ১৯২৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে আরএসএসের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংগঠন সেইদিন থেকে শুরু করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষদিন পর্যন্ত ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থেকেছেন। শুধু তাই-ই নয়, ভারতের প্রত্যেকটি স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়েই প্রত্যক্ষ বিরোধিতাও করে এসেছেন।
আরএসএসের হেগড়েওয়ারের জীবনী থেকে জানা যাচ্ছে, ১৯৩০ সালে গান্ধীজি লবণ সত্যাগ্রহ শুরু করলেন। তিনি সেসময় “সর্বত্র এই নির্দেশ পাঠালেন সঙ্ঘের কোনো সদস্য যেন এই সত্যাগ্রহে অংশ না নেয়। যদিও কেউ স্বেচ্ছায় অংশ নিতে চায় তাকে বাধাও দেওয়া হবে না।” অর্থটা কী দাঁড়াল? সংঘের কোনো দায়িত্বশীল সদস্য সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার অধিকারী নেই। যদিও এই আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য সংঘের সেবকদের মধ্যে উৎসাহের এতটুকুও কমতি ছিল না। কিন্তু হেগড়েওয়ার এই উৎসাহকে সরাসরি নিরস্ত করেছিলেন। হেগড়েওয়ারের উত্তরসূরী এম এস গোলওয়ালকর এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন— “আন্দোলন চলছিল ১৯৩০-৩১ সাল ধরে। সেই সময়ে অন্য অনেক লোক ডক্টরজির কাছে গিয়েছিল। তাঁরা ডক্টরজির কাছে অনুরোধ করে বলেছিল, এই আন্দোলন দেশের স্বাধীনতা আনতে সাহায্য করবে এবং এতে অংশ নিতে সংঘের এতটুকুও দ্বিধা করা উচিত নয়। সেই সময়ে, তাঁদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক যখন বলেন, দেশের জন্য তিনি জেলে যেতেও প্রস্তুত, ডক্টরজি তাঁকে বলে, “নিশ্চয়ই যাবেন। কিন্তু তারপরে আপনার পরিবারের দেখাশোনা কে করবে?’ যথারীতি ভদ্রলোকটি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমার যা সম্পত্তি আছে তাতে আমার পরিবারের দুই বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ চলে যাবে –শুধু তাইই নয়, তার থেকে আমার মুক্তির জন্য যা খরচ হতে পারে, তারও জোগাড় হয়ে যাবে। তখন ডক্টরজি তাঁকে বলেন, আপনার যদি এতটাই সম্পত্তি থেকে থাকে, তা হলে চলে আসুন, জেলে যাওয়ার বদলে সংঘের জন্য দুই বছর সময় দিন। এই বাক্যালাপের পরে অবশ্য সেই ভদ্রলোক জেলেও যাননি, আর কখনও সংঘের সেবা করার জন্যও ফিরে আসেননি।” কী বুঝলেন? আপনি না বুঝলেও আরএসএসের তাবড় তাবড় নেতারা বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছিল।
হেগড়েওয়ার নিজে কখনো স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন? আরএসএসে বর্তমান নেতারা কিন্তু ওনাকে ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী’ বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। হ্যাঁ, আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং জেলেও গেছিলেন। তবে ‘স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে নয়। আরএসএস থেকে প্রকাশিত তাঁর জীবনী থেকে জানা যায়, তাঁর জেলে ঢোকার মূল কারণ ছিল “সেখানকার স্বাধীনতাপ্রেমী, আত্মদানকারী কয়েদিদের দলের মধ্যে ঢুকে তাঁদের সঙ্গে সংঘের উদ্দেশ্য আর কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করা এবং সংঘের কাজের জন্য তাঁদের ভবিষ্যতের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা”। অর্থাৎ ব্রিটিশ মারতে গিয়ে নয়, সংঘের প্রচারের দায়েই এই জেলযাত্রা।
চল্লিশের দশকের শেষদিকে, ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধি যখন ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ শুরু করেছেন, সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের গৃহমন্ত্রণালয়ের লেখা একটি নোট থেকে জানা যায় যে, আরএসএসের নেতারা গৃহমন্ত্রকের সচিবের সঙ্গে দেখা করেন এবং “সঘের সদস্যরা আরও বেশিমাত্রায় ‘সিভিক গার্ড হিসাবে যোগদান করবে”– এই মর্মে সচিবকে আশ্বস্ত করেন। এই সিভিক গার্ড’ নামক বিভাগটি তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা’-র প্রয়োজন মেটাতে। বিয়াল্লিশে ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শুরু হওয়ার দেড় বছর পর ব্রিটিশদের অধীনস্থ বম্বে সরকার প্রভূত সন্তুষ্টির সঙ্গে একটি মেমোতে লেখেন— “সংঘ পরিবার যথাযথভাবে নিজেদের আইনের সীমানায় সংযত রেখেছে এবং ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে থেকে শুরু হওয়া দেশজোড়া অশান্তির সঙ্গে কোনোভাবেই নিজেদের জড়ায়নি।”
ডান্ডি মার্চের মতো ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগদান করতে না-পেরে আরএসএসের সেবকেরা এবারেও তাঁদের নেতৃত্বের উপর চূড়ান্ত হতাশ হয়ে পড়েছিল, কারণ সংগঠন তাঁদের আন্দোলনে যোগদান করতে দেননি। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে সেবকদের মগজ ধোলাই ঠিকমতো হয়নি। নেতারা যখন ভাবছেন দেশের আগে হিন্দুত্ব, তখন সেবকরা ভাবছেন হিন্দুত্বের আগে দেশ। গোলওয়ালকরের নিজের ভাষায়, “১৯৪২-এও অনেকের মনেই জোরদার সেন্টিমেন্ট কাজ করছিল … যে সংঘ কেবল অকর্মণ্য লোকেদের আখড়া, অর্থহীন বাগাড়ম্বর করে কেবল; শুধু বাইরের লোক নয়, সংঘের সেবকেরাও এইভাবে সংঘের সমালোচনা করত। তাঁরা প্রচণ্ডভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিল।”
দেশের একটা বড়ো অংশ যখন ব্রিটিশদের রক্তে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল, তখন আরএসএস কেন নিষ্ক্রিয় থেকে ব্রিটিশকে মলম দেওয়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল? যুক্তি আছে, এক অদ্ভূত যুক্তি দিয়ে থাকে আরএসএস নেতৃত্ব। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে দেওয়া এক বক্তৃতায় (যার কয়েক মাস পরেই ব্রিটিশদের সৃষ্ট এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৩০,০০,০০০ বাঙালির মৃত্যু হয়) গোলওয়ালকর বলেন— “সংঘ আজকের সমাজের এই অবক্ষয়ের জন্য অন্য কাউকে দোষ দিতে চায় না। মানুষ যখন অন্যকে দোষ দিতে শুরু করে, তখন বোঝা যায় দুর্বলতা তাঁর নিজের মধ্যেই আছে। দুর্বলের উপর হওয়া অত্যাচার অনাচারের জন্য সবলকে দোষ দেওয়া বৃথা … সংঘ তার মূল্যবান সময় অন্যকে দোষারোপ করে বা সমালোচনা করে নষ্ট করতে ইচ্ছুক নয়। আমরা যখন জানিই যে প্রকৃতির নিয়মেই বড়ো মাছ ছোটো মাছকে খেয়ে ফেলে, তখন তার জন্য বড়ো মাছকে দোষ দেওয়া বৃথা। প্রকৃতির বেঁধে দেওয়া নিয়ম, ভালো হোক বা খারাপ, তাই-ই পরম সত্য। তাকে অন্যায় বললেই সেই নিয়ম বদলে যায় না।” হাসবেন না প্লিজ।
১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে নৌ-বিদ্রোহের জের হিসাবে ব্রিটিশ যখন পাকাপাকিভাবে ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, তখনও গোলওয়ালকর যেসব সংঘীরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিতে চেয়েছিল তাঁদের তীব্র সমালোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আরএসএসের মুখপত্র ‘দ্য অর্গানাইজার’-এ প্রকাশিত এক সম্পাদকীয়তে সংঘ সরাসরি ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার বিরোধিতা করে, এবং লেখে যে— “এটা কোনোদিন হিন্দুদের নিজেদের পতাকা হবে না, হিন্দুরা একে সম্মানও করবে না।” সম্পাদকীয়তে আরও লেখা হয়, “তিন সংখ্যাটা এমনিতেই অশুভ, অতএব তিনটে রঙওয়ালা একটা পতাকা দেশের জাতীয় পতাকা হিসেবে বিবেচিত হলে তা দেশবাসীর উপর খুবই বাজে মানসিক প্রভাব ফেলবে এবং দেশের প্রতি সেটা ক্ষতিকারকও হবে।”
এবার একটু মহান দেশপ্রেমী’ সাভারকরের সঙ্গে পরিচয় করা যাক। কে এই সাভারকর? ইনি আমাদের খুব পরিচিত সেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর, যাঁকে ‘ভারতরত্ন’ দিতে চায় মোদি-শাহ সরকার। কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে ‘ভারতরত্ন দেওয়ার অধিকার একমাত্র ভারত সরকারের। কোন্ গুণবিচারে দেওয়া হয়? ‘ভারতরত্ন’ সম্মান প্রদান করা হয় সর্বোচ্চ স্তরের ব্যতিক্রমী সেবা/কার্যের স্বীকৃতি স্বরূপ। ১৯৫৪ সালে নিয়ম অনুসারে, শুধুমাত্র শিল্পকলা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেই এই সম্মান দেওয়া হত। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিয়ম পরিবর্তন করে মানবিক প্রচেষ্টার যে-কোনো ক্ষেত্রে এই সম্মান প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৪ সালের নিয়মে মরণোত্তর ভারতরত্ন’ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু ১৯৫৫ সালে জানুয়ারি মাসে সেই নিয়ম পরিবর্তন করে ‘মরণোত্তর ভারতরত্ন’ প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয়। ১৯৬৬ সালে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রথম ‘মরণোত্তর ভারতরত্ন’ দেওয়া হয়।
সাভারকর সশস্ত্র জিহাদে বিশ্বাস করতেন। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে দেখা করেছিলেন ইটালির ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনির সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছিল মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দলের আদলে একটি জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী দল তৈরি করা। পরে মুঞ্জের হাত থেকে ব্যাটন নিয়ে হিন্দুত্ববাদের ‘পোস্টারবয়’ হয়ে ওঠেন সাভারকর। লন্ডনে বসে ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের আগুন তাঁকে উদ্বেলিত করে তোলে। মদনলাল ধিংড়া ১৯০৯ সালে খোদ ইংল্যান্ডে বসেই কার্জন ওয়াইলিকে খুন করেন। মদনলাল ধিংড়া ছিলেন সাভারকরের শিষ্য। এরপর অনেকগুলো বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের জন্য ১৯১০ সালে ব্রিটিশ সরকার সাভারকরকে গ্রেফতার করে। পরের বছরই তাঁকে আন্দামানের কুখ্যাত সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেয়। ১৯১১ সালে জেলে ঢোকার কয়েক মাসের মধ্যেই শুকিয়ে আমসি। ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে লেখেন তাঁকে যেন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই মুক্তি দেওয়া হয়। আন্দামানে সেলুলার জেলে থাকাকালীন এইভাবে একাধিক বার ব্রিটিশরাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন। যথারীতি ব্রিটিশ সরকার তাঁর ক্ষমাভিক্ষায় কর্ণপাত করেনি। ১৯১৩ সালে আবার ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে চিঠি লেখেন তিনি। ১৯২১ সালে তাঁকে আন্দামান থেকে থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯১১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত উপযুপরি ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন এই ‘বিপ্লবী।
১৯১৩ সালের মুচলেকায় কী লিখেছিলেন দেশপ্রেমী’ সাভারকর? একজন ভারতীয় হিসাবে আপনি গর্ববোধ করতে পারেন কি না দেখুন– “যদি সরকার বাহাদুর তাঁদের নানা রকমের দয়া এবং গভীর বদান্যতার দ্বারা আমাকে মুক্তি দেন, তাহলে আমি সাংবিধানিক উন্নয়নের একজন আত্মমগ্ন প্রবক্তা ভিন্ন অন্যকিছুই যে নই এবং উন্নয়নের সর্বোচ্চ শর্ত হল ইংরেজদের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য –এ কথাটাই জীবন দিয়ে প্রমাণ করে দেব। যতদিন আমরা জেলে বন্দি অবস্থায় আছি ততদিন ভারতের মহামহিম রাজের প্রতি অনুগত শয়ে শয়ে হাজার হাজার প্রজার পক্ষে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়। কারণ রক্তের বন্ধনই আসল বন্ধন। যদি আমাদের মুক্তি দেওয়া হয়, তাহলে জনসাধারণ তাঁদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই সরকারের প্রতি আনন্দ ও গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে– যে সরকার শাস্তি দেওয়া অথবা প্রতিহিংসার পরিবর্তে ক্ষমা এবং সংশোধন করতে জানে।”
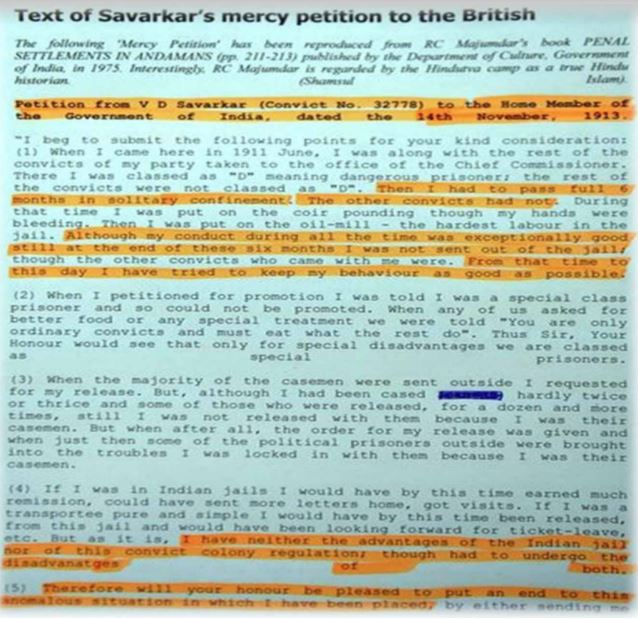
[সাভারকরের সেই মুচলেকা]
যে সাভারকরের নামে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে গোটা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল, সেই সাভারকরই ব্রিটিশ সরকারের কাছে মুচলেকাতে লিখেছিলেন– “সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি আমার মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমার এই পরিবর্তনের ফলে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে বসবাসকারী বহু বিভ্রান্ত যুবক আবার সঠিক পথে ফিরে আসবে। এইসব যুবকেরা আমাকে তাঁদের পথপ্রদর্শক হিসাবে মনে করে। সরকার যেরকমভাবে চাইবে, আমি সেইরকমভাবেই সরকারকে সেবা করতে প্রস্তুত আছি। আমার এই পরিবর্তন হল আমার বিবেকের সিদ্ধান্ত। আমার স্থির বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও আমার আচরণ একইরকম থাকবে।” হ্যাঁ, উনি কথা রেখেছিলেন শেষদিন পর্যন্ত। সংগ্রামী ভারতবাসীদের সঙ্গে বেইমানি করলেও ব্রিটিশদের সঙ্গে বিন্দুমাত্র বেইমানি করেননি। শহিদের রক্তে যখন ভারতের মাটি লালে লাল হয়ে যাচ্ছিল, তখন উনি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রিটিশদের পদলেহনে নিয়োজিত ছিলেন। ওনাকে মুক্তি না-দিলে ব্রিটিশরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন? উনি লিখছেন –“এর ফলে যে সুবিধাগুলো পাওয়া যাবে, সেই সুবিধাগুলো আমাকে জেলে আটকে রাখলে কোনো অবস্থাতেই পাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে একমাত্র মহামান্য সরকার বাহাদুরই দয়াপরবশ হতে পারেন। পিতৃসুলভ সরকারের দরজায় না ফিরলে একজন অবোধ অনুতপ্ত সন্তান আর কোথায় ফিরবে?” সেই ‘অবোধ সন্তান’ শ্রীমান সাভারকর চার বছর জেলের ডাল-ভাত খেয়ে আবেদন-নিবেদন করে অবশেষে ১৯২৪ সালে মুক্তি পান। তিনি শেষদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং চিরকাল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুর জো-হুজুর হয়েই ছিলেন এবং এর অবকাশে গোটা দেশে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়ে সফলতার সঙ্গে ব্রিটিশদের স্বপ্নপূরণ করেছে। উনি ছাড়া এমন একটা স্বাধীনতা সংগ্রামীর নাম বলতে পারবেন না যে শাস্তির ভয়ে মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে দেশের বিরুদ্ধে ব্রিটিশদের বুট পালিশ করেছে। ১৯২৪ সালে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে সাভারকর আর কক্ষনো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। আর ব্রিটিশ প্রভুর বশংবদ হয়ে থেকে কীভাবে তাঁকে সাহায্য করা যায়, সেই প্রচেষ্টাই করে গেছেন ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, ‘হিন্দুত্ব’ নামক এক বিভেদকামী তত্ত্ব বাজারে ছাড়া। যে তত্ত্ব মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বের আর-এক রূপ। বস্তুত আরএসএসের কোনো সদস্যই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই অংশগ্রহণ করেনি। তবে দেশের ভিতর সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়ানোর কাজটা সুচারুভাবে করে গেছে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ মদতে। চল্লিশের গোড়ার দিকে সাভারকর নেতাজির মুখের উপর বলেছিল— তাঁর এখন প্রধান কাজ ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ‘হিন্দু যুবকদের নাম লেখানো। তাঁর প্রিয় স্লোগান ‘রাজনীতির হিন্দুত্বকরণ’ ও ‘হিন্দুত্বের সামরিকীকরণ।
অথচ ভাবুন তো, যখন আত্মীয়পরিজন সহ বহু মানুষের চাপ ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত ভগৎ সিংয়ের উপর, তখন সবাই বলছেন ব্রিটিশের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে। মাত্র ২৩ বছরের যুবক ভগৎ সিং ব্রিটিশরাজকে চিঠি লিখলেন। তিনি লিখলেন, “তাঁদের যেন ফাঁসির পরিবর্তে ফায়ারিং স্কোয়াডে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা হয়! বিপ্লবী যতীন দাসের অসামান্য আত্মত্যাগ, কমরেড ভগবতী চরণ ও বীরযোদ্ধা চন্দ্রশেখর আজাদের গৌরবময় আত্মবলিদানের ধারাবাহিকতায়, তাঁদের আত্মত্যাগ, সামান্য এক সংযোজন মাত্র।” চিঠিতে পরিষ্কার করে তিনি জানিয়ে দেন, “এই লড়াই চলবেই।” এমনকী স্বপ্নের কথাও বলে যান সেই চিঠিতে, “ভারতের শ্রমজীবী মানুষ ভবিষ্যতে একদিন ব্রিটিশ বা ভারতীয় পরজীবীদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন।”
যে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে এত তুলকালাম করে থাকে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা, সেই হিন্দু কে বা কারা? গোলওয়ালকর বললেন– “When we say this is the Hindu nation, there are some who immediately come up with the questions about the Muslims and Christions dwelling in this land … but the crucial question is rather they remember that they are the children of this soil … no … together with the change in their faith gone is the spirit of love and devotion for the nation. They have also developled a feeling of identification with the enemy of this landf.” সাভারকরের হিন্দুর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে –“সিন্ধুনদ থেকে সমুদ্র অবধি বিস্তৃত ভারতবর্ষকে যে একযোগে পিতৃভূমি’ জ্ঞান করে, সে-ই হিন্দু।” “পিতৃভূমি ও পুণ্যভূমি’র সরল সমীকরণের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে সাভারকরের প্রার্থিত রাষ্ট্র-কাঠামো। ওই সমীকরণের মোদ্দা কথা হল— মুসলমান বা খ্রিস্টানরা যেহেতু আরব বা প্যালেস্টাইনকে তাঁদের পুণ্যভূমি’ জ্ঞান করে, তাই তাঁদের দেশাত্মবোধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব! সাভারকর লেখেন তাঁর ‘হিন্দুরাষ্ট্র বিষয়ক এক ইস্তেহার। সেই ইস্তেহারটি হল— (১) সংখ্যালঘুদের স্বাধীন ধর্মাচরণের সুযোগ থাকবে, কিন্তু কড়া নজর রাখা হবে যাতে সংখ্যাগুরুদের ন্যায়সম্মত অধিকার তারা কোনোমতেই খর্ব না করে, রাষ্ট্রের ভেতর আরেকটা রাষ্ট্র বানিয়ে না বসে। (সেই কারণে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অহর্নিশি চিৎকার করে বলে মমতা ব্যানার্জি পশ্চিমবঙ্গকে ‘ইসলামিক স্টেট’ ‘পাকিস্তান বানিয়ে দেবে মুসলিম তোষণ করে। মহানগরের রাজাবাজার বা পার্কসার্কাস বা খিদিরপুর বা গার্ডেনরিচ সহ রাজ্যের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে কত সহজে ও কৌশলেই ‘মিনি পাকিস্তান’ বলে দাগিয়ে দেয়।) (২) নাগরি জাতীয় লিপি, হিন্দি জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃত দেবভাষা রূপে পরিগণিত হবে। (হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা গত ৭০ বছর ধরে বোঝাতে চেয়েছে হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা। এই নির্জলা মিথ্যা কথা বহু মানুষ বিশ্বাসও করেন। সত্য হল ভারতের কোনো রাষ্ট্রভাষা নেই। কোনোদিনও হবে না। সেটা হতেও দেব না।) (৩) দু-হাত খুলে অভ্যর্থনা জানাতে হবে যন্ত্রযুগকে– শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের লক্ষ্যে ব্যক্তিপুঁজিকে নানাভাবে জোগাতে হবে সাহায্য ও উৎসাহ। (সেই কারণেই বোধয় ভারতের প্রথম সারির পুঁজিপতিরা হাজার হাজার কোটি টাকা ঝেড়ে দিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে যায়। আবার হাজার হাজার কোটি টাকা মকুবও করে দেওয়া হয়। করোনা আবহে দেশের জিডিপির হার মাইনাস ২৪, সাধারণ মানুষ যখন না-খেয়ে মরছে, আত্মহত্যা করছে, তখন দেশে ১৫ জন নতুন পুঁজিপতির জন্ম দিল। দেশে মোট পুঁজিপতি হল ১১৭ জন। একা আম্বানির জিডিপি হারই প্লাস ৪০। ) (৪) পুঁজিপতি ও শ্রমিক— দু-পক্ষের স্বার্থকেই নিয়ন্ত্রণ করা হবে জাতীয় প্রয়োজনের নিক্তিতে। কোনো শিল্পসংস্থা যদি দুর্ভাগ্যবশত লোকসানের মুখে পড়ে, তাহলে তার দায়ভাগ শ্রমিকদেরও নিতে হবে। (শিল্পসংস্থার লোকসান হলে শ্রমিকরা তার দায় ভাগ করে নেব, কিন্তু মুনাফার ভাগ হবে না।) (৫) ধর্মঘট-লকআউটের জেরে যদি উৎপাদন-ব্যবস্থা টালমাটাল হয়, তাহলে সে-সব কঠোর হস্তে দমন করবে রাষ্ট্র। (বাজপেয়ির সরকার থেকে মোদি সরকার– পোস্টাল বিভাগের ইডি কর্মচারীদের গণ-আন্দোলন থেকে এনআরসি বিরোধী গণ-আন্দোলন –সর্বত্রই আরএসএসের রক্তরসে তৈরি বিজেপির ভূমিকা আমরা দেখেছি। ইডিদের কর্মবিরতি আন্দোলন এক মাস চলার পর বাজপেয়ি সরকার জানিয়ে দিল, ‘কোনো দাবি মানা হবে না। হয় কাজে যোগ দিন, নইলে সেনা নামিয়ে কাজ চালাব। এর ফলে সেই আন্দোলন ভেস্তে গিয়েছিল বটে, তারপর থেকে পুরো ডাকব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়ল। আর উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সেই থেকে কুরিয়ার রাজ শুরু হয়ে গেল গোটা দেশে। এনআরসি বিরুদ্ধে গোটা দেশের মানুষ যখন পথে নামল, মাসের পর মাস পথের উপর অবস্থানে বসল, পুলিশ এলোপাথাড়ি গুলি করে আন্দোলনকারীদের মারল। দিল্লির হত্যাকাণ্ডে ৫০ জন মানুষ গুলিবিদ্ধ হল এবং মৃত্যু হল। সরকার আন্দোলনকারীদের কথা শোনা তো দূরের কথা, তখনও বলেই চলেছে। ‘এনআরসি হচ্ছেই’। বস্তুত রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নই ফ্যাসিবাদের মূল অস্ত্র।) (৬) ব্যক্তিগত মালিকানা হবে রাষ্ট্রীয় নীতির অন্যতম স্তম্ভ। (অর্থাৎ ‘একা খাব, একা খাবে’ নীতি। যৌথ যা কিছু, সামাজিক বিন্যাস থেকে অর্থনীতি, সবেতেই এদের বিরাট আপত্তি। ফলত আম্বানি-আদানিরাই হয়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় নীতির স্তম্ভ।) (৭) হিন্দুদের ‘পুণ্যভূমি’র নাম হবে ‘ভারত’ অথবা ‘হিন্দুস্থান’। (গোটা উপমহাদেশ তো একটি দেশের নাম ছিল না। ছিল অসংখ্য দেশ বা রাষ্ট্রের সমাহার, নগর-রাষ্ট্র। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য পৃথক, শাসকব্যবস্থা পৃথক, মুদ্রা পৃথক, সামরিক এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের হয় শত্রুপক্ষ অথবা মিত্রপক্ষ। প্রতিটি প্রদেশের প্রধান আরাধ্যা দেবতাও পৃথক। আছে নানা সম্প্রদায়ের পৃথক দেবতা। এক দেশ এক শাসন কবে ছিল এই উপমহাদেশে?
প্রথমেই আসি ভরত রাজার নাম থেকে ভারতবর্ষ নাম প্রসঙ্গে। ভরত নামক কোনো রাজাই সমগ্র উপমহাদেশের শাসক বা মালিক ছিলেন না। উপমহাদেশের একটি অতি ক্ষুদ্র অঞ্চলের গোষ্ঠীপতি ছিলেন তিনি। ঋগবেদে বর্ণিত ভরত জনগোষ্ঠীর নামানুসারে যে ভারতবর্ষের কথা বলা হয়েছে, তা মূলত যমুনা ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে। এই অঞ্চলেই ভরত জনগোষ্ঠীরা বসবাস করত। যমুনা ও সরস্বতীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে কেউ যদি ‘ভারতবর্ষ’ বলতে চায়, আপত্তি নেই। এবার আসা যাক ‘হিন্দুস্তান’ নাম প্রসঙ্গে। সুদূর অতীতে ‘হিন্দুস্তান’ বলতে বোঝাত উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলটিকে। অর্থাৎ উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণের বিন্ধ্য পর্বতমালার মধ্যবর্তী অংশই হিন্দুস্তান। একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী তুর্কি-আফগান মুসলিমরা ভারতের উত্তরাঞ্চলকে ‘হিন্দুস্তান’ নামে অভিহিত করে। বাস্পত্য সংহিতায় বলা হয়েছে –“হিমালয়ম সমারভ্য যবদিন্দুসারোভরং তাং দেবনির্মিতং দেশং হিন্দুস্থানং প্রচক্ষতে” –অর্থাৎ দেবতা নির্মিত যে দেশ হিমালয় থেকে ভারত মহাসাগর (ইন্দু সরোবর, সম্ভবত মানস সরোবরকেই বোঝানো হয়েছে।) পর্যন্ত প্রসারিত, তারই নাম ‘হিন্দুস্থান’। আজকের ভারতের মানচিত্রে হিন্দুদের পুণ্যভূমি কোন্ অংশ? ‘হিন্দু’ শব্দটি আমরা ঠিক কবে থেকে পেলাম? বুৎপত্তিগতভাবে হিন্দু শব্দটি দ্বারা সিন্ধু নদের অববাহিকায় বসবাসরত সকলকে বোঝানো হয়। হিন্দু এবং হিন্দি শব্দ দুটিকে সংস্কৃতির পরিচায়ক হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে সেই সমস্ত মানুষের জন্য, যাঁরা সিন্ধুনদের পাশে বসবাস করছেন। হিন্দু শব্দটি এসেছে (পার্সিয়ান হয়ে) সংস্কৃত শব্দ সিন্ধু (ঐতিহাসিক স্থানীয় সিন্ধু নদী বা ইন্ডাস্ রিভার) থেকে। এর অবস্থান ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে (বর্তমানে পাকিস্তান এবং উত্তর ভারতের অংশে)। গেবিন ফ্লাডের মতে, “আসল পরিভাষা হিন্দু প্রথম দেওয়া হয় পার্সিয়ান ভৌগোলিক পরিভাষা থেকে, যা দ্বারা সিন্ধু নদীর পাশে বসবাসকারী মানুষদের বোঝানো হত। শব্দটি দিয়ে তখন ভৌগোলিক অবস্থান বোঝানো হত এবং এর দ্বারা কোনো ধর্মকে বোঝানো হত না।” আঠেরো শতাব্দীর শেষের দিকে, ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও ঔপনিবেশিকরা ভারতীয় ধর্মের অনুসারীদেরকে একত্রে (একক কোনো ধর্মকে নয়) হিন্দাস’ হিসাবে নির্দেশ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ‘Hinduism’ বা হিন্দুধর্ম শব্দটি ইংরেজি ভাষায় সূচিত হয় ভারতীয়দের ধর্ম বিশ্বাস, দর্শন এবং সংস্কৃতিকে বোঝানোর জন্য। আর্যাবর্ত, যেখানে চতুঃবর্ণ ব্যবস্থার চল, অর্থাৎ উত্তর ভারত, তাকেই গোটা ভারত উপমহাদেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার অন্যায় প্রচেষ্টা।)
সাভারকররা মারাঠি জাতি। মূলত গোড়ার দিকে মারাঠিদের অস্তিত্ব প্রসঙ্গেই সবচেয়ে বেশি জাগ্রত ছিলেন। গুজরাটিরাও একই চিন্তাভাবনা বহন করে। কারণ গুজরাটি ও মারাঠিরা একই প্রদেশের মানুষ ছিলেন। উগ্র হিন্দুত্ববাদের জন্মদাতা এঁরাই। এঁরাই এঁদের তৈরি সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের বীজ গোটা উপমহাদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে সাভারকর শুরু করেন মরাঠি ভাষাশুদ্ধি আন্দোলন –মারাঠির সঙ্গে আরবি-ফারসির সংস্রব চুকিয়ে দেওয়ার আয়োজন ছিল সেটি। পিতৃভূমির যোগ্য জাতীয় পতাকার জন্যে সাভারকর তিন প্রতীক বেছে নেনে— কুণ্ডলিনী, ওঙ্কার ও কৃপাণ। নকশাটি হিন্দু মহাসভা’ গ্রহণ করলে ফাউ হিসেবে যুক্ত হয় স্বস্তিক। সাভারকরের অভিমত– “শস্ত্রবিহীন যে তার প্রণবনাদে কেউ কান দেয় না, হাতে কৃপাণ না-থাকলে মূলাধারচক্রে ঘা দিয়ে কুলকুণ্ডলিনীকে চাগিয়ে তোলা যায় না; ঐশীশক্তির দুর্লভ প্রেরণা কাম্য হলে হিন্দুদের আগে পরতে হবে যুদ্ধসাজ, অর্জন করতে হবে সামরিক প্রতিভা।”
সঙ্ঘীদের আদিগুরু বালকৃষ্ণ শিবরাম মুঞ্জে মূলত দুটো কারণ দেখিয়ে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। মুঞ্জে ছিলেন গান্ধির অহিংসা ও ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী। বুকে মণ্ডল, হাতে কমণ্ডলু, চোখে খোয়াইশ— একটি জঙ্গি হিন্দুত্ববাদী দল তৈরি করতে হবে। এরপর ১৯২৫ সালে তৈরি হয়ে গেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। ১৯৩১ সালে মুঞ্জে দেখা করে এলেন ফ্যাসিস্ট একনায়ক মুসোলিনির সঙ্গে। মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট দলের আদলে গড়ার স্বপ্ন দেখত ও দেখাতে সংঘ। মুঞ্জে-শিষ্য সাভারকর গুরুর স্বপ্ন সাকার করতে জানকবুল করবেন এতে অবাক হওয়ার কী আছে। প্রয়োজনে ব্রিটিশদের বুট চেটে সেই স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। গুরুর যোগ্যতম শিষ্য। সাভারকর কথা রেখেছেন মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত। ১৯৬১ সালে ১৫ জানুয়ারি প্রকাশ্য সভায় দেওয়া জীবনের শেষ অভিভাষণে সাভারকর বললেন— “কেবলমাত্র সামরিক সামর্থ্যের বাটখারা দিয়েই দেশীয় মহত্ত্বের পরিমাপ করা যায়; যে গণতন্ত্র ভীরু এবং পদে পদে শত্রুর সামনে মাথা নোয়াতে কুণ্ঠিত হয় না তা ত্যাজ্য; নপুংসক গণতন্ত্রের চেয়ে হিটলার শতগুণে শ্রেয়; ভারতের উচিত, তার সামরিক বাহিনীকে আরও আধুনিক ও জোরদার করা। ভারতের কর্তব্য ক্রমাগত নতুন ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধোপকরণ বানিয়ে চলা –যেমন, হাইড্রোজেন বোমা।”
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আরএসএসের প্রকট বিরোধিতা ছিল। ব্রিটিশদের তাঁরা শত্রু মনে করত না। বরং বন্ধু মনে করত। বরং ভারতের মুসলিমদেরই চরম শত্রু মনে করত। স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা বিরোধিতা করত বা এখনও করে তাঁরা কখনোই জাতীয়তাবাদী বা দেশপ্রেমিক হতে পারে না। এঁদের ‘রাজাকার’ বলে। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে রাজাকারের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রচুর রাজাকারের ফাঁসি হয়েছে। আমাদের দেশের রাজাকারদের জন্য সে ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কারণ এই রাজাকারদের উপজীব্যে ধর্মের উস্কানি আছে। আজ সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধীরাই দেশপ্রেমিক সেজেছে, দেশপ্রেম শেখায়।
স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আরএসএসের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে গোলওয়ালকর বলেছিলেন— “ব্রিটিশ বিরোধিতাকে ভাবা হচ্ছে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের সমার্থক। এই প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সমগ্র স্বাধীনতা আন্দোলন, তার নেতৃবর্গ ও সাধারণ মানুষের উপর বিনাশকারী প্রভাব ফেলেছিল” (চিন্তাচয়ন, প্রথম খণ্ড, পৃ: ১২৫)। অর্থাৎ আরএসএসের কাছে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল একটি প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন। ফলে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলা আরএসএস যে সর্বদাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখবে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাস্তবে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বা শান্তিপূর্ণ কোনো সংগ্রামেই আরএসএস অংশগ্রহণ করেনি। আরএসএস ভারতীয় জাতীয়তাবাদকেই স্বীকার করে না। হিন্দু মুসলিম-বৌদ্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের শত-সহস্র বছরের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এবং পরিশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অধীনে একই শোষণ-যন্ত্রণা, একই অত্যাচার-বঞ্চনার শিকার হওয়ার কারণে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে ভারতের গড়ে ওঠাকেই তাঁরা অস্বীকার করে। তাঁদের মতে, “আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে, সব কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসাবে এখানে বসবাস করেছে।” (গোলওয়ালকর, চিন্তাচয়ন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ১২৩-২৪)। আরএসএসের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোনো সারবত্তা নেই। আমরা একমত হতে পারি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে। তিনি বলেছেন –“কোনো সভ্যতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও পাওয়া যায় না। একটি সুসভ্য জাতি আসিয়া কোনো জাতির সহিত মিশিয়া যাওয়া ছাড়াই যে জাতি সভ্য হইয়া উঠিয়াছে-এরূপ একটি জাতিও জগতে নাই।” (বিবেকানন্দ রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪২)। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকেও স্মরণ করতে হয়। তিনি বলেছেন— “ভারতবর্ষের কেবল হিন্দু চিত্তকে স্বীকার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের সাহিত্য, শিল্পকলা, স্থপতিবিজ্ঞান প্রভৃতিতেও হিন্দু-মুসলমানের সংমিশ্রণে বিচিত্র সৃষ্টি জেগে উঠেছে। তারই পরিচয়ে ভারতবর্ষীয়ের পূর্ণ পরিচয়।” (রবীন্দ্র রচনাবলি, চতুর্দশ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯, বিশ্বভারতী সংস্করণ)।
আমাদের দেশ ভারত যখন ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল, যখন ব্রিটিশদের অত্যাচারে জর্জরিত, যখন দেশের তরুণেরা মুক্তির মন্দির সোপান তলে আত্ম বলিদান দিয়েছে, তখন কী ভূমিকা নিয়েছিল আরএসএস? ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলন গোটা দেশে ১৯২১-২২ সালে তীব্র রূপে ফেটে পড়েছিল। ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়গত পার্থক্য গৌণ করে হাজার হাজার মানুষ এক হয়ে আন্দোলনে নেমেছিলেন। অবিভক্ত বাংলাতেও এই আন্দোলন প্রবলভাবে আছড়ে পড়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতা সহ হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে হেডগেওয়ারের বিদ্বেষপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই গণসংগ্রামের মধ্যে আরএসএস প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ার দেখতে পেলেন ‘অশুভ শক্তির জাগরণ। তাঁর কথায়— ‘মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের ফলে দেশে উৎসাহ ক্ৰমে শীতল হয়ে যাচ্ছিল এবং এই আন্দোলন সৃষ্ট অশুভ শক্তিগুলি সমাজজীবনে বিপজ্জনকভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছিল। …অসহযোগের দুগ্ধ পান করে বেড়ে ওঠা যবন-সর্প তার বিষাক্ত নিঃশ্বাস নিয়ে দেশে দাঙ্গার প্ররোচনা দিচ্ছিল” (ভিশিকার-১৯৭৯, পৃঃ ৭)। ভারত ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে গোলওয়ালকর এও পর্যন্ত বলেছিলেন- “এই সংগ্রামের খারাপ ফল হতে বাধ্য।” ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলন থেকে তাঁরা নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্ত দিল্লি অ্যাসেম্বলিতে বোমা নিক্ষেপ করলেন, উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদে আলফ্রেড পার্কে ১৯৩১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হলেন বিপ্লবী নেতা চন্দ্রশেখর আজাদ। ১৯৩১ সালে ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরুকে ফাঁসি দিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গোটা দেশ যখন উত্তাল, সে সময় আরএসএসের কোনো সদস্যই সেই উত্তাল সময়ের শরিক হলেন না। ১৯৩০ সালের কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংয়ে বিনয়কৃষ্ণ বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশচন্দ্র গুপ্তের (বিনয়-বাদল-দীনেশ) ঐতিহাসিক অলিন্দ যুদ্ধ, ১৯৩০-৩২ সালের চট্টগ্রামে মাস্টারদা সূর্য সেনের বীরত্বপূর্ণ লড়াই থেকে শুরু করে প্রীতিলতার শহিদ হওয়া পর্যন্ত কোনও ক্ষেত্রেই আরএসএস তথা সংঘীদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসারদের বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৪৬ সালে নৌ-বিদ্রোহ, ওই বছরের ২৯ জুলাই দেশব্যাপী ধর্মঘট– কোথাও সংঘীরা নেই। কোনো যোগ ছিল না বলা যায় না। ১৯৩৯ সালে অটলবিহারী তখন আরএসএসের স্বয়ংসেবক। ১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে যোগ দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন অটল ও তাঁর দাদা প্রেম। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান মুচলেকা দিয়ে। অবশ্য ইতিহাসের অধ্যাপিকা তনভির নাসরিন বলেছেন –“অটলজির মুচলেকার ভিত্তিতে ১৯৪২ সালে লীলাধর বাজপেয়ির জেল হয়েছিলবলে দাবি করা হয়। কিন্তু পরে তদন্ত করে দেখা গেছে যে কাগজপত্র আদালতে পেশ করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে লীলাধর বাজপেয়ির পাঁচ বছরের জেল হয়। তাতে অটলজির মুচলেকা ছিল না। এক তরুণ যিনি তখন উর্দু জানতেন না। তাঁকে দিয়ে উর্দুতে লেখা একটি মুচলেকাপত্র সই করিয়ে নেওয়া ব্রিটিশ সরকারের জন্য মোটেও কঠিন কাজ ছিল না সে সময়।” বিয়াল্লিশে মাতেশ্বর গ্রামে আন্দোলন চলাকালীন ধৃত হন অটলবিহারী। উর্দু ভাষায় লেখা বয়ানের নিচে সই করেছিলেন। কিন্তু সেই বয়ান তাঁকে পড়ে শোনানো হয়েছিল বলে নিচে আরও একটি সই করেছিলেন তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট। পরে বহুবার এই বিষয়টি অটলবিহারী বাজপেয়িকে প্রশ্নের মুখে পড়ছে হয়। প্রতিবারই তিনি বলেছিলেন –“সত্যিটা লুকিয়ে আছে দুটোর মাঝখানে।”
না, এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামে আরএসএসের কোনো ভূমিকা নেই। বরং ব্রিটিশদের সাহায্যে একটাই কাজ করেছে– মুসলমানদের ধরো, মুসলমানদের পিটাও এবং মুসলমানদের দেশ থেকে বিতারিত করো। উপমহাদেশে মুসলিম সম্প্রদায়কে অতিষ্ট করে তুলেছিল, আতঙ্কিত করে তুলেছিল। যার ফল ভারত ভেঙে দু টুকরো। ভারত ভেঙে দুই টুকরো হয়ে যাওয়ার পরও শান্তি পায়নি। আজও একইভাবে মুসলমানদের ধরো, মুসলমানদের পিটাও এবং মুসলমানদের দেশ থেকে বিতারিত করো কার্যক্রম জারি রেখেছে। যদিও আরএসএসরা দেশভাগ চায়নি। আরএসএস চেয়েছিল ভারত উপমহাদেশকে মুসলিম শূন্য করতে। আরএসএসরা চেয়েছিল মুসলিমরা ভারত ছেড়ে যেখানে খুশি চলে যাক। ভারতে থাকতে পারবে না। ভারতে থাকতে হলে মুসলিমদের ‘হিন্দু হয়ে থাকতে হবে। ভারতীয় মুসলিমদের ‘জয় শ্রীরাম’, ‘বন্দেমাতরম’ ‘ভারত মাতা কি জয়’ বলতেই হবে। আদতে দেশভাগের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল ব্রিটিশ আর কংগ্রেসের। ১৯৪০-এর দশকে আরএসএসের ভূমিকা প্রসঙ্গে আন্ডারসন এবং ডামলে বলেছেন— “গোলওয়ালকর বিশ্বাস করতেন আরএসএসকে নিষিদ্ধ করার কোনোরকম অজুহাত ব্রিটিশ শাসকদের দেওয়া চলবে না।” ১৯৪৩ সালের ২৯ এপ্রিল গোলওয়ালকর আরএসএসের সদস্যদের উদ্দেশ্যে একটি নির্দেশ জারি করে আরএসএসের সমস্ত বিভাগগুলি বন্ধ করে দেন। এই আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আরএসএস সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়, “আরএসএস আইনশৃঙ্খলার পক্ষে এখনই বিপজ্জনক– এ কথা বলার যুক্তি নেই।” ব্রিটিশদের তরফ থেকে এর থেকে বড়ো পুরস্কার সংঘীদের আর কী হতে পারে।
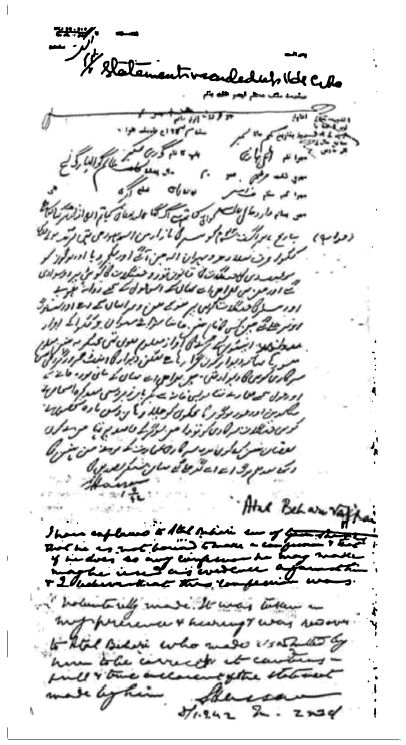
[অটলবিহারী বাজপেয়ির সেই মুচলেকা]
আরএসএসের লোকরা স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বলে সাভারকর জেলে গিয়েছিলেন, হেডগেওয়ার জেলে গিয়েছিলেন ইত্যাদি। সাভারকরের জেলের কীর্তি তো আগেই বলেই, এবার হেডগেওয়ারের কীর্তির কথা বলি। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের সময় হেডগেওয়ার জেলে গিয়েছিলেন বটে। আরএসএস প্রকাশিত তাঁর এক জীবনী গ্রন্থে বলা হয়েছে- “১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্যের ডাক দিয়েছিলেন। …ডাক্তার সাহেব (ডাঃ হেডগেওয়ার) সব জায়গায় খবর পাঠালেন সংঘ যেন। এই সত্যাগ্রহে অংশগ্রহণ না করে। সে যাই হোক, ব্যক্তিগত ভাবে যাঁরা অংশগ্রহণ করতে চাইবে তাঁদের বাধাও দেওয়া হবে না। এর অর্থ হল সংঘের কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না” (সিপি ভিশিকর, সংঘবিকাশ কে বীজ, ডাঃ কেশব রাও হেডগেওয়ার, নিউ দিল্লি, পৃ: ২০)। হেডগেওয়ার অবশ্যই সংঘের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেননি। তাহলে এসময় জেলে গেলেন কেন? আরএসএস প্রকাশিত হেডগেওয়ারের জীবনী গ্রন্থে লেখা হয়েছে— “ডাক্তার সাহেবের এই প্রত্যয় ছিল জেলের ভিতর তিনি একদল স্বদেশপ্রেমী, অগ্রগামী, নামজাদা লোক পাবেন। তাঁদের সঙ্গে তিনি সংঘ নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং সংঘের কাজে তাঁদের টেনে আনতে পারবেন। অর্থাৎ, স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে হেডগেওয়ার জেলে যাননি, তিনি জেলে গিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের যেভাবেই হোক স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে সরিয়ে ব্রিটিশদের বুট চাটাবে।
ভারত উপমহাদেশে হিন্দু মৌলবাদ যখন মধ্যগগনে, তখন মুসলিম মৌলবাদের উত্থান হল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বাতাবরণে মুসলিম নেতৃত্ব জেগে উঠল। ব্রিটেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের ব্যবচ্ছেদ ও তুরস্কের খলিফার ক্ষমতা খর্ব করলে ক্ষুব্ধ হয় ভারতীয় মুসলিমরা। এর ফলে ভারতের ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে খিলাফত আন্দোলন শুরু করে। অবশ্য মুসলিম লিগের সঙ্গে কংগ্রেসও ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলনে শামিল হয়। তবে কংগ্রেস খিলাফত আন্দোলনকে ঋণ ভেবে মুসলিম লিগও গান্ধিজির নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও স্বরাজের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে শোধ দিয়েছিলেন। এভাবেই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ তৈরি হলে সাময়িকভাবে হলেও সাম্প্রদায়িক বিভেদ হ্রাস পায়। এই সাময়িক সম্প্রীতিটা সে সময়ের রাজনীতিকরা দীর্ঘায়িত করতে ব্যর্থ হলেন সদিচ্ছা অভাবে।
অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন চলার সময় ভারতীয় রাজনীতিতে যে অভূতপূর্ব হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও আন্তরিকতার ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তা কিছুকাল পরেই দ্রুত ফ্যাকাশে হতে থাকল। কেন এমন হল? কারণ
(১) সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বাড়তে থাকল। ১৯২২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে কিছু আন্দোলনকারী চৌরিচৌরায় বেশ কিছু পুলিশকে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। ১৯২২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গান্ধিজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। এদিকে তখন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী নেতা কামাল পাশা (মোস্তাফা কামাল আতাতুর্ক)সেখানকার ক্ষমতা দখল করে খলিফার রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খলিফা পদের অবসান ঘটান। এর ফলে তুরস্কের খলিফার সমর্থনে ভারতে খিলাফত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া অর্থহীন হয়ে পড়ল। আন্দোলনও বন্ধ হয়ে গেল মাঝপথে। যে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মৈত্রী ও সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, আন্দোলন থেমে যেতেই সব উবে গেল। অতএব বোঝাই যায় এই সাময়িক সম্প্রীতির বাতাবরণ যে তৈরি হয়েছিল তা ছিল মেকি, বালির বাঁধ। আন্তরিক নয়, কার্য উদ্ধারের কৌশলমাত্র।
(২) ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে খিলাফত কমিটির সভায় পূর্ণ স্বরাজ ও সহিংস নীতি গ্রহণের প্রশ্নে হসরত মোহানি ও গান্ধিজির মধ্যে বিরোধ বাঁধে। গান্ধিজি পূর্ণ স্বরাজের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগে রাজি না-হলে উলেমা গোষ্ঠী ক্ষুব্ধ হয়। উলেমারা জঙ্গি আন্দোলনে বিশ্বাসী, চরমপন্থী সংগ্রাম চায়। এরপর খিলাফত আন্দোলন বন্ধ হলে একমাত্র মৌলানা মোহম্মদ আলি ও মৌলানা শওকত আলি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন –“আমরা প্রথমে মুসলিম, পরে ভারতীয়”।
(৩) এই সময়কালে একে অপরের প্রতিপক্ষ ভেবে নিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়। একদিকে যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা সংগঠন’ ও ‘শুদ্ধি’ আন্দোলনের উদ্যোগী হচ্ছিলেন, অপরদিকে তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতারা তানজিম’ ও ‘তাবলিগ’ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শক্তিবৃদ্ধির উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। ভাবটা এমন যে– যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
(৪) গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পরপরই হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা তৈরি হয়। উভয়পক্ষের অসহিষ্ণুতা ও ইন্ধনের ফলে উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। ১৯২৩ সাল থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৩ বছরের মধ্যে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে ৭২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ব্রিটিশ প্রশাসন তখন ভারতের মসনদে বসে বসে ভ্রাতৃঘাতী হত্যালীলার মজা নিচ্ছিল।
(৫) ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোর অধিবেশনে মোহম্মদ আলি জিন্নাহ গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে তীব্র সমালোচনা করেন এবং মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচন সমর্থন করেন। এই অধিবেশনে মুসলিম লিগ বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা এবং সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দাবি জানায়। এই সময় থেকে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগের ঐক্য বিনষ্ট হয়। এটা ছিল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক হঠকারিতা, যার ফল ভোগ করছে গোটা দেশের মানুষ। সেদিন যদি সামান্য নমনীয়তা প্রদর্শন করতে পারত, তাহলে হয়তো দেশটা শেষপর্যন্ত দু টুকরো হত না। যাই হোক, কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লিগের সম্পর্ক নষ্ট হলে লিগ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে সরে আসে এবং তাঁদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করতে থাকে।
(৬) ১৯২৭ সালে ভারতের নতুন সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সাইমন কমিশনের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেস এই কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। অপরদিকে জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগের একাংশ এই কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিলেও লিগের ‘পাঞ্জাব গোষ্ঠী নামে পরিচিত মোহম্মদ শফি, ফিরোজ খাঁ নুন, ফজলি হোসেন, মোহম্মদ ইকবাল এই কমিশনকে স্বাগত জানায়। বস্তুত স্বরাজ দলের পতনের ফল ১৯২৭ সাল থেকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন যখন নিস্তরঙ্গ হয়ে ওঠে তখন সাইমন কমিশনের নিয়োগ দেশে আবার কর্মচাঞ্চল্য এনে দেয়। ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন আবার উত্তাল হয়ে ওঠে। যখন ১৯১০ সালে ‘India Council Act’ পাশ হয়, তার ১০ বছর পরের একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করে সেই আইনের কার্যকারিতা বিচার করে দেখার কথা ঘোষণা করা হয়। সেই অনুসারে ১৯২৯ সালে একটি কমিশন নিয়োগ করার কথা। কিন্তু দু-বছর আগেই ব্রিটিশ সরকার এই কমিশন গঠন করার কথা ঘোষণা করে। কারণ প্রথমত, ১৯২৯ সালে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনের বছর। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের শাসন সংস্কারের দাবি ব্রিটিশ সরকারকে বাধ্য করেছিল দু-বছর আগেই কমিশন নিয়োগ করতে। তৃতীয়ত, কমিশন নিয়োগ এর উদারতাকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশ সরকার নির্বাচনে অনুকূল হাওয়া তৈরি করতে চেয়েছিল। স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ৭ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। সকলেই ছিলেন সাদা চামড়ার ব্রিটিশ। কোনো ভারতীয়কেই এই কমিশনে নেওয়া হয়নি। এই কমিশনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল— (ক) মন্টেগু-চেমসফোর্ড আইনের কার্যকারিতা বিচার করা, (খ) ভারতীয়দের প্রশাসনিক যোগ্যতার মূল্যায়ন করা এবং (গ) ভবিষ্যতে কতটুকু শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রয়োজন তা স্থির করা। এই সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশবাসীও বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। কারণ, প্রথমত, কমিশনে কোনো ভারতীয় সদস্য না-থাকায় সেখানে ভারতীয়দের দাবি-দাওয়া প্রতিফলিত হবে না। দ্বিতীয়ত, ভারতীয়দের শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা বিচার করবে একটি অ-ভারতীয় কমিশন, তা ভারতের পক্ষে খুবই মর্যাদা হানিকর। তাই দেশবাসী কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস এই মর্মে প্রস্তাব প্রথম দেয় –(অ) ভারতের সাইমন কমিশন যেদিন পদার্পণ করবে সেদিনই তাঁরা গণবিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। (আ) কমিশনের জিজ্ঞাসাবাদে কোনোরূপ সহযোগিতা করবে না। (ই) আইনসভা কর্তৃক কমিটি নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে। পরিশেষে কমিশনকে সামাজিক বয়কট করা হবে। মতাদর্শ নির্বিশেষে ভারতের সব রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করে সাইমন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ জানায়। বাধা-বিঘ্ন ও প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও সাইমন কমিশন কাজ চালিয়ে যায়। অবশেষে কমিশন ১৯৩১ সালে সরকারের কাছে তার রিপোর্ট ও সুপারিশ উপস্থাপন করে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাস হয়। সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনে দলমত-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে। ভারতের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া প্রথম শ্রেণির নেতাদের নিগ্রহ ও আত্মত্যাগ, সংবিধান রচনা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ প্রভৃতি এই আন্দোলনকে এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করেছিল, যা পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনকে অনেক বেশি গতিময় করে তোলে। (৭) ১৯২৮ সালের আগস্ট মাসে ভারতীয়দের সংবিধানের রচনার যোগ্যতা আছে কি না তা নিয়ে সাইমন কমিশনে প্রশ্ন তোলা হলে লখনউয়ে একটি সর্বদলীয় অধিবেশনে মতিলাল নেহরু সংবিধানের একটি খসড়া পেশ করে। এই খসড়া নেহরু রিপোর্ট নামে পরিচিত। ওই বছরেই ২২ ডিসেম্বর কলকাতার সর্বদলীয় অধিবেশনে মুসলিগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ ওই খসড়ায় লিগের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা দাবি করেন। অধিবেশনে তাঁর দাবিগুলি নাকচ হলে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে অধিবেশন ত্যাগ করেন এবং মোহম্মদ শফি, মোহম্মদ ইকবাল, আগা খাঁ প্রমুখ প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হয়। লিগের শক্তি বৃদ্ধি হয়। ১৯২৮ সালে জানুয়ারি মাসে পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে সভাপতি করে সর্বদলীয় সম্মেলনে একটি কমিটি গঠিত হয়, যার কাজ ছিল ভবিষ্যৎ ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ বিবেচনা ও নির্ধারণ করা, বিশেষত সাম্প্রদায়িক সমস্যাটি সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা ও শাসনতন্ত্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক নিরূপণ করা। ওই সম্মেলনে ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন মতামতের প্রায় ২৮টি প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধিত্ব করে। মতিলাল নেহরু ছাড়া অন্যান্য সদস্য ছিলেন আলি ইমাম, শোয়েব কোরেশি, এম.এস অ্যানি, এম.আর জয়াকর, জি.আর প্রধান, সরদার মঙ্গল সিং, তেজ বাহাদুর সপ্রু ও এম.এন যোশী। ওই সময়কার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কমিটির সচিব হিসাবে কাজ করেন। যেহেতু শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি কী হবে তা নিয়ে বামপন্থী ও ডানপন্থীদের মধ্যে প্রচণ্ড মতভেদ ছিল, তাই কমিটি একটি ফর্মুলা অবলম্বন করে যাতে বলা হয় যে, স্ব-শাসিত ডোমিনিয়নগুলির শাসনতন্ত্রের মডেলে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা হবে। কমিটি একটি খসড়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে গিয়ে যে সমস্ত সুপারিশের কথা বলে তার মধ্যে একটি ধারার ছিল সুদূরপ্রসারী প্রভাব, যা ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতাকে পুরোপুরি পাল্টে দেয়। রিপোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা যে মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করবে এমন সম্ভাবনাকে অমূলক ভীতি হিসাবে অভিহিত করা হয়। এটি পৃথক নির্বাচনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু শুধু সেখানে তাঁদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করে। তড়িঘড়ি করে প্রণীত খসড়া রিপোর্টটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্য, যেমন— পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রেখে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস অর্জন, দেশীয় রাজ্যসমূহের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাদি অক্ষুণ্ণ রেখে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য একটি পূর্ণ মর্যাদার। প্রদেশ প্রতিষ্ঠা এবং শাসনতন্ত্রে অধিকারসমূহের ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করা।
নেহরু রিপোর্ট বাংলার মুসলিম রাজনৈতিক অঙ্গনে গভীর মর্মবেদনার কারণ হয়েছিল। তাঁরা এর মাঝে হিন্দু আধিপত্যবাদের অপচ্ছায়া দেখতে পায়। প্রথম নির্বাচনের মূলনীতি ছিল বাংলার মুসলিম রাজনীতির অপরিহার্য শর্ত এবং হঠাৎ করে এর প্রত্যাখান মুসলমানরা প্রতিপক্ষ হিন্দুদের দ্বারা মুসলিম স্বার্থের উপর বিশ্বাসঘাতকতা বলে গণ্য করে। তাঁরা দাবি করে যে, যেহেতু এ প্রদেশটিতে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাই তাঁদেরকে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন প্রদান করা উচিত এবং তাঁদেরকে হিন্দুদের অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে শোষণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। হিন্দুরা এ দাবিগুলির ভিতর কোনো যৌক্তিকতা খুঁজে পায়নি। বরং তাঁরা দাবি করে যে, যদিও তারা সংখ্যালঘু, তবুও তাঁদের অতীতের কার্যাবলি ও বর্তমানের যোগ্যতার ভিত্তিতে সংসদে তাঁদের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য।
নেহরু রিপোর্ট একটি সর্বাত্মক দলিল হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়নি, শুধু শাসনতন্ত্রের ধরন কী হবে তা নিয়ে একটি আন্তঃদলীয় চুক্তি প্রণয়নই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাই এটি নতুনভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা ছাড়া তেমন অর্থবহ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারেনি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর চোদ্দো দফা, নেহরু রিপোর্টের সংশোধনী হিসাবে পেশ করা হয় এবং তার মধ্যে মুসলমানদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংরক্ষণের উপাদানসমূহ এতে সন্নিবেশিত হয়েছিল। খসড়া সংবিধানটিতে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকার, দায়িত্বশীল সরকার, জনগণের ১৯ টি মৌলিক অধিকার, সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার, কোনো ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনোরূপ সম্পর্ক না-রাখা প্রভৃতির উল্লেখ ছিল। ঐতিহাসিক সুমিত সরকার বলেন, “পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সরকার প্রণীত কোনো সংবিধানেই স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়নি।”
মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ সেই চোদ্দো দফা দাবিতে কী ছিল? একটু দেখে নেওয়া যাক –(১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন, (২) প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, (৩) আইনসভাগুলিতে মুসলিমদের যথেষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দান, (৪) মুসলিমদের জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ, (৫) মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, (৬) বাংলা, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রেখে ভারতের প্রদেশগুলির পুনর্গঠন, (৭) সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ধর্মপালনের স্বাধীনতা দান, (৮) কোনো আইনসভায় যে-কোনো সম্প্রদায়েরই তিন-চতুর্থাংশ সদস্য কোনো বিলের বিরোধিতা করলে সেই বিল প্রত্যাহার, (৯) প্রাদেশিক আইনসভায় অনুমতি ছাড়া সংবিধান পরিবর্তন না করা, (১০) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম সদস্য গ্রহণ করা, (১১) রাজ্য ও স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মুসলিমদের জন্য পদ সংরক্ষণ করা, (১২) সিন্ধু প্রদেশকে বোম্বাই প্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নতুন প্রদেশ গঠন করা, (১৩) বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাংবিধানিক সংস্কার ঘটানো এবং (১৪) মুসলিম শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ।
আপনারা সবাই জিন্নাহর চোদ্দো দফা দাবিগুলি পড়লেন। এই দাবিগুলিতে কোনো অংশে কি কোনোরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে? এই দাবিগুলিতে কোনো অংশে কি কোনোরূপ ভারতকে মুসলিম রাষ্ট্র বানানোর পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে? এই দাবিগুলিতে কোনো অংশে কি কোনোরূপ আলাদা পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে? এই দাবিগুলিতে কোনো অংশে কি কোনোরূপ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী চিন্তাভাবনার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে? সবকটি প্রশ্নের উত্তর– না। বরং বলা যায় এটি একটি গঠনমূলক প্রস্তাব। আধুনিকমনস্ক চিন্তার ফসল। বাদরের পিঠে ভাগ নয়, ন্যায্য বণ্টন। নেহরু রিপোর্টের সঙ্গে জিন্নার চোদ্দ দফা দাবিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিলে হয়তো অন্য ভারতের জন্ম দিতে পারতাম। পশ্চিম আর পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে দেখতে হত না। ধর্মনির্বিশেষে এক অখণ্ড ভারতের নাগরিক হতাম আমরা। ব্রিটিশদের পরাজয় হতই। আসলে ভারতভাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশদের জয়ী করে আমরাই হেরে গেলাম।
মজার ব্যাপার হল— ব্রিটিশ সরকার বরাবরই ভারতের জাতীয়তাবাদীদের ‘Elitist politicians’ বলে ব্যঙ্গ করত ও নিজেদের জনগণের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর বলে প্রচার করত। এই ‘Elitist politician’-রাই জনগণের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার দাবি করেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার কখনো এর ধারে কাছেও যায়নি। এই প্রসঙ্গে বলা উচিত শুধু মুসলিম লিগই নয়, ব্রিটিশ সরকার শিখ ও খ্রিস্টানরা, মাদ্রাজের অব্রাহ্মণ দল, ডঃ আম্বেদকরের অনুন্নত গোষ্ঠী প্রভৃতি নেহরু রিপোর্টের বিরোধিতা করেছিল।
অন্যদিকে বেশ কিছু মুসলিম নেতা ‘All India Liberally Federation’, বেশ কিছু সংখ্যাগরিষ্ঠ নেহরু রিপোর্টের প্রতি সমর্থন জানায়। জাতীয় কংগ্রেসও নেহরু রিপোর্টকে সানন্দে গ্রহণ করে। এটা ছিল কংগ্রেসের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক ভুল। মুসলমানদের বিরোধিতায় ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত পুলকিত হয়। ভারত সচিব ভাইকাউন্ট পিল ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইনকে মুসলমানদের প্রতি সহৃদয় আচরণ করতে বলেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারের ‘Divide and Rule’ নীতিরই জয় হল।
১৯৩০-এর দশকের শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের মুসলিমদের বিশ্বাস ছিল যে, স্বাধীনতার পর মুসলিমরা ব্রিটিশ ভারত নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে পারবে। হিন্দু ও স্বায়ত্তশাসন দাবি করা অন্যান্যরাও একই ধারণা পোষণ করত। তবে এর বাইরেও অনেকের মত ছিল। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লিগের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে স্যার মোহাম্মদ ইকবাল ভারতে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ডাক দেন। চৌধুরী রহমত আলি ১৯৩৩ সালে একটি পুস্তিকায় সিন্ধু অববাহিকায় ও ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অন্যান্য স্থানে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আহ্বান জানান। পাকিস্তান সৃষ্টিতে অবদান রাখায় তাঁরই আর-এক স্বদেশি এবং মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ নিজ দেশে যে বিপুল শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেছিলেন, তার কিয়দংশের দাবিদার ছিলেন তিনিও। কেন-না মৃত্যুর ১৮ বছর আগে তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন ‘পাকস্তান’ ধারণার। এমনকি ‘পাকস্তান’ নামটিও তো তাঁরই দেওয়া। ১৯৩৩ সালে রহমত আলি প্রকাশ করেছিলেন একটি পুস্তিকা, যার শিরোনাম তিনি দিয়েছিলেন ‘Now or Never : Are we to live or perish for ever?’ এর সঙ্গে একটি চিঠিও সংযুক্ত করেছিলেন তিনি, যেখানে লিখেছিলেন– “আমি আবেদন করছি ভারতের পাঁচটি উত্তরাঞ্চলীয় প্রশাসনিক একক –পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত (আফগান) প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানে বসবাসকারী ‘পাকস্তান’ এর ৩০ মিলিয়ন মুসলিমের পক্ষ থেকে। এই আবেদনে আছে তাঁদেরকে একটি পৃথক জাতি হিসাবে মর্যাদা দেওয়ার দাবি, যা ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের থেকে স্বতন্ত্র। পাশাপাশি ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণে পাকস্তানের জন্য একটি পৃথক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অনুমোদন করারও দাবি। হিন্দু-মুসলিম যে বিরাট সমস্যা সেটির সমাধানকল্পে আমাদের প্রস্তাবিত সমাধান সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত আমাকে জানালে আমি খুব খুশি হব। আমার বিশ্বাস, যেহেতু আপনারাও এই জটিল সমস্যার একটা ন্যায়সংগত ও স্থায়ী সমাধানে আগ্রহী, সেহেতু এই আবেদনে যে লক্ষ্যগুলি বর্ণিত হয়েছে সেগুলির প্রতি আপনাদের পূর্ণ সম্মতি ও সক্রিয় সমর্থন থাকবে।”
এভাবেই নিজেকে ‘পাকস্তান জাতীয় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা দাবি করে, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত (আফগান) প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সহযোগে মুসলিমদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি পেশ করেছিলেন আলি, যেটির প্রাথমিক নাম তিনি দিয়েছিলেন পাকস্তান। ইংরেজিতে ‘Pakstan’ শব্দটির মাধ্যমে তিনি তাঁর উল্লিখিত পাঁচটি অঞ্চলকে নির্দেশ করেছিলেন। পাঞ্জাবের P, আফগান প্রদেশের A, কাশ্মীরের K, সিন্ধুর ১, এবং বেলুচিস্তানের tan নিয়ে তৈরি হয়েছিল Pakstan। অবশ্য ‘পাকস্তান’ উচ্চারণ শ্রুতিমধুর হচ্ছিল না বলে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের পূর্বেই মাঝে ‘ই’ যোগ করে সৃষ্ট ‘পাকিস্তান’ শব্দটি বেশি জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়, এবং আলিও সেটিকেই মেনে নেন।
রহমত আলি তাঁর পরবর্তী একটি বইয়ে পাকিস্তান শব্দটির ব্যাখ্যা আরও বিশদে বিবৃত করেন— “পাকিস্তান একই সঙ্গে ফারসি ও উর্দু শব্দ। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় আমাদের আবাসভূমিগুলোর নাম। যেমন— পাঞ্জাব, আফগানিয়া, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান থেকে গঠিত হয়েছে। এর অর্থ পাকদের ভূমি –যাঁরা আত্মিকভাবে পবিত্র ও বিশুদ্ধ।” রহমত আলির পাকিস্তানের দাবিতে যে কথা বলা হয়েছিল, সেখানে উল্লেখ ছিল না মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার কথা, যা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর প্রথমে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে ভারতের অন্যান্য মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর জন্যও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন আলি দেখেছিলেন। যেমন বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের জন্য তিনি প্রস্তাব করেছিলেন ‘বঙ্গিস্তান’ নামটি এবং দক্ষিণ ভারতের নিজাম শাসিত অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য ‘ওসমানিস্তান। এছাড়া মুসলিমদের জন্য তাঁর প্রস্তাবিত আরও ছোটো ছোটো বেশ কিছু স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের মধ্যে ছিল ‘হায়দারিস্তান’, ‘সিদ্দিকিস্তান’, ‘ফারুকিস্তান’, মুইনিস্তান’, ‘মাপলিস্তান’, ‘সাফিস্তান’, ‘নাসারিস্তান’ (শেষ দুইটি শ্রীলঙ্কার অন্তর্ভুক্ত) ইত্যাদি। তাঁর হাত থেকে বাদ পড়েনি এ অঞ্চলের সাগরগুলোও। বঙ্গোপসাগরের সম্ভাব্য নতুন নাম তিনি দিয়েছিলেন ‘বজিয়ান সাগর’, পাকিস্তানি উপকূলে আরব সাগরের নাম ‘পাকিয়ান সাগর’, লক্ষদ্বীপ সাগরের নাম ‘সাফিয়ান সাগর। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অবস্থানে গড়ে ওঠা বৈচিত্র্যপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের নাম তিনি দিতে চেয়েছিলেন ‘পাকাশিয়া’ (Pakasia) বা ‘দিনিয়া’ (Dinia)। খেয়াল করে দেখুন, দ্বিতীয় শব্দটি India’ শব্দের অক্ষরগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে সৃষ্ট। এছাড়া শব্দটি ধর্মের আরব্য ধারণা ‘দ্বীন’ হতেও অনুপ্রাণিত। বোঝাই যাচ্ছে চৌধুরী রহমত আলি ‘প্যান ইসলামিক নামে ভয়ংকর এক অসুখে অসুস্থ একজন ব্যক্তি।
যাই হোক, অনেক কংগ্রেস নেতা ভারত রাষ্ট্রের জন্য একটি ক্ষমতাশালী কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতী হলেও জিন্নাহ সহ বহু মুসলিম রাজনীতিবিদরা নিজ সম্প্রদায়ের জন্য শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া তা মানতে অস্বীকৃতি জানান। কংগ্রেসের অন্যান্য মুসলিম সমর্থকরা স্বাধীনতার পর ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের ব্যাপারে সমর্থন জানালেও মদনমোহন মালব্য, বল্লবভাই প্যাটেল ও অন্যান্য সমমনা নেতারা স্বাধীন ভারতে গোরু হত্যা নিষিদ্ধের মতো আইন এবং উর্দুর পরিবর্তে হিন্দিকে সরকারি স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী ছিলেন। এসব কর্মকাণ্ডের ফলে মুসলিমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে। তবে কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিমদের সমর্থন একেবারেই উঠে যায়নি। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস ও লিগ জোট সরকার গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরে। প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকার মুসলিমদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুভূতি অনুধাবনের চেষ্টা করেনি। এসব কারণে কংগ্রেসের এই শাসনের পরই শুধু মুসলিম লিগ পাকিস্তানের দাবি তোলে। মুসলিম লিগ দাবি করে যে, তাঁরা মুসলিমদের স্বার্থ একাই সুরক্ষা করতে সক্ষম। ইতিহাসবিদ আকবর এস আহমেদের মতে জিন্নাহ নিজের মুসলিম পরিচয়, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে নিজস্ব হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আমৃত্যু এই পরিচয় তার মধ্যে বজায় থাকে। এছাড়া ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিক থেকে তিনি মুসলিম পোশাক গ্রহণ করতে থাকেন।
১৯৩৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলাইন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা করেন। শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। পরের দিন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলাপ না-করে ভারতের যুদ্ধে প্রবেশের ঘোষণা দেন। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সেই প্রসঙ্গে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ১৯৪১ সালে ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার ২৩ তম অধিবেশনে বলেন— “ভারতের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, ভারত সরকারের সমস্ত যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে হিন্দুদের অবশ্যই দ্বিধাহীন চিত্তে সমর্থন করতে হবে। ..হিন্দুদের বৃহৎ সংখ্যায় সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে যোগ দিতে হবে” (সাভারকর সমগ্র, খণ্ড-৬, মহারাষ্ট্র প্রান্তিক হিন্দু সভা, পৃ: ৪৬০)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য পূরণের জন্য যখন নতুন সশস্ত্র ব্যাটেলিয়ান তৈরির সিদ্ধান্ত নিল, তখন সাভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এই প্রচেষ্টাকে সফল করতে একটা বড়ো সংখ্যক হিন্দু যুবকদের নাম নথিভুক্ত করাতে হবে। সেদিন হিন্দু মহাসভা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য দেশের নানা প্রান্তে সহায়ক কেন্দ্র খুলেছিল, যাতে হিন্দু যুবকেরা সহজেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে। এই বাহিনীকেই ব্রিটিশ পাঠিয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের হত্যা করতে। সাভারকর সেই কাজে ব্রিটিশদের পাশে ছিলেন। এই গোলামির পুরস্কারস্বরূপ ভাইসরয়ের জাতীয় প্রতিরক্ষা কাউন্সিলে সাভারকরের পছন্দমতো লোক মনোনীত করা হল। সে জন্য টেলিগ্রামে ভাইসরয়কে ধন্যবাদ দিলেন সাভারকর। টেলিগ্রামটি এই রকম—- “Your Excellence Announcement Defense Committee With Its Personnel Is Welcome Hindu Mahasabha Views With Special Satisfaction Appointment of Messrs. Kalikar And Jamandas Mehta” (‘Binayak Damodar Savarkar Whirl Wind Propaganda’– AS Binde, P 451)। ১৯৪২ সালে হিন্দু মহাসভার কানপুর অধিবেশনে সাভারকর বলেছিলেন— “বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে। হিন্দু মহাসভা জানে যুক্তিসংগত আপসের দ্বারাই আমাদের এগোতে হবে। এই যুক্তিসংগত আপসের প্রমাণ হল সম্প্রতি সিন্ধু প্রদেশে একত্রে সরকার চালানোর জন্য হিন্দু মহাসভা মুসলিম লিগের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। … বাংলায় ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রীত্বে এবং আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির পরিচালনায় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা সাফল্যের সাথেই চলছে।” (সাভারকর সমগ্র- খণ্ড ৬, পৃ: ৭৯-৮০) এই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ব্রিটিশ বিরোধিতার জন্য তৈরি হয়নি। সাভারকরের ‘পরম শ্রদ্ধেয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বলেছিলেন, “এখন যুদ্ধকালীন অবস্থায় জাতীয় গভর্নমেন্ট এমনভাবে গঠিত হবে যাতে মিত্রপক্ষের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় যুদ্ধ করা সম্ভব হয়” (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ, পৃঃ ১১৬)। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিয়াল্লিশের (১৯৪২) ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনেরও বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন— “আমি মনে করি না, গত তিন মাসের মধ্যে যেসব অর্থহীন উচ্ছঙ্খলতা ও নাশকতামূলক কাজ করা হয়েছে, তার দ্বারা আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভের সহায়তা হবে।” (রাষ্ট্র সংগ্রামের এক অধ্যায়— শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, পৃঃ ৬১) ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন শ্যামাপ্রসাদের কাছে অর্থহীন উচ্ছলতা’ ও ‘নাশকতামূলক কাজকর্ম বলে মনে হয়েছে। তাঁর কথা অনুযায়ী মাতঙ্গিনী হাজরাদের বলিদান ফালতু! তাই তিনি মনে করতেন— এই আন্দোলন দমন করা উচিত এবং কীভাবে এই আন্দোলন দমন করা যায়, তার একটা তালিকাও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে পেশ করেছিলেন।
এদিকে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না-করার প্রতিবাদে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রকগুলি পদত্যাগ করে। এর বিপরীতে মুসলিম লিগ যুদ্ধের প্রচেষ্টায় ব্রিটেনকে সমর্থন করেছিল। মুসলিম লিগ এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিল যে, কংগ্রেস দ্বারা প্রভাবিত স্বাধীন ভারতে মুসলিমদের সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হবে। হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত ছিল না, তাঁরাও যুদ্ধপ্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। দুই প্রধান শিখ গোষ্ঠী, ইউনিয়নপন্থী এবং অকলি দলও ব্রিটেনকে সমর্থন করে এবং বৃহত্তর সংখ্যায় শিখদের বিশ্বযুদ্ধের সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে আহ্বান জানায়।
অপরদিকে ভারতজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভও দেখা দেয়। জিন্নাহ ও গান্ধির সঙ্গে সাক্ষাতের পর লিনলিথগো ঘোষণা করেন যে, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত ভারতের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়ে আলোচনা মুলতবি রাখা হল। ১৪ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস একটি অধিবেশনে তাৎক্ষণিক স্বাধীনতা দাবি করে। দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে ১০ নভেম্বর আটটি প্রাদেশিক সরকার পদত্যাগ করে এবং এসব প্রদেশের গভর্নররা এরপর থেকে ফরমান জারি করে শাসন করতে থাকেন। অন্যদিকে জিন্নাহ ব্রিটিশদের গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। ফলে ব্রিটিশরাও তার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং মুসলিম লিগকে ভারতের মুসলিমদের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা শুরু করে। তবে মুসলিম লিগ যুদ্ধে ব্রিটেনকে কার্যতভাবে সমর্থন করেনি। স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ভাইসরয় জিন্নাহর কাছে মুসলিম লিগের অবস্থান জানতে চায়। সাংবিধানিক উপকমিটিতে শর্ত প্রদানের জন্য ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারি মুসলিম লিগের ওয়ার্কিং কমিটি চারদিন ধরে বৈঠক করে। ৬ ফেব্রুয়ারি জিন্নাহ ভাইসরয়কে জানান যে, মুসলিম লিগ ফেডারেশন পৃথক রাষ্ট্রের পক্ষপাতী। লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বকে গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে ব্রিটিশ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বের প্রদেশগুলোর জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রস্তাব করা হয় এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য সুরক্ষার কথাও বলা হয়। ১৯৪০ সালে ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লিগের অধিবেশনে এই প্রস্তাবই পাশ হয়।
যখন দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা উঠলই তখন প্রশ্ন ওঠে জিন্নাহই কি এই দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভাবক? ভারত-ভাগের জন্য জিন্নাহর এই দ্বিজাতিতত্ত্বকে দায়ী করা হয়ে থাকে। বহু বহু বছর ধরে এই কথা ইতিহাসে বলা হয়েছে, জিন্নাহই দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলে ভারত ভাগ করেছে। বহু ইতিহাস লেখক কংগ্রেসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে ভারত-ভাগের সমস্ত দায় জিন্নাহর কাঁধে চাপিয়েছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস গ্রন্থে বর্তমানেও তাই আছে। দেশভাগ বলতে যদি বাংলা ভাগ ও পাঞ্জাব ভাগ বোঝানো হয়, তাহলে সেটা জিন্নাহ কোনোদিনই চাননি। তখনকার সময় পাঞ্জাব ও বাংলাকে রাজনৈতিক বিবেচনায় একটি পূর্ণ জাতীয় ভুখণ্ড বোঝাত। অর্থাৎ পাঞ্জাবি ও বাঙালিদের মধ্যে জাতিসত্ত্বার বিকাশ এমন পর্যায়ের পৌঁছেছিল যা রাজনৈতিকভাবে অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে জাতি হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ঘটনার পর্যবেক্ষণে যেটা বেরিয়ে আসে সেটা হল জিন্নাহ কখনোই পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হোক, তা চাননি। পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ হয়েছে হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের (সর্দার প্যাটেলের) গোয়ার্তুমির কারণেই। তাঁদের বক্তব্য ছিল, গোটা ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কলোনী ভাগ হলে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করতে হবে। ফলে ভাগ হয়েছে দুটি দেশ— পাঞ্জাব এবং বাংলা। যাকি অঞ্চলসমুহ দেশ পর্যায়ে উন্নীত ছিল না। আর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কলোনীকে দেশ মনে করাটাই নিরেট অজ্ঞানতা ছাড়া কিছুই নয়। অবশ্যই গণতান্ত্রিক সমাজে যে যা খুশি দাবি বা বক্তব্য চালিয়ে যেতে পারে। নিরপেক্ষভাবে তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যদি তা মানসম্মত হয়।
ইতিহাসের সাল-তারিখের নিরিখে প্রথম দ্বিজাতিতত্ত্বের উত্থাপন করেছিলেন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিবিদ সৈয়দ আহমদ খান বাহাদুর, ১৮৮৮ সালে। তিনি বললেন– “ভারতে হিন্দু ও মুসলমান নামক দুটি জাতি বাস করে। ইংরেজরা চলে গেলে তাঁদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হবে। হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে থাকতে পারবে এই নিষ্ফল আশা পোষণ না-করাই উচিত।” স্যার সৈয়দ আহমদ বলেন –”Is it possible that under these circumstances two nations– the Mohammadan and Hindu– could sit on the same throne and remain equal in power? Most certainly not. It is necessary that one of them should conquer the other and thrust it down. To hope that both could remain equal is to desire the impossible and the inconceivable.” তবে সৈয়দ আহমদের কথায় পৃথক রাষ্ট্রের কোনো রূপ ও রেখা ছিল না। নেহাতই হিন্দু ও মুসলিম পৃথক জাতি একথাই বলেছেন। পৃথক ধর্ম পৃথক জাতি তো বটেই। এর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। আমরা যেমন একাধারে বাঙালি জাতি, হিন্দু জাতি ও মুসলিম জাতি এবং ভারতীয় জাতি। সবই সত্য। তা ছাড়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তখনও পর্যন্ত বিকশিত হয়নি।
আমরা ইতিহাসে লাল-বাল-পালের কথা পড়েছি স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে। অবশ্য তাঁরাই স্বাধীনতা সংগ্রামী। কিন্তু এ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যতটা-না ছিল ব্রিটিশদের কাছ থেকে, তার চেয়ে বেশি ছিল মুসলিমদের কাছ থেকে। লাল’ হলেন ‘পাঞ্জাব কেশরী’ লালা লাজপত রায়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা। আরএসএসের জন্মের এক বছর আগেই লালা লাজপত রায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশভাগের প্রস্তাব উপস্থাপিত করে ফেলেছেন। ১৯২৪ সালে নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লালা লাজপত রায় ‘ইরাবতী থেকে ব্ৰহ্মপুত্র’ নামে ধারাবাহিকভাবে ট্রিবিউন’ পত্রিকায় তেরোটি প্রবন্ধ লেখেন, সেখানে তিনি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভারত ভাগের কথা উচ্চারণ করেন। (জাতীয়তাবাদী জিন্নাহ— মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়) তিনি সেখানে ‘হিন্দু ভারত’ মুসলিম ভারত’ কথাটি প্রথম উচ্চারণ করেন এবং হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার জন্য দরকার বোধে বাংলা এবং পাঞ্জাব ভাগ করার কথাও লিখেছিলেন। (জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা— যশোবন্ত সিংহ) তাহলে দেখা যাচ্ছে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবক কংগ্রেসেই। হিন্দু পুনরুত্থানবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্বের স্রষ্টা লালা লাজপত রায় প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার উদগ্র বাসনায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পিছনে ‘সেফটি ভালভ’ তত্ত্বের অবতারণা করেন। লাহোরের ‘প্রতাপ’ পত্রিকায় লালা লাজপত রায়ের ভাবশিষ্য নেতা লালা হরদয়ালের একটি প্রবন্ধে ভয়াবহ উগ্র আত্মম্ভরিতা প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। তিনি ঘোষণা করেন যে, হিন্দুস্থানের এবং পাঞ্জাবের হিন্দু জাতির ভবিষ্যত চারটি স্তম্ভের উপর উপর নির্ভরশীল। হিন্দু সংগঠন, হিন্দু রাজ, হিন্দুস্থানের মুসলমানদের হিন্দুধর্মে দীক্ষা প্রদান এবং আফগানিস্তান ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলি জয় করে সেইসব দেশের মানুষকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দান। না-হলে হিন্দুরা সবসময় বিপদের মধ্যে থাকবে এবং হিন্দু। জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পরবর্তী অধিবেশনে বলা হয়, বলপ্রয়োগ করে যেসব হিন্দুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের আবার হিন্দুধর্মের ছত্রছায়ায় ফিরিয়ে আনতে হবে; হিন্দি ভাষা জনপ্রিয় করতে হবে এবং হিন্দু উৎসব অনুষ্ঠানের প্রসার ঘটাতে হবে। (হিন্দু ধর্ম ও ভারতীয় হিন্দু সমাজ— এ. জি. বেলস্কি) অথচ ভাবতে অবাক লাগে এটা ভেবে যে, লালা হরদয়াল যে কলেজে অধ্যয়ন করতেন, সেই কলেজে দর্শনশাস্ত্র পড়াতেন মোহাম্মদ আল্লামা ইকবাল। ইকবাক, ‘সারে জহাঁ সে অচ্ছা হিন্দোসিহ্যাঁ হমারা/হম বুলবুলে হ্যায় ইসকি ইয়ে গুলসিত হমারা’ অপূর্ব অমর সংগীতটির স্রষ্টা। লালা হরদয়ালের সঙ্গে ইকবালের সুগভীর মিত্রতার সম্পর্ক ছিল। লালা হরদয়ালের অনুরোধে মোহাম্মদ ইকবাল অ্যাসোসিয়েশনের উৎঘাটন সমারোহে অধ্যক্ষতা করার জন্য রাজি হন। এমনকি সেই সমারোহ অনুষ্ঠানে ইকবাল তাঁর এই প্রসিদ্ধ গানটি গেয়ে শোনান। ইকবালের প্রতিষ্ঠিত জামায়েত ইসলামি পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামি পুনর্জাগরণের স্বপ্ন দেখেছিল। ১৯৩০ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের এক অধিবেশনে বললেন –“হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে মাত্র ৮ কোটি মুসলমান। সকলের মাঝে এঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই এর সমাধান হিসাবে হয় ব্রিটিশদের গোলামি করতে হবে, নয় সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক ও ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যেতে হবে।”
তৃতীয়বার দ্বিজাতিতত্ত্ব উচ্চারিত হল হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকারের মুখ দিয়ে। তিনি ১৯৩৭ সালে ৩০ ডিসেম্বর হিন্দু মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে বললেন– “প্রধানত দুটি জাতি ভারতবর্ষে, হিন্দু এবং মুসলিম।” তিনি পুনরায় ১৯৩৮ সালে বললেন– “ভারতবর্ষে, আমাদের হিন্দুস্থানে হিন্দুরাই হল প্রধান জাতি আর মুসলমানরা সংখ্যালঘু একটি গোষ্ঠী।” হিন্দু মহাসভার ১৯৩৬ সালের এক বিবৃতিতে বলা হয় –“হিন্দুদের মনে রাখা উচিত যে হিন্দুস্থান একমাত্র হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমি এবং তাঁদের জীবনের লক্ষ্য হল আর্য-সংস্কৃতি এবং হিন্দু ধর্মের বিকাশ সাধন। ভারত একমাত্র হিন্দুদেরই দেশ এবং হিন্দু সংস্কৃতির বাহক।” সাভারকার ১৯৩৭ সালে আবার হিন্দু জাতীয়তাবাদের তত্ত্বকে এক সম্পূর্ণ ও সর্বব্যাপী রূপ প্রদান করেন। তিনি ভারতে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিষয়ক তত্ত্বের মূল বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, সেই তত্ত্বের বনিয়াদ হল পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত চারটি বিশ্বাস— হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরাজ। সাভারকারের মতে, হিন্দুস্তানে উদ্ভুত যে-কোনো ধর্মের মানুষই হিন্দু। যেমন— হিন্দু, শিখ, বুদ্ধ, জৈন। কিন্তু মুসলমান আর খ্রিস্টানরা নয়। সেই সঙ্গে তিনি দাবি তোলেন যে, হিন্দুরাই হিন্দুরাষ্ট্রের পুরোদস্তুর নাগরিক। হিন্দুদের পবিত্র ভূমির উপর দাবি উত্থাপনকারী মুসলমানদের তিনি বিদেশি’ আখ্যা দিয়ে ‘অখণ্ড ভারত’ ধ্বনি তোলেন। সাভারকারের মতে, “স্বাধীন ভারতই জাতি-রাষ্ট্র হিসাবে একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র অথবা হিন্দুরাজই হতে পারে। কিছুদিন পর বলা হল, “হিন্দুরাই প্রথম শ্রেণির নাগরিক আর মুসলিম সম্প্রদায় হল ‘দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। অতএব সর্বাগ্রে মুসলিমদের ভারত থেকে বিতাড়িত করতে হবে। মুসলমানদের ভারতে থাকতে হলে, হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেই থাকতে হবে।” এরপর মুসলিম সম্প্রদায়দের আর করণীয় থাকতে পারে? যা করা উচিত, যে প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত, যে ভাবনা ভাবা উচিত, সেটাই ভাববে যেটা সবাই ভাববে। এই বাতাবরণে জিন্নাহের দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রকাশে আমি কোনো অন্যায় দেখি না। আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার সবার আছে, আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার সবার থাকা উচিত। আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকার যদি হিন্দু সম্প্রদায়ের দস্তুর হয়, মুসলিমদের ক্ষেত্রেও দস্তুর। জাত্যাভিমানকে অস্বীকার যায় না। জিন্নাহ দ্বিজাতি তত্ত্বের কথা বলেন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তার আগে বহুবার দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা বলেছেন বর্ণহিন্দুরাই। জিন্নাহ হিন্দুদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বহু পরে দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে নেন মাত্র। বরং বলা যায়, জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্ব আসলে উভয়পক্ষের সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত। হিন্দুত্ববাদীরা তো এটাই চেয়েছিল। হিন্দুত্ববাদীদের যে মনোস্কামনা পূর্ণ হয়নি, তা হল, শেষপর্যন্ত মুসলিম শূন্য হিন্দুরাষ্ট্রটাই গড়তে পারেনি। সেটা বাস্তবিকও নয়। মাঝখান থেকে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে জোড়া তো দূরের কথা, দেশটাই দু টুকরো হয়ে গেল। লাভ তো হলই না, উলটে প্রভূত লোকসান হল। দেশভাগ কি আটকানো যেত না? অবশ্যই যেত। আসলে কারোর সদিচ্ছা ছিল না। সদিচ্ছা ছিল না কংগ্রেসের। জিন্নাহর মনে বিশ্বাস ছিল, কংগ্রেস আর গান্ধি মিলে এর একটা সুরাহা করবেন। ফলে তিনি হিন্দু মহাসভার উস্কানিকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন অনেকদিন পর্যন্ত।
যাই হোক, লাহোর প্রস্তাব নিয়ে গান্ধি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে তিনি বলেন যে, ভারতের অন্যান্যদের মতো মুসলিমদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এ নিয়ে বেশ সরব ছিলেন। যদিও জওহরলাল নেহরু লাহোর প্রস্তাবকে ‘জিন্নাহর চমৎকার প্রস্তাব’ বলে অবিহিত করেন। নেহরু কেন বললেন এমন কথা? নেহেরু আন্তরিকভাবেই চেয়েছিলেন জিন্নাহ মতো প্রভাবশালী মানুষ ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াক। কারণ জিন্নাহর উপস্থিতিতে তাঁর পক্ষে স্বাধীন ভারতের অভিভাবক হওয়া মুশকিলের ব্যাপার। এদিকে জিন্নাহকে গেলাও যাচ্ছে না, ফেলাও যাচ্ছে না। নেহরু বুঝে গেছেন এই ভারত উপমহাদেশে নেহেরুর যতটা গ্রহণযোগতা, ঠিক ততটাই জিন্নাহর গ্রহণযোগতা। এক বনে দুটো সিংহ তো পাশাপাশি থাকতে পারে না। নেহরুও তাই মনে মনে খুঁজছিলেন এমন একটা পথ, যে-পথে শ্যাম ও কুল দুই-ই রাখা যাবে। সাপ মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। জিন্নাহও নেহরুর মনের কথা পড়ে ফেলেছিলেন। একই পরিবারে থেকে দুই ভাইয়ে কোন্দল না-করে পাকাপাকি পাকিস্তানের প্রস্তাব দিলেন। নেহরু হবেন মূল ভূখণ্ড ভারতের অভিভাবক, জিন্নাহ। হবেন নতুন দেশ পাকিস্তানের অভিভাবক। ল্যাঠা চুকে গেল। না, সেই ল্যাঠা পুরোপুরি চুকলো না। কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতের ৭০ বছরেও সেই ল্যাঠা চোকানো যায়নি। সেই ল্যাঠার নাম ‘কাশ্মীর। পরের অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রইল।
ভারত যেমন বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারেনি, তেমনই বিনা রক্তপাতে ভারত ভাগও হয়নি। ব্রিটিশ শাসন ও অনুমিত বৰ্ণহিন্দুর আধিপত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম লিগ আহুত হরতাল ডাকা। হল ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট, যেটা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) নামে ইতিহাসে খোদিত হল। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের পটভূমি কী? সংগ্রাম দিবসের পটভূমি হল, মুসলিম লিগ কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে মুসলিম লিগ রাজনৈতিকভাবে বেকায়দায় পড়ে। একগুঁয়ে কংগ্রেসকে পরিকল্পনার ব্যাপারে সম্মত করাতে কেবিনেট মিশনের ব্যর্থতাকে মুসলিম লিগ ব্রিটিশের বিশ্বাসঘাতকতা’ বলে অভিহিত করে। আর এই একই কারণে লিগ নেতা মোহম্মদ আলি জিন্নাহ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকে বিদায় জানিয়ে পাকিস্তান অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম কার্যসূচি’-র ডাক দেন। ১৯৪৬ সালের ২৭-২৯ জুলাই মুসলিম লিগের এক কাউন্সিল সভায় এ মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে সেদিন আসলেই কী হয়েছিল, সেটা জানা দরকার।
এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর অচিরেই লিগ ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ আগস্টকে ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ ঘোষণা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ওই দিন ভারতের সমস্ত প্রদেশে সবরকম ব্যাবসায়িক কার্যকলাপ বন্ধ রাখা ও সর্বাত্মক হরতাল পালনের জন্য লিগ নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম জনসাধারণের প্রতি এক নির্দেশ জারি করা হয়। বাংলায় পুনর্গঠিত মুসলিম লিগের নেতা এবং প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি অনুভব করেন যে, বাংলায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসটি রীতিমতো জঙ্গি মেজাজে পালিত হওয়া উচিত। ওই দিবস উপলক্ষে দিবসটিকে সফল করে তুলতে তাঁর ব্যাপক প্রস্তুতির ফলে এক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়, যা সম্ভবত তিনি কখনও চান নি। পরিস্থিতি তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং নিষ্ঠুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর প্রাণহানি ঘটে। এই দাঙ্গার সময় কলকাতার একটা বিরাট অংশ জুড়ে কয়েকদিন ধরে আগুন জ্বলতে থাকে। কলকাতার এই দাঙ্গা অচিরেই অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে, বিহার ও নোয়াখালি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার দাঙ্গা উভয় পক্ষের জন্যই ছিল কমবেশি সমান ক্ষতিকর। তবে অন্যত্র এটি একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিহারে প্রায় একপেশেভাবে মুসলমান ও নোয়াখালিতে হিন্দুরা প্রাণ হারায়। তবে সামগ্রিকভাবে কলকাতা দাঙ্গায় প্রাণহানি মুসলমানদের মধ্যে অনেক বেশি হয়। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস প্রত্যক্ষ ফলাফল প্রদান করে। ওই দিনই ভারতের নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় এবং ওই দিনই যুক্তবাংলার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্বের খণ্ডিতাকারের বিষয়টি চিরকালের মতো নির্ধারিত হয়ে যায়। বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।
লিগ সরকারে যোগ দেবে শর্তে জিন্নাহ মন্ত্রিসভায় কংগ্রেসের সঙ্গে সংখ্যাসাম্য ও মুসলিমদের ব্যাপারে ভেটো নিয়ে তাঁর দাবি ত্যাগ করেন। নতুন গঠিত মন্ত্রিসভা দাঙ্গার প্রেক্ষিতে বৈঠকে বসে। কংগ্রেস চাইছিল যে ভাইসরয় যাতে শীঘ্রই আইনপরিষদ আহ্বান করেন এবং যাতে সংবিধান রচনার কাজ শুরু করা হয়। এছাড়া তাঁদের ইচ্ছা ছিল যাতে লিগের মন্ত্রীরা অনুরোধে যুক্ত হয় বা সরকার থেকে পদত্যাগ করে। জিন্নাহ, লিয়াকত ও নেহেরুর মতো নেতাদের লন্ডনে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য ওয়াভেল চেষ্টা করেন। আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার সময় অংশগ্রহণকারীরা ঘোষণা করেন যে, ভারতের অনিচ্ছুক কোনো অংশের উপর তা কার্যকর করা হবে না। লন্ডন থেকে ফেরার সময় জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি খান কায়রোতে কয়েকদিন অবস্থান করে প্যান ইসলামিক বৈঠকে অংশ নেন।
শেষপর্যন্ত মুসলিম লিগ সংবিধান নিয়ে আলোচনায় অংশ নেয়নি। ব্রিটিশ পরবর্তী হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে জিন্নাহর সম্মতি ছিল না। এর মধ্যে ছিল সম্মিলিত সামরিক বা যোগাযোগ প্রক্রিয়া। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর নাগাদ তিনি ডমিনিয়ন মর্যাদায় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। লন্ডন সফর শেষপর্যন্ত ব্যর্থ হয়। তিনি আশা করেছিলেন যে বাংলা ও পাঞ্জাব অবিভক্ত অবস্থায় পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে এই দুই প্রদেশেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অ-মুসলিম সংখ্যালঘুদের উপস্থিতি ছিল। এটলির মন্ত্রিপরিষদও দ্রুত ভারত ত্যাগ করতে চাইছিল। তবে ওয়াভেলের উপর এ ব্যাপারে তাঁদের বেশি আস্থা ছিল না। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরের শুরুর দিকে তাঁরা ওয়াভেলের উত্তরসুরির ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন এবং শীঘ্রই লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভাইসরয় করে পাঠানো হয়। বিশ্বযুদ্ধে কৃতিত্বের জন্য তিনি ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে রানি ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্র হিসেবে লেবার পার্টিও তাকে পছন্দ করত।
১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি এটলির ভাইসরয় হিসাবে মাউন্টব্যাটেনের নিয়োগ ঘোষণা করেন এবং বলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন নাগাদ ব্রিটেন ভারতের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। ভারতে আসার দুই দিন পর ২৪ মার্চ মাউন্টব্যাটেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এর মধ্যে কংগ্রেস দেশবিভাগের ব্যাপারে সম্মত হয়। পরবর্তীতে জওহরলাল নেহরু এ ব্যাপারে বলেছেন যে তাঁরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং দেশবিভাগ তাঁদের মুক্তি দিতে। পারত ও তাঁরা তা গ্রহণ করেন। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে গঠিত ভবিষ্যত ভারতের দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস নেতাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তাঁরা দাবি করেন যে, যদি পাকিস্তান গঠন করা হয় তবে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে।
স্বয়ং জিন্না প্রথম দিকে দেশভাগ চাননি, দেশশাসনে ক্ষমতার বাঁটোয়ারা চেয়েছিলেন মাত্র। সেটা কীভাবে হবে, তাই নিয়ে ১৪ পয়েন্ট দিয়েছিলেন, সেটা যখন মানা হল না, তখন পাকিস্তান প্রস্তাব করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ওইসব মুসলিম নেতারা জিন্নার সঙ্গে না-গিয়ে দেশভাগের বিরোধিতা করে গিয়েছেন। অতএব জিন্নাহ দেশভাগ করে আলাদা দেশ চেয়েছিলেন বলে উপমহাদেশের সমস্ত মুসলমানই চেয়েছিলেন, এটা বললে অতি সরলীকরণ হয়। নেতাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে উড়িয়ে দেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকে না। জিন্নাহর আশঙ্কা ছিল যে, ব্রিটিশরা ভারত থেকে চলে যাওয়ার পর কংগ্রেস প্রধান আইনসভায় মুসলিমরা তাঁদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবে। তিনি দাবি করেন যে, স্বাধীনতার পূর্বেই সেনাবাহিনীকে ভাগ করতে হবে। এজন্য এক বছরের মত সময় দরকার ছিল। মাউন্টব্যাটেন আশা করেছিলেন স্বাধীনতার পর একটি যৌথ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু জিন্নাহ চাইছিলেন স্বাধীন রাষ্ট্রের আলাদা সেনাবাহিনী থাকুক। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক পর্যায়ে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দি অখণ্ড বাংলাকে ভারত ও পাকিস্তানের মতো স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গঠনের প্রস্তাব করেন। মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এ ব্যাপারে তাঁর একাত্মতা প্রকাশ করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল কলকাতা ছাড়া বাংলা অর্থহীন, তাই তিনি বাংলাকে অখণ্ড রাখতে উৎসাহী ছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত কংগ্রেস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বিরোধিতায় এবং বিলিওনিয়ার বিড়লার স্বার্থে বাংলা ভাগ হয়ে যায়। উপরতলার নির্ধারকদের কাছে। শ্যামাপ্রসাদের করুণ আবেদনই ছিল দেশ ভাগ হোক বা না হোক বাংলা ভাগ করতেই হবে।
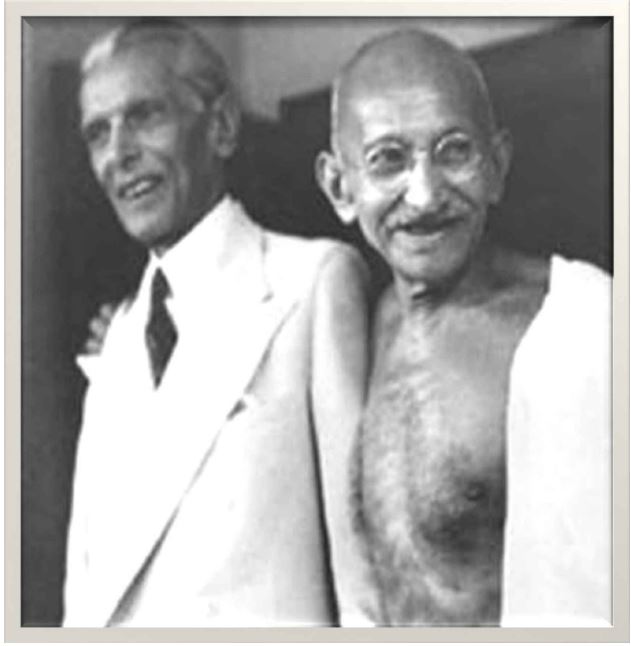
[গান্ধি ও জিন্নাহর সম্পর্ক মধুর, তারপরেও ভারতভাগ রাখা যায়নি]
বাংলার ভাগ্য বাংলার জনগণের উপর নির্ভর করছিল না, নির্ভর করছিল সম্পূর্ণ বাইরের তিনটে শক্তি উপর। তাদের মধ্যে আপস ও চুক্তির উপর নির্ভর করেই বাংলাকে দু-ভাগ করতে হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লিগ নেতৃত্ব প্রস্তুত ছিল বাংলাকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে একটি অবিভক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করতে। কিন্তু স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা এবং তাঁদেরই চাপে বাংলাকে দ্বি-খণ্ডিত করা হল। মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীরা একটি পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন। এই পরিকল্পনায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল স্থির করার যে তাঁরা হিন্দুস্তানে যাবেন, না অন্য প্রদেশের সঙ্গে মিলে আলাদা গ্রুপ তৈরি করবেন, নাকি স্বাধীন থাকতে চান। মূলত বাংলা ও পাঞ্জাবের প্রতিনিধিদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তিনটি সম্ভাবনার মধ্যে একটি বাছাই করে নেওয়ার। সেই তিনটি সম্ভাবনা ছিল— (১) সমগ্র বাংলা ও পাঞ্জাব হিন্দুস্তানে অথবা পাকিস্তানে যোগদান করতে পারে, (২) বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত হয়ে এক অংশ হিন্দুস্তানে এবং অন্য অংশ পাকিস্তানে যেতে পারে এবং (৩) বাংলা ঐক্যবদ্ধ থেকে পৃথক রাষ্ট্র হতে পারে। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তৃতীয় বিকল্পটির বিরুদ্ধে নেহরুর জোরালো আপত্তি ছিল এবং এই পরিকল্পনাও নাকচ হয়ে যায়। অর্থাৎ নেহরু চাইল না বাংলা ও পাঞ্জাব পৃথক হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিক। অতএব নেহরুর নির্দেশে রিফর্মস কমিশনার ভি. পি. মেনন নতুন এক পরিকল্পনা রচনা করলেন। এই নতুন পরিকল্পনার বলা হল বাংলা ও পাঞ্জাবকে হয় সমগ্রভাবে হিন্দুস্তানে বা পাকিস্তানে যেতে হবে, নয়তো আংশিক পাকিস্তানে আর আংশিক হিন্দুস্তানে থাকতে হবে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে অখণ্ড বাংলার ও পাঞ্জাবের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। অন্য প্রদেশগুলিকে হয় হিন্দুস্তানে নয় পাকিস্তানে যেতে হবে। জোর করে ঠেলে দেওয়া হল সাধারণ মানুষকে। জোর করে বিভাজন রেখা টেনে এক লহমায় বিদেশি করে দেওয়া হল।
অথচ ১৯৪৭ সালের ৪ মার্চ ভারত সচিবের একটা স্মারকলিপিতে তিনটি রাষ্ট্রের উদ্ভবের সম্ভাবনার কথাই বলা হয়েছিল— (১) উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাকিস্তান; (২) আসাম-সহ হিন্দুস্থান; এবং (৩) স্বাধীন বাংলা। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার ভারত ও বর্মা কমিটি প্রদেশগুলিকে, বিশেষ করে বাংলাকে, যদি তাঁরা চায় তাহলে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক থাকার অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৭ মে একটি স্মারকলিপিতে ভারতসচিব লিস্টওয়েল বলেছিলেন— “ঐক্যবদ্ধ থাকার ও নিজের সংবিধান নিজে রচনা করার অধিকার নিশ্চয়ই বাংলাকে এবং সম্ভবত পাঞ্জাবকেও দেওয়ার পক্ষে যুক্তি আছে।” মাউন্টব্যাটেন নিজেও কিছুদিন ধরে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান থেকে পৃথক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন বাংলার কথা চিন্তা করেছিলেন। বাংলার ব্যারিস্টার-নেতা সোহরাওয়ার্দি (Suhrawardy) মাউন্টব্যাটেনের স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে বলেন— “যথেষ্ট সময় পেলে তিনি বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস করেন। ১৯৪৭ সালে ২৮ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানালেন— তাঁর এবং তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের পরিকল্পনা পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান থেকে পৃথক অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত রেখেছে। জিন্না কোনো আপত্তি করবে না। জিন্নাহ একটুও ইতস্তত না-করে বলেছিলেন— “আমি আনন্দিত হব… তাঁরা ঐক্যবদ্ধ ও স্বাধীন থাকুক সেটাই ভালো হবে”। ২৮ এপ্রিল মাউন্টব্যাটেনের প্রধান সচিব মিয়েভিলের সঙ্গে আলোচনার সময় লিগের সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত আলি খাঁ বলেছিলেন— “বাংলা কখনোই বিভক্ত হবে না— এই তাঁর বিশ্বাস, তাই তিনি বাংলা নিয়ে উদ্বিগ্ন নন। তিনি মনে করেন যে, বাংলা হিন্দুস্তানে বা পাকিস্তানে যোগদান করবে না এবং পৃথক রাষ্ট্র থাকবে”। ১৯৪৭ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি নেহরু বললেন— “পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হবে। আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েই এ কথা বলছি”। ১ মে মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব দিলেন যে, বাংলা থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্যরা প্রথমে ভোট দিয়ে ঠিক করবেন যে, তাঁরা পৃথক স্বাধীন বাংলার পক্ষে, না হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানে যোগদান করতে চান। পরে তাঁরা বাংলা ভাগ হবে কি না সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবেন। ৪ মে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি ও টেলিগ্রামের মাধ্যমে জানালেন –“বাংলার জনগণের মতামত নেওয়ার জন্য গণভোট হতে পারে। তার জন্য কমপক্ষে তিন মাস সময় লাগবে”। তখনও পর্যন্ত সাল-তারিখ স্থির ছিল ১৯৪৮ সালের জুনের মধ্যে ব্রিটিশরা পাকাপাকিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। অতএব এই সময়ের মধ্যে বাংলায় গণভোট সম্পূর্ণ করার জন্য যথেষ্ট। সময়। এই গণভোটের মাধ্যমে বাংলা ঐক্যবদ্ধ থাকবে, না বিভক্ত হবে বাঙালির ভবিষ্যৎ কোনটা হবে।— সেদিনের অবিভক্ত বাংলার ছয় কোটির কিছু বেশি বাঙালির ভাগ্য নির্ধারণ হবে। বাঙালি না হিন্দুস্তানি, না পাকিস্তানি –বাঙালির এক বৃহৎ ও পৃথক দেশ জন্ম হত।
হঠাৎ মাউন্টব্যাটেনের মত সম্পূর্ণ বদলে গেল। ৮ মে তিনি তাঁর চিফ অব স্টাফ’ লর্ড ইসমেকে টেলিগ্রাম করে জানালেন— ভি. পি. মেননের মাধ্যমে প্যাটেল ও নেহরু জানিয়েছেন যে, যতদিন না নতুন সংবিধান সম্পূর্ণ তৈরি হচ্ছে ততদিনের জন্য তাঁরা ডোমিনিয়ন স্টেটাস নির্দিষ্ট সময়ের আগে চান। ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ এগিয়ে দিতে হবে। প্যাটেল ও নেহরুর কেন যে এত তাড়া, তা বোধগম্য না-হওয়ার কারণ নেই। হস্তান্তরের দিন-তারিখ এগিয়ে আনতে পারলে গণভোট করা আর কোনোমতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ তাঁদের মর্জি অনুসারে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান করে দেওয়া যাবে। মাউন্টব্যাটেন লিখলেন— “এ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে যত সুযোগ এসেছে, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা অবশ্যই প্রশাসনিক বা অন্য কোনো বাধা মানব না।” এইসব ব্রিটিশদের কার্যকলাপ দেখে ভাবি, আমরা কি সত্যিই ব্রিটিশদের তাড়াতে পেরেছিলাম? নাকি ব্রিটিশরাই বাধ্য হয়ে ভারত ছেড়ে চলে গেছে, অন্যান্য উপনিবেশগুলি ছেড়েছিল। ব্রিটিশরা এত ফোঁফড়দালালি করার সুযোগ পায় কী করে? মধ্যস্থতা করার অধিকার পাবে কেন? ভারত কি তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তি ছিল নাকি? ভারতের জাতীয় দলগুলি ওদের দাদাগিরি মেনে নিচ্ছিল কেন? কোন স্বার্থে? এর জন্যেই কী, যা হয়েছে ব্রিটিশরাই করে দিয়ে গেছে, আমরা কিছু জানি না এটা বোঝাতে?
৯ মে ‘অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা’-র প্রতিনিধিকে প্যাটেল বললেন— তাঁরা চান শীঘ্রই ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হোক ১০ মে মাউন্টব্যাটেন ও তাঁর সহকর্মীদের এক বৈঠকে নেহরু বললেন, “ডোমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক”। একটা কথা দিনের আলোর মতো সত্য, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব বরাবর বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। পাকিস্তান হোক বা না হোক, তবু বাংলাকে ভাগ করতেই হবে। বাংলার শক্তি ও মেধার ভয়ে ভীত নেহরুরা চেয়েছিলেন বাংলাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত দিক থেকে পঙ্গু করে দিতে। যদি বাংলা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত, তাহলে বাংলা দেশকে নেতৃত্ব দিত। বিড়লা প্রমুখ মাড়োয়ারি বড়ো বড়ো পুঁজিপতিদের ঘাঁটি ছিল এই কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গকে তাঁরা কখনো হাতছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্বাধীন বাংলার জন্ম নিলে তাঁদের ব্যাবসার পাততাড়ি গোটাতে হত কলকাতা থেকে।
২৫ মে লন্ডনের নিউজ ক্রনিকল পত্রিকার সংবাদদাতাকে নেহরু বললেন : “ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে যদি থাকে, তবেই শুধু আমরা ঐক্যবদ্ধ বাংলায় রাজি হতে পারি”। ৩১ মে তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বললেন— “ব্রিটিশ সরকার স্বাধীন বাংলার প্রস্তাবে যে সম্মত আছে তা ঘোষণা করেছে এবং নেহরুর ইচ্ছার কথাও বললেন— “পণ্ডিত নেহরু বলেছেন যে, বাংলা স্বাধীন হবে, তাতে তিনি রাজি হবেন না “। ঐতিহাসিক সুনীতিকুমার ঘোষ লিখেছেন— “দুটি প্রধান দলের মধ্যে একটি দল মুসলিম লিগ রাজি ছিল। ব্রিটিশরাজও রাজি ছিল। কিন্তু প্রধান দলের মধ্যে অন্যটি কংগ্রেস রাজি ছিল না। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের জন্যই বাংলা দ্বিখণ্ডিত হল”। মুসলিম বড়ো শিল্পপতি ইস্পাহানিও অবিভক্ত স্বতন্ত্র বাংলা রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকে একটি ফাঁদ বলেছিলেন। নেহরুদের সঙ্গে তফাত এই যে, তিনি এটিকে হিন্দুদের চক্রান্ত বলেছিলেন। তাঁর মতে, বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষায় ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর মুসলমানদের গ্রাস করে ফেলা ছিল হিন্দুদের রচিত এই ফাঁদের উদ্দেশ্য। বিড়লাদের রাজনৈতিক মুখপাত্ররা এবং ইস্পাহানি দুই বিরোধী পক্ষ, এই পরিকল্পনাকে দুই বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করেছিলেন। সেটাই স্বাভাবিক। এই পরিকল্পনা দুই পুঁজিপতি গোষ্ঠীরই স্বার্থের প্রতিকূল ছিল। বাংলা-বিভাজনে দুইয়েরই স্বার্থ ছিল।
শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশংকর রায় প্রমুখ ব্যক্তিরাও অবিভক্ত স্বাধীন বাংলার জন্য চিঠি-চাপাঠি করছিলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন শরৎ বসুর কাছে একটি চিঠি লেখেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। চিঠিটি বয়ান ছিল এরকম— “I have now discussed the scheme roughly with Pandit Nehru and then Sarder. Both of them are dead against the proposal and they are of opinion that it is merely a trick for dividing Hindu and Scheduled Caste leaders. With them it is not merely a suspicion but almost a conviction. They also feel that money is being lavishly expended in order to secure Scheduled Caste Votes. If such is the case, you should give up the struggle at least at present. For the unity purchased by corrupt practices would be worse than a frank partition, it being a recognition of the established division of hearts and the unfortunate experiences of the Hindus. I also see that there is no prospect of transfer of power outside the two parts of India.” অর্থাৎ, “আমি বিষয়টি নিয়ে পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দারের সঙ্গে কথা বলেছি। উভয়েই ওই প্রস্তাবের (যুক্ত বাংলা প্রস্তাব) ঘোরতর বিরোধী। তাঁরা মনে করেন যে, হিন্দু এবং তফশীলি জাতিকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে এটি একটি চালবাজি। তাঁরা এ ব্যাপারে শুধু সন্দেহই করেন না, এটি তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন যে, অখণ্ড বাংলার সপক্ষে তফশীলি সম্প্রদায়ের ভোট কেনার জন্য দেদারসে টাকা খরচ করা হচ্ছে। তাই যদি হয়, তাহলে অন্তত এই মুহূর্তের জন্য আপনার সংগ্রাম (যুক্ত বাংলার পক্ষে) স্থগিত করা উচিত। কারণ, বাংলা বিভক্তির চেয়েও টাকা দিয়ে বাংলার অখণ্ডতা ক্রয় আরও খারাপ। আমি আরও দেখতে পাচ্ছি যে, ভারতকে দুই ভাগে ভাগ করার বাইরে (পাকিস্তান ও ভারত) ক্ষমতা হস্তান্তরের আর কোনো সম্ভাবনা নাই।” গান্ধিজির এই চিঠি এবং সেখানে দুর্নীতির উল্লেখ শরৎ বসুকে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তোলে। তিনি গান্ধিজির কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করেন— “Information false, punish informants, if information true, punish bribe givers and bribe-takers.” অর্থাৎ, “যদি আপনার খবর মিথ্যা হয়, তাহলে যাঁরা খবর দিয়েছে তাঁদেরকে শাস্তি দিন। আর যদি খবর সত্য হয়, তাহলে যাঁরা ঘুষ দিয়েছে এবং যাঁরা ঘুষ খেয়েছে তাঁদেরকে শাস্তি দিন”। এই টেলিগ্রাম পেয়ে গান্ধিজি বিব্রত হন। কারণ ঘুষের অভিযোগের তদন্ত করার মতো মানসিক প্রস্তুতি তাঁর ছিল না। তিনি শরৎ বসুকে এই বলে শান্ত করার চেষ্টা করেন যে, যেহেতু অধিকাংশ হিন্দু এবং কংগ্রেস বাংলাকে ভাগ করার বিষয়টি মেনে নিয়েছে তাই এখন তার পক্ষে (শরৎ বসুর পক্ষে) চুপচাপ বিষয়টি মেনে নেওয়াই উচিত। যা-ই হোক, গান্ধিজির এই চিঠির পরদিন অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ৯ জুন শরৎ বসু জিন্নাহর কাছে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠির বয়ান– “My dear Jinnah, I have to thank you most sincerely for your courtesy and cordiality toward me and for the consideration you gave to my suggestions. Bengali is passing through the greatest crisis in her history, but she can yet be saved. She can be saved if you will kindky give the following instructions to Muslim Members of the Bengal Legislative Assembly.
1. At the Meeting to be held of all members of the Legislative Assembly (other than Europeans) at which a decision will be taken on the issue as to which constituent Assembly the province as a whole would join if it were subsequently decided by the two parts to remain united, to vote, neither for the Hindustan Constituent Assembly nor for the Pakistan Constituent Assembly, and to make it clear by a statement in the Assembly or in the press or otherwise, that they are solidly in favour of Bengal having a Constituent Assembly of its own.
The request I am making to you is in accordance with the views you expressed to me when we met. But it seems to me that if you merely expressed your views to your Members and not gave them specific instruction as to how to vote, the situation cannot be saved. I hope you will do all in your power to enable Bengal to remain united and to make her a free and independent State.” অর্থাৎ, “প্রিয় জিন্নাহ, আপনার কাছে আমি যেসব সুপারিশ করেছিলাম সেগুলো আপনি বিবেচনা করেছেন এবং আমার প্রতি যে সৌজন্য ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বঙ্গদেশ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এখন অতিবাহিত করছে। তবে এখনও সময় আছে তাকে বাঁচানোর। বঙ্গদেশকে বাঁচানো যেতে পারে, যদি আপনি অনুগ্রহ করে বঙ্গীয় আইন সভার মুসলিম সদস্যের প্রতি নিন্মোক্ত নির্দেশ জারি করেন
.
(১) ইউরোপীয় সদস্য ছাড়া ওই আইন সভার সমস্ত সদস্যের যে সভা অনুষ্ঠিত হবে সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে যে এই প্রদেশ অর্থাৎ বঙ্গদেশ সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ অখণ্ডভাবে কোনো গণপরিষদে যুক্ত হবে। তাঁরা সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যে, তাঁরা ভারতীয় গণপরিষদে যোগ দেবে না, পাকিস্তান গণপরিষদেও যোগ দেবে না। তাঁরা অখণ্ড থাকবে। তাঁরা আইনসভায় বিবৃতি দিয়ে হোক অথবা সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েই হোক, তাঁরা ঘোষণা করবে যে বাংলার একটি নিজস্ব আইন সভা থাকবে। তাঁরা সেই আইন সভার পক্ষে দৃঢ় সমর্থন জানাবে।
আমি আপনাকে এই অনুরোধ করছি আপনার ইচ্ছা অনুসারে, যে ইচ্ছা আপনি প্রকাশ করেছিলেন যখন আমাদের দুজনের দেখা হয়। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে, বাংলাকে অখণ্ড রাখার পক্ষে মুসলিম লিগ সদস্যদের কাছে আপনি শুধুমাত্র আপনার মতামত দিয়েছিলেন। তবে বাংলাকে অখণ্ড রাখার পক্ষে কীভাবে ভোট দিতে হবে, সে ব্যাপারে তাঁদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো নির্দেশ দেননি। আমি আশা করি, বাংলাকে অখণ্ড রাখার জন্য এবং তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র করার জন্য আপনার ক্ষমতায় যা যা আছে তার সব কিছুই আপনি প্রয়োগ করবেন।”
জিন্নাহর কাছে চিঠি লিখেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তার ৬ দিন পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৪ জুন গান্ধিজির কাছে শরৎ বসু কড়া ভাষায় তার জবাব দেন— “I can say definitely and emphatically that there was nothing in the nature of trickery… the feeling or suspicion that money is being expended to secure Scheduled Caste votes is entirely baseless. My faith remains unshaken and I propose to work in my own humble way for the unity of Bengal. Even after the raging and tearing campaign that has been carried on in favour of partition, I have not the slightest doubt that if a referendum were taken, the Hindus of Bengal by a large majority would vote against partition. The voice of Bengal has been stifled for the moment but I have every hope that it will assert itself.” অর্থাৎ, “আমি সুনিশ্চিতভাবে এবং জোর দিয়ে বলতে পারি যে, এখানে ছলচাতুরির কোনো ব্যাপার ছিল না। তফসিলি জাতির ভোট নেওয়ার জন্য টাকা খরচ করা হচ্ছে বলে যে ধারণা বা সন্দেহ জন্মেছে, সেটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমার বিশ্বাস অবিচল রয়েছে এবং আমি বাংলার ঐক্য ধরে রাখার জন্য আমার সাধ্যমত চেষ্টা করে যাব। বাংলার বিভক্তির জন্য যে প্রবল প্রচারণা চলছে তারপরেও আমি বলতে চাই যে, বাংলার বিভক্তির জন্যে যদি কোনো গণভোট (রেফারেন্ডাম গ্রহণ করা হয়, তাহলে আমার মনে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই যে, বাংলার হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। এই মুহূর্তে বাংলার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ করা হয়েছে, কিন্তু আমার বিপুল বিশ্বাস যে একদিন তাঁদের মতামত প্রতিষ্ঠিত হবেই।”
শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ গ্রন্থে তিনি লিখেছেন— “১৯৪৭ সালের জুন মাসে ঘোষণা করা হল ভারতবর্ষ ভাগ হবে। কংগ্রেস ভারতবর্ষকে ভাগ করতে রাজি হয়েছে এই জন্য যে, বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে। আসামের সিলেট জেলা ছাড়া আর কিছুই পাকিস্তানে আসবে না। বাংলাদেশের কলকাতা। এবং তার আশপাশের জেলাগুলোও ভারতবর্ষে থাকবে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব ও মুসলিম লিগ নেতারা বাংলাদেশ ভাগ করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বর্ধমান ডিভিশন আমরা নাও পেতে পারি। কলকাতা কেন পাব না? কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলাদেশ ভাগ করতে হবে বলে জনমত সৃষ্টি করতে শুরু করল। বাংলাদেশ যে ভাগ হবে, বাংলাদেশের নেতারা তা জানতেন না। সমস্ত বাংলা ও আসাম পাকিস্তানে আসবে এটাই ছিল তাদের ধারণা।… এই সময় শহিদ (সোহরাওয়ার্দি) সাহেব ও (আবুল) হাশিম সাহেব মুসলিম। লিগের তরফ থেকে এবং শরৎ বসু ও কিরণশঙ্কর রায় কংগ্রেসের তরফ থেকে এক আলোচনা সভা করেন। তাঁদের আলোচনায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলাদেশ ভাগ না-করে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা যায় কি না? শহিদ সাহেব দিল্লিতে জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তার অনুমতি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। বাংলাদেশের কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতারা একটা ফর্মুলা ঠিক করেন। বেঙ্গল মুসলিম লিগ ওয়ার্কিং কমিটি একটি ফর্মুলা সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করে। যতদূর আমার মনে আছে, তাতে বলা হয়েছিল, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। জনসাধারণের ভোটে একটা গণপরিষদ হবে। সেই গণপরিষদ ঠিক করবে বাংলাদেশ হিন্দুস্তান না পাকিস্তানে যোগদান করবে, নাকি স্বাধীন থাকবে। যদি দেখা যায় যে, গণপরিষদের বেশি সংখ্যক প্রতিনিধি পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষপাতী, তবে বাংলাদেশ পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানে যোগদান করবে। আর যদি দেখা যায় বেশি সংখ্যক লোক ভারতবর্ষে থাকতে চায়, তবে বাংলাদেশ ভারতবর্ষে যোগ দেবে। যদি স্বাধীন থাকতে চায়, তাও থাকতে পারবে। এই ফর্মুলা নিয়ে সোহরাওয়ার্দি ও শরৎ বসু দিল্লিতে জিন্নাহ ও গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে যান। শরৎ বসু নিজে লিখে গেছেন যে জিন্নাহ তাকে বলেছিলেন, মুসলিম লিগের কোনো আপত্তি নাই, যদি কংগ্রেস রাজি হয়। ব্রিটিশ সরকার বলে দিয়েছে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত না-হলে তাঁরা নতুন কোনো ফর্মুলা মানতে পারবেন না। … শরবাবু কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে অপমানিত হয়ে ফিরে এসেছিলেন। কারণ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাকে বলেছিলেন, ‘শরৎ বাবু পাগলামি ছাড়েন, কলকাতা আমাদের চাই।’ মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরু কোনো কিছুই না-বলে শরত্বাবুকে সর্দার প্যাটেলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর মিস্টার প্যাটেল শরৎবাবুকে খুব কঠিন কথা বলে বিদায় দিয়েছিলেন। কলকাতা ফিরে এসে শরৎ বসু খবরের কাগজে বিবৃতির মাধ্যমে একথা বলেছিলেন এবং জিন্নাহ যে রাজি হয়েছিলেন সে কথা স্বীকার করেছিলেন। … জিন্নাহর জীবদ্দশায় তিনি কোনোদিন শহিদ সাহেবকে দোষারোপ করেন নাই। কারণ, তাঁর বিনা সম্মতিতে কোনো কিছুই তখন করা হয় নাই। খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেব ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২২ এপ্রিল ঘোষণা করেছিলেন, ‘যুক্ত বাংলা হলে হিন্দু-মুসলমানের মঙ্গলই হবে। মওলানা আকরম খাঁ সাহেব মুসলিম লিগের সভাপতি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন, “আমার রক্তের উপর দিয়ে বাংলাদেশ ভাগ হবে। আমার জীবন থাকতে বাংলাদেশ ভাগ করতে দেব না। সমস্ত বাংলাদেশই পাকিস্তানে যাবে।’ এই ভাষা না-হলেও কথাগুলোর অর্থ এই ছিল। আজাদ কাগজ আজও আছে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের কাগজ বের করলেই দেখা যাবে।” কংগ্রেস সুচতুরভাবেই ইতিহাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছিল, তা দিয়েছিল নিজেদের রাজনৈতিক মুনাফা লাভের অভিপ্রায়ে। তাঁরা মুসলিমদের প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিল, সকল মুসলমান নেতৃবর্গ ও জনগণ পাকিস্তান’-এর পক্ষে। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিমদের অবদানকে পক্ষান্তরে অস্বীকার করে এসেছে কংগ্রেস। ফলে আজ বিজেপি আজ সেই সুযোগটাই নিচ্ছে। কংগ্রেস ভেবেছিল এইসব ক্ষত কার্পেটের নীচে চাপা রেখে অনন্তকাল ধরে তাঁরাই ভারত শাসন করবে। বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই সেইসব ক্ষত দগদগে হয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তবে শুধু কংগ্রেসের দিকে আঙ্গুল তুললেই হবে না। একইরকম উচ্চতায় আঙ্গুল তুলতে হবে হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দিকেও।
১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ শাসন ও অনুমিত বৰ্ণহিন্দুর আধিপত্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে মুসলিম লিগ আহুত হরতাল, যার ঘোষিত নাম ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস বা Direct Action Day। আসুন এবার একটু দেখে নেওয়া সেদিনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ কীভাবে ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস’। একটা হরতাল কীভাবে হত্যালীলায় শেষ হয়? পাশাপাশি দুটো উত্তর পাওয়া যায়– (১) রাজনৈতিক উসকানি এবং (২) হিন্দু মুসলিমদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা। রাজনৈতিক উসকানির প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি আঙুল ওঠে হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দির দিকে। অনেকে এমনও বলেন যে সোহরাওয়ার্দিই দাঙ্গার রূপকার, তাঁর পরিকল্পনার ছক অনুসরণেই প্রায় সব কিছু ঘটেছে। সোহরাওয়ার্দি কেন্দ্রে থাকলেও আসলে এইসব বক্তাদের নিশানায় থাকে গোটা মুসলিম লিগ। এর উৎস হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে চরম হিংসাত্মক মনোবৃত্তি। এঁদের বক্তব্য হল –(১) সোহরাওয়ার্দি পুলিশের রাশ টেনে রেখেছিলেন, (২) সেনার সাহায্য চাইতে দেরি করেছিলেন এবং (৩) পুলিশ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে তাঁর দুবৃত্ত অনুচরদের নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর ‘দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস বাংলা তথা গোটা উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ধারণায় একটা বাঁক এনেছিল বলেই মনে করা কলকাতার সেই দাঙ্গায় হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে হিংসার বিস্ফোরণে যত মানুষ খুন হল, যত সম্পত্তি ধ্বংস হল, অতীতে তার নজির মেলে না। দেশ জুড়ে দাঙ্গার জমি যেন তৈরি হয়ে গেল কলকাতার, দেশভাগ পর্যন্ত। শুধু কলকাতাতেই নয়, দাঙ্গা হয়েছিল বিহার ও নোয়াখালিতেও। লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, ভিটা ছাড়া করা হয়েছে। যাঁদের হত্যা করা হল, ভিটে ছাড়া করা হল সেইসব নিরীহ হতদরিদ্র মানুষরা কি হিন্দুস্তান পাকিস্তান চেয়েছিল কোনদিন?
জনম মুখোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৮ আগস্ট, ২০১৭) একটি নিবন্ধে লিখেছেন– “প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি ও সে যুগের নথিপত্র থেকে যে ছবি মেলে, তা সুপরিকল্পিত হিংসার ছবি নয়। তা সম্পূর্ণ অরাজক, বিস্ফোরক এক পরিস্থিতির ছবি, যার গতিপ্রকৃতি আগাগোড়াই ছিল অনিশ্চিত। কখন তা কোন্ দিকে ঘুরে যাবে, তা বোঝা প্রায় অসম্ভব ছিল। অবাধে লুটতরাজ চলেছিল, যাতে অংশ নিয়েছিল পুলিশ অফিসাররাও। সোনার গয়নার দোকান একেবারে খালি করে সব লুটেপুটে নিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। রেশনের দোকান লুট, গলিতে পিছন থেকে ছুরি মেরে খুন, প্রতিবেশীদের বাঁচাতে পাড়ায় পাড়ায় পিকেট, শহর জুড়ে পর পর অগ্নিকাণ্ড। ফাঁকা শেড খুঁজে জড়ো হত হিংস্র জনতা, হাতের কাছে যা মেলে, তা দিয়ে অস্ত্র বানানো হত। প্রোমোটারদের চক্রান্তে সংখ্যালঘু মধ্যবিত্ত বাড়িগুলিতে নৃশংস হত্যালীলা চলতে থাকে। আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে পাল্টা আক্রমণ চলে। সেই সঙ্গে অনবরত ঘুরপাক-খাওয়া গুজব, যা আরও ভয় ছড়াল, আরও হিংসা উসকে দিল, এক চরম পরিণামের আশঙ্কায় সবাইকে অস্থির করে তুলল।
পরাধীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দির সেই সময়ের ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখেছেন– “এ কথা সত্য যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি দাঙ্গার প্রথম দিন পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। কিন্তু সে সময়ের নথিপত্র স্পষ্ট করে দেয় যে, ১৬ আগস্ট দুপুরের পর থেকেই পরিস্থিতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছিল পুলিশ, কারণ তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। পুলিশ থানাগুলোর উপরেই আক্রমণ শুরু হয়, রাস্তায় রাস্তায় হিংস্র জনতার সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ চলতে থাকে। কলকাতা দ্রুত চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ডায়রেক্ট অ্যাকশন’ মিছিল ময়দানে হওয়ার কথা ছিল বিকেল চারটেয়। তার আগেই, বিকেল তিনটের মধ্যে পুলিশ কমিশনার ফোন করে গভর্নরকে অনুরোধ করেন সেনা নামাতে। অনুরোধ খারিজ করা হল। ব্রিগেডিয়ার সিক্সস্মিথ, যিনি সেনা সাহায্য পাঠানোর অনুরোধকে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেন, পরবর্তী কালে বিবৃতি দেন যে তিনি ভয় পেয়েছিলেন, মিলিটারি শক্তির ব্যবহার হয়তো এই দলে দলে আসা জনতার অভিমুখকে ঘুরিয়ে দিতে পারে… আমরা জানতাম ১৬ তারিখের পরিস্থিতি পালটে হয়তো সরকার-বিরোধী দাঙ্গার রূপও নিতে পারে। অতএব সোহরাওয়ার্দি যে পুলিশকে চেপে রেখেছিলেন, সেনা সহায়তার আবেদনে ইচ্ছে করে বিলম্ব করেছিলেন, এই ধারণা ধোপে টিকছে না। পুলিশ কমিশনার নিজেই বুঝেছিলেন যে, পরিস্থিতি পুলিশের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেনা সহায়তা দিতে অস্বীকার করেছিল ব্রিটিশ, সোহরাওয়ার্দি নন। এ-ও স্পষ্ট যে ব্রিটিশরা বুঝেছিল পরিস্থিতি অত্যন্ত অনিশ্চিত, রাস্তায় সেনা নামালে তা ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধেও বাঁক নিতে পারে। অর্থাৎ সেই প্রথম দিনটিতে হিংসার কোনো নির্দিষ্ট রূপ ছিল না, তা যে-কোনো দিকে ঘুরে যেতে পারত। তা ছিল একটা নিয়ন্ত্রণহীন, বিস্ফোরক পরিস্থিতি, সুকৌশলে পরিকল্পিত ঘটনা নয়।”
তা হলে কলকাতার হিংসার যে উন্মত্ততা দেখা দিল, তাকে আমরা ব্যাখ্যা করব কীভাবে? শ্রীমুখোপাধ্যায় লিখছেন –“আমার মনে হয়, তা বুঝতে হলে কলকাতার ইতিহাসকে আর একটু বড়ো পরিসরে দেখতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জনসংখ্যার প্রবল চাপ তৈরি হয় কলকাতার উপর। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে কলকাতার জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছিল। গৃহস্থের বাসস্থানের আকাল দেখা দিল, অল্প জায়গায় প্রচুর লোক চাপাচাপি করে থাকতে বাধ্য হল, ব্রিটিশ এবং মার্কিন সেনারা যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসের উপর দখল কায়েম করল। ১৯৪৩ সালের মধ্যে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ। উপবাসক্লিষ্ট মানুষ দলে দলে গ্রাম থেকে কলকাতা আসতে শুরু করল। শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাঁদের দেহ পড়ে থাকতে দেখল শহরবাসী। সেই চরম কালোবাজারির দিনে সরকারি বাঁধা দামে জিনিস পাচ্ছিলেন কেবল কলকাতার সাবেক বাসিন্দারা, সরকারি খাতায় যাঁদের নাম রয়েছে। কলকাতা তখন বাঁচার একমাত্র আশ্রয়, কোনোমতে শহরের উপর একটু দখল কায়েম করার জন্য হুড়োহুড়ি চলছে। ১৯৪৬ সালের মধ্যে যে পরিস্থিতি তৈরি হল কলকাতায়, তা হিংসার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। গোটা বাংলার মানুষই এক অসহনীয় দশক কাটিয়েছেন তত দিনে। কলকাতার ঘটনাকে বুঝতে গেলে তাঁদের হিসেবে না ধরলে ভুল হবে। আমি এ কথা বলছি না যে, ছেচল্লিশের দাঙ্গার ব্যাখ্যা খুঁজতে গিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা উসকানিকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া উচিত। এ দুটোই দাঙ্গার হিংস্রতাকে বাড়িয়েছিল, কিন্তু দাঙ্গাকে বুঝতে হলে কেবল আলাদা করে এ দুটো কারণকে চিহ্নিত করাই যথেষ্ট নয়। আরও নানা বিষয়ের দিকে তাকাতে হবে। যেমন, সেই সময়ের আর্থিক ও সামাজিক কাঠামো, জনসংখ্যার চাপ, শহরের এলাকার উপর দখল ও তার ব্যবহারের নকশায় পরিবর্তন প্রভৃতি। এগুলো ধরলে দাঙ্গার ব্যাখ্যা অত সরল মনে হবে না।”
এ-কথাও মাথায় রাখতে হবে যে, সে সময়ে ৬০ লক্ষ মানুষের শহর কলকাতা মাত্র ১২০০ সদস্যের একটি পুলিশ বাহিনী ছিল, যে-বাহিনীতে মাত্র ৬৩ জন ছিলেন ধর্মে মুসলিম। আর অফিসারদের মধ্যে একজন ডেপুটি কমিশনার ও একজন ওসি ছাড়া সকলেই ছিলেন হিন্দু। আর যদি লাশ গোনার হিসাবই করতে চাওয়া হয়, তাহলে জেনে রাখা ভালো যে সুরঞ্জন দাশ সহ ছেচল্লিশের দাঙ্গা নিয়ে গবেষণা আছে এমন সব ইতিহাসবিদই একটি বিষয়ে মোটামুটি একমত। তা হল এই দাঙ্গায় মুসলিমদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা হিন্দুদের তুলনায় ঢের ঢের বেশি। এর কারণটি কিন্তু খুব জটিল নয়। ধনী হিন্দু ও ধনী মুসলিমদের পক্ষে পিঠ বাঁচানো অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছিল (ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল)। কিন্তু সামাজিক ও অন্য ধরনের নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত গরিব মানুষের পক্ষে তা সহজ ছিল না। আর ১৯৪৬ সালে কলকাতার বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলিমই ছিলেন দরিদ্র শ্রেণির।
আগেই উল্লেখ করেছি, ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট যখন মুসলিম লিগের পাকিস্তান দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের কর্মসূচি হিসেবে উপমহাদেশের সর্বত্র মুসলমানগণ ওই দিন সকল কাজ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সফল করতে রাস্তায় নামে, অপরদিকে হিন্দু জনমতও পাকিস্তান-বিরোধী শ্লোগানকে কেন্দ্র করে সুসংগঠিত হতে থাকে এবং বিরোধিতায় পথে নামে। বাংলার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তেমন একটা হিন্দু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু দলের অধিকাংশ সমর্থক ছিল হিন্দু, তাই কংগ্রেস সদস্যদের একটি অংশ পাকিস্তান আন্দোলনকে আসন্ন বিপদ হিসাবে উপলব্ধি করে হিন্দুদের একাত্মতা বিষয়ে প্রবল অনুভূতি প্রকাশ করার প্রয়াস পায়। তাঁদের প্রচারণা নিঃসন্দেহে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চেতনাকে প্রজ্বলিত করেছিল। বিশেষত মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় থাকার কারণে ওই দিবস বাংলায় সফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ১৬ আগস্ট ভোরে উত্তেজনা শুরু হয় যখন মুসলিম লিগের স্বেচ্ছাসেবকেরা উত্তর কলকাতায় হিন্দু ব্যবসায়ীদের দোকানপাট বন্ধ রাখতে বাধ্য করে এবং হিন্দুরা এর প্রতিশোধ হিসাবে লিগের শোভাযাত্রার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ হিংসাত্মক কার্যাবলি দ্বারা যে এলাকা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল তা হল দক্ষিণে বউবাজার স্ট্রিট, পূর্বে আপার সার্কুলার রোড, উত্তরে বিবেকানন্দ রোড ও পশ্চিমে স্ট্রান্ড রোড দ্বারা বেষ্টিত রাজধানীর বহুল জনাকীর্ণ অংশটি। সরকারি হিসাব মতে এই দাঙ্গায় বেসরকারি হিসাবে ৪,০০০ লোক নিহত ও ১,০০,০০০ আহত হয়। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন হত্যার ঘটনা ছাড়া ২২ তারিখের পর কলকাতার পরিস্থিতি শান্ত হয়।
১৯৪৬ সালের দাঙ্গায় লিপ্ত জনতার মধ্যে মধ্যদেশীয় লোকজনের আধিক্য ছিল। মুসলমানদের মধ্যে কসাই, কারখানার শ্রমিক, রাজমিস্ত্রী, ডক শ্রমিক ও মধ্য কলকাতার বস্তিসমূহের অন্যান্য বাসিন্দারা সক্রিয় ছিল। মুসলমান ছাত্ররা, যাদের মধ্যে মহিলাও অন্তর্ভুক্ত, তাঁরা ১৬ আগস্টের সমাবেশে যোগদান করে। তেমনি হিন্দুদের মধ্যেও অত্যুৎসাহী লোকজনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল কসাই, গোয়ালা, ঝাড়ুদার, রিকশা চালক, সরকারি অফিস, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও নগরীর সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের রাখা নিজস্ব দারোয়ান প্রভৃতি।

কসাই (যাঁরা গোরু বা খাসি বা পাঁঠা হত্যা করে মাংস বিক্রি করে), দেখা যাচ্ছে কলকাতার দাঙ্গায় উভয় পক্ষ থেকেই কসাইরা অংশ নিয়েছিল। কিন্তু কোনো মুসলিম নরহন্তার কসাইয়ের নাম উঠে আসেনি শিরোনামে। এমনকি কুখ্যাত কোনো গণ-হত্যাকারীর নামও পাওয়া যায় না। তাহলে ধরে নিতেই হয় এই গণহত্যা ছিল একতরফা। অথচ যে হিন্দু কসাইয়ের নাম পাওয়া যায়, তাঁর নাম গোপাল পাঁঠা। পাঁঠা কাটতেন বলেই এঁর নাম গোপাল পাঁঠা। আসল নাম গোপাল মুখার্জি। কলকাতা দাঙ্গায় তাঁর অবদান কী? ভয়ংকর অবদান। সেই কারণের তো হিন্দু সংহতির লোকেরা আজও তাঁকে স্মরণ করে। সেই গোপাল পাঁঠা একদিনের মধ্যে ৮০০ হিন্দু ও শিখ যুবক সঙ্গে নিয়ে গড়ে তোলে এক বাহিনী এবং মুসলিমদের কচুকাটা করতে শুরু করে। বস্তুত নরহত্যাকারী গোপাল পাঁঠা আক্রমণরত কোনো মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেননি, তাঁদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। তিনি বস্তিতে বস্তিতে ঢুকে কাপুরুষের মতো নিরীহ নিরস্ত্র হতদরিদ্র মুসলমান ও মুসলমানদের পরিবারের উপর হামলা করেছে এবং হত্যা করেছে।
তবে অন্য ইতিহাসও পাওয়া যায় এই দাঙ্গার এবং সেটা বিপরীতমুখী ইতিহাস। ফলে বিভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবু সেটাও জেনে রাখা উচিত। ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’-এর প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল শ্রীগোলকবিহারী মজুমদার (আই.পি.এস) ছেচল্লিশের আতঙ্কের দিনগুলো ভুলি নি’ শিরোনামের একটি প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন –“রাত ১১/১২টা নাগাদ (১৬ আগস্ট, ১৯৪৬) পাড়ায় ওরা আবার আক্রমণ করল। দেখলাম একদল লোক— তাদের হাতে ছোরা, তরোয়াল ইত্যাদি নানা অস্ত্রশস্ত্র। তারা চিৎকার করে বলছে, “আজ তো এক এক হিন্দুকো কোরবানি করেগা। মা, বাবা, দিদি, আমি, ভাগ্নে সবাই সন্ত্রস্ত। যে-কোনো মূহুর্তে আমরা আক্রান্ত হতে পারি। সবচেয়ে বেশি ভয় দিদিকে নিয়ে। দিদি দেখতে খুব সুন্দরী। ভাবলাম দিদিই হবে ওদের প্রথম টার্গেট। হিন্দু মেয়েদের উপর ওদের বরবারই লোভ। চার পাঁচদিন পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলেও আতঙ্ক কাটেনি। ইউনিভার্সিটি খোলা ছিল। রাজাবাজারের উপর দিয়ে আমাকে যেতে হত। একদিন দেখলাম, গোরু কেটে যেমন হুকের সাথে ঝুলিয়ে রাখে, তেমনিভাবে দেখলাম, হাত পা কাটা হিন্দু মেয়েদের চুল বেঁধে সব ঝুলিয়ে রেখেছে। বীভৎস আর নৃশংস সেই দৃশ্য।” দেবকুমার বসু ১৯৪৬-এর দাঙ্গার কয়েকটা দিন’ শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন– “রাজাবাজারের সামনের ভিক্টোরিয়া কলেজ ও স্কুল। মেয়েদের কলেজ ও হোস্টেল একদম ফাঁকা, সব পালিয়েছে। কেবলমাত্র রাস্তায় দোতলার জানালায় চারটি মেয়েকে খুন করে রাস্তায় দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে কে বা কারা। এই নৃশংসতা ও বীভৎসতা যারাই দেখেছেন, তারাই অনুভব করতে পারেন যে, আমাদের মতো যুবকেরা কেন উত্তেজিত হয়ে ক্ষিপ্ত হবে। কেউ এই হোস্টেলের দিকে তাকালে রাস্তায় দিকের জানালাগুলি ইট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া আছে, দেখবেন। আজ ষাট বছর পরেও বন্ধ আছে। কাদের ভয়ে?” তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল তাঁর ডায়েরিতে (১৯৪৬, ৩ নভেম্বর) লেখেন –“পলাশির যুদ্ধে যত লোক নিহত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি লোক নিহত হয়েছে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ে।” গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং সম্পর্কে লিওনার্ড মোসলে তার বই ‘The Last Days of the British Raj’ গ্রন্থে লিখেছেন— “ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া পোল পার হয়ে হাওড়া থেকে দলে দলে আসতে শুরু করল মারাত্মক অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত অবাঙ্গালি মুসলমান গুণ্ডারা এবং তারা মিশে গেল চৌরঙ্গী, চিৎপুরে অপেক্ষমান মুসলমানদের সঙ্গে, শুরু হল প্রলয়কাণ্ড— কলকাতার মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের হিন্দু এলাকাগুলিতে। ইসলামের বিশ্বপ্রেম গ্রাস করে নিল অরক্ষিত মুসলমান পরিবেষ্টিত হিন্দু পরিবারগুলিকে। আর্ত আহতদের আর্তনাদ, লাঞ্ছিত নারীর ভয়ার্ত ক্রন্দন চাপা পড়ল– ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান এবং ‘আল্লাহো আকবার’-এর উন্মত্ত কোলাহলে। আগুনে জ্বলতে থাকল হিন্দুদের স্থাবর-অস্থাবর সব কিছু, আকাশে উঠল কুণ্ডলায়িত কালো ধোঁয়া।”
কলকাতার বদলা নিতে মুসলিম সম্প্রদায় নোয়াখালিতে দাঙ্গা শুরু দিল। সশস্ত্র মুসলিমরাও অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল নোয়াখালির অসহায় হিন্দুদের উপর। ১৯৪৬ সালের ১০ অক্টোবর নৃশংস গণহত্যা হয় নোয়াখালিতে। নোয়াখালি দাঙ্গা ‘নোয়াখালি গণহত্যা’ বা ‘নোয়াখালি হত্যাযজ্ঞ’ নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারত স্বাধীন হওয়ার এক বছর পূর্বে অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৪৬ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের পূর্ব বঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশ) নোয়াখালি জেলায় স্থানীয় মুসলিমদের সংঘটিত ধারাবাহিক গণহত্যা, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা। এতে নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ, বেগমগঞ্জ, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর, ছাগলনাইয়া ও সন্দ্বীপ থানা এবং ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর, লাকসাম ও চোদ্দোগ্রাম থানার অধীনে প্রায় ২০০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হিন্দুদের উপর এই গণহত্যা প্রায় চার সপ্তাহ ধরে অব্যাহত ছিল। এতে প্রায় ৫,০০০ হিন্দু হত্যা করা হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। শুধু হত্যা নয়— হিন্দু নারী ধর্ষণ, এবং হাজার হাজার হিন্দু নারী-পুরুষদের জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। প্রায় ৫০০০ থেকে ৭৫০০ বেঁচে থাকা হতভাগ্যকে কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ও অন্যান্য জায়গার অস্থায়ী আশ্রয় শিবির গুলিতে আশ্রয় দেওয়া হয়। এছাড়া প্রায় ৫০,০০০ হিন্দু আক্রান্ত এলাকার অসহায় পশুর মতো জীবনযাপন করতে থাকে। কিছু এলাকায় হিন্দুদেরকে স্থানীয় মুসলিম নেতাদের অনুমতি নিয়ে চলা ফেরা করতে হত। জোর খাটিয়ে ইসলামে ধর্মান্তরিতদের কাছ থেকে লিখিত রাখা হয়েছিল, যেখানে লেখা ছিল তাঁরা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরিত হয়েছে। তাঁদেরকে একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে বা ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হত এবং যখন কোনো আনুষ্ঠানিক পরিদর্শক দল পরিদর্শনে আসত তখন তাঁদেরকে ওই নির্দিষ্ট বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হত। হিন্দুদেরকে ওই সময় মুসলিম লিগকে চাঁদা দিতে হত, যাকে বলা হত জিজিয়া (যা একসময় ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মুসলিম শাসন আমলে হিন্দুরা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বাড়তি কর দিত শাসকদের)। অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি দাঙ্গাকে একটি সাধারণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা’ হিসাবে দেখানোর বিতর্ককে প্রত্যাখান করেন। তিনি এ ঘটনাকে একটি সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের। উপর সংখ্যাগুরু মুসলিমদের সুপরিকল্পিত এবং সুসংঘটিত আক্রমণ’ বলে বর্ণনা করেন। সেই যাত্রা বেঁচে যাওয়া হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় এবং তাঁরা কোনোদিন তাঁদের নিজেদের গ্রামে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারেনি। এর মধ্যে কংগ্রেস নেতৃত্ব ভারত বিভাগ মেনে নেন, যার ফলে শান্তি মিশন এবং আক্রান্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিত্যক্ত হয়। বেশির ভাগ বেঁচে যাওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দুরা তাঁদের বাড়ি-ঘর ফেলে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে চলে আসে।
ওই বছরই ২৯ আগস্ট ছিল ঈদ-উল-ফিতরের দিন। সেদিন থেকেই নোয়াখালির মানুষের মনে আশঙ্কা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। পরিকল্পিতভাবে একটি গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হল যে, হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায় অস্ত্র হাতে জোট বাঁধছে। ফেনি নদীতে মাছ ধরার সময় কিছু হিন্দু জেলেকে মুসলিম সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। তাঁদের একজন মারা যায়, আর আরও দুজন মারাত্মক আহত হয়। মুসলিমরা মারণাস্ত্র নিয়ে চর উড়িয়াতে ৯ জন হিন্দু জেলেকে আক্রমণ করে। তাঁদের বেশির ভাগ মারাত্মক জখম হয়। ৭ জনকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। রামগঞ্জ থানার আওতাধীন বাবুপুর গ্রামের কংগ্রেস নেতার পুত্র দেবীপ্রসন্ন গুহকে মুসলিমরা হত্যা করে। দেবীপ্রসন্নের আর-এক ভাই এবং তাঁদের কর্মচারীকে মারাত্মকভাবে আহত করে তাঁরা। দেবীপ্রসন্নের বাড়ির সামনে থাকা কংগ্রেস অফিস আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। জামালপুরের কাছে মনপুরার চন্দ্রকুমার কর্মকারকে ও ঘোষবাগের হোটেল কর্মচারী যামিনী দেকে হত্যা করা হয়। চর পার্বতীর তাজুমিয়ার হাটে দেবীসিংহপুরের অশু সেনকে নৃশংসভাবে পেটানো হয়। বাঁশপাড়ায় রাজকুমার চৌধুরীকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার পথে মারাত্মকভাবে পিটিয়ে জখম করে ফেলে রাখা হয়। কানু চরে ৬ থেকে ৭টি হিন্দু পরিবারের সমস্ত সম্পত্তি লুট করে নিয়ে যায় মুসলমানরা। করা পাড়ায় ভারী অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত মুসলিম সন্ত্রাসীদের দল যাদব মজুমদারের বাড়িতে হানা দেয় এবং তাঁর সমস্ত সম্পদও লুট করে নিয়ে যায়। তাতারখিলের মোহন চক্রবর্তী, মির আলিপুরের নবীনচন্দ্র নাথ এবং ললিতপুরের রাধাচন্দ্র নাথের বাড়ি-ঘর লুট করা হয়। চণ্ডীপুরের যদুনাথ মজুমদারের শিবমন্দিরেও হামলা করার পর অপবিত্র করে মুসলিমরা। দাদপুরের নগেন্দ্র মজুমদার এবং রাজকুমার চৌধুরীর পুজোর ঘর দুবৃত্তরা অপবিত্র করে এবং মুল্যবান মূর্তিগুলি লুট করে নিয়ে যায়। কেথুরির ঈশ্বরচন্দ্র পাঠক, মারকচরের কেদারেশ্বর চক্রবর্তী, আংপাড়ার অনন্তকুমার দে, তাতারখিলের প্রসন্নমোহন চক্রবর্তী সহ অনেকের বাড়ির দুর্গা প্রতিমা, ছবি ভেঙে ফেলে মুসলিমরা। (নোয়াখালি। নোয়াখালি –শান্তনু সিংহ)
ত্রিপুরা থেকে যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস (এমএলএ) অক্টোবরের ১৪ তারিখে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের কাছে চিঠিতে লেখেন— নোয়াখালির রামগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় হাজার হাজার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের উপর নির্যাতন করে মুসলিমরা। তাঁদের বাড়িঘর লুটপাট করে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয় বসত ভিটা, আর তাঁদেরকে জোর করে ইসলামে ধর্মান্তরকরণের মতো ঘৃণ্য কাজ করে তাঁরা। মুসলমান আক্রমণকারী বাহিনী দাস পরিবারের ১৯ জন সদস্যকে নির্মমভাবে হত্যা করে। হত্যার আগে বাড়ির মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়। মুসলিমরা রামগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের আওতাধীন নোয়াখোলা গ্রামের চৌধুরী পরিবারের উপর হামলা চালায় বর্বর দাঙ্গাকারীরা। হামলাকারীরা উন্মত্তের মতো হত্যার তাণ্ডবলীলা চালায়, লুটপাট করে এবং আগুন লাগিয়ে দেয়। ওই বাড়ির মোট ৮ জন পুরুষ সদস্যের সবাইকে হত্যা করা হয়। বাড়ির মহিলাদের টেনে হিঁচড়ে ঘর থেকে বের করে প্রকাশ্য দিবালোকে জনসম্মুখে গণধর্ষণ করা হয়। মুসলিমদের আর-একটি দল রামগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের গোবিন্দপুরের যশোদা পাল ও ভরত ভূঁইয়ার বাড়িতে আক্রমণ করে। তাঁরা পরিবারের ১৬ জন সদস্যকে দড়ি দিয়ে বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। বাড়ির মহিলাদের উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়। আমিশাপাড়া এবং সাতঘরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকার ভৌমিক এবং পাল পরিবারের সবাইকে আগুনে পুড়িয়ে ছাই বানানো হয়। এই দুই পরিবারের ১৯ সদস্যকে হত্যা করে মুসলিমরা। বাড়ির নারীদের সম্মানহানি করা হয়। গোলাম সরোয়ারের নিজস্ব বাহিনী নন্দীগ্রামের নাগ পরিবারের বাড়িঘর আগুনে পুড়িয়ে শুধু ক্ষান্ত হয়নি, রমণীকান্ত নাগের প্রতিষ্ঠিত পোস্ট অফিস ও বিদ্যালয় ভবনও পুড়িয়ে দেয়। কুঞ্জকুমার নামে বৃদ্ধকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করে দাঙ্গাকারীরা। ১৩ অক্টোবর দুপুর ১২টার সময় মারাত্মক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত ২০০-২৫০ জনের মুসলিমদের একটি দল চাঙ্গিরগাঁওয়ের হিন্দুদের উপর হামলে পড়ে। তাঁরা হিন্দুদের ১,৫০০ মণ ধান পুড়িয়ে ভস্মে পরিণত করে দেয়। এলাকার সমস্ত মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা সকল হিন্দু মহিলাদের শাঁখা ভেঙে ফেলে, সিঁথির সিঁদুর মুছে দেয়, আর হিন্দু পুরুষদের নামাজ পড়তে বাধ্য করে। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনির স্ত্রী সুচেতা কৃপালনি নোয়াখালিতে নারী উদ্ধার করতে যান। তখন দাঙ্গার খলনায়ক গোলাম সরোয়ার ফতোয়া দেয়, যে সুচেতাকে ধর্ষণ করতে পারবে তাঁকে বহু টাকা দেওয়া হবে এবং ‘গাজি’ উপাধিতে ভূষিত করা হবে। বিপদ আসতে পারে আন্দাজ করে সুচেতা সবসময় পটাসিয়াম সাইনাইড ক্যাপসুল গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন। (নোয়াখালি নোয়াখালি– শান্তনু সিংহ)
এডওয়ার্ড স্কিনার সিম্পসন তাঁর রিপোর্টে কেবলমাত্র ত্রিপুরা জেলার তিনটি পুলিশ স্টেশন, যেমন— ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর ও হাজিগঞ্জের অন্তর্ভুক্ত এলাকাতেই ২২,৫৫০টি ধর্মান্তকরণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন। ডঃ তাজ-উল ইসলাম হাসমি মনে করেন, নোয়াখালি গণহত্যায় যে পরিমাণ হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে তার কয়েকগুণ বেশি হিন্দু মহিলাদের ধর্ষণ এবং ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে। এম.এ.খান এর মতে, নোয়াখালির ৯৫ ভাগ হিন্দুদেরই জোরপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তকরণ করেছিল মুসলমানরা। বিচারপতি জি.ডি, খোসলা বলেছেন, নোয়াখালির সমগ্র হিন্দু জনগোষ্ঠীর সর্বস্ব লুট করে নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদেরকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছিল। পাশবিক হিন্দু নিধন আর ন্যাক্কারজনক ধর্মান্তকরণের খবর বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ হতে শুরু করে আশ্চর্যজনকভাবে মুসলিম লিগ পরিচালিত “The Star of India’ সংবাদপত্র জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণের ঘটনা অস্বীকার করে বসল। যদিও অ্যাসেম্বেলিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রশ্নের উত্তরে হোসেন শহিদ সোহরওয়ার্দি বলেন— শুধুমাত্র ত্রিপুরা জেলাতে ৯,৮৯৫ টি ধর্মান্তকরণের ঘটনা ঘটেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখলেন– “কলকাতার দাঙ্গা বন্ধ হতে না-হতেই আবার দাঙ্গা শুরু হল নোয়াখালিতে। মুসলমানরা সেখানে হিন্দুদের ঘরবাড়ি লুট করল এবং আগুন লাগিয়ে দিল। ঢাকায় তো দাঙ্গা লেগেই আছে।”
সোহরাওয়ার্দি তাঁর স্মৃতিকথায় লেখেন— “অমৃতবাজার পত্রিকা এবং কংগ্রেসের অন্যান্য পত্রিকাগুলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের সম্পাদকের নামে অকস্মাৎ একটি বিবৃতি ছাপে যে, ৫০,০০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে এবং অগণিত নারীকে অপহরণ করা হয়েছে। এ খবরে উত্তেজিত হয়ে যুক্তপ্রদেশের গারমুখতেশ্বারে হিন্দুরা মুসলিমদের লাঞ্ছিত করে এবং গণহত্যা চালায় এবং বিহার প্রদেশের সর্বত্র ১,০০,০০০ মুসলমান নারী, পুরুষ ও শিশুকে অবিশ্বাস্য বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বাস করা হয়। চারদিন ধরে বিহারের পল্লি অঞ্চলে হিন্দু দাঙ্গাকারীরা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ধর্ষণ, মানুষের অঙ্গহানি করার মাধ্যমে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এবং স্পষ্টতই বেশ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, এর পেছনে বিহার সরকার ও হিন্দু পুলিশ সদস্যদের মদত ছিল।”
শুধু নোয়াখালি কেন, পূর্ববঙ্গের (এখন বাংলাদেশ) বরিশাল, খুলনা, ঢাকা সর্বত্র মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী হিন্দুবাদী লেখক রবীন্দ্রনাথ দত্ত তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা “দ্বিখণ্ডিতা মাতা, ধর্ষিতা ভগিনী” নামক ছোট্ট পুস্তিকায় লিখেছেন –“১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট আমি ঢাকা শহরের বাসিন্দা ছিলাম। ওই সময় অসংখ্য হিন্দুদেরকে হত্যা করে সমস্ত মৃতদেহগুলি উলঙ্গ করে (যাতে বীভৎসতা দেখে হিন্দুরা ভয় পায়) ট্রাক বোঝাই করে হিন্দুপাড়া ওয়ারিতে পাঠিয়ে দেওয়া হত দাহ করানোর জন্য। ওই মৃতদেহগুলির মধ্যে উলঙ্গ মহিলাদের দেহ এবং এবং শিশুদের মস্তকবিহীন দেহও ছিল। উলঙ্গ মহিলাদের স্তন এবং তলপেটের মাংস নরপশুরা কামড়ে তুলে নিয়েছিল। একদিন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওইপ্রকার এক মহিলার মৃতদেহ দেখে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। শিশুদের মাথাগুলি লাইটপোস্ট বা অন্য কিছুর সঙ্গে বাড়ি দিয়ে খুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ট্রাকের পাটাতনের নিচে ত্রিপল পেতে দেওয়া হত, যাতে রাস্তায় রক্ত না-পড়ে। ট্রাক থেকে মৃতদেহগুলি হাত পা ধরে নামানোর সময় আমাদের পায়ের পাতা রক্তে ডুবে যেত। অবস্থা একটু শান্ত হলে যখন স্কুল কলেজ খুলল, তখন আমাদের সহপাঠী মুসলিম লিগের কট্টর সমর্থক ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, হিন্দুদের মৃতদেহগুলি শ্যামপুর ঘাটে না-পাঠিয়ে উয়ারির হিন্দু পাড়ায় পাঠানো হল কেন? তারা বলল, লিগ নেতারা তোদের ভয় দেখানোর জন্য ওখানে পাঠিয়েছে। কারণ পাকিস্তানের দাবি না মানলে তোদেরও ওই একই অবস্থা হবে।”
নোয়াখালির পালটা বদলা বিহারে। ১৯৪৬ নোয়াখালির দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিহারে দাঙ্গার সুত্রপাত হয়। ৩০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বরের মধ্যকার সংগঠিত বিহার দাঙ্গার ফলে ভারত বিভাজন ত্বরান্বিত হয়। ২৫ থেকে ২৮ অক্টোবরের মধ্যে বিহারের ছাপরা এবং শরণ জেলায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পরে। শীঘ্রই পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুরেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’-তে লিখলেন –“.. শুরু হল বিহারে ভয়াবহ দাঙ্গা। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় মুসলমানদের উপর প্ল্যান করে আক্রমণ করা। হয়েছিল। এতে প্রচুর নিরীহ মুসলিম মারা যায়, বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।” নোয়াখালি যাত্রার আগে থেকেই গান্ধিজির কাছে খবর আসতে থাকে বিহারে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সেখানে ভূমিকা বদলে গেছে, বিহারে আক্রমণকারী হিন্দু আর আক্রান্ত মুসলমান, কচুকাটা করা হচ্ছে। এখানে রক্তপাত হচ্ছে মুসলমানের, পূর্বপুরুষের ভিটে থেকে উৎখাত হচ্ছে মুসলিমরা। বিহারের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রী ডা. সৈয়দ মাহমুদের লেখা বিবরণ থেকে মুসলমানদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের বৃত্তান্ত পড়ে গান্ধিজি স্তম্ভিত হয়ে যান। মনে হয়, “happenings of Noakhali seemed to pale into insignificance”। মাহমুদ অনুরোধ করেন গান্ধিজি নোয়াখালি ছেড়ে এ বার বিহারে চলে আসুন এবং বিহারি মুসলমানদের বাঁচান।
,
বিহারে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খিলাফত আন্দোলনের সময়ও ভালো ছিল। কিন্তু প্ররোচনার ফাঁদে পা দিয়ে পরে সেই সম্পর্কের অবনতি হয়। ডা. সৈয়দ মাহমুদ, অধ্যাপক আবদুল বারির মতো নেতা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ক্রমে হয়ে উঠছিল হিন্দুদের পার্টি, আর লিগ হচ্ছিল মুসলিমদের পার্টি। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার খবর এসে পৌঁছোয় বিহারের শহরে ও গ্রামে। বিহারের বহু মানুষ কলকাতায় কর্মরত ছিল, তাঁরা কলকাতার দাঙ্গায় স্বজন ও সম্পত্তি হারায়। সেখানকার দাঙ্গার কাহিনি ‘gruesome, sometimes exaggerated’ হয়ে বিহারে ছড়িয়ে পড়ে ও তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি করে। হিন্দু মহাসভা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার আহ্বান জানায়। সংবাদপত্রগুলিও দায়িত্বহীনভাবে উত্তেজনা বাড়ায়। ১৯৪৬ সালে ২৫ অক্টোবর কলকাতা এবং পূর্ববঙ্গের ঘটনার বিরুদ্ধে বিহারে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশাল আক্রমণাত্মক মিছিল বেরোয়। বিহারে অন্ধকার দেওয়ালি পালন করা হয়। মসজিদে মসজিদে বলা হয়— ওদের শোক, আমাদের উৎসব। দাঙ্গা লেগে যায়, আর হাজার হাজার মুসলমান সম্প্রদায়ের মৃত্যু হয়।
ডা. মাহমুদের বিবরণ থেকে জানা যায়, হত্যাকাণ্ডে নির্যাতনে উৎখাত হয়ে সাড়ে তিন লক্ষ মুসলমান বাড়ি জমি-স্বর্ণালংকার নামমাত্র দামে বেচে বিহার ছেড়েছে। তিনি নিজে একটি গ্রামে মৃত মানুষে ভরতি পাঁচটি কুয়ো দেখেন, অন্য গ্রামে এমন দশ-বারোটি কুয়ো। অনেক সময় আক্রান্ত মানুষেরা ‘with the courage of despair’ সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল, সমরক্ষায় নিজেদের মেয়েদের হত্যা করেছিল— কিন্তু দাঙ্গাবাজদের জোয়ার তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মরণের পারে। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যে ছিল না তা নয়, তাঁরা কিছু মানুষকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা প্রতিরোধের ক্ষমতা তাঁদের ছিল না। বহু কংগ্রেস নেতা, কংগ্রেসের ঘোষিত নীতির কথা ভুলে এই দাঙ্গার অংশ নেয়। এই দাঙ্গায় বিহারে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায় মানুষের অস্তিত্বের ভিত নড়ে যায়। তাঁরা চলে আসে গ্রাম থেকে শহরে। আশ্রয় নেয় শরণার্থী শিবিরে। পরে শুরু হয় দলে দলে বিহার ত্যাগ। ছিন্নমূলদের মুসলিম লিগ বাংলায় চলে যেতে উৎসাহ দেয়। কারণ মুসলমান শাসনাধীন বাংলাই হল তাদের পক্ষে ‘land of promise’। দেশভাগের পর পশ্চিম থেকে গণপ্ৰব্ৰজনের মাধ্যমে যারা পূর্ব পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল, তাঁদের একটা বড়ো অংশ ছিল অবাঙালি, উর্দুভাষী এবং বিহারি মুসলমান। ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন, “দুঃখজনক হলেও বিহারের দাঙ্গা বাংলার দাঙ্গাপীড়িত হিন্দুদের বাঁচিয়েছে”। বিহার থেকে পাঞ্জাব হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে দাঙ্গা। নরহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগে পাঞ্জাব ও বঙ্গপ্রদেশের দাঙ্গা দেশের সব জায়গা ছাপিয়ে গেছিল। বাঙালি এবং পাঞ্জাবিরা যেভাবে দেশবিভাগের মূল্য দিয়েছে, এমনটা দেশের কোনো জাতিকে দিতে হয়নি।

[কলকাতার দাঙ্গা পরবর্তী দৃশ্য]
কলকাতায় দাঙ্গায় পরেই মুসলিম লিগ এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা ব্রিটিশের পরিকল্পনায় তড়িঘড়ি সায় দিয়ে দিলেন। আটচল্লিশে নয়, সাতচল্লিশেই দেশ চাই। নিকুচি করেছে ওসব গণভাট। মেনে নিলেন যে, দেশভাগই একমাত্র সমাধান। সেই নিরিখে কলকাতার দাঙ্গা যেমন দেশভাগের হিংসার গোড়াপত্তন, তেমনই দেশভাগের সপক্ষে শক্তপোক্ত একটা রাজনৈতিক যুক্তিরও সূচনা। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর দেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেল। দিল্লিতে বসে সাহেবরা যে স্বপ্ন দেখছিলেন, তা পূর্ণতার পথে এগোতে শুরু করল। যাঁরা এতদিন দেশবিভাগ ও বাংলা বিভাগের বিরোধিতা করছিল তাঁরাও শেষ রক্ষা করতে পারল না। এমন পরিস্থিতির জন্য হিন্দু-মুসলিম কেউ-ই দায় এড়াতে পারে না। সমানভাবে দায়ী। কোনো পক্ষ এক ইঞ্চি কম নয়, এক ইঞ্চি বেশিও নয়। কলকাতা, নোয়াখালি ও বিহারে যে ভয়ংকর দাঙ্গার হত্যালীলা সংঘটিত হয়েছিল তার দায় কোনো সম্প্রদায়ই এড়িয়ে যেতে পারে না। উপরতলার নেতারা চাইছিলই এমন একটা দাঙ্গা হোক, হত্যালীলা হোক। এটা যত ভয়ংকর হবে, ততই দেশভাগ দ্রুত অনিবার্য হয়ে যাবে এবং ক্ষমতালোভরা ক্ষমতায় বসবে। উপরতলার নেতারা না-চাইলে এমন হত্যালীলা কিছুতেই হতে পারত না। ব্রিটিশ-পুলিশের ভূমিকাও দর্শকের মতো হত না। ব্রিটিশ-পুলিশ ন্যূনতম সক্রিয় থাকলে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারত না।
শুরু হল দেশভাগ তথা বাংলা ভাগের প্রক্রিয়া। ১৯৪৭ সালে ১ মে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্যাটেলকে লেখেন— “অনুগ্রহ করে বাংলাকে বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে দেবেন না”। এছাড়াও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক জায়গায় লিখেছেন– “ইহারা (মুসলমানরা) হিন্দু সমাজের তলানির নোংরা হইতে এক দল ধর্মান্তরিত মানুষ— যাহারা সবদিক দিয়ে হীনতর। মুসলমান প্রাধান্য বজায় থাকিবার অর্থ বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতি উচ্ছেদ”। এখানে একটা কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্যামাপ্রসাদের ধারণা বাঙালি মুসলমানদের একটা বড়ো অংশ যেহেতু হিন্দুদের নীচু শ্রেণির থেকে সৃষ্ট, তাই তাঁরা কত নিকৃষ্ট। শ্যামাপ্রসাদ ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন— “প্রদেশটি যে গুরুতর সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, তার একমাত্র শান্তিপূর্ণ সমাধান হচ্ছে বাংলার বিভাজন। এর ফলে যে যে অঞ্চলে বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য আছে সেখানে তাঁরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বিকশিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করবে, তাঁরা উভয়ই শীঘ্র উপলব্ধি করবে যে, দুটি (প্রস্তাবিত) প্রদেশে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা উভয়েরই স্বার্থের অনুকূল হবে”। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুণগ্রাহী হিন্দু মহাসভার নেতা বলরাজ মাথোক লিখেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন— “কংগ্রেস ভারত-বিভাজন করেছিল আর আমি করেছিলাম পাকিস্তান-বিভাজন”। তিনি দাবি করেছিলেন যে, বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে তিনিই পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব পাঞ্জাবকে পাকিস্তান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কংগ্রেস ও লিগের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গেই আপস করেছিল এবং সেই আপসের ফলেই বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাজন হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদরা যথার্থই অবান্তর। বিড়লা-গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলরাও দীর্ঘদিন ধরে চেয়েছিলেন হয় অখণ্ড ভারত অথবা বাংলা ও পাঞ্জাবের বুক চিরে দুই প্রদেশের এক এক খণ্ড তাঁদের শাসিত ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে এবং সেই দাবি তাঁরাই আদায় করেছিলেন। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ (যিনি ওই সময় বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ও শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করছিলেন) এক সাক্ষাৎকারে গর্ডনকে বলেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ সেই সময়ে একান্তে বলছিলেন—”এখন আমরা বিভক্ত করি এবং ইংরেজরা চলে যাক। তারপর আমরা সমগ্র অঞ্চল দখল করে নেব”। এই বেরিয়ে এলো শ্যামাপ্রসাদের আসল মুখ। বাংলাভাগ করে উনি হিন্দুদের উদ্ধার করেছিল, সেটা ছিল মুখোশ। ওই বছরেই ১৯ মার্চ শ্যামাপ্রসাদ বাংলা বিভাজনের পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন। হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবে বলা হয়েছিল— “…যতক্ষণ-না বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। এবং এর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শান্তি আসবে না”। এ কথাটায় শ্যামাপ্রসাদবাবু দেশভাগের পর ভুলে গেলেন? নাকি এই ‘যুদ্ধং দেহি’ ভাবটা মুখোশ ছিল? শ্যামাপ্রসাদ নিজে ছিলেন শ্বাপদদের শিবিরে— বিড়লা-গোয়েঙ্কাদের শিবিরে। বাংলা-বিভাজনের জন্য যাঁরা দায়ী তিনি ও হিন্দু মহাসভা তাঁদের সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। সেইজন্যই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নেহরু মন্ত্রিসভায় শিল্পমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৮ আগস্টে লেখা এক রিপোর্টে লন্ডনে কর্তৃপক্ষকে মাউন্টব্যাটেন জানিয়েছিলেন বাংলার গভর্নর বারোজ, যিনি শ্যামাপ্রসাদকে বিলক্ষণ চিনতেন, মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন যে, শ্যামাপ্রসাদ এতই নীচ যে তাঁর পেটের তলা দিয়ে সাপও গলতে পারবে না। (“.Borrows who knows him (Shyamaprasad] well, described him to me recently as being so low that a snake could not crawl under his belly.”)
বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের একটা বড়ো অংশকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ সেবন করিয়ে দিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হিন্দুদের বিপথে চালিত করার সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর সংগঠন। তাঁর বিষময় ফল ফলে ছিল ছেচল্লিশের দাঙ্গায়। সেই দাঙ্গায় মুসলিম নিধনে শ্যামাপ্রসাদ তৃপ্ত। কারণ তিনি সেসময়ে খুব উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভিন্ন বিতর্কিত বিবৃতি দিতে শুরু করেন। হিন্দু ভাবাবেগকে নিজের পক্ষে আনতে নানা প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দিতেন। এই কাজ করার জন্য তিনি আরএসএসের কাছ থেকে সবরকমের সুযোগ-সুবিধা ও সহযোগিতা পেতেন। তেতাল্লিশের (ইংরেজি ১৯৪৩, বাংলা ১৩৫০) মন্বন্তর সৃষ্টির পিছনে অন্যতম প্রধান ষড়যন্ত্রী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। আর-একজন প্রত্যক্ষ দায়ী ছিলেন, তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের রাষ্ট্রনীতি। এই মন্বন্তরে বাংলাজুড়ে ৩০ লক্ষ (অন্য সূত্রে ৩৫ থেকে ৩৮ লক্ষ) মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে মানুষের এত মৃত্যু হচ্ছে শুনে চার্চিল বলেছিলেন– “ভারতীয়রা খরগোশের মতো বাচ্চা জন্ম দেয়, আর এত মানুষ যদি মারাই গিয়েই থাকে, তবে ন্যাংটো ফকিরটা মরে না কেন? ‘ন্যাংটো ফকির’ বলতে গান্ধিজিকে বোঝানো হয়েছে। ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে এমন অপমানজনক কথা বলায় চার্চিলের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সেদিন কোনো প্রতিবাদ করেননি। তেতাল্লিশের মন্বন্তর যে জেনোসাইড ছিল, সেই বিষয়ে এখন আর কোনো তর্ক হয় না। বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়ে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য ছিল, “পূর্ববাংলায় তথা পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবাংলায় ও হিন্দুস্তানে মুসলমানদের জামিন (hostage) হিসাবে ব্যবহার করা হবে”। অর্থাৎ পূর্ব বা পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের অন্যত্র নিরপরাধ মুসলিমদের উপর তার শোধ নেওয়া হবে। আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন– “কিছু গোষ্ঠীর মধ্যে খোলাখুলিই বলা হচ্ছিল যে, পাকিস্তানে হিন্দুদের ভয় করার কিছু নেই, কারণ ভারতবর্ষে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ মুসলমান থাকবে; পাকিস্তানের হিন্দুদের উপর অত্যাচার হলে তার ফল ভারতবর্ষে মুসলিমদের ভোগ করতে হবে।” অনুরূপ ১৯৪২ সালের ৭ অক্টোবর জিন্নাকে একটি চিঠিতে চৌধুরী খালিকুজ্জামান লিখেছিলেন— “পাকিস্তান ধারণার পিছনে অন্যতম মৌলিক নীতি হচ্ছে, হিন্দু প্রদেশে মুসলমানদের মতো মুসলমান প্রদেশেও হিন্দুদের জামিন রাখতে হবে। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের (আঞ্চলিক পুনর্গঠনের ফলে) আমাদের প্রভাবের বাইরে চলে যেতে দিই, তাহলে সংখ্যালঘু মুসলিম প্রদেশে মুসলিমদের নিরাপত্তা খুবই হ্রাস পাবে।” যদিও দেশভাগের পর ওসব জামিন-টামিন কোনো কাজে আসেনি। বাংলা তথা ভারত উপমহাদেশকে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার পরে পূর্ববাংলা থেকে যে হিন্দুরা ভিটেমাটি ত্যাগ করে পশ্চিমবাংলায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁরা নেহরু-প্যাটেল-শ্যামাপ্রসাদদের কেন্দ্রীয় ভারত সরকারের কাছ থেকে কী রকম সহৃদয় ব্যবহার পেয়েছিলেন, সে সবাই দেখেছিলেন বা দেখছেন দৃষ্টিহীন না-হলে।
১৯৪৭ সালে ২ জুন চূড়ান্ত পরিকল্পনা ভাইসরয় কর্তৃক ভারতীয় নেতাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। বলা হয় যে ১৫ আগস্ট ব্রিটিশরা দুটি ডমিনিয়নের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। প্রদেশগুলো নির্ধারণ করবে যে তাঁরা বিদ্যমান আইনসভা বহাল রাখবে নাকি নতুন গঠন করবে অর্থাৎ পাকিস্তানে যোগ দেবে কি না। বাংলা ও পাঞ্জাবও পক্ষ নির্বাচন ও বিভাগ নিয়ে গণভোটে অংশ নেবে। একটি সীমানা কমিশন বিভক্ত প্রদেশের সীমানা। বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার পার্শ্ববর্তী আসামের মুসলিম অধ্যুষিত সিলেট জেলাও গণভোটে অংশ নেবে। ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন, নেহেরু, জিন্নাহ ও শিখ নেতা বলদেব সিং রেডিওতে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। জিন্নাহ ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেন। পরে পাঞ্জাব ও বাংলায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষপর্যন্ত দুটি প্রদেশ বিভক্ত হয়। সিলেট ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পাকিস্তান সৃষ্টির পর জিন্নাহ পাকিস্তান ডমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল হন। অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসাবে থেকে যান।
ব্রিটিশদের ভারত ছাড়তেই হবে একথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই স্থপতি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৫ সাল নাগাদ পুরোপুরি বুঝে গিয়েছিল। বুঝে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। কোমর ভেঙে দুরমুশ। উপনিবেশগুলি চালিয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছিল না। এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। আর্থিকভাবে সাহায্য পাওয়ার আশায় ব্রিটেন সে সময় আমেরিকার কাছে গিয়েছিল। আমেরিকা ব্রিটেনের সেই আবেদনে সাড়া না দিয়ে উপনিবেশগুলো ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিল। কোনোরকম আর্থিক সাহায্য সম্ভব নয়। ব্রিটেনের আর কোনো পথ খোলা রইল না উপনিবেশ রক্ষা করার। অগত্যা উপনিবেশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল।
তখনকার ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে ৩০ জুনের আগেই ভারতবর্ষের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। সেজন্য ১৯৪৬ সালে মার্চ মাসে কেবিনেট মিশন’ নামে একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে। এর কয়েক মাস পরেই জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হলেও মুসলিম লিগ প্রথমে তাতে যোগ দেয়নি। অনেক আলোচনার পর ১৯৪৬ সালে অক্টোবর মাসে মুসলিম লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। ইতোমধ্যে কলকাতা এবং নোয়াখালি সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ঘটনা ঘটে গেছে। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৪৭ সালের ২২ মার্চ নতুন ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছেন চিতায় আগুন দিতে। তাঁর কাজ ছিল ভারতকে ভেঙে দু-টুকরো করে দুটো প্রধানমন্ত্রীকে দুটো ‘দেশ’ হাতে তুলে দেওয়া। একই সঙ্গে দু-দেশের গভর্নর জেনারেল হয়ে থাকারও স্বপ্ন ছিল তাঁর চোখে। যদিও দু-দেশের গভর্নর জেনারেল হওয়ার স্বপ্ন তাঁর হয়নি। ভারতে কয়েক বছরের জন্য গভর্নর জেনারেল হিসাবে থাকতে পারলেও পাকিস্তানে তাঁর পশ্চাতে পদাঘাত করেছিল।
যাই হোক, ব্রিটিশ সরকারের নিয়োগ করা কেবিনেট মিশনের লক্ষ্য ছিল পুরো ভারতবর্ষকে অখণ্ড রেখে বিভিন্ন অঞ্চলে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন নতুন ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল হওয়ার পর ইংরেজদের মাথায় ভিন্ন চিন্তাও আসা শুরু করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তখন অনেকগুলো বৈঠক করেন ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির তখনকার প্রেসিডেন্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। লর্ড মাউন্টব্যাটেন মৌলানা আজাদকে বলেছিলেন, ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু তার আগে ভারতবর্ষে চলমান হিন্দু-মুসলমান সংঘাত বন্ধের জন্য একটা পদক্ষেপ নিতে হবে। মৌলানা আজাদ মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়েছিলেন, কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যকার মতপার্থক্য অনেক কমে এসেছে। তখন ব্রিটিশ কেবিনেট মিশন ভারত ভাগের ক্ষেত্রে বাংলা এবং আসামকে একত্রে রেখেছিল। কিন্তু কংগ্রেস এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা করে। আসাম এবং বাংলা একসাথে থাকবে কি না এ নিয়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্য শুরু হল। দুই পক্ষের মতপার্থক্য এমন একটি। জায়গায় পৌঁছোল যে, তখন তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয়ে পড়ল।
মৌলানা আজাদ প্রস্তাব করেছিলেন এ বিষয়টি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের উপর ছেড়ে দিতে। কিন্তু তখনকার কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাতে রাজি হলেন না। তাঁরা এ বিষয়টিতে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মধ্যস্থতা চাননি। এরই মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অবিশ্বাসের মধ্যে এক জায়গায় এক সঙ্গে বাস করা বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছিল। কলকাতা দাঙ্গায় পর হিন্দু-মুসলমান সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালি ও বিহারে। একদিকে যখন সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে তখন প্রশাসন তখন একটি গা-ছাড়া ভাব নিয়েছে। প্রশাসনে থাকা ইউরোপীয়রা তখন কাজে মন দিচ্ছে না। কারণ তাঁরা বুঝতে পারছিল, যে-কোনো সময় ব্রিটিশরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, তাই তাঁরা শুধু দিন গুনছিল নিষ্ক্রিয় থেকে।
ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটিশরা যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করে দিয়েছিল, সেখানে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের মধ্যে কিছু দপ্তর ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেয়েছিলেন কংগ্রেস নেতা প্যাটেল এবং অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মুসলিম লিগ নেতা লিয়াকত আলি খানকে। কিছুদিনের মধ্যেই কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারলেন, মুসলিম লিগের হাতে অর্থ দপ্তরের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়াটা বিরাট ভুল হয়েছে। কারণ লিয়াকত আলি খানের অনুমোদন ছাড়া প্যাটেল একজন চাপরাশিও নিয়োগ করতে পারছিলেন না। ফলে কংগ্রেস নেতাদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত।
মৌলানা আজাদের বর্ণনা অনুযায়ী, কংগ্রেস নেতা প্যাটেলের কারণেই এ পরিস্থিতির তৈরি হয়। কারণ প্যাটেল স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিজ হাতে রেখে লিয়াকত আলি খানকে অর্থ দপ্তর দিয়েছিলেন। ১৯৪০-এর দশকে ভারতীয় কংগ্রেসের সিনিয়র নেতা আবুল কালাম আজাদ। এমন প্রেক্ষাপটে লর্ড মাউন্টব্যাটেন পরিস্থিতির পুরোপুরি সুযোগ নিয়েছিলেন। নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতপার্থক্যের সুযোগে তিনি ধীরে ধীরে পূর্ণ ক্ষমতা নিজের কাছে নিয়ে নেন। লর্ড মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন, একমাত্র ভারত বিভক্ত হলে এর সমাধান হতে পারে। মৌলানা আজাদ লিখেছেন, লর্ড মাউন্টব্যাটেন উভয়পক্ষকে খুশি রাখতে চেয়েছিলেন এবং উভয়পক্ষকে বুঝিয়েছিলেন যে, পাকিস্তানের সৃষ্টি না-হয়ে উপায় নেই। মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেসের সিনিয়র নেতাদের মনে পাকিস্তান সৃষ্টির বীজ বপন করেছিলেন। আর ভারতীয় নেতাদের মধ্যে প্যাটেলই মাউন্টব্যাটেনের এ ধারণা সবার আগে গ্রহণ করেছিলেন।
এটা বলাই যায়, ভারতবর্ষ ভাগ করার জন্য বল্লভভাই প্যাটেল আগে থেকেই মানসিকভাবে অর্ধেকটাই তৈরি ছিলেন। প্যাটেল ধরেই নিয়েছিলেন, মুসলিম লিগের সঙ্গে একত্রে কাজ করা যাবে না এবং প্যাটেল এক পর্যায়ে জনসম্মুখে বলেই ফেললেন, “মুসলিম লিগের হাত থেকে মুক্তি পাওরার জন্য তিনি ভারতবর্ষ ভাগ করতেও রাজি আছেন।” এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, সর্দার প্যাটেলই ছিলেন ভারতবর্ষ ভাগের স্থপতি। ভারতবর্ষ বিভক্ত করার ফর্মুলা বিষয়ে প্যাটেল মনস্থির করার পর লর্ড মাউন্টব্যাটেন মনোযোগ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরুর দিকে। এ ধরনের ফর্মুলার কথা শুনে প্রথমে নেহেরু খুবই রাগান্বিত হন। কিন্তু লর্ড মাউন্টব্যাটেন নেহরুকে ভারতবর্ষ ভাগ করার উপকারিতা বিষয়ে ক্রমাগত বোঝাতে থাকেন। এ বিষয়ে নেহরুর রাগ প্রশমিত না-হওয়া পর্যন্ত মাউন্টব্যাটেন তাঁর তৎপরতা গোপনে চালিয়ে গেছেন। একটা পর্যায়ে এসে নেহরু ভাগে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু ভারত ভাগ করার বিষয়ে জওহরলাল নেহেরু শেষ পর্যন্ত কীভাবে রাজি হলেন?
মৌলানা আজাদ মনে করেন, এর দুটি কারণ আছে। (১) নেহরুকে রাজি করানোর বিষয়ে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের স্ত্রীর একটি বড়ড়া প্রভাব ছিল। লেডি মাউন্টব্যাটেন ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী। এছাড়া তাঁর মধ্যে আকর্ষণীয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় ছিল, যার মাধ্যমে সে অন্যদের আকৃষ্ট করতে পারত। লেডি মাউন্টব্যাটেন তাঁর স্বামীকে খুব শ্রদ্ধা করতেন এবং অনেক সময় যাঁরা প্রথমে তাঁর স্বামীর কাজের সঙ্গে একমত হতে পারতেন না, তাঁদের কাছে স্বামীর চিন্তা-ভাবনা পৌঁছে দিয়ে তাঁদের সম্মতি আদায় করতেন। ভারত ভাগ করার পিছনে নেহরুর রাজি হওয়ার আর-একটি কারণ ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। এই ভারতীয় ব্যক্তি ১৯২০-এর দশক থেকে লন্ডনে বসবাস করতেন। কৃষ্ণ মেনন ছিলেন নেহরুর একজন বড়ো ভক্ত এবং নেহরুও কৃষ্ণ মেননকে খুবই পছন্দ করতেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সমন্বয়ে ভারতবর্ষে যখন অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয় তখন নেহরু কৃষ্ণ মেননকে লন্ডনে হাই কমিশনার নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মেননের বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের আপত্তি ছিল। কারণ ১৯৩০-এর দশকের প্রথম দিকে ব্রিটেনের লেবার পার্টির একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে কৃষ্ণ মেনন ভারত সফর করেছিলেন। ১৯৪৬ সাল নাগাদ দিকে কৃষ্ণ মেনন যখন আবার ভারতে আসেন তখন লর্ড মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারত ভাগ করার বিষয়ে কৃষ্ণ মেননের মাধ্যমে নেহেরুকে রাজি করানো যাবে।
মৌলানা আজাদ যখন জানতে পারলেন যে ভারত ভাগ করার বিষয়ে নেহরু এবং প্যাটেল মোটামুটি একমত হয়েছে, তখন তিনি ভীষণ হতাশ হয়েছিলেন। মৌলানা আজাদ মনে করতেন, ভারত বিভক্ত হলে সেটি শুধু মুসলমানদের জন্যই নয়, পুরো ভারতের জন্যই সেটি খারাপ হবে। তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের মূল সমস্যা ছিল অর্থনৈতিক। সাম্প্রদায়িক সমস্যা কোনো বড়া সমস্যা ছিল না।
ভারত ভাগ করার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না-নিতে প্যাটেল এবং নেহরুকে বোঝানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন মৌলানা আজাদ। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। ভারত ভাগ করার বিষয়ে প্যাটেল এতটাই অনড় ছিলেন যে, তিনি অন্য কারও মতামত শুনতে মোটেই রাজি ছিলেন না। প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে মৌলানা আজাদ তাঁর বইতে লিখেছেন, “আমরা পছন্দ করি কিংবা না করি, ভারতবর্ষে দুটো জাতি আছে। হিন্দু এবং মুসলমানরা একজাতি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। যখন দুই ভাই একসঙ্গে থাকতে পারে না, তখন তাঁরা আলাদা হয়ে যায়। তাঁদের পাওনা নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার পরে তাঁরা আবার বন্ধু হয়ে যায়। কিন্তু তাঁদের যদি একসঙ্গে থাকতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাঁরা প্রতিদিন ঝগড়া করবে। প্রতিদিন মারামারি করার চেয়ে একবার বড়ো ঝগড়া করে আলাদা হয়ে যাওয়াটাই ভালো।”
আজাদের বর্ণনায়, জিন্নাহ হয়তো ভারত ভাগ করার পতাকা উত্তোলন করেছিলেন, কিন্তু এখন প্যাটেল সে পতাকা বহন করেছেন। ভারত ভাগ করার বিষয়ে প্যাটেল যেভাবে প্রকাশ্যে কথা বলতেন, জওহরলাল নেহরু সেভাবে বলতেন না। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকারের নির্বাহী পরিষদে মুসলিম লিগের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে গিয়ে নেহরুর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রতিদিনই ঝগড়া হত। সেজন্য নেহরু মৌলানা আজাদকে বলেছিলেন ভারতবর্ষ ভাগ না-করে কোনো উপায় নেই। নেহেরু মৌলানা আজাদকে অনুরোধ করলেন, তিনি যাতে ভারত ভাগের বিরোধিতা না-করেন এবং বাস্তবতা মেনে নেন। নেহরু এবং প্যাটেলের এ অবস্থানের কারণে মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ তাঁর পাকিস্তান সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে আরও জোরালো অবস্থান নিলেন। জওহরলাল নেহরুকে সতর্ক করে মৌলানা আজাদ বলেছিলেন, “আমরা যদি ভারত ভাগ করার বিষয়ে একমত হই, তাহলে ইতিহাস কোনোদিনও আমাদের ক্ষমা করবে না।”
প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরুকে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধিজি ছিলেন মৌলানা আজাদের শেষ ভরসা। একদিন মৌলানা আজাদ গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে গেলে গান্ধিজি বলেন, “ভারত ভাগের বিষয়টি এখন বড়ো একটি ভয়ের কারণ হয়েছে। মনে হচ্ছে বল্লভভাই (সরদার প্যাটেল) এবং জওহরলাল আত্মসমর্পণ করেছে। আপনি এখন কী করবেন? আপনি কি আমার পাশে থাকবেন নাকি আপনিও মত পরিবর্তন করেছেন? কংগ্রেস যদি ভারত ভাগের প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে সেটা আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে হতে হবে। আমি যতদিন জীবিত আছি ততদিন ভারতবর্ষ ভাগ মানব না।”
কয়েকদিন পরে গান্ধিজি লর্ড মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করলেন। এরপর প্যাটেল গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করে প্রায় দুই ঘণ্টা বৈঠক করলেন। সে আলোচনার বিষয়বস্তু জানা যায়নি। কিন্তু এরপর যখন মৌলানা আজাদ গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করলেন, তখন বিস্ময়ে হতবাক হলেন মৌলানা আজাদ।
কারণ ভারত ভাগ করার ফমূলা নিয়ে গান্ধিজির আগের যেটা ছিল সেটা অবস্থান বদলে গেল। তিনি ভারত বিভক্তি সমর্থন না-করলেও, আগের মতো জোরালো বিরোধিতাও করলেন না। গান্ধির এ অবস্থান দেখে মৌলানা কালাম আজাদ হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে গান্ধিজি জানালেন, তিনি প্রস্তাব করেছেন যাতে জিন্নাহ সরকার গঠন করে এবং তাঁর পছন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা তৈরি করে। এ বিষয়টি গান্ধিজি তুলে ধরেন মাউন্টব্যাটেনের কাছে এবং মাউন্টব্যাটেন তাতে রাজি হয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন মৌলানা আজাদকে বলেছিলেন, মি: গান্ধীর প্রস্তাব যদি কংগ্রেস মেনে নেয় তাহলে ভারত বিভক্তি এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু নেহরু ও প্যাটেল গান্ধিজির এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁরা দুজনে মিলে গান্ধিজিকে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। তখন গান্ধিজি বলেন, ভারতবর্ষ বিভক্তি অনিবার্য। আহা, যেন মনে হচ্ছে একই পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পদ-সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা চলছে –নেহেরু ও জিন্নাহ। মধ্যস্থতা করছেন ঘরের ভিতরের লোক গান্ধিজি, কালাম আজাদ ও বাইরের লোক মাউন্টব্যাটেন।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটি ভাগ হবে কীভাবে? মৌলানা কালাম আজাদ রাজি না-থাকলেও ভারত ভাগ করার বিষয়ে কংগ্রেসের বাকি নেতৃত্ব সেটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারপরেও মৌলানা আজাদ তাঁর শেষ চেষ্টা হিসাবে। গান্ধিজিকে আবারও বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি গান্ধিজিকে বলেন, বর্তমানে যে অবস্থা চলছে সেটি আরও দুই বছর চলুক। প্রকৃত ক্ষমতা এখন ভারতীয়দের হাতে। এ পরিস্থিতি যদি দুই বছর পর্যন্ত চলে, তাহলে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগ এ সময়ের মধ্যে তাঁদের অবস্থান বদলে একটি ঐকমত্যে পৌঁছোতেও পারে। মৌলানা আজাদ ভেবেছিলেন, দুই বছর পর্যন্ত স্থিতাবস্থা বজায় থাকলে এক পর্যায়ে মুসলিম লিগ একমত হতে বাধ্য হবে। কিন্তু গান্ধিজি যেমন এ প্রস্তাব বাতিল করলেন না এবং আবার কোনো আগ্রহও দেখালেন না। এর মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার জন্য মাউন্টব্যাটেন লন্ডন চলে যান। মৌলানা আজাদ মনে করেন, মাউন্টব্যাটেন ভারত বিভক্ত করার পক্ষেই ছিলেন এবং তিনি তাঁর পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারকে বোঝাতে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩০ মে মাউন্টব্যাটেন ভারতে ফিরে আসেন। ২ জুন তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পরিকল্পনা সংবলিত ‘শ্বেতপত্র প্রকাশ করেন। সেখানে ভারত-বিভক্তির রূপরেখা তুলে ধরা হয়।
ব্রিটিশ সরকারের এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষ অখণ্ড রাখার সব আশা শেষ হয়ে গেল। মৌলানা আজাদ মনে করেন, ভারতবর্ষ ভাগ করার পিছনে ভারতীয়দের স্বার্থের চেয়ে ব্রিটিশদের স্বার্থ বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। এজন্য শেষ পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁরা ভারত ভাগ করার দিকেই এগিয়ে গেল। ব্রিটেন মনে করেছিল, যদি অখণ্ড ভারত স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে সে দেশটির উপর তাঁদের অর্থনৈতিক প্রভাব থাকবে না। বিভক্ত ভারত ব্রিটেনের স্বার্থ হাসিল করত বলেই তাঁদের ধারণা। মৌলানা আজাদ লিখেছেন, শেষপর্যন্ত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে তার স্বাধীনতার মূল্য দিতে হল। মধ্যস্থতাকারী দুই ব্যক্তি গান্ধিজি ও মৌলানা আজাদ ভারতকে অখণ্ড রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। পার্থক্য হল –গান্ধিজি হতাশরোগীর মতো মাঝপথে হাল ছেড়ে দিলেন ১০০ মিটার দৌড়ে, মৌলানা কালাম আজাদ ম্যারাথন দৌড়ে শেষবিন্দু পর্যন্ত আন্তরিক চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এরপরেও গান্ধিজি হলেন মহাত্মা’, আর মৌলানা কালাম আজাদ বিস্মৃতপ্রায়!
ইসলাম ধর্ম নিশ্চয়ই বিদেশি, সৌদি আরবের। কিন্তু ভারতের মুসলমানরা অবশ্যই ভারতীয়। যাঁরা মুসলিমদের ‘বিদেশি’ বলে চিৎকার করে গলা ফাটান, তাঁদের উদ্দেশে তেমনই একজন ‘বিদেশি মুসলমানের সাক্ষাৎকার পড়াব, যিনি কারও থেকে কোনো অংশে কম স্বদেশি তথা ভারতীয় ছিলেন না। ইনি ১৮৮৮ সালে ১১ নভেম্বর সৌদি আরবে পবিত্র মক্কা শরিফে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আফগানিস্তানের হেরাত থেকে ভারতে আসেন। ইনি মুসলিমদের পৃথক ভূখণ্ডের বদলে অখণ্ড ভারতকেই সমর্থন করতেন। সেই ‘মহাত্মা’র নাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। সাভারকররা যেমন সমগ্র হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না, তেমনই জিন্নাহরাও সমগ্র মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করে না। দূরদর্শী মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামও মানুষ কখনো ভুলবে না। ভারত-পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার আগে ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সাংবাদিক সোরিশ কাশ্মীরিকে একটি সাক্ষাৎকার দেন। লাহোরের উর্দু পত্রিকা ‘চাতান’-এ সাক্ষাৎকারটি ছাপা হয়। পরে সোরিশ কাশ্মীরির লেখা বই ‘আবুল কালাম আজাদ’-এও এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ ছাপা হয়। তবে পত্রিকা ও বইটি রহস্যজনকভাবে বিলুপ্ত হলে সাক্ষাৎকারটিও হারিয়ে যায়। কয়েক বছর আগে পাকিস্তানের প্রাক্তন মন্ত্রী আরিফ মোহাম্মদ খান সাক্ষাৎকারটি উদ্ধার করে ইংরেজিতে তর্জমা করেন। বাংলাদেশের শফিক আহমেদের বাংলায় তর্জমায় সাক্ষকারটি ঢাকার দৈনিক কালের কণ্ঠে ছাপা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে প্রশ্ন করা হল–
সাংবাদিক : হিন্দু-মুসলমানের এই বিভেদ ও ঝগড়া এখন এমন তুঙ্গে উঠেছে, তাতে কি মনে হয় না একটা সমঝোতায় পৌঁছানো একেবারে অসম্ভব! আপনি কি মনে করেন না, অবস্থা এখন এরকম যে পাকিস্তানের জন্ম একেবারে অবশ্যম্ভাবী?
কালাম আজাদ : যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান হত তবে আমি তা নিশ্চয়ই সমর্থন করতাম। হিন্দুদেরও একটা অংশ এটা এখন সমর্থন করছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও অর্ধেক পাঞ্জাব একদিকে, অন্যদিকে অর্ধেক বাংলা যদি চলে যায় তবুও যে বিরাট ভারতভূমি থাকবে তার উপর আর সাম্প্রদায়িক দাবিদাওয়া থাকবে না। আমরা যদি মুসলিম লিগের কথায় আসি, তাহলে তাদের ভাষায় এই নতুন ভারতবর্ষ হবে প্রকৃতপক্ষে একটি হিন্দু রাষ্ট্র। এটা অবশ্য কোনো স্থিরমনস্ক সিদ্ধান্ত নয়। এটা হবে একটা সামাজিক বাস্তবতার তার্কিক সিদ্ধান্ত। যে দেশে শতকরা ৯০ ভাগ লোক হিন্দু ও যাঁরা আবহমানকাল থেকে নিজেদের নীতি ও আত্মিক বৈশিষ্ট্যে লালিত পালিত, তারা নতুন কোনো পরিবেশ স্বীকার করবে না। যেসব কারণে ভারতের মাটিতে ইসলামের ভিত্তিমূল স্থাপন করেছিল, তা এখন দেশভাগের এই রাজনীতিতে একেবারে অকেজো হয়ে পড়েছে। সাম্প্রদায়িক ঘৃণা এমন আকার ধারণ করেছে যে, ইসলাম ধর্ম প্রচার একেবারেই অসম্ভব। এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ধর্মকে এক বিরাট আঘাত করেছে। মুসলমানরা কোরান থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। মুসলমানরা যদি কোরান ও হজরত মোহাম্মদের জীবনী থেকে শিক্ষা নিত ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি তার সঙ্গে সংমিশ্রণ না-করত, তবে ইসলাম প্রচারের গতি ব্যাহত হত না। মোগল সাম্রাজ্যের শেষের দিকে মুসলমান জনসংখ্যা ছিল ২২ দশমিক ৫ মিলিয়ন বা সোয়া দুই কোটি, যা কিনা এখনকার সংখ্যার অনুপাতে প্রায় ৬৫ শতাংশ। তার পর থেকে মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েই চলেছিল। যদি মুসলমান রাজনীতিবিদরা অভদ্র ভাষায় গালাগাল না-করতেন (হিন্দুদের প্রতি) ও একশ্রেণির মানুষ, যাঁরা ব্রিটিশদের তাঁবেদার ছিল, তারা যদি এ দুই ধর্মের বিভেদকে আরও বড় করে না-দিত তবে আজ ইসলামের শক্তি আরও বৃদ্ধি পেত।
ইসলামকে আমরা রাজনৈতিক বিভেদ ও ঝগড়ায় প্রাধান্য দিয়েছি, অথচ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে নীতিবোধ জাগ্রত করে মানব আত্মার পরিবর্তন। ব্রিটিশ আমলে আমরা ইসলামকে এক নির্দিষ্ট পরিধিতে আবদ্ধ করে রেখেছিলাম ও অন্যান্য ধর্ম যেমন— ইহুদি, পার্সি ও হিন্দুদের মতোই আচরণ করতাম। ভারতীয় মুসলমানরা ইসলামকে এক জায়গাতেই থামিয়ে রেখে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল। কতকগুলো শাখা অবশ্য ব্রিটিশদেরই সৃষ্টি। ফলে এসব শাখার কোনো গতি বা ইসলামিক মূল্যবোধ রইল না। ইসলামের মূলমন্ত্র ক্রমাগত কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে নিজেদের সমুন্নত রাখা। এটা এখন তাদের কাছে এক অপরিচিত বিষয়। অবশ্যই তাঁরা মুসলমান, তবে নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো। রাজনৈতিক শক্তির কাছেই ওরা মাথানত করেছে, ইসলামের মূল্যবোধের কাছে নয়। ওরা রাজনীতির ধর্মকে কোরানের ধর্মের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়। পাকিস্তান হচ্ছে একটা মতাদর্শ। এটা ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যা উত্তরণের উপায় কি না সেটা তর্কসাপেক্ষ। তবে পাকিস্তান দাবি করা হচ্ছে ইসলামের নামে। ইসলামে কোথাও লেখা নেই, ইসলামবিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে দেশ ভাগ করে ফেলতে হবে। কোরান বা হাদিসে এ ধরনের নির্দেশ আছে কি? এমন কোনো ইসলামী পণ্ডিত আছেন কি, যিনি স্রষ্টার এই বিরাট পৃথিবী উপরোক্ত কারণে ভাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন? এই মতাদর্শে আমরা যদি দেশ ভাগ করি, তবে ইসলাম যে একটি সার্বজনীন ধর্ম তার ভিত্তি কোথায় রইল? ভারতসহ অ-মুসলমান দেশে এই ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আমরা কী ব্যাখ্যা দেব?
ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে দেশভাগ মুসলিম লিগের এক অদ্ভুত চিন্তা। ওরা এটাকে এক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত করতে পারে, তবে কোরান বা ইসলামে এর কোনো বিধান বা নির্দেশ নেই। একজন ধার্মিক মুসলমানের আসল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত? ইসলামের আলোকে ছড়িয়ে দেওয়া, না নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ বিভক্ত করা? এই পাকিস্তান দাবি মুসলমানদের কোনো উপকারেই আসবে না। পাকিস্তান সৃষ্টি হলে মুসলমানদের কী উপকার হবে— এ প্রশ্ন এখনও তর্কসাপেক্ষ; তবে এটা নির্ভর করবে কী ধরনের নেতৃত্ব দেশ শাসন করবে তার উপর। পশ্চিমা চিন্তাধারা ও দর্শন এই সংকটকালকে আরও সংকটময় করে তুলবে। মুসলিম লিগ এখন যে পথে চলছে তাতে আমার স্থির বিশ্বাস যে একদিন পাকিস্তান ও ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ইসলাম একটি দুষ্প্রাপ্য বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। এটা সংক্ষেপে বললাম, তবে স্রষ্টাই জানেন ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে। পাকিস্তান যখনই সৃষ্টি হবে, তখন থেকে শুরু হবে ধর্মীয় সংঘাত। যতদূর আমি দেখতে পাচ্ছি, যাঁদের হাতে ক্ষমতার লাগামটা থাকবে, তারাই ইসলামের সমূহ ক্ষতি করবে। তাঁদের যথেচ্ছাচারের জন্য পাকিস্তানের যুব সম্প্রদায় ওদের থেকে একেবারে আলাদা হয়ে যে-কোনো আন্দোলনে নেমে পড়তে পারে, যা মোটেই ধর্মভিত্তিক হবে না। আজকাল দেখা যাচ্ছে, কোনো কোনো প্রদেশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সেখানকার মুসলিম যুবসম্প্রদায় তুলনামুলকভাবে মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশের যুবসম্প্রদায় থেকে অধিকতর ধর্মভাবাপন্ন। আপনি দেখবেন, আলেমদের বর্ধিত প্রভাবেও পাকিস্তান ধর্মের ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলবে।
সাংবাদিক : কিন্তু আলেমরা কায়েদে আজমের (এমএ জিন্নাহ) সঙ্গে ছিলেন।
কালাম আজাদ : সম্রাট আকবরের সঙ্গেও অনেক আলেম ছিল। ওরা একটা নতুন ধর্মও আবিষ্কার করল। ব্যক্তিগত কারও সম্পর্কে আলোচনা নাই-বা করলাম। আমাদের ইতিহাসে আলেমদের কর্মকাণ্ডের খতিয়ান ভরা। সর্বযুগে তারা ইসলামের অপমান ও মর্যাদাহানি করেছে। তবে তাদের মধ্যে দু-চারজন অবশ্য ব্যতিক্রম। এই এক হাজার বছরের মুসলমানের ইতিহাসে কতজন সম্মানিত ব্যক্তির নাম ওরা উচ্চারণ করেছে? ইমাম হাম্বল ও ইবনে তাইমিয়া সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য ওরা করেনি। ভারতবর্ষেও আমরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার পরিবার ছাড়া আর কারও কথা মনে করতে পারি না। উলেমা সানির সৎ সাহস সম্পর্কে আমরা অবগত এবং সেই উলেমাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল রাজদরবারের সঙ্গে যুক্ত অন্য উলেমাদের নালিশ ও উসকানির পরিপ্রেক্ষিতে। সে উলেমারা এখন কোথায়? ওদের এখন কি কেউ সম্মান দেখায়?
সাংবাদিক : মাওলানা, বলুন তো যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, তবে তাতে দোষের কী আছে? ইসলামকে তো ব্যবহার করা হচ্ছে সম্প্রদায়ের ঐক্য রক্ষার কাজে।
কালাম আজাদ : যে কাজের বা কারণের জন্য ইসলামকে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা ইসলামের মানদণ্ডে মোটেই সঠিক নয়। জামালের যুদ্ধে (হজরত আলি ও হজরত আয়েশার যুদ্ধ) তলোয়ারের আগায় কোরান ঝুলিয়ে যুদ্ধ করা হয়েছিল। এটা কি ঠিক হয়েছিল? কারবালা যুদ্ধে যাঁরা আমাদের নবির পরিবারবর্গকে হত্যা করল, সেসব মুসলমানও আমাদের নবির সঙ্গী বা সাহাবা বলে দাবি করে। এটা কি উচিত বলে মনে হয়? হাজ্জাজ নামে সেনানায়ক ছিলেন, তিনি তো মক্কার পবিত্র মসজিদ আক্রমণ করেছিলেন। এটা কি উচিত বলে গণ্য করা হবে? কোনো পবিত্র বাণী অসৎ চিন্তা বা কর্মকে সঠিকতার নীতির আওতায় আনতে পারে না। যদি পাকিস্তান সৃষ্টি মুসলমানদের জন্য সঠিক হত, তবে আমি অবশ্যই তা সমর্থন করতাম। কিন্তু এই দাবির মধ্যে আমি অন্তর্নিহিত বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আমি আশা করি না মানুষ আমাকে সমর্থন করবে, কিন্তু আমিও আমার বিবেকের বিরুদ্ধে যেতে পারি না। মানুষ সাধারণত জোরজবরদস্তি বা অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার কাছে নতিস্বীকার করে। মুসলমানরা এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি কথাও শোনার পক্ষপাতী নয়, যতক্ষণ-না পর্যন্ত এরা এটা হাতে পায় ও ভোগ করতে পারে। আজকের মুসলমানরা সাদাকে কালো বলতে রাজি আছে, কিন্তু পাকিস্তান দাবি ছাড়বে না। এই দাবি বন্ধ করার উপায় হচ্ছে— হয় ব্রিটিশ সরকারের তা মেনে না-নেওয়া অথবা মি. জিন্নাহকে অন্য প্রস্তাবে রাজি করানো। (কংগ্রেস) ওয়ার্কিং কমিটির অন্য সহকর্মীদের কাছ থেকে জানলাম, ভারত বিভাগ মোটামুটি নিশ্চিত। কিন্তু আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এই দেশভাগ অশুভ ও অমঙ্গল শুধু ভারতের জন্য নয়, পাকিস্তানও সমভাবে এর ভাগীদার হবে। বিভাগটা হচ্ছে ধর্মের জনসংখ্যার সংখ্যাগুরুত্বের উপর ভিত্তি করে, কোনো প্রাকৃতিক সীমারেখা যেমন— পাহাড়, মরুভূমি, নদী এদের উপর ভিত্তি করে নয়। সীমারেখা একটা টানতেই হবে, তবে ওটা কতদিন স্থায়ী হবে বলা কঠিন।
পাকিস্তান সৃষ্টির কল্পনা একটা ঘৃণা থেকে জন্ম নিয়েছে এবং যতদিন ঘৃণা বেঁচে থাকবে, ততদিনই এর অস্তিত্ব। এই ঘৃণা ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ককে গ্রাস করে ফেলবে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্ব হওয়া বা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সম্ভব নয়, যদি-না এ দুটি দেশ আকস্মিক কোনো বিপদের মধ্যে পড়ে। দেশভাগের এই রাজনীতি এ দুটি দেশের মধ্যে এক বিরাট প্রাচীর তৈরি করবে। পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের সব মুসলমানকে সেখানে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ তার ভূমিস্বল্পতা। পক্ষান্তরে হিন্দুদেরও পশ্চিম পাকিস্তানে বাস করা সম্ভব নয়। ওদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। এর প্রতিক্রিয়া ভারতেও দেখা যাবে এবং ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তিনটি পথ খোলা থাকবে— (১) তারা তখন লুট ও নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয়ে পাকিস্তানে চলে যাবে, কিন্তু পাকিস্তান কতজনকে জায়গা দিতে পারবে? (২) তারা হত্যা বা অন্যান্য অত্যাচারের কবলে পড়বে। মুসলমানদের এক বিরাট অংশকে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, যতদিন-না দেশভাগের এই তিক্ত স্মৃতি মুছে যায়। (৩) দারিদ্র্য, লুণ্ঠন ও রাজনৈতিক হতাশার শিকার হয়ে বহু মুসলমান ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করতে পারে।
মুসলিম লিগের বিশিষ্ট মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে যাবে। ধনী মুসলমানরা পাকিস্তানের শিল্প-কলকারখানা ও ব্যাবসা দখল করে পাকিস্তানের অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ কজা করে ফেলবে। কিন্তু তিন কোটি মুসলমান ভারতে পড়ে থাকবে। তাদের জন্য পাকিস্তান কী রেখেছে? হিন্দু ও শিখদের পাকিস্তান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর ওদের অবস্থা আরও সাংঘাতিক আকার ধারণ করবে। পাকিস্তান তখন নিজেও বহু সমস্যায় জর্জরিত হবে। সবচেয়ে বড়ো ভয়, বাইরের শক্তি পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইবে। এবং কালক্রমে এই নিয়ন্ত্রণ কঠিন রঙ্গু হয়ে পাকিস্তানকে বাঁধবে। ভারতের অবশ্য এ সমস্যা নেই। তার ভয় শুধু পাকিস্তানের শত্রুতা। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মি. জিন্নাহর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে বাংলা। তিনি জানেন না, বাংলা বাইরের কোনো নেতৃত্ব মেনে নেয় না। আজ কিংবা কাল তারা সে নেতৃত্ব অস্বীকার করবে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফজলুল হক জিন্নাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তাকে মুসলিম লিগ থেকে বহিষ্কার করা হলো। সোহরাওয়ার্দিও যে জিন্নাহকে খুব সম্মানের চোখে দেখতেন, সেটাও বলা যায় না। মুসলিম লিগ কেন, কংগ্রেসের ইতিহাসই দেখা যাক। সুভাষচন্দ্র বসুর বিদ্রোহের কথা সবাই জানেন। গান্ধিজি সুভাষ বসুর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় অত্যন্ত নাখোশ ছিলেন ও তাকে সরানোর জন্য রাজকোটে আমরণ অনশন শুরু করলেন। সুভাষ বসু গাঁধির বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে কংগ্রেস থেকে সরিয়ে নিলেন। বাংলার পরিবেশ। এমনই যে বাঙালিরা বাইরের নেতৃত্ব অপছন্দ করে এবং তখনই বিদ্রোহ করে, যখন দেখে যে তাদের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে।
যতদিন জিন্নাহ ও লিয়াকত আলি জীবিত আছেন, ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রতি তাদের বিশ্বাস থাকবে। কিন্তু ওরা যখন থাকবেন না, তখন যে-কোনো ছোটো ছোটো ঘটনায় ওদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠবে। আমি মনে করি, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বহু দিন একসঙ্গে থাকা মোটেই সম্ভব নয়। এই দুই ভূখণ্ডে ধর্ম ছাড়া আর কোনো বাঁধন নেই। আমরা মুসলমান— এই মর্মে কোথাও স্থায়ী রাজনৈতিক ঐক্য গড়ে ওঠেনি। আরব দেশগুলি আমাদের সামনে এক ধর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষা— সবই এক। কিন্তু তাদের সরকার ভিন্ন ভিন্নভাবে গঠিত এবং প্রায়ই এরা ঝগড়া-কলহ ও শত্রুতার মধ্যেই আছে। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা, নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার ও জীবনপ্রবাহ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একেবারে আলাদা। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে এখন ওদের মনে যে উষ্ণতা আছে, তা পরে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে এবং বিরোধ ও প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠবে। তখন বাইরের শক্তিগুলি এতে ইন্ধন জোগাবে ও একসঙ্গে এই দুই খণ্ড আলাদা হয়ে যাবে। পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর যাই ঘটুক না-কেন, অন্য প্রদেশগুলি পারস্পরিক বিরোধ ও ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে পুরো পশ্চিম পাকিস্তানকে রণক্ষেত্রে পরিণত করবে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নিজেদের আলাদা আলাদা জাতি বলে ঘোষণা করবে। এই যখন অবস্থা হবে, তখন পুরো ব্যাপারটা বাইরের শক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। তখন পাকিস্তান বলকান বা আরব রাজ্যের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এ সময় হয়তো আমরা নিজেদের প্রশ্ন করব— কী পেলাম, আর কী হারিয়েছি।
আসল বিষয় হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম নয়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। পৃষ্ঠপোষকতা ও বিশেষ বিশেষ সরকারি সুবিধাতেই ওরা অভ্যস্ত। এখন ভারতের এই নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্তিকে তারা ভয়ের দৃষ্টিতে দেখছে। নিজেদের ভয়টাকে ঢেকে রাখার জন্য তারা দ্বিজাতিতত্ত্বের ব্যাপারে সোচ্চার এবং একটা মুসলিম রাষ্ট্র চায়, যেখানে তারা সম্পূর্ণ অর্থনীতিটাকে কজা করতে পারে ও সেখানে অন্যান্য প্রতিযোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ। দেখা যাক, কত দিন এই বঞ্চনাকে ওরা বাঁচিয়ে রাখতে পারে। আমি মনে করি, দেশ ভাগ হওয়ার পর পাকিস্তান কী কী সমস্যায় জর্জরিত হবে—
(১) অযোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব সামরিক শাসন ডেকে আনবে, যা নাকি অনেক মুসলমান রাষ্ট্রে ঘটেছে।
(২) প্রচুর বৈদেশিক ঋণের বোঝা।
(৩) প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না-থাকায় সংঘর্ষ অনিবার্য।
(৪) অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবং বিভিন্ন এলাকা বা প্রদেশের মধ্যে অন্তর্বিরোধ।
(৫) নতুন ধনী এবং শিল্পপতিদের দ্বারা জাতীয় সম্পত্তি লুট ও আত্দসাত।
(৬) অসন্তোষের উৎপত্তি, ধর্ম থেকে যুব সম্প্রদায়ের বিচ্যুতি এবং পাকিস্তান মূলমন্ত্রে ধস নামা।
(৭) নব্য ধনীদের শোষণ থেকে একটা শ্রেণিসংগ্রামের আশঙ্কা।
(৮) পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র।
এ অবস্থায় পাকিস্তানের স্থায়িত্ব খুবই একটা চাপের মুখে পড়বে ও কোনো মুসলিম রাষ্ট্র থেকে কার্যকরী সাহায্য পাওয়া যাবে না। অন্য রাষ্ট্রগুলির কাছ থেকে শর্তসাপেক্ষ সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তবে পাকিস্তানের মূলমন্ত্র ও রাষ্ট্রকে এর জন্য প্রচুর মূল্য দিতে হবে।
সাংবাদিক : প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলমানরা এখন কেমন করে নিজেদের পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রাখবে এবং কেমন করে মুসলিম রাষ্ট্রে নাগরিকদের উপরোক্ত গুণগুলি বিস্তারলাভ করবে?
কালাম আজাদ : ফাঁকা বুলি দিয়ে মূল বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না— এটা শুধু যে-কোনো আলোচনাকে বিকৃত পর্যায়ে আনতে পারে। মুসলমান সম্প্রদায়ের পরিচয় বা স্বকীয়তা বলতে আমরা কী বুঝি? ব্রিটিশ দাসত্বেও যদি আমরা আমাদের স্বকীয়তা না-হারিয়ে থাকি, তবে স্বাধীন ভারতে তা হারাব কেন— যেখানে রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রের বিশেষ গুণাবলি কি বলতে পারেন? আসল বিতর্কের বিষয় ধর্মরক্ষা ও উপাসনার পূর্ণ স্বাধীনতা। এর বাধা কোথায়? এই স্বাধীনতা কি ৯০ মিলিয়ন মুসলমানকে ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে একেবারে অসহায় করে দেবে? বিশ্বের এক বিরাট শক্তি হচ্ছে ব্রিটিশ, তারাই যখন তা পারেনি, তাহলে হিন্দুদের এমন কি শক্তি আছে, যাতে ওরা এই ধর্মীয় স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ করতে পারবে? এই প্রশ্ন তাঁরাই তুলেছে যাঁরা পশ্চিমা কায়দায় শিক্ষিত, নিজেদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিস্মৃত ও রাজনৈতিক ফাঁকা বুলিতে অভ্যস্ত। ভারতের ইতিহাসে মুসলমানদের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কি মনে করেন, মুসলমান রাজারা ইসলামের সেবা করত? ইসলামের সঙ্গে ওদের নামমাত্র সম্পর্ক ছিল। তাঁরা ইসলাম প্রচারক ছিলেন না। ভারতের মুসলমানরা সুফি-ফকিরদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতাবদ্ধ। অথচ এই সুফিদের অনেককে রাজাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছিল। অধিকাংশ মুসলমান রাজা নিজেরাই নিজেদের উলেমা সংসদ তৈরি করে নিয়েছিলেন, আর তাঁরাই ছিলেন ইসলামের মূল্যবোধ ও আত্মিক বৈশিষ্ট্য প্রচারে সবচেয়ে বড়ো বাধা। ইসলাম তার আদি বৈশিষ্ট্যের আবেদনে প্রথম ১০০ বছরের মধ্যে হেজাজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু যে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করেছিল তা একেবারে অন্য ধরনের এবং যাঁরা এই ইসলাম নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা কেউই আরব ছিলেন না। এবং এই ইসলাম তার আসল মূলমন্ত্র থেকে অনেকাংশে বিচ্যুত। তবুও সংস্কৃতি, সংগীত, শিল্প, স্থাপত্য এবং ভাষার উপর মুসলমান শাসনকালের এক বিরাট ছাপ ও স্বাক্ষর থেকে গেছে। ভারতের সাংস্কৃতিককেন্দ্র যেমন দিল্লি, লখনোউ কী বার্তা বহন করছে? সেখানে অন্তর্নিহিত মুসলিম বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পাচ্ছে।
যদি মুসলমানরা মনে এই শঙ্কা পোষণ করে এবং বিশ্বাস করে, স্বাধীন ভারতে তাদের দাসত্ব করতে হবে, তবে আমি তাদের ধর্ম ও হৃদয়ের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় দেখছি না। যে মানুষ জীবন সম্পর্কে বীতরাগ বা অনাসক্ত, তাকে সাহায্যের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়। কিন্তু যে সাহসহীন, ভীতু তাকে সাহসী ও শক্তিমান করা সম্ভব নয়। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানরা এখন কাপুরুষ। তাদের স্রষ্টাভীতি নেই, আছে মানুষকে ভয় করা। এতেই বোঝা যাবে, কেন মুসলমানরা তাদের অস্তিত্বে সন্দিহান। একেবারে মিথ্যা কল্পনার শিকার।
ব্রিটিশরা যখন দেশ দখল করল, তখন তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ব্যবস্থা নিল। কিন্তু তাতে মুসলমান সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায়নি। পক্ষান্তরে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, তার থেকে বেশিই বৃদ্ধি পেল। মুসলমান সংস্কৃতির আত্মিক বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের একটা নিজস্ব মাধুর্য আছে। তা ছাড়া ভারতের তিনদিকে মুসলিম রাজ্য। তাহলে কেন সংখ্যাগুরুরা ভারতের ৯০ মিলিয়ন মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? এতে তাদের কী লাভ হবে? ৯০ মিলিয়ন মুসলমান নিশ্চিহ্ন করা কি এতই সহজ? বস্তুত আমার মনে হয়, মুসলিম সংস্কৃতির আবেদনের প্রভাবে এমন একদিন আসতে পারে, যখন ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই হবে স্বাধীন ভারতের সর্ববৃহৎ সম্প্রদায়।
পৃথিবীর জন্য প্রয়োজন স্থায়ী শান্তি ও দার্শনিক চিন্তাধারা। হিন্দুরা যদি কার্ল মার্কসের অনুসারী হতে পারে, পশ্চিমের দর্শন ও জ্ঞান অনুশীলন করতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে যদি ইসলামের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করে, তবে এর নীতি থেকে অনেক উপকার পেতে পারে। বস্তুত ওরা বিশ্বাস করে, কোনো সংকীর্ণতা বা অনুদারতা ইসলামের মধ্যে নেই এবং স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায়ও বিশ্বাসী নয়। ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও প্রত্যেকের জন্য সমান অধিকার— এই মন্ত্রের এক বিশ্বব্যাপী আহ্বান। ওরা জানে ইসলাম হচ্ছে এক প্রেরিত পুরুষের ঘোষণা, যার মাধ্যমে কেবল সষ্টার উপাসনার কথাই বলা হয়েছে। ইসলাম হচ্ছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভেদাভেদ থেকে মুক্তি এবং সমাজকে পুনর্গঠনসহ তিনটি মূলনীতির উপর দাঁড়ানো। যেমন— স্রষ্টায় বিশ্বাস, ন্যায়বিচার ও জ্ঞান।
আমাদের এই চরমপন্থী মনোভাব ও ব্যবহার অমুসলমানদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। যদি আমরা আমাদের স্বার্থপর উদ্দেশ্য দিয়ে ইসলামকে অপবিত্র না করতাম, তাহলে অনেক সত্যান্বেষী ইসলামের মধ্যে সান্ত্বনা পেত। পাকিস্তানের সঙ্গে ইসলামের কোনো যোগ নেই। এটা মুসলিম লিগের একটা রাজনৈতিক দাবি, যা দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, ভারতীয় মুসলমানদের এটাই হবে জাতীয় লক্ষ্য। আমার মনে হয়, যে সমস্যায় মুসলমানরা ভুগছে, এটা তার কোনো সমাধান নয়। এটা আরও সমস্যা ডেকে আনবে।
আমাদের নবি বলেছেন, স্রষ্টা আমার জন্য গোটা পৃথিবীকে একটা মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন। এখন আমাকে এই মসজিদ ভাগ করতে বোলো না কিন্তু। যদি এই ৯ কোটি মুসলমান সারা ভারতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে এবং দু-একটা প্রদেশে ওরা সংখ্যাগুরু হয় এবং সেই প্রদেশগুলির পুনর্গঠন চায়, তবে তার মধ্যে কিছু যৌক্তিকতা থাকতে পারে। কিন্তু এ ধরনের দাবি ইসলামের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। তবে শাসনব্যবস্থার কারণে তা মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা একেবারে বিপরীত। যতগুলি প্রদেশ ভারতের শেষ সীমানায় আছে, তার প্রায় সবই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং ওদের সীমানা অন্য মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এখন এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে কি কেউ উৎখাত করতে পারে? পাকিস্তান দাবির মাধ্যমে আমরা এক হাজার বছরের ইতিহাস থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি এবং মুসলিম লিগের পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি— ৩০ মিলিয়ন মুসলমানকে হিন্দুরাজের কবলে থাকতে হবে। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, যা নাকি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে, সেটা একসময় দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি করবে ও বহিরাষ্ট্রের ইন্ধন জোগানোর ফলে এটা বিরাট যুদ্ধের আকার নেবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তান সৃষ্টির মধ্যে যদি এত ভয় ও আশঙ্কা নিহিত থাকে, তবে হিন্দুরা এটার বিরোধিতা করছে কেন? আমার মনে হয়, এই বিরোধিতা ওদের মধ্যে দুই মতাদর্শীর কাছ থেকে আসছে। একদল মনে করে, পাকিস্তান একটি সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ঘাঁটি হবে। একটি স্বাধীন ও অখণ্ড ভারত হলে সে নিজেকে সব চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে। আর-এক দল যারা পাকিস্তান দাবির বিরোধিতা করছে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের উসকে দেওয়া, যাতে তারা তাদের পাকিস্তান দাবি সম্পর্কে আরও কঠিন অবস্থান নিতে পারে। আর এভাবে ওরা মুসলমানমুক্ত একটা দেশ লাভ করবে। সংবিধান অনুযায়ী মুসলমানদের নিরাপত্তা পাওয়ার পূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু দেশভাগ হলে তাতে কোনো ফল লাভ হবে না। পাকিস্তান দাবি এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক ভ্রান্ত সমাধান।
ভবিষ্যতে ভারত সাম্প্রদায়িক সমস্যার সম্মুখীন হবে না, তবে শ্রেণি সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। মূলধন ও শ্রম বা মালিক-শ্রমিকের সংঘর্ষ চলবে। কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বাড়ছে, আর এটাকে মোটেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা উচিত হবে না। এই আন্দোলন নির্যাতিত বা শোষিত জনগণের জন্য সংগ্রাম করে যাবে। মুসলমান পুঁজিবাদী ও জমিদার শ্রেণির মনে এই আশঙ্কা বলবৎ। এখন এরা সম্পূর্ণ ব্যাপারটায় একটা সাম্প্রদায়িক রং দিয়ে অর্থনৈতিক সমস্যাটাকে একটা সাম্প্রদায়িক বিবাদে পরিণত করেছে। কিন্তু মুসলমানরা একা এটার জন্য দায়ী নয়। এই কৌশল প্রথমে ব্রিটিশরা তৈরি করে ও পরে আলিগড়ের রাজনীতিমনস্ক ব্যক্তিরা এটা গ্রহণ করে। পরে হিন্দুদের অদূরদর্শিতায় বিষয়টা আরও ঘোলাটে হয়ে যায়। এখন মনে হচ্ছে দেশভাগ ছাড়া স্বাধীনতা পাওয়া যাবে না।
জিন্নাহ এককালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতীক ছিলেন। কংগ্রেসের এক অধিবেশনে সরোজিনী নাইডু তাকে এই উপাধি দিয়েছিলেন। উনি দাদাভাই নৌরাজির শিষ্য ছিলেন। উনি ১৯০৬ সালে মুসলমানদের এক ‘ডেপুটেশন’-এ অংশগ্রহণ করতে রাজি হননি। সেই সময় থেকেই ভারতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ বপন শুরু হল। ১৯১৯ সালে তিনি জাতীয়তাবাদী হিসাবে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে মুসলমানদের আলাদা দাবি উত্থাপনের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। ১৯২৫ সালের ৩ অক্টোবর ‘টাইমস অব ইন্ডিয়া’ পত্রিকায় একটা চিঠি লিখেছিলেন, যাতে তিনি কংগ্রেস একটি হিন্দু সংগঠন’ এই যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯২৫ ও ১৯২৮ সালে সর্বদলীয় অধিবেশনে তিনি যুক্তভোটের সপক্ষে তার অভিমত রেখেছিলেন। ১৯২৫ সালে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বলেছিলেন, প্রথমত ও শেষ পর্যন্ত আমি একজন জাতীয়তাবাদী’ এবং হিন্দু ও মুসলমান সহকর্মীদের বললেন, তারা যেন সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলিকে পরিহার করে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিকে এক সত্যিকারের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে।
১৯২৮ সালে যে সাইমন কমিশন ভারতে এসেছিল তা ‘বয়কট করার ডাক জিন্নাহ দিয়েছিলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি দেশভাগের সপক্ষে ছিলেন না। তিনি বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে বলেছিলেন তারা যেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর কাজ করে যায়। কিন্তু তখনই ক্ষুব্ধ হলেন যখন কংগ্রেস মুসলিম লিগকে বাদ দিয়ে সাতটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করল। ১৯৪০ সালে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবক্ষয় ঠেকাতে তিনি দেশভাগ সমর্থন করলেন। আমার সম্পর্কে মতামত দেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকার মি. জিন্নাহর আছে। তার বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে আমার কোনোই সন্দেহ নেই। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা ও পাকিস্তান দাবির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। এখন তিনি এই দাবি ছাড়তে পারেন না, কারণ এতে তার সম্মানের লাঘব হবে।
সাংবাদিক : এখন এটা পরিষ্কার যে মুসলমানরা পাকিস্তান দাবি ছাড়বে না। যুক্তি, তর্ক, বিচারবোধ এদের মাথায় কেন ঢুকছে না?
কালাম আজাদ : কোনো নীতিবিচ্যুত জনতার উদ্দামতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বড়ো কঠিন কাজ। কিন্তু কারোর বিবেককে দাবিয়ে রাখা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। মুসলমানরা আজকাল আর হাঁটে না। ওরা আবেগতাড়িত হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সমস্যা হচ্ছে, মুসলমানরা স্থিরভাবে কখনো হাঁটতে শেখেনি। হয় তারা দৌড়াবে কিংবা স্রোতের টানে ভেসে যাবে। একশ্রেণির মানুষ যখন আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান হারিয়ে ফেলে তখন তাদের ঘিরে রাখে কাল্পনিক সন্দেহ ও ভয়। তখন তারা কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল বিচার করতে অক্ষম। সংখ্যার শক্তি দিয়ে জীবনের মূল্যকে অনুভব করা যায় না। কেবলমাত্র দৃঢ় বিশ্বাস ও কল্যাণমুখী কাজেই তা লব্ধ হবে। এই ব্রিটিশ রাজনীতি মুসলমানদের মনে প্রচুর আশঙ্কা ও অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। এখন তারা এতই ভীত ও সন্ত্রস্ত যে, তারা চায় ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার আগেই যেন দেশভাগ হয়ে যায়। ওরা কি মনে করে দেশভাগ হলেই সব আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়া যাবে? এই শঙ্কা যদি সত্যিই থাকে, তবে এগুলি তাদের সীমান্তে গিয়ে আঘাত হানবে এবং তা থেকে বেশ বড়ো রকম একটা যুদ্ধ বাধবে। জীবন ও ধনসম্পত্তির যে বিরাট ক্ষতি হবে তা হবে চিন্তার বাইরে।
সাংবাদিক : হিন্দু ও মুসলমান দুটো ভিন্ন জাতি। তাদের মধ্যে সাদৃশ্যও নেই। এদের মধ্যে ঐকমত্য কেমন করে সৃষ্টি হবে?
কালাম আজাদ : এই বিতর্ক বহু আগেই বাতিল হয়ে গিয়েছে। আল্লামা ইকবাল ও মাওলানা হোসেন আহমেদ মাদানির মধ্যে এ বিষয়ে চিঠিপত্র লেখালেখি হয়েছিল, তা আমি পড়েছি। কোরানে কওম’ শব্দটা কেবলমাত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্যই প্রযোজ্য নয়, অন্যান্য মানুষও এর শামিল। মিল্লাত (সম্প্রদায়), কওম (জাতি) এবং উম্মত (উপদল)— এসব শব্দের ব্যুৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক করে কোনো ফল লাভ হবে না। ধর্মের দিক থেকে দেখলে ভারত বহু মানুষ, যেমন— হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, পারসি, শিখদের মাতৃভূমি। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের পার্থক্য বিরাট। তবে এই পার্থক্য ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে অন্তরায় হবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আবার এটাও মানা যায় না— দুটো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ভারতকে অখণ্ড রাখার অন্তরায়। আসল বিষয় হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এবং কেমন করে আমরা তা লাভ করতে পারি। স্বাধীনতা হচ্ছে আশীর্বাদ এবং প্রত্যেকের এটা পাওয়ার অধিকার আছে। ধর্মের ভিত্তিতে এটা লাভ করা যায় না। মুসলমানদের মনে রাখা উচিত যে, তারাই হচ্ছে বিশ্বব্যাপী জনগণের জন্য ঐসলামিক বার্তা বহনকারী। ওরা কোনো ক্ষুদ্র জাতি বা গোষ্ঠী নয় যে, তাদের এলাকায় অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না। সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হবে— ভারতের মুসলমানরা সবাই একই সম্প্রদায়ের নয়। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে তাঁরা বিভক্ত। হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়িয়ে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে, কিন্তু ইসলামের নামে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না। তাঁদের কাছে ইসলাম অর্থ নিজেদের গোষ্ঠীর প্রতি নির্ভেজাল আনুগত্য। ওহাবি, সুন্নি, শিয়া ছাড়াও আরও অনেক গোষ্ঠী আছে, যাঁদের অনেকের সাধু বা পীরের প্রতি আনুগত্য রয়েছে। ছোটো ছোটো বিষয়, যেমন— নামাজের সময় হাত ভোলা বা সজোরে ‘আমিন’ শব্দ উচ্চারণ করা নিয়েও বহু বাদানুবাদ হয়েছে। কিন্তু সমাধানে পৌঁছোনো যায়নি। উলেমারা যখন-তখন “তকফির’ (কাউকে নাস্তিক ঘোষণা করা) ব্যবহার করছে। আগে ওরা ইসলাম ধর্মকে অবিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছে দিত, আর এখন ওরা বিশ্বাসীদের কাছ থেকেও ইসলামকে সরিয়ে দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে— কত সৎ ও ধার্মিক মুসলমানকে কাফের বলে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে। একমাত্র নবিরাই পারতেন এমন যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে।
তাঁদেরও এ ব্যাপারে বহু যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল এবং বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যখন যুক্তি ও বুদ্ধি বিদায় নিয়ে চলে যায় এবং মানুষের মনোভাব প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, তখন ধর্ম-সংস্কারকের কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার চেয়েও বহুগুণে খারাপ। মুসলমানরা এখন তাদের সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে এক কঠিন অবস্থান নিয়েছে। ধর্মের চেয়ে রাজনীতিই ওদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং পার্থিব জিনিসের মধ্যেই ওরা ধর্মের মূল খুঁজে পায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, যাঁরা আমাদের ভালো করতে এসেছিল, তাদের আমরা বিদ্রূপ করেছি ও বহু মানুষের ত্যাগ ও স্বার্থহীন কর্মকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছি। আমরা কে? আমরা সাধারণ মরণশীল জীব। এমনকি বড়ো বড়ো প্রেরিত পুরুষ বা নবিকেও এসব পুরনো রীতিনীতি আঁকড়ে ধরা রক্ষণশীল মানুষদের শিকার হতে হয়েছিল।
সাংবাদিক : আপনি আপনার ‘আল হিলাল’ পত্রিকার প্রকাশনা বহুদিন আগেই বন্ধ করে দিয়েছেন। এটা কি আপনার মুসলমানদের বুদ্ধিমত্তার প্রতি হতাশা কিংবা মনে করেছেন নির্জন মরুভূমিতে আজান দিয়ে কোন ফল লাভ হবে না?
কালাম আজাদ : আমি ‘আল হিলাল’ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছি, তার অর্থ এই নয় যে এর সত্যতা ও সতোর উপর বিশ্বাস হারিয়েছি। এই পত্রিকা বহু মুসলমানের মনে এক বিরাট আলোড়ন এনেছিল। ওরা ইসলাম, মানুষের স্বাধীনতা ও ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যকে নিজেদের মনে দৃঢ় করেছে। এই অভিজ্ঞতায় আমিও প্রচুর লাভবান হয়েছি। মনে হয়েছিল মোহাম্মদের সঙ্গে যাঁরা থাকতেন, সেই সাহাবিদের মতো আমিও অনেক কিছু শিখলাম। আমি নিজে মোহাবিষ্ট হয়ে সেই পৌরাণিক ‘ফিনিক্স পাখির মতো পুড়ে গিয়ে আবার নবজীবনে ফিরে এলাম। ‘আল হিলাল’ তার উদ্দেশ্য সাধন করেছে ও নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে নিজকে পুনর্মূল্যায়ন করে দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য সময় ও মন উৎসর্গ করে দিয়েছিল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উপর নির্ভরশীল এবং হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির চাবিকাঠি। এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও আমি স্থির নিশ্চিত ছিলাম, ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে এবং পৃথিবীর কোনো শক্তিই এটা রোধ করতে পারবে না। মুসলমানদের তখন কী ভূমিকা থাকবে, সে ব্যাপারেও আমি পরিষ্কার চিন্তা করেছিলাম। আমি আশা করেছিলাম, মুসলমানরা যেন অন্যান্য দেশবাসীর সঙ্গে একত্রে হাঁটে এবং ইতিহাস যেন কখনো বলতে না পারে— ভারতীয়রা যখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছিল তখন মুসলমানরা নীরব দর্শকের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল; কখনো যেন না বলতে পারে, ভারতবাসী যখন প্রবল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল এবং স্বাধীনতার সৈনিকদের নৌকা ডুবে যাচ্ছিল, তখন মুসলমানরা আনন্দে হাততালি দিচ্ছিল।
সংঘ পরিবারের দেশসেবকরা দেশভাগের জন্য একতরফাভাবে অহর্নিশি মুসলিম লিগ ও মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলিকেই দায়ী করে। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা হয়। ৩৪ বছর পর ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে লিগের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়েই তাঁরা প্রথম পৃথক দেশের দাবি তোলে। কিন্তু তার বহু আগে ১৯২৩ সালের আগেই হিন্দু মহাসভার নেতা সাভারকার ধর্মভিত্তিক পৃথক দেশের ধারণা উপস্থিত করেছিলেন। তিনি হিন্দুত্ব’ নামক গ্রন্থে ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলিম দুটি পৃথক জাতির তত্ত্ব পেশ করেন। আরএসএস ঘেঁষা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারও তাই বলেছেন— “সাম্প্রদায়িক পথে ভারত বিভাগের ধারণাটির উদ্ভাবনের জন্য বিপুল পরিমাণে দায়ী হল হিন্দু মহাসভা”। মুসলিম লিগ সাভারকারের ওই বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করেছিল।” ফলে এটা পরিষ্কার, ভারতভাগের জন্য হিন্দু মৌলবাদ ও মুসলিম মৌলবাদ উভয়ই দায়ী। কোনো একটি সম্প্রদায়ের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিলে ইতিহাস মিথ্যা হয়ে যায় না। ধর্মীয় মৌলবাদীদের আগ্রহ নিশ্চয়ই ছিল। তারপরেও বলব, এই ভারতভাগ কী রোখা যেত না? হয়তো যেত, উভয় পক্ষে সদিচ্ছা থাকলে। ব্রিটিশরা মনেপ্রাণেই চেয়েছিল ভারত ভেঙে দুটি পৃথক রাষ্ট্র হোক। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত করে সদস্যসংখ্যা বাড়ানো। উপনিবেশ ছেড়ে যেতে যেতেও বেনিফিট নেওয়ার অনন্তকালের প্রচেষ্টা। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ’ হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এমন স্বাধীন দেশগুলো নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্যসংখ্যা সর্বমোট ৫৪টি। এই দেশগুলির মধ্যে অবশ্যই আছে। ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ। বর্তমানে বিশ্বে মানুষের সংখ্যা ৭৪০ কোটি। এর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ, অর্থাৎ ২৪০ কোটি মানুষই কমনওয়েলথের আওতাভুক্ত দেশগুলোয় বাস করে। জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড়ো দেশ ভারত। এই সংখ্যার অর্ধেক মানুষই ভারতে বাস করে। আবার অনেক সদস্য আছে যে দেশ কখনোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিল না। ১৯৯৫ সালে মোজাম্বিক আর ২০০৯ সালে রোয়ান্ডা কমনওয়েলথের সদস্য হয়। দেশ দুটি কখনোই ব্রিটিশ কলোনি ছিল না। তবে কয়েকবার সংগঠনটি তাদের সদস্যও হারিয়েছে। নির্বাচনে কারচুপি নিয়ে জিম্বাবুয়ের সদস্যপদ স্থগিত করা হলে, ২০০৩ সালে রবার্ট মুগাবে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যায়। ১৯৯৯ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের জেরে পাকিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত করা হয়। তবে সাড়ে চার বছর পর তাঁরা আবার সেই পদ ফেরত পান। বর্ণবাদ নিয়ে সমালোচনার জেরে ১৯৬১ সালে কমনওয়েলথ থেকে সরে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ১৯৯৪ সালে তাঁরা আবার এর সদস্য হয়। সর্বশেষ মালদ্বীপ ২০১৬ সালে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে যায়।
ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ কমনওয়েলথভুক্ত মাত্র ১৬টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে আছে। বাকি দেশগুলোর ৬ টিতে নিজেদের রাজা আছে আর ৩১টি দেশ প্রজাতন্ত্র। বিশ্বের চারভাগের একভাগ ভূমি কমনওয়েলথভুক্ত। সবচেয়ে বেশি ভূমি রয়েছে কানাডায়। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ভূমি রয়েছে। তবে বাকি দেশগুলোর বেশিরভাগই ছোটো। প্রশান্ত মহাসাগরে ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু দ্বীপ দেশও আছে। একদা ব্রিটেনের রানির প্রতি সদস্য দেশগুলিকে আনুগত্য প্রদর্শন করা বাধ্যতামূলক থাকলেও পরে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। সমালোচকরা বলেন, কমনওয়েলথ হচ্ছে কলোনি-উত্তর একটি ক্লাব। এরকম ফরাসি ঔপনিবেশিক দেশগুলোকে নিয়েও একটি জোট আছে, যার নাম ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অফ লা ফ্রানকোফোনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে স্বাধীনতা পাওয়া দেশগুলোকে নিয়ে আছে কমনওয়েলথ অফ ইন্ডিপেনডেন্ট স্টেটস।
এই কমনওয়েলথের উদ্দেশ্য– (১) আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জাতিসংঘকে সাহায্য করা, (২) প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষা করা, (৩) দারিদ্র, অজ্ঞতা ও রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়াই করা, (৪) সাম্য প্রতিষ্ঠায় অনুসন্ধিৎসু হওয়া, (৫) বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতা করা, (৬) অবাধ ও মুক্তবাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, (৭) লিঙ্গগত বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা, (৮) মজবুত পরিবেশ সংরক্ষণ, (৯) মৌলিক গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানবাধিকারের বিকাশ, (১০) ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের প্রয়োজনসমূহের স্বীকৃতি, (১১) সুশীল সমাজের ভূমিকাকে গুরুত্ব প্রদান করা এবং (১২) পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতা প্রভৃতি। এইসব শর্তে ব্রিটিশদের উপনিবেশ সাম্রাজ্যে ঢুকিয়ে কুক্ষিগত করেছে। আজকের ব্রিটিশ নাগরিকরা এটা ভেবে গর্বিত বোধ করে, আত্মশ্লাঘা বোধ করে যে, একদা তাঁদের পূর্বপুরুষরা এই ৫৪ দেশ শাসন করত, ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওরা এই ৫৪টি দেশকে পিতৃভূমি মনে করে তৃপ্তিলাভ করে। এই ৫৪ টি দেশের প্রত্যেকটির ন্যাড়া বাঁধা আছে ব্রিটেনের কাছে। সে অর্থে এই ৫৪টি দেশ ১০০ শতাংশ সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারিনি। শর্তসাপেক্ষেই। আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, স্বাধীনতা না-বলে হস্তান্তর বলা উচিত।
..
.
ভারত যদি সত্যিই ব্রিটিশ মুক্ত হয়, তাহলে কেন ব্রিটিশদের রাজস্ব দিতে হয়? কারণ ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৭৩ বছর পরেও মহারাষ্ট্রের অমরাবতী থেকে মর্তুজাপুরের মধ্যে অবস্থিত রেললাইনটি আজও ব্রিটিশের অধীনস্থই আছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। ৭৩ বছর কেটে গেল আমাদের দেশ ‘স্বাধীন হয়েছে। এই ৭৩ বছর পরও ভারতবর্ষের একটি জায়গা আছে, যা আজও ব্রিটেনে অধীনে! এই রেললাইনটি জন্য প্রতি বছর ভারত সরকারকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা কর দিতে হয় ব্রিটিশ সরকারকে। অমরাবতী বিখ্যাত ছিল কার্পাস তুলো উৎপাদনে। যার খ্যাতি সারা দেশের বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশরা ব্যাবসার স্বার্থে কার্পাস তুলো মুম্বাই বন্দরে আনার উদ্দেশ্যেই এই রেলপথটি নির্মাণ করে। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সংস্থা ক্লিক নিক্সন এই রেলপথটি স্থাপন করে। যার মোট দৈর্ঘ্য হল ১৮৯ কিলোমিটার। রেলপথটি স্থাপন করতে ১৩ বছর সময় লাগে। ধীর গতিতে চলা এই ট্রেনটি সম্পূর্ণ যাত্রা করতে ৬-৭ ঘণ্টা সময় লাগে। যার মধ্যে ছোটো-বড়ো ১৭ টি স্টেশনে থামে। এই রুটে শকুন্তলা এক্সপ্রেস’ চলার কারণে এটি শকুন্তলা রুট’ নামেই পরিচিত হয়। প্রায় ১০০ বছরের পুরনো এই ট্রেনটি বাষ্প ইঞ্জিনের সাহায্যে চলত। ১৯৯৪ সালে এটি ডিজেল ইঞ্জিনের দ্বারা চালানো শুরু হয়। এই ৫ বগি ট্রেনটিতে প্রতিদিন এক হাজারেরও বেশি মানুষ যাতায়াত করেন। ১৯৫১ সালে রেলপথের জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তখন এই রেলপথ রুটটি ভারত সরকারের অধীনে আসেনি। ব্রিটিশ সরকার এত টাকার কর নেওয়া সত্ত্বেও এই ট্রেনটি কোনো মেরামত করা হয় না। গত ৬০ বছর ধরে এই রেল ইঞ্জিনের কোনো মেরামত করা হয়নি। তাই এখন এর সর্বাধিক গতি ঘণ্টায় মাত্র ২০ কিলোমিটার।
ভারত তার ডোমিনিয়ন মর্যাদার সঙ্গে এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে একটি স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। সময়কাল ‘ডোমিনিয়ন’ মর্যাদা দেওয়ার তারিখ (১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট) থেকে ৯৯ বছর পরে, অর্থাৎ ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য ব্রিটিশরা ভারতের সঙ্গে ঠিক কী কী চুক্তি করেছিল, তা প্রকাশ্যে এসে যাবে ২০৪৬ খ্রিস্টাব্দে, অর্থাৎ আর মাত্র ২৬ বছর পর।
কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা গোপনে জানিয়েছিলেন যে, সাময়িক কিছু সময়ের জন্য ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বললেও তাঁদের ভারতবর্ষ কখনো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বা কমনওয়েলথ ত্যাগ করবে না। তবে তাঁদের এই আশ্বাস গোপন রাখতে হবে, না হলে কংগ্রেস সংগঠনকে ভোমিনিয়ন স্টেটাসে রাজি করানোতে অসুবিধা হবে। মাউন্টব্যাটেনের মতো এটলিও খুবই খুশি হয়ে ডোমিনিয়ন প্রধানমন্ত্রীদের সেই সংবাদ জানিয়েছিলেন। (IDBI, x, 974-5-emphasis added) মাউন্টব্যাটেন ১১ মে টেলিগ্রাম করে লন্ডনকে জানালেন, দীর্ঘদিন ধরে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যপূরণের জন্য আমাদের অবশ্যই ১৯৪৭ সালের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দিতে হবে। এর ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কী কী লাভ হবে তা তিনি উল্লেখ করেছেন (IDBI., 774)। অর্থাৎ ভারত ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন মুক্ত হলেও পরোক্ষ শাসন মুক্ত হতে পারেনি। সেই কারণেই বোধহয় ভারতের শিল্পপতিরা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংকঋণ ফাঁকি দিয়ে ব্রিটেনে পালিয়ে যায় এবং ব্রিটেন তাঁদের শেল্টার দেয় পরম আত্মীয়ের মতো। সেই কারণেই বোধহয় এখনও তাঁদের তৈরি ভারতের স্থাপত্যগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্রিটেন থেকে টাকা পাঠায়। সেই কারণেই বোধহয় আজও ব্যস্ত কলকাতায় ভর্তুকিতে ট্রাম চলে, সংস্কার হয়। লোকসালে চললেও তুলে দেওয়া যায় না।
বাস্তবে ধর্মভিত্তিক জাতি দাঁড়ায় না। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও, ধর্মের ভিত্তিতে তারা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ থাকতে পারেনি। সেখানে কয়েক ডজন পৃথক দেশ আছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ধর্মও একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ গঠন করতে পারেনি। যদি মুসলিমরা ধর্মের ভিত্তিতে একটি জাতি হত তাহলে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টি হত না। এ দেশে হিন্দুর সঙ্গে ‘জাতির বিষয়টিকে অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে হিন্দুত্ববাদীরা। কিন্তু তাঁদের এই প্রশ্নটির তো উত্তর দিতে হবে, হিন্দুমাত্রেই যদি এক জাতি হয়, তা হলে নেপালের হিন্দুরা কোন্ জাতি? ইন্দোনেশিয়ার হিন্দুরা কোন্ জাতি?
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি স্বাধীনতা উৎসবে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বটে। এমনকি ঠিক হয়েছে পার্টি অফিসে লাল ঝান্ডার সঙ্গে তেরঙা পতাকা ওড়ানো হবে। কিন্তু মনে মনে কেউ কেউ জানেন, স্বাধীনতা বলে যা এলো, তা আসলে একটা অন্তর্বর্তী স্বায়ত্তশাসন– ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়েছিল, এই স্বাধীনতার তার সঙ্গে কোনো মিল নেই। এখানে খোলসটা পালটে বড়োেলাটই হয়েছেন গভর্নর জেনারেল। সেই কারণেই কমিউনিস্টরা বললেন– “লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।”
‘ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়”– এই কথা বলে কি কমিউনিস্টরা কেবলই বাজার গরম করেছে? কিন্তু কমিউনিস্টরা ছাড়াও অনেকেই তো বলে থাকে ভারতের স্বাধীনতা আসলে ‘নকল স্বাধীনতা। এত রক্তপাতের পর, এত প্রাণ বলিদানের পর, এত এত গরিব মানুষের ভিটেমাটি চাটি হওয়ার শেষ পর্যন্ত ‘নকল’! স্বাধীনতার ফাঁকি, কতটা ফাঁকি সেটা জানতে আগ্রহী পাঠকরা বিমলানন্দ শাসমলের লেখা ‘স্বাধীনতার ফাঁকি’ বইটি পড়ে দেখতে পারেন। বিমলানন্দ শাসমল হলেন অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের কৃতি সন্তান।
আমরা কি সত্যিই একটি পৃথক জাতীয় দেশ? আপনি কি শীর্ষ (Power Transfer) চুক্তির কথা শুনেছেন? জ্যাকব মাইকেল লিখছেন– (১) ব্রিটিশ লেবার পার্টির একজন মন্ত্রী স্টাফোর্ড ক্রিপস ১৯৪২ সালের মে মাসে গান্ধির কাছে একটি প্রস্তাব নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে ‘CRIPS offer’ নামে পরিচিত একটি মিশন নিয়ে ভারত সফর করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতে ‘Dominion Status’ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তবে ১৯৪৭ সালের জুনে লন্ডনে হাউস অফ কমন্সে গৃহীত বিল হিসাবে চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার আগে পর্যন্ত এই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলেছিল, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল থেকে ভারত থেকে মাউন্টব্যাটেনের রিপোর্টের ভিত্তিতে, যখন তিনি ভাইসরয় হয়েছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭’ নামে পরিচিত এই বিলটি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ভারতে Dominion Status প্রদানের জন্য পাস হয়েছিল। (২) ব্রিটেনের সংসদ কর্তৃক গৃহীত ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭’-এর সংক্ষেপে পূর্ববর্তী প্রস্তাবিত শীর্ষের এক এক্সিকিউটিভ নাম ছিল, যা আজও ব্রিটিশ হেফাজতে অত্যন্ত শ্রেণিবদ্ধ রয়েছে, ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল অসংখ্য খণ্ডের মধ্যে মাত্র ১২ টি এবং উচ্চ সেন্সরযুক্ত খণ্ডগুলি। ভারতে পাবলিক লাইব্রেরিগুলিতে এই খণ্ডগুলি ‘TOP SERIES 1942-47’ নামে পাওয়া যায়। (ষষ্ঠ ভলিউম ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের ১৪২ থেকে ১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে ‘War Criminal’ হিসাবে সুভাষচন্দ্র বসুর গ্রেপ্তার সম্পর্কিত বৈঠকে আলোচনা হয়)। (৩) ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭’-এর পূর্ববর্তী ডায়ার্কির (Diarchy) অধীনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত কিছু বিধিনিষেধযুক্ত বিষয় আছে, যেগুলির চুক্তিতে এই বিষয়গুলিতে ভারতীয়দের স্থানান্তর করা হয়নি। এটা ১৯৪৭ সালে ভারতীয় ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্টের শীর্ষস্থানীয়। (৪) সীমাবদ্ধ বিষয়গুলির মধ্যে কর, রাজস্ব, বৈদেশিক সম্পর্ক/নীতিমালা, বিচার বিভাগ, পুলিশ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কার্যকর হওয়া পূর্ববর্তী চুক্তিগুলির সঙ্গে জড়িত। এটি ভারতীয় ইউনিয়নকেও বেঁধে দিয়েছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অফ নেশনসকে, যাঁরা ব্রিটিশ সার্বভৌমকে কমনওয়েলথের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, যাঁর কাছে সমস্ত আধিপত্যকে আনুগত্যের শপথ নিতে হয়েছিল। এই আনুগত্য যে আইনটিতে প্রবেশ করেছিল, আইনটি কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকে ৯৯ বছরেরও কম সময়ের জন্য স্থায়ী হবে বলে মনে করা হচ্ছে।
৯৯ বছর ধরে ভারতের ইজারা দাবির পক্ষে সমর্থন করার জন্য কোনো সরকারি দলিল নেই। কারণ এই জাতীয় সংবেদনশীল দলিল প্রত্যেকের মনকে আগুনে পোড়াতে পারে দেশপ্রেমিক ভারতীয় হিসাবে এই ভেবে। যে, তাঁরা বছরের পর বছর ধরে প্রতারিত হয়েছিলেন। তবে রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ নেওয়ার পরে প্রতিটি প্রধানমন্ত্রী স্বাক্ষরিত এই দলিলগুলি একটি চিরন্তন সত্য। রাষ্ট্রপতির কার্যালয় আরটিআইয়ের পরিধির বাইরে থাকায় আরটিআই ধারার মাধ্যমে এই দলিলের তথ্য প্রকাশের কোনো প্রচেষ্টাও সম্ভব নয়। সুতরাং, প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত এই নথিগুলির বিষয় ধরে রাখা অসম্ভব, কারণ তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে গোপনীয়তার সঙ্গে নথির অংশ তৈরি করে। এর জন্য কিছু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন হবে, যা এই। নথিগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রকাশিত হবে, সেই ক্ষেত্রে তাঁদেরকে বিচারের সামনে আনতে হবে এবং এটি অনুসরণ করার জন্য বিস্তৃত আন্তর্জাতিক প্রভাব ফেলবে। ব্রিটিশরা ১৫ আগস্টের মধ্যরাতে ‘ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭’-এর অধীনে একটি ঘোষণার মাধ্যমে ভারতকে ছেড়ে যায় ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। ভারতে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছিল, হোয়াইট অফিসারদের সঙ্গে ভারতের কর্তৃত্বের প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতের ভাইসরয় এবং তারপরে ১৯৪৮ সালে জুন পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল লুই ফ্রান্সিস অ্যালবার্ট ভিক্টর নিকোলাস মাউন্টব্যাটেন ছিলেন ভারতে এমনই একজন কর্মকর্তা। একটি ডোমিনেশন কেমন হবে? ডোমিনিয়ন হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্ব-শাসিত বিভাগ, ব্রিটিশ কমনওয়েলথে আনুগত্যের সঙ্গে। যদিও ‘আধিপত্যের মর্যাদা’ সেই দিনটির সঙ্গে শেষ হয়েছিল, যখন ভারত একটি স্বাধীন সংবিধানের প্রজাতন্ত্র হয়ে উঠল। আমরা এখনও ভারতীয় সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ডোমিনিয়ন বিধানগুলিতে আবদ্ধ আছি। ১৯২৬ সালে বালফোরের (Balfour) ঘোষণাপত্রে কী সংজ্ঞায়িত হয়েছে তা দেখুন, ‘ডোমিনিয়ন কী? ডোমিনিয়ন হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়, কিন্তু ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের একটি সাধারণ আনুগত্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ হয়। ভারত তার আধিপত্য মর্যাদার সঙ্গে এইভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে একটি স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায় হয়েছিল। সময়কাল ‘আধিপত্য’ মর্যাদা দেওয়ার তারিখ থেকে ৯৯ বছর পরে এবং এই জাতীয় সমস্ত ‘ডোমিনিয়ান’ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকার জন্য নিজেকে অঙ্গীকার করতে হবে। ভারতের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত ভারতের বর্তমান ফেডারেল কাঠামোটি ভারত সরকার আইন ১৯৩৫’ অনুসারে, ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিযুক্ত। এর অনেকগুলি ধারা রয়েছে, যা পরবর্তীতে শীর্ষ চুক্তিতে গৃহীত হয়েছিল। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, যা ব্রিটিশ সরকারের একটি সৃষ্টি, ১৯৩৫ সালে উল্লিখিত আইনের অনেকগুলি ধারাতেও আবদ্ধ। ১৭৭৬ খ্রিস্টাব্দের আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুসারে –“যে ঐক্যবদ্ধ উপনিবেশগুলি হল এবং যথাযথ স্বাধীন হওয়া উচিত স্বতন্ত্র রাজ্য। তাঁরা ব্রিটিশ রাজার প্রতি সমস্ত আনুগত্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এবং তাঁদের এবং গ্রেট ব্রিটেনের রাজ্যের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক সংযোগ রয়েছে এবং একেবারে দ্রবীভূত হওয়া উচিত। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭-এ লেখা চুক্তি অনুসারে, আমরা আধিপত্যের স্থিতির অধীন ছিলাম। এটাও লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে একমত হওয়ার পরে আমাদের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল হিসাবে সি রাজগোপালচারীকে নেহেরু নিযুক্ত করেছিলেন। ভারত প্রজাতন্ত্র হয়ে উঠলেও আমাদের একটি সংবিধান ছিল, যা আমাদের উপর ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে বাধ্য করা হয়েছিল এবং এই সংবিধানটি ব্রিটেনের পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য বিভিন্ন সংবিধানের সংমিশ্রণ ছিল, যার মতে, আমাদের সংবিধান ছিল প্রণয়ন।
যদিও কোনো পাবলিক রেকর্ড পাওয়া যায়নি, তবে এটি এখনও ভারতের জনগণের দ্বারা জানা যায় যে, ব্রিটেনের সম্রাটের কাছে স্বীকৃতি স্বীকারের রূপটি তৈরি করা হয়েছিল। নেহরু লিখেছেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট– “I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty, KING GEORGE THE SIXTH, Emperor of India, His Heirs, and Successors, according to law.” এবং নেহরুর দ্বারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অফিসের অনুমোদনের রূপটি এইভাবে তৈরি হয়েছিল –“I, Jawaharlal Nehru, do solemnly affirm that I will well and truly serve our Sovereign, KING GEORGE THE SIXTH, Emperor of India, in the Office of Member of the Governor General’s Executive Council, and that I will do right to all manner of people after the laws and usages of India without fear or favor of affection or ill-will.” বলা হয় যে নেহেরু প্রথমে এই শব্দগুলি আবৃত্তি করতে অস্বীকার করেছিলেন। কিন্তু অন্য বিকল্প না-পেয়ে তা করতে হয়েছিল। ভারত প্রজাতন্ত্রের পরেও বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন ব্রিটিশ। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ অফিসার ছিল রোনাল্ড ইভেলো-চ্যাপম্যান (Ronald Ivelaw-Chapman) এবং জেরাল্ড গিবস (Gerald Gibbs) যথাক্রমে ১৯৫১ এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বিমান বাহিনীর প্রধান ছিলেন। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কেবল আমাদের নিজস্ব ভারতীয় নাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিমান বাহিনী বিষয়ক কর্ণধার হন।
১৯৫৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ডঃ আম্বেদকর রাজ্যসভায় (সংসদে) তাঁর বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলেছিলেন– “People always keep saying to me: “Oh, you are the maker of the Constitution.” My answer is I was a hack. What I was asked to do, I did much against my will. “My friends tell me that I have made the Constitution. But I am quite prepared to say that I shall be the first person to burn it out. I do not want it. It does not suit anybody….” আম্বেদকর খোলামেলাভাবে জানিয়েছিলেন যে, তিনি ভারতীয় সংবিধানকে সুসংহত করার জন্য যেভাবে কথা বলেছেন তাতে তিনি খুশি হননি।
সাংবাদিক-গবেষক শমীন্দ্র ঘোষ তাঁর একটি লেখায় স্পষ্টভাবে বলেছেন– “১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ভারত হল ‘ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ডোমিনিয়ন’। ভারতবর্ষের নাম হল ইংরেজিতে ‘ডোমিনিয়ন অব ইন্ডিয়া’, বাংলায় ব্রিটিশের ‘ভারত অধিরাজ্য’; ২৬ জানুয়ারি ১৯৫০ সালে সংবিধান প্রবর্তনের সময়ে নাম হল ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া’; সংক্ষেপে ভারত ও ইন্ডিয়া। পতাকা হল তেরঙ্গা ও অশোকচক্র। নীতিবাক্য হল ‘সত্যমেব জয়তে’। সঙ্গীত হল ‘জনগণমন-অধিনায়ক..’। রাজধানী হল দিল্লি। মুদ্রা হল ‘রুপি’; ৬৪ পয়সায় ১ টাকা গণনা করা হল। ভাষাসমূহ হল ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি এবং ২১টি অন্যান্য ভাষা; সরকারি কাজের ভাষা ইংরাজি। সরকার হল ‘সাংবিধানিক রাজতন্ত্র’। রাজা হলেন ব্রিটিশ রাজা ষষ্ঠ জর্জ। গভর্নর জেনারেল তথা সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ নাগরিক ও ব্রিটিশ রাজার কর্মচারী। ২২ জুন ১৯৪৮ সালে এই পদে বসলেন চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী। তিনি শপথ নিয়েছিলেন— “আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি মহারাজা ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতি আইনানুসারে বিশ্বস্ত থাকব ও অনুগত থাকব; এবং আমি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী শপথ নিচ্ছি যে, আমি গভর্নর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থেকে মহারাজা ষষ্ঠ জর্জ, তাঁর বংশধর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে সেবা করব।” প্রধানমন্ত্রী হলেন জওহরলাল নেহেরু। ব্রিটিশ কমনওয়েলথে সদস্য থাকল ভারত। অর্থাৎ ব্রিটিশরা পরোক্ষে ভারতশাসন শুরু করল। তাঁদের আজ্ঞাবহ দাসেদের নেতা হলেন নেহরু। ভারতের গণপরিষদ গ্রহণ করল ভারত অধিরাজ্য’-এর ক্ষমতা। তবে তা সার্বভৌম ছিল না। ১১ টি ব্রিটিশশাসিত প্রদেশ যুক্ত হল। বাকি ৬৩৫টি দেশীয় সামন্তরাজা-শাসিত ও করদরাজ্য ছিল, যেগুলো সেদিনও যুক্ত হয়নি উক্ত অধিরাজ্যে। পৃথক ছিল চন্দননগর, গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা, নগর হাবেলি, পন্ডিচেরি (বর্তমান নাম পুদুচেরি), বনগাঁ (সংযুক্তি ডিসেম্বর ‘৪৭) বহু বিদেশি-শাসিত স্বতন্ত্র উপনিবেশ। ওইদিনটি ভারতের গণপরিষদের পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয়।
কংগ্রেস কখনোই ব্রিটিশদের উচ্ছেদ চায়নি। তাঁরা চেয়েছিল ব্রিটিশ শাসনেই নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার। বাল গঙ্গাধর তিলক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির (১১ ডিসেম্বর ১৯০৬) এক সভায় বলেছিলেন, “ইংরাজ সরকারের উচ্ছেদ চাই না। কিন্তু রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই করতে হবে। নরমপন্থীরা ভাবেন আবেদন নিবেদন করে এই অধিকার লাভ করবেন, আমরা ভাবি প্রবল চাপ সৃষ্টি করলেই তা পাওয়া যাবে।” ব্রিটিশরাজ সিংহাসনের প্রতি গান্ধিজির আনুগত্য ছিল খুবই গভীর। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গান্ধিজির গভীর আনুগত্য আরও প্রকাশ পেল ১৯২১ সালের আমেদাবাদ কংগ্রেসে মৌলানা হসরৎ মোহানির যখন বললেন– “ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হল ভারতীয়দের জন্য বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা।” এই কথা শুনে গান্ধিজি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। অহিংস অসহযোগ মন্ত্রের উদ্ভাবক যখন একদিকে ইংরেজি বস্ত্র, শিক্ষা, বাণিজ্য সবকিছু বর্জন করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন, পাশাপাশি তিনিই আবার ব্রিটিশ প্রভাবমুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নে সিংহবিক্রমে বাধা দিলেন। দেশকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে দেশের লাখো লাখো যুবক-যুবতী আত্মবলিদান দিচ্ছেন, তখন ভারতের জাতীয় নেতাদের মধ্যে অধিকাংশ হিন্দুরা একবাক্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তত্ত্বাবধানেই থাকার পক্ষপাতী ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, মতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ। এঁরা বারবার বলেছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় থেকে স্বাধীনতা লাভ করাই অধিক বাঞ্ছনীয়। তাঁদের মতে পূর্ণ স্বাধীনতা কিছুই না, খুবই নিকৃষ্ট আদর্শ। ডোমিনিয়ন স্টেটাসই সবচেয়ে মহত্তম আদর্শ। স্বাধীন ভারতের নেতাদের ষষ্ঠ জর্জের নামে শপথ নেওয়া এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে আশ্চর্য হই না।
যাই হোক, ভারত ভাগ হলেও বাংলা ভাগ নিয়ে যথেষ্ট জলঘোলা হয়েছিল, তার সাক্ষী ইতিহাস। বাংলা ভাগের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নাম জড়িয়ে আছে, ঠিক তেমনি জড়িয়ে আছে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের নামও। আমরা এবার একটু জেনে নিতে পারি বাংলা ভাগের সঙ্গে যোগেন মণ্ডলের সম্পর্ক কী ছিল। দেশভাগের প্রাক্কালে অবিভক্ত বাংলার দলিত নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গকে নিয়ে অখণ্ড বাংলার দাবির সমর্থক ছিলেন। অখণ্ড বাংলার দাবি মানে দেশভাগ হলে ভারতকে তিনটি খণ্ডে ভাগ করতে হবে- ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলা। অর্থাৎ ভারত উপমহাদেশ ভেঙে দুটি নয়, তিনটি স্বাধীন দেশ তৈরি হবে। তবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলা যে অদূর ভবিষ্যতেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে তা বিভিন্ন হিন্দু বাঙালি নেতারা ভাবতে শুরু করলেন। আজও অনেককে বলতে শুনি শ্যামাপ্রসাদ বাংলাকে দু-টুকরো না করলে গোটা বাংলাই পাকিস্তান হয়ে যেত। সেইসঙ্গে এটা বলে না খণ্ডিত পূর্ববঙ্গ (পূর্ব পাকিস্তান) ১৯৭১ সালে বাঙালিদের হাতেই ফিরে এলো। অখণ্ড বাংলা হয়তো হয়নি, কিন্তু বাঙালির দেশ বাংলাদেশ ভারতের পূর্বদিকে বিরাজমান। বাঙালির একমাত্র নিজের দেশ। যাই হোক, অখণ্ড বাংলা নাকি পাকিস্তান হয়ে যাবে সেই আশঙ্কা ছড়িয়ে বহু নেতা অখণ্ড বাংলার দাবি সমর্থন করেননি। হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি দাবি তুলেছেন যে, দেশভাগ হলে মুসলিম লিগ যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য সমগ্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানায় তা হতে দেওয়া যাবে না। কেননা, অখণ্ড বাংলায় তখনও ২৮ শতাংশ হিন্দু ছিল, যাঁদের জীবন ও ধর্ম প্রস্তাবিত পাকিস্তানে বিপন্ন হবে। শ্যামাপ্রসাদ দাবি তুলেছিলেন যে, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে বাংলার পশ্চিমাংশের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তখনকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং মেঘনাদ সাহা, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট জন শ্যামাপ্রসাদের দাবিকে সমর্থন জানালে বাংলা ভাগ করে পশ্চিম বাংলাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। ভারতের উপর দিয়ে ২,২০৪ কিলোমিটার অতিক্রম করে এসে অখণ্ড বাংলা যদি। পাকিস্তান হয়ে যেত, তাহলে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরও বহুদিন আগেই পাকিস্তান হয়ে যেত। তা তো হয়নি। কারণ সেটা ছিল অলীক কল্পনা।
বাংলার ভবিষ্যৎ কী হবে এই পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গের দলিত নমঃশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এক অদ্ভুত পদক্ষেপ নিলেন, যার ভয়াবহ ফল ভবিষ্যতে তিনি নিজে এবং তাঁর অনুগামী লক্ষ লক্ষ দলিত উদ্বাস্তু ভোগ করেছেন। দেশভাগের প্রাক্কালে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল প্রথমে অখণ্ড বাংলার দাবির পক্ষে থাকলেও শীঘ্রই তিনি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে মোহম্মদ আলি জিন্না ও মুসলিম লিগের হাত শক্ত করেন। গণভভাটের মাধ্যমে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রীহট্ট জেলার পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তিতেও তাঁর যথেষ্ট উদ্যোগ ছিল। লিগের হাত শক্ত করার পুরস্কারস্বরূপ দেশভাগের পর যোগেন মণ্ডল পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করেন। কিন্তু যোগেন মণ্ডল ও তাঁর অনুগামীরা পূর্ববঙ্গের দলিত নমঃশূদ্রদের বোঝান যে, উচ্চবর্ণ নয়, অনগ্রসর মুসলিমরাই অনগ্রসর দলিত হিন্দু নমঃশূদ্রদের ভাই। তাই দলিতদের দেশ ছাড়তে হবে না। তিনি আশ্বাস দেন যে, পূর্ববঙ্গে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে সহাবস্থানেই দলিতরা সুখে থাকবেন। আর যদি দলিত হিন্দুদের কখনও ভারতে চলে যেতেই হয়, তবে সবাইকে নিরাপদে ভারতে পাঠিয়ে তিনি যাবেন শেষ ট্রেনে।

[বাঁদিকে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ এবং ডানদিকে পাকিস্তানের আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল]
অবশ্য কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। দেশভাগের পরপরই সংখ্যাগুরু মুসলিমরা পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নির্যাতন চালায়। ফলে যোগেন মণ্ডলের নেতৃত্বের প্রতি একদা আস্থাশীল দলিত নমঃশূদ্র। সম্প্রদায় ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে দেশ ছেড়ে নিঃস্ব উদ্বাস্তু হয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পূর্ববঙ্গের যে মাটিতে তাঁদের জন্ম, সেই মাটি তাঁদের আশ্রয় দেয়নি, বিতাড়িত করেছে। সামাজিক অবহেলার চরম শিকার এই দলিত নমঃশূদ্র বাস্তুহারার দল মাতৃভূমি ছেড়ে প্রথমে আশ্রয় নিয়েছেন এপার বাংলার শিয়ালদহ-সহ বিভিন্ন রেলস্টেশনে, রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প, ধুবুলিয়া ক্যাম্পসহ অন্যান্য উদ্বাস্তু শিবিরে, আর খোলা আকাশের নীচে নানা জায়গায়। তাঁদের জীবনে দুর্দশার সীমা ছিল না।
এদেশে ব্রিটিশ শাসনকালে পূর্ববঙ্গের নমশূদ্ররা ছিল সেখানকার হিন্দু জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বড়ো অংশ। ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় তাঁদের আধিক্য ছিল। অশিক্ষা, অচিকিৎসা, দারিদ্র্য, রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতার অভাব ছিল তাঁদের নিত্যসঙ্গী। পূর্ববঙ্গের হিন্দু কৃষকদের মধ্যে ৯০ শতাংশই ছিল নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু ১৯৪৭ সালে দেশভাগ এই সম্প্রদায়কে ছারখার করে দেয়। দেশভাগের লগ্নে নমঃশূদ্রদের গুরুত্বপূর্ণ দুজন নেতা ছিলেন –একজন ছিলেন মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরু প্রমথরঞ্জন ঠাকুর (পি আর ঠাকুর বলেই বেশি পরিচিত মতুয়া সম্প্রদায়ের কাছে) এবং অন্যজন ছিলেন পাকিস্তানের প্রথম আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। দেশভাগের পর প্রমথরঞ্জনের পরিবার এপার বাংলায় চলে এলে তাঁর অনুগামী নমঃশূদ্রদের একাংশ এপারে চলে আসেন। অন্যদিকে যোগেন্দ্রনাথ তাঁর অনুগামী নমঃশূদ্রদের আশ্বস্ত করেন যে, ভারতে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, পূর্ববঙ্গে মুসলিমদের সঙ্গেই তাঁরা শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন। এভাবে দেশভাগ ঐক্যবদ্ধ নমঃশূদ্র সম্প্রদায়কে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।
যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আশ্বাসে যাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে থেকে গেলেন, সাম্প্রদায়িক কারণে তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন স্থানে সংখ্যাগুরুর আক্রমণে প্রচুর হিন্দু খুন হতে থাকে। এই সাম্প্রদায়িক গণহত্যা নিয়ে সমালোচনা শুরু হলে পাক সরকার তা বেমালুম অস্বীকার করে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তদন্ত করার ভার দেয় যোগেন্দ্রনাথের হাতেই। সেদিন যোগেন্দ্রনাথ তদন্তের রিপোর্ট দেন যে, যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গণহত্যার কথা বলা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, আইনমন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলেরই প্রাণসংশয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাঁর অনুগামী বিশাল সম্প্রদায়কে না-জানিয়েই পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ১৯৫০ সালে কলকাতায় আশ্রয় নেন। কলকাতা থেকেই ৮ অক্টোবর ১৯৫০ সালে তাঁর পদত্যাগপত্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রায় ৮০০০ শব্দে লেখা পৃথিবীর দীর্ঘতম এই পদত্যাগপত্রের ছত্রে ছত্রে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুদের উপর মুসলিম দাঙ্গা ও নির্যাতনের বিবরণ ফুটে উঠেছে। এখানে তিনি স্বীকার করেন যে, তদন্তের রিপোর্টে তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে হিন্দু গণহত্যার ঘটনা ধামাচাপা দেন। এই পত্রে তিনি নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন যে, মুসলিম লিগের পক্ষ নিয়ে কাজ করা তাঁর জীবনের কত বড়ো ভুল ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিন্দু নিধনের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান থেকে যোগেনবাবুর পালিয়ে আসা এবং পাক মন্ত্রীসভা থেকে তাঁর পদত্যাগ করা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। পাকিস্তানে এক হিন্দু ক্যাবিনেট মন্ত্রীর যদি এই অবস্থার শিকার হতে হয়, তবে দেশভাগের সময়কার পূর্ববঙ্গের ২৮ শতাংশ হিন্দুর কীরূপ দুর্দশা হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। (সুভাষ বিশ্বাস)।
এ কেমন স্বাধীনতা? ব্রিটিশদের চাকর বাকর হওয়ার স্বাধীনতা? সত্যকে চেপে দেশের মানুষের প্রতি মিথ্যাচারের স্বাধীনতা? প্রতারণার স্বাধীনতা? দেশ বেচে দেওয়ার চক্রান্তের স্বাধীনতা? অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট রাত ১২ টা বা ১৫ই আগস্ট রাত ১২টাতে ভারত স্বাধীন হয়নি। হয়েছিল ব্রিটিশ অধীনস্থ দেশ। যার রাজা ষষ্ঠ জর্জ। সর্বোচ্চ পদ গভর্নর জেনারেল ছিলেন ব্রিটিশ লর্ড মাউন্টব্যাটেন। প্রধানমন্ত্রিত্বটা শুধু দেশীয়। অর্থাৎ ৭৩ বছর ধরে দেশের মানুষকে মিথ্যাটাকে খাওয়ানো চলছেই। মিথ্যা আরও আছে। যেমন ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি মিথ্যাচার করে হিন্দি ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি খরচ করে চলেছে। সাংবিধানিকভাবে ভারতের কোনো রাষ্ট্রভাষাই নেই। আরও একটি মিথ্যাচার ভারতের জাতীয় ফুল হল পদ্ম। না, ভারতের কোনো জাতীয় ফুল নেই। থাকলে কোনো রাজনৈতিক দল দলের প্রতীক হিসাবে পদ্মফুলকে ব্যবহার করতে পারে না।
প্রসঙ্গত আর-একটু তথ্য জানাই, ভারত স্বাধীন কি না সে সিদ্ধান্ত নেবে ভারতবাসী, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নয়। যে কোনো বিচারে ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এক মহাভ্রান্তি। প্রথমে স্বাধীনতা দিবস পালন হত ২৬ জানুয়ারি, যে দিনটি ভারতীয়দের দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। ২৬ জানুয়ারির পরিবর্তে ১৫ আগস্ট উদযাপনের অর্থ ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা। কারণ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট যে ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল সেখানে ভারতকে ‘ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দেওয়া হয়েছিল, স্বাধীনতা নয়। ১৫ আগস্ট ভারতীয়দের জন্য কোনদিন স্মরণীয় হতে পারে না। মূলত এই দিনটিতে ভারতমাতার অঙ্গচ্ছেদন হয়েছিল আর লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম বিপন্ন হয়েছিল। সেদিন মানুষ আনন্দ করেনি, আনন্দ করতে পারেনি। সেদিন শুধু মানুষের বুকফাটা কান্না আর হাহাকার বাতাস ভারী করেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশহীন হয়ে পড়েছিল। তাই ২৬ জানুয়ারিকেই ‘স্বাধীনতা দিবস’ এবং ১৫ আগস্টকে ‘জাতীয় শোক দিবস’ হিসাবে পালন করা উচিত।
ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলেও, ভারতে যে এখন ফিরিঙ্গি শাসন করে না, এটাতে তো দ্বিমত থাকার কথা নয়। ব্রিটিশরা ভারতকে দেশীয় শাসকদের হাতে দিয়ে যাবে সেই পরিকল্পনা অনেক আগের। সেই। কারণেই ব্রিটিশ পতাকা সরিয়ে দিয়ে ভারতীয়দের নিজস্ব পতাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল ১৯১৬ সাল থেকেই।
১৯১৬ সালে অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশের মছলিপত্তনম শহরের নিকটস্থ ভাটলাপেনামারু গ্রামের বাসিন্দা পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়া একটি সাধারণ জাতীয় পতাকার রূপদানের চেষ্টা করেন। যদিও ভারতের বর্তমান পতাকাটির প্রকৃতি ডিজাইনার এক মুসলিম নারী সুরাইয়া বদরুদ্দিন তায়াবজি। পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার পতাকার মাঝে ছিল চরকা, সুরাইয়া বদরুদ্দিন তায়াবজি সংযোজন করলেন অশোকচক্র। চরকার পরিবর্তে সারনাথ স্তম্ভ থেকে। অশোকচক্রটি গৃহীত হয় পতাকায়। কেন তিনি অশোকচক্র সংযোজন করলেন তা জানা যায় না। তবে চরকার বদলে অশোকচক্রকে গ্রহণ করার ব্যাপারটি নেহরু স্বাগত জানান। তিনি পতাকায় চরকার বদলে ধর্মচক্র সংযোজনের বিষয়টিকে বাস্তবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ বলে মনে করেন। স্মতব্য, ধর্মচক্রটি বৌদ্ধধর্মের, যা বৌদ্ধসম্রাট অশোকের সৃষ্টি। কলকাতা থেকে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট যে জাতীয় পতাকার ডিজাইন ছিল। কমলা, হলুদ ও সবুজ ত্রিবর্ণের ছিল। সবুজ অংশে বামদিকে ছিল হিন্দু চিহ্ন সূর্য এবং ডানদিকে ছিল মুসলিম চিহ্ন চাঁদ-তারা। মাঝে হলুদ অংশে ছিল সংস্কৃত ভাষায় ‘বন্দেমাতরম’ লেখা। উপরে কমলা অংশে ছিল অষ্টবৃন্তের আটটি ফুল। গ্রহণ হয়নি। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী সংগঠন যুগান্তর সমিতি পার্টি কংগ্রেস একটি পতাকার প্রস্তাব করেছিলেন। পতাকাটি ছিল সম্পূর্ণ লাল রঙের, আর টকটকে লাল জমিতে তলোয়ার ও ত্রিশূল গুণিতক আকারে অবস্থান করছে। সেই গুণিতক আকারের উপরের ফাঁকা অংশে চাঁদ-তারা এবং নীচের অংশে একটি চক্র। বোঝাই যাচ্ছে এই পতাকার ডিজাইনে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত পতাকা হয়ে উঠেছিল। ঋষি অরবিন্দ ঘোষের ভাই বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও স্বামী বিবেকানন্দের ছোটো ভাই ভূপেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাবিত ছিল পতাকাটি। ১৯০৭ সালে ভিখাজি কামা কর্তৃক প্রথম উত্তোলিত পতাকায় ছিল সবুজ, হলুদ ও লাল ত্রিবর্ণ। সবুজ অংশে ছয়টি ফোঁটা পদ্মফুল। মাঝের হলুদ অংশে ছিল সংস্কৃত ভাষায় ‘বন্দেমাতরম’ লেখা। নীচে লাল অংশের বামদিকে মুসলিমদের চাঁদ এবং ডানদিকে হিন্দুদের সূর্য। ১৯১৭ সালে বাল গঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ত পরিচালিত হোমরুল আন্দোলন একটি নতুন পতাকার জন্ম দেয়। এই পতাকায় পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ আনুভূমিক ডোরা ছিল। উপরের বাঁদিকে আয়তাকার ইউনিয়ন পতাকা ছিল আন্দোলনের আকাক্ষিত ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভের প্রতীক। উপরের উড্ডয়নভাগে ছিল সাদা অর্ধচন্দ্র ও তারা। হিন্দুদের পবিত্র সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রতীকরূপে সাতটি সাদা তারা পতাকায় খচিত ছিল। এই পতাকাটি অবশ্য সর্বসাধারণ্যে জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯২১ সালে বেসরকারিভাবে গৃহীত হয় যে হয় যে পতাকাটি সেটিও ত্রিবর্ণের। তবে উপরে সাদা, মাঝে সবুজ এবং নীচে লাল। তিন অংশ জুড়ে আছে একটি চরকা, চরকার চাকাটি বামদিকে ঘোরানো। ১৯৩১ সালের পতাকাটিও ত্রিবর্ণের –উপরে গৈরিক, মাঝে সাদা, নীচে সবুজ। সাদা অংশে একটি চরকা, যাঁর চাকা ডানদিকে ঘোরানো। আজাদ হিন্দও একটি ত্রিবর্ণের পতাকা তৈরি করেছিল, যার উপরের অংশ গৈরিক, মাঝের অংশ সাদা এবং নীচের অংশ সবুজ। মাঝের সাদা অংশে একটি লক্ষমান বাঘ। মহাত্মা গান্ধির ইচ্ছানুসারেও একটি নতুন পতাকার নকশা করা হয়। সেই ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার উপরে ছিল সাদা, মধ্যে সবুজ ও নীচে নীল, যা যথাক্রমে সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায়, মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতীক। তিনটি ডোরা জুড়ে খচিত ছিল চরকার ছবি। আনুভূমিক তেরঙা ডোরা সংবলিত এই পতাকাটি আয়ারল্যান্ডের জাতীয় পতাকায় সমরূপ ছিল। উল্লেখ্য, আয়ারল্যান্ডের পতাকা আর-একটি প্রধান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী আন্দোলনের প্রতীক। জাতীয় কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে এটি উত্তোলিত হয়। যদিও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কখনোই এটিকে সরকারি পতাকা হিসাবে গ্রহণ করেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে এর ব্যাপক প্রয়োগও অন্যদিকে চোখে পড়ে না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রেড এনসাইন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিরূপে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ১৯৪৫-৪৭ সময়পর্বে জাতিসংঘে এই পতাকাটিই ভারতের পতাকা হিসাবে ব্যবহৃত হত।
বর্তমান ভারতের জাতীয় পতাকায় গেরুয়া রং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। মধ্যস্থলে সাদা রং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বভাবের পথপ্রদর্শক সত্যপথ আলোর প্রতীক। সবুজ রং মৃত্তিকা তথা সকল প্রাণের প্রাণ উদ্ভিজ্জ জগতের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্বন্ধটি ব্যক্ত করছে। সাদা অংশের কেন্দ্রস্থলে অশোকচক্র ধর্ম অনুশাসনের প্রতীক। মনে রাখতে হবে এই ধর্মীয় অনুশাসনটি বৌদ্ধধর্মের। সত্য ও ধর্ম এই পতাকাতলেই কর্মরত সকলের নিয়ন্ত্রণনীতি। এছাড়া চক্রটি গতিরও প্রতীক। স্থবিরতায় আসে মৃত্যু। জীবন গতিরই মধ্যে। অপ্রাসঙ্গিকভাবে কেন আমি ভারতের পতাকার বিবর্তন নিয়ে লিখলাম? লিখলাম এই কারণে যে, এই বিবর্তনেই লক্ষ করা যাচ্ছে ধর্ম নিয়ে পিং পং খেলা। ভারত যেহেতু বহু ধর্মের দেশ, তাই কে থাকবে কে থাকবে না তারই একটা ঠান্ডা লড়াই পরিলক্ষিত হয় পতাকায়। শেষ পর্যন্ত রয়ে যায় নিরীহ বৌদ্ধধর্ম। না রইল হিন্দু, না রইল মুসলিম, রইল শিখ। এমন একটা ধর্মের উপস্থিতি রাখা হল, যে ধর্ম ভারতের জমিতে মাইক্রোস্কোপে দেখতে হয়। বৌদ্ধ অধ্যুষিত চট্টগ্রাম ততক্ষণে পাকিস্তানে চালান করে দেওয়া হয়ে গেছে।
ভারতের জাতীয় প্রতীকটি বৌদ্ধধর্ম থেকে চয়ন করা হয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসেবে অশোকের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষের মুদ্রণরূপ গৃহীত হয়। জাতীয় প্রতাঁকে গৃহীত রূপটিতে চতুর্থ সিংহটি দেখা যায় না, কারণ স্তম্ভশীর্ষে এটি পিছনে অবস্থিত ও সামনে থেকে দৃষ্টিগোচরে আসে না। সিংহের পায়ের তলায় যে ভিত্তিভূমির কেন্দ্রে ধর্মচক্র, ডানদিকে ষাঁড় ও বাঁদিকে লক্ষমান ঘোড়া দেখা যায়। বাঁয়ে ও ডানে একদম ধারে ধর্মচক্রের দুটি ধার দেখা যায়। জাতীয় প্রতাঁকের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল দেবনাগরী হরফে খোদিত ‘সত্যমেব জয়তে’ নীতিবাক্যটি, যা মূল স্তম্ভশীর্ষে দেখা যায় না। অশোকের সিংহচতুর্মুখ স্তম্ভশীর্ষ একটি ভাস্কর্য যেখানে চারটি এশীয় সিংহ পরস্পরের দিকে পিঠ করে চারদিকে মুখ করে বসে রয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে এই ভাস্কর্যর রৈখিক প্রতিরূপ ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আনুমানিক ২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট অশোকের শাসনকালে সারনাথ নামক স্থানে একটি অশোক স্তম্ভের শীর্ষে এই ভাস্কর্যটি স্থাপন করা হয়। যে রাষ্ট্রটি ‘হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে বদ্ধপরিকর, যে রাষ্ট্রটি ৫০০০ হাজার বছরের প্রাচীন হিন্দুদের দেশ, যে রাষ্ট্রে হিন্দু ছাড়া কারোরই থাকার অধিকার নেই, যে রাষ্ট্রে কেবলমাত্র হিন্দুরাই রামজাদা বাকিরা হারামজাদা’ –সেই রাষ্ট্রে হিন্দুদের কোনো প্রতীক পাওয়া গেল না! যে হিন্দুত্ববাদীরা বাবরি মসজিদের নীচে ৫০০ বছর আগের রামমন্দির খুঁজে পেলেন, অথচ দেশের জন্য হিন্দু প্রতীক খুঁজে পেলেন না। হিন্দুত্ববাদীরা কি জানতেন না সম্রাট অশোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন? তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী নন? অবশ্যই জানতেন।

আপনি যা লিখেছেন তার বেশির ভাগ মনগড়া । কোথা থেকে তথ্য পেলেন তা লেখেন নি।।।