২০০১ : আ স্পেস ওডিসি – আর্থার সি ক্লার্ক
ভাষান্তর : মাকসুদুজ্জামান খান
[ষাটের দশকে ব্যতিক্রমী চিত্র পরিচালক স্ট্যানলি কুবরিক হঠাৎ ভাবলেন, প্রকৃত সায়েন্স ফিকশন চাই। সর্বব্যাপী, সর্বদৃষ্টির এক সায়েন্স ফিকশন বানাতে চাইলেন যাতে বিজ্ঞান আসবে পুরোপুরি যুক্তির কাঁধে ভর করে। স্নায়ুক্ষয়ী কাহিনী আসবে বিজ্ঞানের সাথে পায়ে পা মিলিয়ে। স্যাটেলাইটের জনক, মহাকাশ অভিযানের ধারাভাষ্যকার কল্পবিজ্ঞানী আর্থার সি ক্লার্ক তাঁকে যে কাহিনী দিলেন তা দিয়ে সৃষ্টি হল ‘২০০১: আ স্পেস ওডিসি’।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র। কিন্তু ক্লার্কের মনে হল, কাহিনী পূর্ণ হয়নি। তিনি একই নামে আরো পরিস্কার করে গুছিয়ে লিখলেন এই উপন্যাস। উনিশশ আটষট্টিতে। মহাকাশ অভিযান নিয়ে সারা পৃথিবীর সব সায়েন্স ফিকশনের আদর্শ।
এল অনেক তত্ত্ব। তারপর এর প্রভাব যে কোথায় পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর প্রতিটি মহাকাশ অভিযানের সায়েন্স ফিকশনে সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ক্লার্কের মহাকাশ মহাকাব্য। ইসরায়েল তার মানবীয় কম্পিউটারের নাম দেয় তার দেয়া ‘হাল’ নামানুসারে, আমেরিকার নাসা আজো ‘ওডিসি’ নামে মিশন চালায়! ‘ওডিসি’ অনুবাদ হয় আটত্রিশটি ভাষায়, এ সিরিজের শেষ বইয়ের জন্য ক্লার্ক পান সায়েন্স ফিকশনে রেকর্ড সম্মানী। চল্লিশ বছরে ক্লার্ক আরো চারটি উপন্যাস লিখলেন। সৃষ্টি হল পৃথিবীর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন সিরিজ। মহাকাশ অভিযানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য।
ত্রিশ লাখ বছর আগে প্রাচীন ক্ষুধা-তৃষ্ণার জান্তবতা থেকে বন মানুষের দল চলা শুরু করে, শুরু হয় ওডিসি, এর শেষ দু হাজার এক সালে, পৃথিবী থেকে বিশ হাজার আলোক বর্ষ দূরের এক বিশাল, দানবাকার নক্ষত্রের গর্ভে। এ ক্লাসিক উপন্যাস না পড়লে যে কোনো বিজ্ঞান সচেতন পাঠকের সায়েন্স ফিকশনের স্বাদ অপূর্ণ থেকে যাবে। আর্থার সি. ক্লার্ক ১৯ মার্চ ২০০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন।]
.
অনুবাদক মাকসুদুজ্জামান খান বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ালেখা করছেন। তিনি আর্থার সি ক্লার্ক ও আইজাক আসিমভের বেশ কিছু লেখা ভাষান্তর করেছেন।
.
বর্তমান পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সায়েন্স ফিকশন লেখক আর্থার চালর্স ক্লার্ক। তিনিই স্যাটেলাইট বিজ্ঞানের জনক। ক্লার্কের অমর কীর্তি ‘২০০১ আ স্পেস ওডিসি’র কথা সায়েন্স ফিকশন পাঠকদের বলাটা এক ধরনের বাহুল্য। সেই চিরায়ত গ্রন্থের অমীমাংসিত রহস্য-পর্দা উন্মোচিত হয়েছে ‘২০১০ ওডিসি টু’তে কিন্তু সেটা শুধুই আগের পর্বের মানুষের শেষ পরিণতি নিয়ে টানা হেঁচড়া নয়। বরং এ খন্ডে তিনি সম্পূর্ণ নতুন, অনন্যসাধারণ আরো একটি পরিণতি রেখেছেন। এটা ২০০১ এর নক্ষত্র শিশুর চেয়ে কোনো অংশে কম ধাক্কা দেয় না পাঠকের মনে।
২০০০ সালের দিকে বিজ্ঞান প্রবেশ করে মহাকাশ যুগে। মানুষ প্রথমবারের মতো পৃথিবীর বাইরে ঘাটি করে। চাঁদের দেশে। আমেরিকান ঘাঁটির নাম ক্ল্যাভিয়াস বেস। সেখানে এক এলাকায় চুম্বক রেখা বারবার এলোমেলো হয়ে যায়।
বিজ্ঞানীরা চল্লিশ ফুট পাথুরে জমির নিচে খুঁড়ে বের করে কালো একটা বস্তু। ত্রিশ লাখ বছরের পুরনো। যত অনুবীক্ষণিক যন্ত্র দিয়েই দেখা হোক, দেখতে একই রকম। সূর্য ওঠার সাথে সাথে সেটা থেকে একটি রেডিও তরঙ্গ ভেসে যায় সৌর জগতের প্রান্তসীমায়। যেন চিৎকার করে বলছে, মানুষ যোগ্য হয়েছে, সে পৃথিবী থেকে চাদে এসে আমাকে খুঁড়ে বের করে আমার গায়ে সূর্যের আলো ফেলেছে… বৃহস্পতি-শনির দিকে পাঠানো হল ডিসকভারি স্পেসশিপ, সাথে মানবীয় কম্পিউটার-হাল। তারপরের সবটুকুই ইতিহাস। অবাক করা ইতিহাস।
ডিসকভারির অধিনায়ক ডেভিড বোম্যান এক অপার্থিব সত্যের মুখোমুখি হয়… এমন কালো বস্তু পৃথিবীতেও ছিল লক্ষ বছর আগে…দু দল বানর পানি নিয়ে ঝগড়া করে ফেরার সময় এর সামনে দাঁড়াত, দেখত ছুঁয়ে… আরাধ্য সত্যের সন্ধান পায় ডেভ বোম্যান। কিন্তু মানুষ তা জানতে পারে না।
মানুষ হারও মানে না। মানতে জানে না। তাই ২০১০ সালে তারা ডিসকভারির সেই ব্যর্থতার কথা মনে রেখেও লিওনভকে প্রস্তুত করার সাহস পায়। কিন্তু এবারের পরিণতিটা অন্যরকম।
.
পঁয়ত্রিশটি ভাষায় অনূদিত মহাকাশ উপন্যাস ওডিসি সিরিজ
২০০১: আ স্পেস ওডিসি
আর্থার সি ক্লাক
অনুবাদ : মাকসুদুজ্জামান খান
.
2001
A SPACE ODYSSEY
ARTHUR C. CLARKE
.
উৎসর্গ
সাত বছরের বন্ধুত্ব শেষে নাফিস আমাকে বলেছিল,
‘দোস, বন্ধু বললে মানুষ আমাদের বন্ধুত্বটা ঠিক বোঝে না।
এখন থেকে আমরা কাজিন।
কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ্য করি,
ভাই হিসেবে পরিচয় দিয়েও গভীরতাটা বোঝানো দুষ্কর
আহমেদ নাফিস শাহরিয়ারকে
.
যঅনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তার পাঠানো চিঠিতে
২২ আগস্ট, ১৯৯৪
প্রিয় আর্থার,
সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।
প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।
অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।
.
কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?
আপনার,
স্ট্যানলি
.
এই ক’দিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।
আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।
আর্থার সি ক্লার্ক
১৬-০৪-১৯৯৯
.
স্ট্যানলির স্মৃতির প্রতি
সামনের ভূমিকাটা লেখার মাত্র সপ্তাহদুয়েক পরেই নিথর করে দেয়া অপ্রত্যাশিত এক খবর পেলাম। স্ট্যানলি কুবরিক সত্তর বছর বয়েসে মারা গেছেন। দু-হাজার এক সালে আমাদের চলচ্চিত্রটার এক নতুন রূপ মুক্তি দেয়ার ইচ্ছা ছিল তাঁর; তার সাথে অংশীদারিত্বের দিন ফুরিয়ে যাওয়াতে আমার অন্তরের অন্তস্থল সত্যি সত্যি ব্যথায় ভরে উঠছে।
২০০১ শেষ করার পর তিন দশকে আমাদের খুব কমই দেখা হয়েছিল। কিন্তু বন্ধুত্ব ছিল অটুট। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় বি বি সি-র দিস ইজ ইউর লাইফ অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতির সময় তাঁর পাঠানো চিঠিতে:
২২ আগস্ট, ১৯৯৪
প্রিয় আর্থার,
সরি, ফিল্মের কাজের চাপ আমাকে আপনার এই বিশেষ সম্মান পাওয়া দেখা থেকে বঞ্চিত করল। নয়তো আজ রাতে আমি অবশ্যই এখানে থাকতাম।
প্রত্যাশা অনুযায়ী আপনিই পৃথিবীর সবচে পরিচিত সায়েন্স ফিকশন লেখক। আপনি এক মানুষ হয়ে আমাদের ধুলোর পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের জগতে নিয়ে যাবার পথে যে কাজ করেছেন তা আর। কোনো একক ব্যক্তিত্ব করতে পারেনি। এমন এক সময়ে নিয়ে যাবার কাজ করছেন যেখানে অচেনা বুদ্ধিমত্তার কাছে মানুষ হবে ঈশ্বর পিতা, বা গডফাদার।
অন্যক্ষেত্রে, যখন এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, ইউনিভার্সের অসীম পথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে অনন্তকাল ধরে, তখন তাদের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়বে, পড়বেই। তারাও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করবে তার প্রতি যিনি তাদের অস্তিত্বের সবচে বড় এবং দূরদর্শী সমর্থক।
কিন্তু কে জানে, আগামীদিনের মানুষ আপনার সেই প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাবে কিনাঃ পৃথিবীতে আদৌ বুদ্ধিমত্তা আছে তো?
আপনার,
স্ট্যানলি
.
এই কদিন আগেও আমি স্বপ্ন দেখছিলাম তাকে নিয়ে। যেমন ছিলেন ১৯৬৪ সনে, তেমনি। প্রশ্ন করলেন, ‘যাক, এখন কী করণীয়?’ তো, যদি এরপর বলে আসলেই কিছু থেকে থাকে, সেখানে ব্রায়ান এ্যলডিসের চমৎকার ছোটগল্প ‘সুপারটয় সারা গ্রীষ্ম জুড়ে ভাল রয়’ অনুসরণে তিনি ‘এ আই’ নামে যে ছায়াছবিটা গড়তে চান এবং নানা ঝুট-ঝামেলায় কুলিয়ে উঠতে পারেননি সেসব কথা মনে পড়ে।
আমার এক জীবনে সবচে গভীর দুঃখের মধ্যে একটা, ২০০১ সাল একদিন আসবে, সেদিন আমার পাশে মহান চলচ্চিত্রকার স্ট্যানলি কুবরিক থাকবেন না।
আর্থার সি ক্লার্ক
১৬-০৪-১৯৯৯
.
সহস্রাব্দ সংস্করণের কথা
আজ পঁয়ত্রিশ বছর হল, একদিন স্ট্যানলি কুবরিক তার সেই ‘ভালো সায়েন্স ফিকশন চলচ্চিত্র’ খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। আসল সত্যি বলতে গেলে, বর্তমানের চোখে ১৯৬৪ সালটা যেন অন্য যুগের অধীনে বাস করে। সেই তখন, মাত্র হাতেগোনা দু-চারজন নভোচর মহাকাশে ঢু মেরেছে এবং মহিলাদের আরো দৈন্যদশা, মাত্র একজন। তখন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘোষণা করলেন, দশক পেরুনোর আগেই মানুষ চাঁদের বুকে পা রাখবে। এখন আমি বাজি ধরতে পারি, খুব বেশি লোক সে কথা বিশ্বাস করেনি সেদিন।
আরো হতাশ করা ব্যাপার হল, মহাকাশে আমাদের চিরসাথী, সবচে কাছের আত্মীয়ের ব্যাপারে আক্ষরিক অর্থে কোনো প্রামাণ্য ধারণা ছিল না আমাদের মনে। এমনকি চাঁদের বুকে প্রথম ভোব নামার সময় কোনো ধুলার সাগরে যে ডুবে যাবে না তাও নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারেনি।
ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য উনিশশো একাত্তরে, যখন আমার মাথা কিছুটা পরিষ্কার ছিল তখন লেখা নন-ফিকশন (আংশিক) টার কথা মনে করিয়ে দিতে দিন। দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অফ ২০০১-এ লিখেছিলাম:
চৌষট্টির বসন্তে… চান্দ্র অবতরণ মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দূরের স্বপ্ন ছিল। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আমরা জানতাম, এ অপ্রতিরোধ্য। আর আবেগের দিক দিয়ে ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি… গ্রিসাম আর ইয়ংয়ের দ্বি-মানব যান আরো এক বছর পরও হালে পানি পায়নি। তখনো চাঁদের বুকের গঠন নিয়ে যুক্তি-পাল্টা যুক্তির ঝড় বইছে… যদিও নাসা আমাদের পুরো ছায়াছবির বাজেট (কোটি ডলারের উপরে) প্রতিদিন খরচ করছে, দেখেশুনে স্পেস অভিযানকে পাহাড় ডিঙানোর চেয়ে লাখ গুণ কঠিন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমার বিশ্বাস ছিল স্থির, মানুষ চাঁদের বুকে হাঁটাহাঁটি করার সময়ও এই ছায়াছবিটা সমান জনপ্রিয়তা রাখবে।
সুতরাং, আমাদের কাহিনীটা লিখতে অনেক ঘাম ঝরাতে হল। এমন কিছু লিখতে হবে যেটা বাস্তবের নির্যাসে সিক্ত থাকবে না শুধু, বরং তাই হবে বাস্তব। আবার সেই বাস্তবটা পরের ক’বছরের মধ্যে হলে চলবে না।
আমাদের প্রথম টাইটেলটা ছিল: কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হল। কিন্তু স্ট্যানলি সোজা কথায় একটা অভিযানের বাইরের রূপ বলে দিতে চাননি। তাছাড়া তিনি আমাকে সারাক্ষণ যে কথাটা বলে মজা পেতেন, তা হল, ‘আমি পৌরাণিকতার ঘ্রাণ নিতে ভালবাসি…’
কিন্তু, আজ ২০০১ এই একটু সামনে। হয়তো সে কারণেই ছায়াছবিটা সাধারণ্যে এক সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। আমার বড় সন্দেহ হয়, তার সবচে বড় স্বপ্নগুলোতেও স্ট্যানলি কখনো কি ভেবেছিলেন যে একটা সুপার বল খেলার ঘোষক যখন ত্যালত্যালে কণ্ঠে বলবে, ‘ইট ওয়াজ এ বাগ, ডেভ। তখন টিভির সামনে বসা দশ কোটি আমেরিকানই সাথে সাথে চিনতে পারবে ঠিক কে (বা কোন জিনিসটা…) কাকে কখন এ কথাটা বলেছিল।
আরো একটা ব্যাপার, আই বি এম তার এক মেশিনের নামকরণ যখন সেই পুরনো হাল এর সাথে মিলিয়ে রাখে তখনো স্মৃতিতে ভারাক্রান্ত হতে হয়। যোড়শ অধ্যায়ে পুরো নামটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।
যদি পুরো ব্যাপারটা স্পষ্ট দেখতে চান তো আপনাদের সেই চমৎকার ভয়েজার ক্রাইটেরিয়ন ডিস্ক দেখার কথা বলব। পুরো মুভিটাতো আছেই, সেই সাথে তৈরির সময়ের ব্যাপারগুলোও দেয়া আছে সেখানে। ছবি শু্যট করার সময়ে বাড়তি দৃশ্য সহ বিজ্ঞানী, শিল্পী, টেকনিশিয়ানদের সাক্ষাৎকারও আছে। সেখানে একজন মোটামুটি তরুণ আর্থার সি ক্লার্কের সাক্ষাৎকারের দৃশ্যও আছে। চাঁদের সেই কনফারেন্স রুমে নেয়া হয়, চারপাশে মুভিতে ব্যবহার করা এমন সব জিনিস ছিল কিছুদিন পরেই যেগুলো চাঁদের বুকে বিশ্রাম করার সুযোগ পায়। ব্যাপারটা শেষ হয় আরো বিরক্তিকর কিছু দৃশ্য দিয়ে। পরবর্তীকালে আসা অ্যাপোলো, স্কাইল্যাব সহ অন্যান্য শাটলের সাথে স্ট্যানলির স্বপ্নের কাজের মিল দেখানো হয় পাশাপাশি তুলনা করে।
আমার কাছে ব্যাপারটা তেমন অবাক করা নয়, চলচ্চিত্রের সাথে বইটির মিল নেই, এ দুয়ের সাথে বাস্তবতার তেমন মিল নেই এবং বাস্তবতার সাথে পাল্লা দিয়ে আরো হাজারটা চলচ্চিত্র, ডকুমেন্টারি তৈরি হচ্ছে। তাই আমি একেবারে শুরুতে ফিরে গিয়ে পুরো ব্যাপারটা কোত্থেকে শুরু হল তা আরেকবার মনে করতে চাই।
১৯৬৪’র এপ্রিলে আমি সিলন ছেড়ে গেলাম। সেকালে এ নামেই ডাকা হত জায়গাটাকে। তারপর নিউইয়র্কে সময় ও জীবদ্দশা নিয়ে লেখা ম্যান এন্ড স্পেস বইটার এডিটিং শেষ করার কাজে ঝুঁকেছিলাম। সেখানকার একটা কথা তুলে দেয়ার লোভ সামলে উঠতে পারছি না।
.
সিলনের ভূ-স্বর্গে বেশ ক’বছর কাটানোর পর আবার নিউইয়র্কে ফিরে আসাটা কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। আই আর টি’র মাত্র তিনটা স্টেশনে ঘুরে বেড়ানোও আমার জন্য মহা ব্যতিক্রম এবং ভালো একটা রিল্যাক্স। বিশেষত দিনগুলো যেখানে কাটত হাতির দলে, প্রবাল রিফে, নানা রঙের মৌসুমে ঘুরে বেরিয়ে ডুবে যাওয়া পুরনো দিনের জাহাজের সাঁতার কেটে হরদম দিন কেটে যেত। অন্যদিকে আজব চিৎকার, হাস্যোজ্জ্বল হাজার মুখ, রহস্যময় সম্পর্কের পথে ম্যানহাটানীয়দের একেবারে নিপাট ভদ্র ব্যবহার বিমোহিত করে মুগ্ধতার অন্য অংশকে; তেমি অবাক করে কোমল হুইসেল বাজাতে বাজাতে দিক-চিহ্নহীন সাবওয়ে স্টেশনে ছুটে চলা বজ্রগতির রেলগাড়িগুলোে, বাহারি বিজ্ঞাপন (কোনো কোনোটা আবার অপেশাদার আর্টিস্ট গুবলেট করে ফেলেছে, সেই কাঁচা হাতের কাজও মানিয়ে যাচ্ছে কেমন করে যেন) অযুত রঙে ঝকমক করছে কতশত ব্র্যান্ডের নাম নিয়ে-দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট, লেভি’স ব্রেড, পাইল’স বিয়ার, আর মুখের ক্যান্সার উৎপাদনে মহা কার্যকর ডজনখানেক ব্র্যান্ডের কামড়া-কামড়ি। মজার ব্যাপার হল, একটা ব্যাপারে অভ্যস্ত হতে আপনার মিনিট পনের সময় লাগবে, ব্যস। এবং একই সময়ে সেটা মিলিয়ে যাবে মন-মগজ থেকে। (রিপোর্ট অন প্ল্যানেট থ্রি থেকে ‘সন অব ড. স্ট্রেঞ্জলাভ’)
.
ম্যান এন্ড স্পেসের উপর আমার কাজ ভালোভাবে এগুনোর সময়টায় সময় আর জীবন নিয়ে কাজের প্রতি ঈর্ষান্বিত এক সমালোচক বলেছিলেন, ‘এই জবানি দেয়ার অধিকার আপনার আছে? কোথায় সেটা?’
আমি মহিলার দিকে সর্বস্ব ভস্ম করে দেয়া একটা দৃষ্টি হেনে বললাম, ‘আপনি তার দিকেই চেয়ে আছেন।’
সুতরাং, স্ট্যানলির সাথে জোছনা উপভোগ করার মতো সময় আমার হাতে ছিল এবং বেশ ভালোভাবেই ছিল। তাঁর সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ট্রেডার ভিক-এ। (তাদের উচিত জায়গাটাকে চিহ্নিত করে রাখা) স্ট্যানলি তখনো তার শেষ ছবি ড, স্ট্রেঞ্জলাভ নিয়ে সোয়াস্তির জাবর কাটছেন এবং আরো উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রজেক্টের ধারণা পাবার অপেক্ষায় দিন গুনছেন। তার লক্ষ্য আরো বড়, ইউনিভার্সে মানুষের অবস্থান নিয়ে কিছু একটা করে দেখানোর ইচ্ছা তাঁর। এমন কিছু করা যার ফলে পুরনো বা নতুন স্কুল শিক্ষকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।
স্ট্যানলি এমন এক লোক, যিনি যে কোনো বিষয় মাথায় আসার সাথে সাথে সেটাতেই একেবারে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠতেন। সকল কাজের মহাকাজি। ততদিনে বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান বিষয়ক বেশ কয়েকটা লাইব্রেরি তিনি হজম করে বসে আছেন। এর মধ্যেই একটা সম্পদের স্বত্ব কজা করে নিয়েছেন যেটাকে বলা হয় ‘শ্যাডো অন দ্য সান। আমার মনে পড়ে, তিনি লেখাটা নিয়ে কিছু বলতে পারেননি এমনকি এর লেখকের নামও আমি জানতাম না। সম্ভবত লোকটা সায়েন্স ফিকশনে নবাগত। কিন্তু বেচারার ক্যারিয়ারের গুড়ে আমি বালি ছড়িয়ে দিলাম। কুবরিকেরও কানে কথাটা এসেছিল, ক্লার্ক অন্যের আইডিয়া ডেভলপে তেমন আগ্রহী নয়। (রামা টুর শেষদিকটা দেখুন, কদশক পরে ক্রেডলের সাথে একটা যোগসূত্র বের করা যায়। তারপর, ফয়সালা হল, আমরা একেবারে নতুন কিছু তুলে আনব।
এখন, মুভি গড়ার আগে স্ক্রিপ্ট চাই, স্ক্রিপ্ট পাবার আগে চাই একটা গল্প। যদিও কালস্রষ্টা কিছু পরিচালক শেষের দু বিষয়কে পুরো উড়িয়ে দেয়ার অনেক চেষ্টা করেছেন, তবু তাদের ছায়াছবি খুঁজে পেতে হলে আপনাকে আর্ট থিয়েটার চষে বেড়াতে হবে। হাতে সময় নেই। আমি স্ট্যানলির হাতে আমার ছোট লেখাগুলোর একটা ফর্দ ধরিয়ে দিলাম, তার মধ্যে ‘দ্য সেন্টিনেল’কে আমাদের দুজনেরই বেশ মনে ধরল; এর উপর একটা ভিত্তি দাঁড় করানো যায়।
উনিশশো আটচল্লিশের ক্রিসমাসে শক্তি বিস্ফোরণের মতো গল্পটা লেখা হয়, বিবিসি ছোটগল্প প্রতিযোগিতার জন্য। গল্পটা মেধা তালিকায় উঠে আসেনি। আমার সারাক্ষণ ভাবনা ছিল, কোনো গল্প উঠল! যাই হোক, আমার গল্পটা পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ জায়গা পায়। আমার ভাবনা ছিল, চাঁদে একটা ট্রিগার পুঁতে রাখা হবে মানব জাতির উত্থানের সংকেত পাঠানোর জন্য।
অনেকে বলে বেড়ায় ২০০১ আসলে দ্য সেন্টিনেলের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এ দুয়ের মিল ততটুকুই যতটুকু মিল আছে ওক গাছের কাণ্ড আর ফলের মধ্যে। মুভিটা বানাতে আরো হাজারটা কাঁচামাল প্রয়োজন, দরকার সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণ। ‘ভোরের প্রথম মোকাবিলা’ থেকেও আরো কিছু তথ্য এল। এটাও পরে অ্যাক্সপেডিশন টু আর্থ-এ যুক্ত হয়। সময় কম। সব চেঁছে ফেলে নতুন করে লেখার মতো পরিস্থিতি হাতে নেই। লেখাটা একটা মাত্র পর্যায়, তারপর আরো এমন ডজনখানেক পর্যায় পেরিয়ে মুভির কারবার শেষ করতে হবে। তাই আরো অন্য চারটা ছোটগল্প থেকে কিছু কিছু অংশ নিতে হয় আমাদের। কিন্তু চলচ্চিত্রটার এই ছ’ অংশ ছাড়া বাকী সব এক্কেবারে নতুন। আমি, স্ট্যানলির সাথে মাথা ঘামাঘামি করে নির্ভেজাল লোনলি সময় কাটিয়েছি মাসের পর মাস, পশ্চিম ২৩ তম স্ট্রিটের ২২২ নম্বরের বিখ্যাত হোটেল চেলসিয়াতে, রুম নাম্বার ১০০৮-এ।
বেশিরভাগ উপন্যাস লিখেছিলাম এখানে। এখানেই ব্যথাভরা ‘দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১’ লিখতে হয়। কেন উপন্যাস লেখা, যেখানে তৈরি করতে চাচ্ছি একটা চলচ্চিত্র! প্রশ্ন করতে পারেন আপনারা। কথাটা সত্যি, নভেলাইজেশন (আহা!) পরে হওয়ার একটা রীতি চালু আছে বেশ জোরদার পন্থায়। স্ট্যানলি ঘড়ির কাঁটা উল্টে দিতে চাইলেন, ব্যস।
কারণ, স্ক্রিনপ্লে’র ঝক্কি জগদ্বিখ্যাত। এত বেশি ডিটেইল হতে হয় যে এটা পড়তে ততটাই খাটনি যতটা হয় লিখতে। জন ফাউলস কথাটা বেশ সুন্দর বলেছিলেন, ‘উপন্যাস লেখা হল অকূল পাথারে সাঁতার দেয়া। আর স্ক্রিনপ্লে? চিত্রনাট্য লিখতে যাওয়া সুগার রিফাইনারির তরল চিনিতে দ্রুত এগুতে চাওয়ার নামান্তর।’
একঘেঁয়েমিতে আমার এলার্জির ব্যাপারটা ধরতে পেরে স্ট্যানলি তাই হয়তো প্রথমে একটা উপন্যাস গড়তে চাইলেন। এর উপর ভিত্তি করেই সাথে সাথে একটা সুন্দর পাণ্ডুলিপি তুলে আনা যাবে। সেই সাথে কিছু পয়সা।)
এবং শেষকালে স্ক্রিনপ্লে আর নভেল একই সাথে সমাপ্তির পথে এগোয়, একই সাথে দ্বিমুখী চাপে পড়ে। তারপর আমি ছবিটা দেখলাম, যেটা খুব কম লেখকই উপভোগ করেছে। (আমার মনে হয় এনজয়’ কথাটা বলা ঠিক হল না।) আর শেষে বদলে দিলাম কয়েকটা চ্যাপ্টার।
সকালে তাড়াহুড়ো করে যে কটা ঘটনার নাম লিখেছি তা থেকে আমাদের নাকে-মুখে খাওয়ার একটু নমুনা পাওয়া যেতে পারে।
.
মে আটাশ, উনিশশো চৌষট্টি, আমি স্ট্যানলিকে বললাম, ‘তারা মেশিন হলেই ভালো, যারা জীবদেহের গঠন নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করবে আমাদের মুভিটাতে। স্ট্যানলি গররাজি, নিমরাজি, পুরো রাজি….
জুন, দুই, গড়ে দৈনিক এক বা দু-হাজার শব্দ লিখছি। স্ট্যানলি বলছেন, আমরা এখানে একটা বেস্ট সেলার পেতে যাচ্ছি অচিরেই।
জুলাই, এগারো, প্লট নিয়ে আলাপ করতে গিয়ে সারাক্ষণ ‘ক্যান্টর’স ট্রান্সফিনিট গ্রুপ নিয়ে বিতণ্ডায় মেতে থাকতে হল। আমি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে সে একজন গণিত-জিনিয়াস।
জুলাই, বারো। সব আছে, শুধু প্লটটা নেই।
জুলাই, ছাব্বিশ। স্ট্যানলির ছত্রিশতম জন্মদিন। তারপর গ্রামে গিয়ে একটা কার্ড পেলাম, লেখা, তুমি কী করে একটা জন্মদিন পালন কর যেখানে যে কোনো মুহূর্তে দুনিয়াটা ফেটে যেতে পারে!’ ( ১৯৯৯ এর আপডেট: আশা করি সেসব কার্ড আরো পাব, প্রচুর পরিমাণে।)
সেপ্টেম্বর, আটাশ। স্বপ্ন দেখলাম, আমি যেন এক রোবট। বারবার বানানো হচ্ছে আমাকে। স্ট্যানলির কাছে আরো দু-অধ্যায় নিয়ে গেলাম, সাথে লেখা, ‘জো লেভিন এ কাজ তার লেখকদের জন্য করে না।’
অক্টোবর, সতের। স্ট্যানলি এমন একটা উপায় পেলেন যাতে এমন একটা রোবট বানানো সম্ভব হবে যেটা আমাদের হিরোদের ভিক্টোরিয়ান সাহিত্যের মতো মহানায়কে পরিণত হবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।
নভেম্বর আটাশ, আইজাক আসিমভকে ফোন করলাম। নিরামিষাশীর আমিষভোজীতে পরিণত হতে কী বায়োকেমিস্ট্রি দরকার তা জানতে।
ডিসেম্বর, দশ। স্ট্যানলি এইচ জি ওয়েলসের থিস টু কাম দেখে আমাকে বললেন যে তিনি জীবনে আর যাই করেন না কেন, আমার উপদেশানুযায়ী কোনো চলচ্চিত্র বানাবেন না।
ডিসেম্বর, চব্বিশ। ধীরলয়ে পাতা উল্টে যাচ্ছি, যাতে স্ট্যানলিকে একটা ক্রিসমাস উপহার হিসেবে দেয়া যায়।
.
এটুকু দেখে মনে হতে পারে আমাদের কাজের সমুদ্র শেষ হয়েছে। কিন্তু না। বিধি বাম। আসলে বইটার দু’তৃতীয়াংশ গেল মাত্র। কারণ, আমাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই এরপর কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু এম জি এম আর সিনেরোমা’র সাথে গাঁটছড়া বাঁধতে এটুকুই যথেষ্ট। তো, বেঁধে ফেললেন স্ট্যানলি। প্রাথমিক নামটা ছিল, জার্নি বিয়োন্ড দ্য স্টার্স’। (অন্য দিকে, কীভাবে সৌরজগৎ বিজিত হয়েছিল তা মোটেও বেখাপ্পা নয়, বরং পরিপূরক। কিন্তু আপনি আমাকে ডাকবেন না, তাহলে আমিও আপনাকে বিরক্ত করব না।)
উনিশশো পঁয়ষট্টির হিসাবে স্ট্যানলি ভবিষ্যৎ কল্পনায় অসম্ভব জটিলতা আনছিলেন। ব্যাপারটা আরো গুবলেট হয়ে যায় যখন সিদ্ধান্ত হল যে শু্যটিং হবে ইংল্যান্ডে যেখানে তিনি এখনো নিউইয়র্ক থেকে পাততাড়ি গোটাননি। গোদের উপর বিষফোঁড়া, কোনোমতেই তার আকাশ ভ্রমণ চলবে না।
সমালোচনা করছি না কিন্তু, পাইলটের লাইসেন্স নেয়ার সময়ও স্ট্যানলির অবস্থা বেশি সুবিধাজনক ছিল বলে মনে হয় না। ঠিক যে কারণে ১৯৫৬ সালে আমি সিডনিতে ড্রাইভিং টেস্টে পাশ করার পর আজো হুইল হাতে নিইনি। আমিও জীবনকে বড্ড ভালোবাসি।
স্ট্যানলি ছায়াছবিটা শেষ করছেন, আমি টানাটানি করছি উপন্যাস ভার্সনটা নিয়ে, শেষভাগ নিয়ে যুদ্ধ করছি। কিন্তু ছাপার বেলায় তার সাথে কথা বলে নেয়ার সময় নেই। তিনি কাজে নাক পর্যন্ত ডুবে আছেন দিনরাত। কসম কেটেছিলেন, বই প্রকাশের আগে মুভিটা মুক্তি দেয়ার জন্য হন্যে হয়ে যাননি। কিন্তু আমি হন্যে হয়ে গিয়েছিলাম আটষট্টিতে।
এর জটিল গোলকধাঁধা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, মুভি থেকে বই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন হবেই। স্ট্যানলি সিদ্ধান্ত নিলেন, ডিসকভারি শিপটা বৃহস্পতিতে নামবে, যেখানে মূল উপন্যাসে সেটা শনির অতিথি, বৃহস্পতির গ্র্যাভিটিশনাল ফোর্সকে কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যায়।
গতিবৃদ্ধির এই পথ ব্যবহার করেছিল ভয়েজার স্পেসক্রাফট; এগার বছর পর।
শনির বদলে কেন বৃহস্পতি? অন্তত তাতে করে কাহিনীর ধারা আরেকটু সহজ হয়, ব্যস। কিন্তু তারচে বড় কারণ হল, স্পেশাল ইফেক্ট ডিপার্টমেন্ট এমন শনি তৈরি করতে পারেনি যেটা স্ট্যানলিকে খুশি করতে পারবে। তাতে ভালই হল, কারণ ভয়েজার মিশনে শনির বলয়কে কল্পনার চেয়েও জটিল হিসেবে উপস্থাপিত করেছিল পরে; ফলে সেই শনি উপস্থাপিত হলে এতদিনে ছবিটা রদ্দি হয়ে যেত।
জুলাই আটষট্টিতে উপন্যাসটা মুক্তি পাবার এক যুগেরও পরে আমার সেই ওডিসি নিয়ে দ্বিতীয় উপন্যাস লেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। সব তো আর আমাদের ইচ্ছানুযায়ী চলে না, ভয়েজারের সেই দারুণ অভিযান আমাকে আরো খুশি করল। আমি আর স্ট্যানলি যে জায়গা নিয়ে স্বপ্নের বেসাতি করেছিলাম সাঁৎ করে সেটাই বাস্তবের দোরগোড়ায় কড়া নাড়তে শুরু করল। বদলে গেল আমার মন-মগজ। কে জমাট পানিতে মোড়া উপগ্রহ আশা করেছিল, কে ভেবেছিল সালফারের অগ্নিগিরির শত কিলোমিটার উঁচু আগুন-বর্ষণ রূপে দোজখ লুকিয়ে আছে বৃহস্পতির আরেক উপগ্রহে।
আজ, সায়েন্স ফিকশন আরো বিশ্বাস্য হতে পারে সত্যিকার সায়েন্সের নির্যাসে সিক্ত হয়ে। তাই, ২০১০: ওডিসি টু এল, সত্যিকার বৃহস্পতির প্রকৃতিকে তুলে ধরে।
এই দু উপন্যাসে আরো একটা বড় পার্থক্য আছে।
প্রথম উপন্যাস এবং চলচ্চিত্র প্রকাশিত হয় মানুষের ইতিহাস দ্বিখণ্ডিত হবার আগের ভাগে, চাঁদে পা রাখার আগেই। নীল আর্মস্ট্রং আর বাজ অলড্রিন নিরব সাগরে পা রাখলেন, ফিকশনের নতুন ধারার আবশ্যকতা বেরিয়ে এল। অ্যাপোলো এইটের চন্দ্রজয়ীরা আগেই চলচ্চিত্রটা দেখেছিলেন। চন্দ্রদেবের দূরপ্রান্তে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেয়া প্রথম মানব চোখগুলো নাকি কী একটা খুঁজে বেড়িয়েছিল। তারা পরে আমাকে বলেছিলেন, তাদের চোখ চাঁদের বুকে কালো একটা প্রস্তর খুঁজেছিল এবং তারা সেটা আবিষ্কারের কথা প্রচারের জন্য মুখিয়ে ছিলেন।
হায়, এমন কোনোকিছুতো ছিল না সেখানে!
অ্যাপোলো তের মিশন আসলে ২০০১ এর সাথে কিছুটা যুক্ত ছিল বলা চলে। হাল কম্পিউটার যখন এই থার্টি ফাইভের ব্যর্থতার কথা ঘোষণা করে তখন সে যে কথাটা ব্যবহার করেছিল তা হল, ‘আনন্দে বাধা দেয়ায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত; কিন্তু আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’
যাক, অ্যাপোলো তেরোর কমান্ড মডিউলের নাম ছিল ওডিসি। মুভির বিখ্যাত জরথুস্ত্র থিমের মতো করে একটা টিভি সম্প্রচার এসেছিল অক্সিজেন ট্যাঙ্ক বিস্ফোরণের পর। তারা পৃথিবীতে যে কথাটা পাঠিয়েছিল, তা হল, ‘হিউস্টন, আমাদের একটা সমস্যায় পড়তে হল…’
লুনার মডিউলটাকে লাইফবোটে পরিণত করে মেধাবী পরিচালনার মাধ্যমে ওডিসিতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। নাসা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর টম পেইন আমার কাছে রিপোর্টটা পাঠানোর সময় কভারে লিখেছিলেন, ঠিক যেমনটা সব সময় আপনি বলে এসেছেন, আর্থার।
এমন আরো অনেক ঘটনা। মহাকাব্যিক যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ ওয়েস্টার-ছয় বা পালাপা বি-দুই এর ঘটনাও মিলে যায়। এগুলো মিসফায়ারিংয়ের কারণে ভুল কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছিল চুরাশি সালে।
কাহিনীর এক পর্যায়ে ডেভিড বোম্যানের ই ভি এ’র বাড়তি অংশ নিয়ে স্পেসশিপ ডিসকভারি থেকে বেরিয়ে গিয়ে হারানো পৃথিবীকে মূল ডিশ দিয়ে বিদ্ধ করতে হয়। (দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ডস অব ২০০১ এর ছাব্বিশতম অধ্যায়ে ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তর লেখাজোকা ছিল।) তারপর সে সেটা ধরতে পেরেও আসল কাজে ব্যর্থ হয়, এলোমেলো ঘোরা বন্ধ করতে পারে না।
চুরাশির নভেম্বরে নভশ্চর জো অ্যালেন স্পেস শাটল ডিসকভারি ছেড়ে বেরোন (না, কথাটা বানিয়ে বলছি না!) তারপর পালাপার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বোম্যানের সাথে তার একটাই পার্থক্য, ব্যাকপ্যাকের নাইট্রোজেন জেটের বা দিয়ে তিনি কাজটা করতে সফল হন।
ডিসকভারির কার্গো বে’ তে স্যাটেলাইটটা নিয়ে আসা সম্ভব হয়। তার দু’দিন পর ওয়েস্টারও উদ্ধার পায়। সে দুটিই ফিরে আসে পৃথিবীতে; আবার চেক করো, আবার ঠিক করো, আবার পাঠাও কালো আকাশে-এবার সফলতা; মানুষের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস ছোট কিন্তু সাহসে ভরা দুর্দান্ত কাজ।
এখনো আমি ফুরিয়ে যাইনি। জো’র এই ঘটনার পর আমি একটা বই পাই হাতে, বইটার নাম, ‘অ্যান্টারিং স্পেস: অ্যান অ্যাস্ট্রোনট’স ওডিসি’, সেই সাথে মলাটে একটা লেখা ছিল:
প্রিয় আর্থার, আমি যখন ছোট্ট এক ছেলে, আপনি আমাকে লেখার পোকা আর স্পেসের পোকা-দুয়েই আক্রান্ত করেন। কিন্তু কেন বলেননি কাজ দুটো বাস্তবে করা কত্তো কঠিন!’
আমি আবেগে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ ধারার সংবর্ধনা আনন্দ দেয় অসীম, সেই সাথে রাইট ব্রাদার্সের মতো অনুভূতি এনে দেয়।
যে উপন্যাস আপনারা পড়তে যাচ্ছেন সেটা মাঝেমধ্যে ভালোভাবেই সমালোচিত হয়েছে। বিশেষত বিস্তর ব্যাখ্যা দেয়াটা একটু দৃষ্টিকটু ঠেকেছে সমালোচকের চোখে। সেই সাথে আরো একটা অভিযোগ, মুভির কয়েকটা রহস্যকে খোলাসা করে ফেলা হয়েছে। এমনকি রক হাডসন প্রিমিয়ারে বলেছিলেন, ‘ক্যান সামওয়ান টেল মি, হোয়াট দ্য হেল দিস ইজ অল অ্যাবাউট?
কিন্তু আমি মোটামুটি স্থির, বইতে সব সময়ই চলচ্চিত্রের চেয়ে একটু বেশি খোলাসা থাকা দরকার, এখানে শব্দ নেই, দৃশ্য নেই, তারপরও বেশি একাগ্রতা আছে। তারপরও আমি ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুললাম ২০১০ লিখে। (পরে পিটার হেইমস্ এটাকেও একটা দারুণ চলচ্চিত্রের রূপ দেন।) জটিলতা বাড়ালাম ২০৬১ লিখে, জটিলতা বাড়ালাম ৩০০১ লিখে।
কোনো ট্রিলজি’রই আসলে চারটার বেশি খণ্ড থাকা মানায় না। তাই প্রমিজ করতে পারি, ৩০০১ ই ফাইনাল ওডিসি।*
[* লেখক বেশিদিন প্রমিজ ধরে রাখতে পারেননি, সর্বজয়া মহাকাব্য এগিয়ে গেছে, অশীতিপর সর্বশ্রদ্ধেয় লেখক, স্পেস সায়েন্স ফিকশনের জনক আর্থার সি ক্লার্ক এই এখনো লিখছেন ওডিসি’র পঞ্চম পর্ব।]
.
প্রারম্ভ কথন
প্রতিটি জীবিত মানুষের সামনে এখন ত্রিশটা ভূত নেচে বেড়ায়। কারণ এখন জীবিত মানুষের সাথে মৃতদের অনুপাতটা এমনি। সময়ের জন্মের পর মোটা দাগে দশ হাজার কোটি মানুষ হেঁটে গেছে ধরিত্রীর এই পথ ধরে।
এখন, সংখ্যাটা আগ্রহ জাগায়। কারণ, আমাদের স্থানীয় সৃষ্টি জগৎ, স্থানীয় গ্যালাক্সি দুধসায়রে বা মিল্কি ওয়েতে কমবেশি এই সংখ্যক তারকাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। তো, এই পথে চলে যাওয়া প্রতি মানবের জন্য একটা করে নক্ষত্র আলোকদায়িনীর রূপ নিল।
কিন্তু তাদের প্রত্যেকেইতো আরাধ্য সূর্যদেব। বেশিরভাগই আমাদের কাছের নক্ষত্র, যাকে আমরা সূর্য বলে জানি তারচে অনেক অনেক বড়। এবং তাদের অনেকেরই, সম্ভবত বেশিরভাগেরই নিজস্ব আরাধনারত গ্ৰহজগৎ থাকার কথা। তাই, মানবজাতির প্রত্যেক সদস্যকে অসীম জায়গা দেয়ার মতো যথেষ্ট স্থান এই এক জগতে আছে। সেই প্রথম বন-মানবের মতো একটা করে নিজস্ব, একেবারে একার ভূমি দিয়ে নিজের মতো বেহেস্ত বা দোজখ সাজিয়ে দেয়া কোনো কঠিন কাজ নয়।
সেই দূর, তারার দেশের সম্ভাব্য স্বর্গ বা নরকের মধ্যে ক’টায় এখন বসতি আছে? সৃষ্টির কোন্ কোন্ সিঁড়ি বেয়ে?
অনুমানের কোনো উপায় নেই। আমাদের পরের প্রজন্মের কাছে স্বপ্ন হয়ে থাকবে যে মঙ্গল বা শুক্র তাদের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ দূরে অবস্থিত সবচে কাছের তারকা-ভুবনটা।
কিন্তু দূরত্ব বিনাশী নয়, দূরত্ব নশ্বর। আমরা, মানবজাতি, একদিন মিলিত হব আমাদের সমকক্ষদের সাথে কিম্বা আমাদের স্বত্বাধিকারীর সাথে; তারার দেশ পেরিয়ে গিয়ে।
মানুষ নিজের অগ্রগতিকে মেনে নিতে বেশ অস্বস্তিতে ভোগে। কেউ এখনো আশা করে যে তারার দেশ ডিঙানো যাবে না। এমন ডিঙি আসবে না কখনো। কিন্তু দলে ভারি হতে থাকারা আজ জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়, এমন মিলন কেন হল না আজো, এখনো, যেখানে আমরা বেরিয়ে পড়তে শিখেছি স্পেসে?’
কেন নয়, অবশ্যই। সেই অতি বাস্তব প্রশ্নের একটা মোটামুটি সন্তোষজনক জবাব দেয়া যায়। কিন্তু মনে রাখবেন, এটা শুধুই এক কল্পনার জাতক।
বাস্তব, আর সব সময়ের মতোই, হবে আরো আরো অনেক অনেক অবিশ্বাস্য।
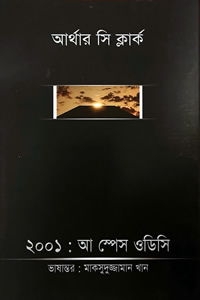
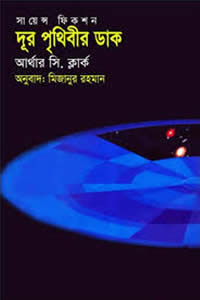
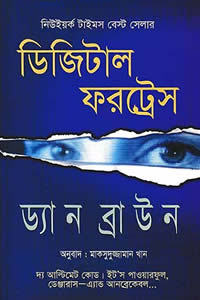
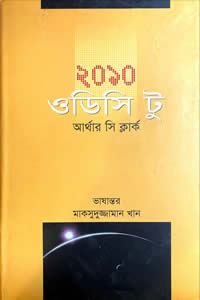


Leave a Reply