সংস্কৃতির ভাঙা সেতু – আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
.
সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
সংস্কৃতি নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ‘আজকালি বড়ো গোল’ দেখা যায়। প্রতিপক্ষ ছাড়া কোনো তর্ক তেমন জমে না, সংস্কৃতি-বিষয়ে কথাবার্তায় একটি শত্রুপক্ষ জুটে গেছে, এই শত্রুবরের নাম ‘অপসংস্কৃতি’। শহর এলাকায় তো বটেই, নিম-শহরে জায়গাগুলোতেও সচ্ছল, এমনকী নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা রংবেরঙের নানারকম রম্য পত্রিকা, টিভি, ফিল্ম ও ভিসিআরের কল্যাণে অপসংস্কৃতির চর্চা প্রাণভরে দেখে এবং নিজেদের জীবনে তার যথাযথ প্রয়োগের জন্য একনিষ্ঠ সাধনা চালায়। এই সাধনা আবার বিনা খরচায় হয় না, এর জন্য পয়সার দরকার। সদাপরিবর্তনশীল কাটছাঁটের কাপড়চোপড়, ষ্টিকার, চেন ইত্যাদি তো বটেই, কোকাকোলা থেকে শুরু করে মদ, গাঁজা, চরস, ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার, টিভি, ভিসিআর, হোন্ডা, গাড়ি-যে যেমন পারে-প্রভৃতি উপাদান ছাড়া এই সাধনা অব্যাহত রাখা বড় কঠিন। এখানে ক’টা বাপ-মা আছে যারা নিয়মিত এসবের জোগান দিতে পারে? তা সে-ব্যাপারেও সাহায্য করার জন্য আমাদের টিভি ও সিনেমাওয়ালারা সদাপ্রস্তুত। হাইজ্যাক, চুরি, ডাকাতি, মারামারি, লক্ষঝম্প প্রভৃতির ছবি দেখিয়ে যুবসম্প্রদায়কে এরা অর্ধসংগ্রহের শর্টকাট পথ রপ্ত করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। এতে পয়সা কামানো চলে, অন্যদিকে পয়সা কামাবার পদ্ধতিটাও ঐ ধরনের সংস্কৃতিচর্চার অবিচ্ছিন্ন অংশ। এইভাবে earn while you learn-কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে যুবসম্প্রদায়ের একটি অংশ একই সঙ্গে অর্থোপার্জন ও সংস্কৃতিচর্চা দুটোতেই সমান পারঙ্গম হয়ে উঠেছে। অর্থাগম হচ্ছে দেখে এদের ‘রক্ষণশীল’ বা ‘রুচিশীল’ বাপ-মাও চুপচাপ থাকাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন। কারণ কোনো কোনো কর্তব্যপ্ৰায়ণ পুত্র তাদের উপার্জিত অর্থের খানিকটা বাড়িতেও ঢালে। এ ছাড়া, এইসব যুবকের অনেকের মধ্যে আজকাল ধর্মচর্চার প্রবণতাও দেখা যায়। সব ওয়াক্ত নামাজ পড়ার সময় না-পেলেও শুক্রবার এরা মসজিদে যায়, মহা ধুমধাম করে ঈদ-শবেবরাত করে, পিরের পেছনে অকাতরে টাকা ঢালে, তাবিজ নেয়, সুলক্ষণ পাথর কেনে এবং মাজার দেখলেই সেজদা দেয়। এইসব দেখে পরহেজগার বাপ মা বেশ তৃপ্ত না, যে যা-ই বলুক, চুরি-চরামি, হাইজ্যাক, ডাকাতি যা-ই করুক, মদ-গাঁজা যতই টানুক, কিন্তু ছেলের আমার ধর্মে মতি আছে; পিরের তেজে এইসব উপসর্গ একদিন ঝরে পড়বে, ততদিনে ঘরে দুটো পয়সা আসছে আসুক, ছেলের কল্যাণে বাপ-মাও জাতে উঠতে পারে, এটাই-বা কম কী?
সমাজের অগ্রসর অংশ বলে এই নিয়ে বুদ্ধিজীবীদের অনুশোচনার অন্ত নেই। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তাঁরা এতই সোচ্চার যে এটাকে তারা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতির পবিত্র গোদুগ্ধের ভাঁড়ে বিপুল পরিমাণ গোচোনা বলে ঠাহর করে ফেলছেন। তাঁদের কাছে আমাদের সংস্কৃতিচর্চার প্রহাদকুলে একমাত্র দৈত্য হল অপসংস্কৃতি। অপসংস্কৃতি প্রচারের দুর্জয় ঘাঁটি টেলিভিশন পর্যন্ত এই নিয়ে আফশোস করার জন্য তাদের হায়ার করতে শুরু করেছে। আমাদের কোনো কোনো বীরপুরুষ বুদ্ধিজীবী টেলিভিশনের পর্দায় অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে চাপাবাজি করে দুটো পয়সা ও নাম কামাতে এতটুকু পেছপা হচ্ছেন না। এখন ক্যান্টনমেন্ট যেমন গণতন্ত্র বিতরণের দাতব্য কেন্দ্র, দরিদ্র ও শূদ্র দেশবাসীকে খাঁটি নির্জলা গণতন্ত্র সরবরাহের হুংকার শোনা যায় সেখানে থেকেই নানারকম লম্প, ঘাবলামো, ভাঁড়ামো ও ইয়ার্কি ফাঁকে ফাঁকে, টেলিভিশনে তেমনি ঘোষিত হয় সুস্থ সংস্কৃতিপ্রচারের সংকল্প। তো সিনেমাই-বা বাদ থাকে কেন? ঢাকায় এখন ধর্মভাবদীপ্ত ফাইটিং ছবি তৈরির মড়ক চলছে। ভরসা করি, এমন ছবির মহড়া নিশ্চয়ই চলছে যেখানে কুম্ফু বা কারাতে-পটু বাঙালি সংস্কৃতিচর্চায় নিবেদিতপ্রাণ কোনো বাহাদুর পিরের পড়া-পানি সেবন করে তার আঁটোসাটো প্যান্ট-গেঞ্জি-পরা প্রেমিকাকে বুকে জড়িয়ে ‘দম-মওলা’ বলে একটা হাঁক ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে ‘অপসংস্কৃতি’-নামক দানবের ওপর।
এই ধরনের সংস্কৃতিচর্চা, এর অনুকরণ, এর নানারকম ওঠানামা–সবই চলে মধ্যবিত্তসমাজে। মধ্যবিত্তসমাজের একটি বড় অংশ নিজেদের সামাজিক ও শ্রেণীগত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয়। একজনের অবস্থান সমাজের কোন স্তরে, তিনি কি মধ্যবিত্ত না উচ্চবিত্তের অন্তর্ভুক্ত, মধ্যবিত্তের বিভিন্ন উপ-বিভাগগুলোর মধ্যে কোনটিতে তিনি বিরাজ করেন–এ-সম্বন্ধে তার স্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। এখন এখানে টাকাপয়সা রোজগারের চোরাগোপ্তা অলিগলি এত বেশি যে, যে-কোনো লোক একদিন বিত্তবান হবার স্বপ্ন দেখতে পারে। পয়সার জোরে সমাজের যে-কোনো স্তরে উঠার বাসনা যে সকলের জীবনেই সফল হবে–তা নয়। বরং সিঁড়ির আকাঙ্ক্ষিত ধাপটি বেশির ভাগ লোকেরই নাগালের বাইরে থেকে যায়, কেউ-কেউ হোঁচট খেয়ে নিচেও গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বাসনা পুষতে বাধা কোথায়? পোষা বাসনাটি দিনদিন ফাঁপে এবং কেউ-কেউ ভাবতে শুরু করে যে গন্তব্যে পৌঁছতে আর দেরি নাই। সুতরাং জীবনযাপনের মান ও পদ্ধতি এবার পালটানো। দরকার। পাশ্চাত্য কায়দায় ওপরতলার জীবনযাপন অনুসরণ করার রেওয়াজ আমাদের। এখানে তেমন পরিচিত নয়। বুর্জোয়া দেশগুলোর উচ্চবিত্তের জীবনযাপনকে আদর্শ ধরে। নিয়ে মধ্যবিত্ত সেটাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে শুরু করে। কিন্তু বুর্জোয়া মূল্যবোধ ও মানসিকতা তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। ওদিকে ওপরের ধাপে ওঠার জন্য মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত এতই উষ্মীব ও অস্থির যে এজন্য হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তা-ই সে আঁকড়ে ধরে। ঐ ধাপে পৌঁছবার জন্য মাজারে বা পিরের কাছে ধরনা দিতেও তার বাধে না। অথচ পাশ্চাত্য বুর্জোয়া মানসিকতা এই ধরনের ধর্মান্ধতাকে অস্বীকার করে। আমাদের মধ্যবিত্তের। জীবনযাপন কিংবা ঈন্ধিত জীবনযাপন এবং মূলবোধ পরস্পরবিরোধী। এদের জীবন তাই নিরাল, এই জীবনের ভিত্তি, বিন্যাস ও তাৎপর্য খুঁজে বের করা খুব কঠিন। এদের সংস্কৃতিও যে নিরালম্ব ও উটকো ধরনের হবে এতে আর সন্দেহ কী? সামন্ত ও গ্রাম্য মূল্যবোধের সঙ্গে বুর্জোয়া জীবনযাপনের এই উকট মাখামাখির ফলে যে-সংস্কৃতি গজিয়ে ওঠে তাও অনেকের চোখে উটকো ঠেকে এবং তখন তাকে অপসংস্কৃতি বলে গাল দেওয়া হয়।
কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের যারা বিশুদ্ধ কিংবা সংস্কৃতিচর্চার জন্য প্রাণপাত করে চলেছেন, নিম্নবিত্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী তো দূরের কথা, সাধারণ ও আরোগ্যপিপাসু মধ্যবিত্তের মধ্যে তারাও কি কোনোরকম সাড়া জাড়াতে পারছেন। সৃজনশীল শিল্পীর হাতে সংস্কৃতির সৌন্দর্যময় ও উদ্দীপ্ত প্রকাশ ঘটবার কথা। কিন্তু সংস্কৃতিচর্চার যে-সংগঠিত প্রকাশ শিল্প সাহিত্যের মাধ্যমগুলোতে দেখি তা দিনদিন নির্জীব ও একঘেয়ে অত্যাসে পরিণত হচ্ছে; কী সাহিত্যে কী চলচ্চিত্রে কী সংগীতে কেবল পানসে ও নিষ্প্রাণ পুনরাবৃত্তি চলছে।
একথা ঠিক যে আমাদের কথাসাহিত্যে আঙ্গিক আগের চেয়ে মার্জিত ও পরিণত রূপ লাভ করেছে। সুখপাঠ্য গল্প-উপন্যাস অনেক লেখা হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ গল্প-উপন্যাস পড়ে মনে হয় যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন নামে নানা কায়দায় একটিমাত্র কাহিনী বয়ান করছেন। সেই কাহিনীও আবার নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা নয়, তিরিশের দশকের কোনো প্রতিভাবান বা চল্লিশের কোনো বুদ্ধিমান লেখকের অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণের তরল ও বিকৃত সংস্করণ। ঢাকার রম্য সাপ্তাহিকগুলোতে বিভিন্ন পালাপার্বণে বছরে কম করে ডজন দেড়েক উপন্যাস বেরোয়। ঈদের জুতো-কাপড়ের সঙ্গে মধ্যবিত্ত ঐসব পত্রিকার একটি কেনে এবং কয়েকদিনের মধ্যে সব লেখা পড়েও ফেলে। একটু তদন্ত করলে দেখা যায় যে এগুলোর বিষয়বস্তু প্রায় একই ধরনের ছিচকাঁদুনে প্রেম ও ধরি-মাছ-না-ই-পানি মার্কা সেক্সের সঙ্গে উদ্ভট ও অভিনব বিপ্লবী প্রসঙ্গ চটকাবার ফলে এগুলো বেশ আঠালো হয় এবং পাঠক একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা এর সঙ্গে সেঁটে থাকেন। পাঠকদের সেঁটে রাখার কায়দা। লেখকদের বেশ ভালোই রপ্ত হয়েছে। এজন্য এদের জাদুগিরি বলে হাততালি দেওয়া যায়, কিন্তু শিল্প বলে মেনে নেওয়া মুশকিল। মানুষের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে কোনো গভীর সত্য বা প্রশ্নের উন্মোচন সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যে অনুপস্থিত। পাঠককে প্রচলিত মূল্যবোধ বা সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো জিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড় করাতে সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য ব্যর্থ।
আঙ্গিকের দিক থেকে আমাদের এখানে সবচেয়ে পরিণতি ঘটেছে কবিতায়। এখন পাঠযোপ্য কবিতার সংখ্যা অনেক। কিন্তু কবিতা লেখাও এখন খুব সহজ অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে। ছন্দ, উপ, রূপক, প্রতীক, চিত্রকল্প সব তৈরি হয়ে আছে; এমনকী প্রতিবাদ ও সংকল্পের ভাষা পর্যন্ত সুলত। এগুলো একসঙ্গে অ্যাসেম্বল করতে পারলেই একটি কবিতা খাড়া করা যায়। ফলে কবিতা জীবনের স্পন্দন ও প্রেরণা থেকে বঞ্চিত।
সংগীত ও নৃত্যকলার চর্চা আজ অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু এই দুই ক্ষেত্রেই সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া খুব দুরূহ। সঙ্গীতের যা-কিছু আজও মানুষকে, অবশ্যই মধ্যবিত্তসমাজের মানুষকে গভীরভাবে স্পর্শ করে তার প্রায় সবটাই আগেকার রচনা। এমনকী আধুনিক কালে শহরের সম্প্রসারণের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতাবোধজনিত যে-নিঃসঙ্গতার অনুভূতি–তারও সফল অনুরণন সাম্প্রতিক সংগীতে পাওয়া যায় না, এজন্যও ধরনা দিতে হয় পুরনো কর্তাদের দুয়ারে। নৃত্যকলায় আজ শিল্পীর প্রচণ্ড, তীব্র ও গভীর অনুভূতি একেবারেই তরঙ্গায়িত হয় না বললে কি বাড়িয়ে বলা হয়? মুদ্রার কসরত দেখাবার মধ্যে নৃত্যের নৈপুণ্য আজ সীমাবদ্ধ।
সফল শিল্পকর্ম মানুষের আনন্দ ও বেদনাকে অমূল্য করে তোলে, বাচাকে করে তোলে অর্থবহ এবং জীবনকে তাৎপর্যময় করে গড়ে তোলার জন্য মানুষকে প্রেরণা জোগায়; সাম্প্রতিক শিল্পচর্চা এইসব শক্তির সবগুলো হারিয়ে ফেলেছে। বিদেশি কিংবা অপরিচিত উচ্চবিত্তের জীবনযাপনে হাস্যকর অনুকরণেকে বলি অপসংস্কৃতি। এর উটকো চেহারা এত উৎট, এত কিভূতকিমাকার যে একে সহজেই কষে গাল দেওয়া যায়। কিন্তু যাকে ‘রুচিশীল বাঙালি শিল্পচর্চা’ বলা হয় যা মধ্যবিত্তের কর্তৃত্বে, মধ্যবিত্তের দ্বারা এবং মধ্যবিত্তের জন্য রচিত–তাও তো মধ্যবিত্তকে উদ্দীপ্ত করতে অক্ষম। শিল্পচর্চার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মেধা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে, কিংবা শিল্পচর্চায় তারা যথেষ্ট নিবেদিতপ্রাণ নন–এসব কথা তো বিশ্বাসযোগ্য নয়। তা হলে?
প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে যে-বিচ্ছিন্নতার ফলে অপসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে, বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্ত বাঙালির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা তেমনি আজ মধ্যবিত্ত বাঙালি সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চাকে পরিণত করেছে একঘেঁয়ে ও প্রাণহীন নিস্পন্দ অভ্যাসে। কারও কারও মনে হতে পারে যে, এতে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের কী এসে যায়? অপসংস্কৃতির চর্চা যতই বাড়ক তাতে তাদের কী? টিভি বা ভিসিআর-এর সম্প্রসারণশীল থাবাবিস্তার সঙ্গেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী ওসবের স্পর্শ থেকে মুক্ত। ওপরে উঠবার স্বপ্নসাধ লালন করা তো। দূরের কথা, একমাত্র সম্পত্তি সবেধন নীলমণি প্রাণটি টিকিয়ে রাখতেই এদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। অন্যদিকে মধ্যবিত্তের রুচি ও মেজাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েও মধ্যবিত্তের বুদ্ধি ও আবেগের কাছে সাড়া-তুলতে-না-পারা সাম্প্রতিককালের ‘রুচিশীল বাঙালি সংস্কৃতি’র ব্যর্থতায় নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর কিছু এসে যায় না। সুতরাং মধ্যবিত্তের যে-ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নবিত্তের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রামে নিবেদিতচিত্ত, তারাই-বা এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?
মাথা থাকলে একটু ঘামাতে হয় বইকী! বিষয়টি যদি রাজনৈতিক কর্মীর মাথায় কামড় না দেয় তো বুঝতে হবে যে সেই মাথায় কামড়াবার মতো কস্তুর অভাব ঘটেছে। আমাদের এখানে সচেতন ও সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা প্রচলিত কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যেই। আজ মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর ফল কারও জন্য ভালো হয়নি। নিম্নবিত্তের মধ্যে শিক্ষার প্রসার একেবারেই নেই। সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতার ফলে দেশের শিক্ষিত অংশের সঙ্গে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মানসিক ব্যবধান ক্রমে বেড়ে চলেছে। শিক্ষিত মানুষের প্রত্যেকেই হল এক-একটি বদমাইশ ও শয়তান–একথা ঠিক নয়। শিক্ষিত মানুষের একটি ছোট অংশ নিম্নবিত্তের মুক্তির জন্য স্থিরসংকল্প। এই অংশটির সঙ্গেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর পূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। তাদের কথাবার্তা, তাদের চিন্তাভাবনা, তাদের আচরণ ও ব্যবহার বুঝে ওঠা নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর আয়ত্তের বাইরে।
মধ্যবিত্তের জন্য এই বিচ্ছিন্নতা মারাত্মক বিপর্যয় টেনে আনছে। যাকে ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ বলে ঢাক পেটানো হয় তা যদি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কর্মপ্রবাহ ও জীবনযাপন থেকে প্রেরণা নিতে না পারে তো তাও অপসংস্কৃতির মতো উটকো ও ভিত্তিহীন হতে বাধ্য। তার বাইরের চেহারা যতই ‘রুচিশীল রুচিশীল’ হোক, তাতে ঘষামাজাভাব যতই থাকুক, তা রক্তহীন হতে বাধ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠের রক্তধারাকে ধারণ না-করে কোনো দেশের সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা কখনো প্রাণবন্ত হতে পারে না। এই বিচ্ছিন্নতার ফলে আজ আমাদের সংস্কৃতি রুগ্নদেহ তার দৃষ্টি ফ্যাকাশে, তার স্বর ন্যাকা এবং নিশ্বাসে প্যানপ্যানানি। যার সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চা মানুষের জীবনকে অর্থবহ করে তুলতে পারে না, তার রাজনীতির ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা কম। আজ অনেক রাজনৈতিক কর্মী নিজেদের সগ্রামী তৎপরতাকে নিষ্ফল ভাবতে ক্ষ করেছেন। বামপন্থি কর্মীদের অনেকেই আজ হতাশ ও বিচলিত। বিভিন্ন বামপন্থি সংগঠনের অধঃপতন যে কোথায় নেমেছে তা বোঝা যায় যখন দেখি যে এরা আজ যে-কোনো ডানপন্থি, প্রতিক্রিয়াশীল ও গণশত্রু দলগুলোর সঙ্গে জোট পাকাতে এতটুকু ইতস্তত করে না। জাতীয় সংহতি, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা রক্ষা এবং গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে এরা প্রমাণিত–জনদ্রোহী শিবিরে ভিড়ে যায়। কিছুদিন আগে নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তিসামর্থ্যের ওপর আস্থা নিয়ে বিভিন্ন এলাকায় যারা আত্মনিয়োগ করেছিলেন শ্ৰেণীসগ্রামে, স্বাধীনতা ও সংহতি’-রক্ষার দাবিত্নে কিত্ত্বা গণতন্ত্রের দামি পাথরটি খোজার। জন্য এঁরা আজ ক্যান্টনমেন্টের নরঘাতকদের কাছে ধরনা দেন। এই অবস্থায় সৎ ও নিষ্ঠাবান বামপন্থি কর্মীর হতাশ না হয়ে উপায় কী? বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারলে এই হতাশা এঁদের আচ্ছন্ন করতে পারত না। মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক সংকট থেকে এরা মুক্ত নন। যে-জনসমষ্টির মুক্তির জন্য এঁরা সগ্রামে নামেন তাদের জীবনযাপন ও সংস্কৃতি এঁদের নাগালের বাইরে। যে-সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সাহিত্য শিল্পের দেহকে রক্তহীন ও চেতনাকে নিস্পন্দ করে তোলে, রাজনীতিকেও তা নিস্তেজ ও তাৎপর্যহীন করতে বাধ্য।
বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশই আসেন নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। ছেলেবেলা থেকে বাড়িতে এরা কিছু-না-কিছু লেখাপড়ার সুযোগ পান। গল্প উপন্যাস তো পড়েনই, কেউ-কেউ কবিতাও পড়েন। একটু বয়স হলে নিজেদের বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্যে চারপাশের জগতের সঙ্গে পড়াশোনা ও নিজেদের চিন্তাভাবনা মিলিয়ে দেখেন। এরা স্পর্শকাতর ও অনুভূতিপ্রবণ নিজেদের শ্রেণীতে, এমনকী নিজেদের বাপ-চাচা কী ভাইবোনদের মধ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্তসমাজে ওঠার দৌড়ে শামিল হওয়ার আহ্বান এরা প্রত্যাখ্যান করেন, সেই দৌড়ে প্রতিযোগী হওয়ার জন্য যেরকম চুরি-চিরামি, বদমাইশি ও জালিয়াতি করা দরকার, তা এদের স্বভাবে নেই। চারপাশে দেখাশোনা এবং স্পর্শকাতর চেতনার সাহায্যে সমাজে শোষণের রূপ সম্পর্কে একটা ধারণা হয়। রাজনৈতিক বই পড়ে সেই ধারণার সঙ্গে যোগ হয় সংকল্প-শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজগঠনের সংকল্প। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের থেকে অতিরিক্ত সুযোগ ভোগ করার সুযোগ পান বলে কারও কারও মধ্যে অপরাধবোধ কখনো মনে কাঁটার মতো বেঁধে। সুবিধাভোগ তখন তার কাছে ভার বলে মনে হয় এবং এই ভাব বেড়ে ফেলার প্রবণতাও সাম্যবাদী সমাজগঠনের আন্দোলনে যোগ দিতে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।
কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান দৃঢ়চেতা ও সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হন। শ্রমজীবীদের শতকরা ৯০ ভাগ বাস করেন গ্রামে, তারা প্রায় সবাই নিরক্ষর। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে তাদের পরিচয় একেবারে নেই বললেই চলে। কিন্তু শৈশবকাল থেকে তারা বড় হন কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ঘোরর প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ায় বুদ্ধিশুদ্ধি তাদের কম নয়, বামপন্থি কর্মী-ছেলেদের ঠিকভাবে শনাক্ত করতে তাদের ভুল হয় না। শ্রমজীবী মানুষ বোঝেন যে লেখাপড়া শিখেও এই ছেলেগুলো টাউট হয়নি এবং ধর্ম বা জাতীয়তাবাদ বা গণতন্ত্রের বুলি কপচানো ও ভোট বাগানো তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। বামপন্থি কর্মীদের নিষ্ঠা ও সততা সম্পর্কে তারা নিঃসন্দেহ।
তবু শ্রমজীবীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে সংগঠিত করা বামপন্থি কর্মীদের আয়ত্তের বাইরে রয়ে যায়। অন্তত এখন পর্যন্ত অবস্থাটা তা-ই। ১৯৬৯ সালের ব্যাপক গণআন্দোলনকেও বামপন্থি ফাগণ সমাজ-পরিবর্তনের লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারেননি। অথচ এই আন্দোলনের সূত্রপাত ও বিকাশ ঘটে তাদের হাতেই। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও সংকল্প নিয়েও বামপন্থি কর্মীগণ শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারছেন না কেন? পার্লামেন্টারি রাজনীতির টাউট নেতাদের ওপর বীতশ্রদ্ধ শ্রমজীবীগণ বামপন্থি কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ না কেন? এর প্রধান কারণ শ্রমজীবীদের সঙ্গে বামপন্থি কমাদের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা। এই বিচ্ছিন্নতা দূর করতে না পারলে শ্রমজীবী মানুষের আস্থা ও আত্মীয়তা লাভ করা অসম্ভব।
নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অধিকাংশই শহরবাসী। বামপন্থি কর্মীদের কাজ করতে হয় গ্রামে, কিন্তু তারা মানুষ হয়েছেন শহরে। এই শহর প্রকৃত শহরও হতে পারে আবার নিমশহরও হতে পারে। রাজধানী বা জেলাশহর বা মহকুমা-শহর তো হতে পারে, আবার থানা বা শিল্পএলাকা বা ছোট বাণিজ্যকেন্দ্র বা রেলওয়ে জংশনকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা নিমশহরও কিন্তু শহর। একটি শহর যত হোট হোক, সেখানকার মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন আশেপাশের গ্রামের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এমনকী নিজেদের গ্রামের জমির ওপর নির্ভরশীল বা আধা-নির্ভরশীল পরিবারের স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েরা ছোটখাটো জীবনযাপন সম্পর্কে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই ছেলেমেয়েদের ছোটখাটো চাকরি করা বা ছোটখাটো ব্যবসা-করা বাপচাচার জীবনের পরম সাধ এই যে, ছেলেরা ভালো চাকরি নিয়ে বড় শহরে যাক, ব্যবসা যদি করে তো বড় শহরে গিয়েই করুক। মেয়েদের বিয়ের জন্য তারা শহরবাসী বর খোঁজেন। শহরের প্রতি এই টান গ্রাম সম্বন্ধে তাঁদের উদাসীন করে তোলে এবং পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই উদাসীনতা ক্রমে পরিণত হয় অবজ্ঞায়।
উদাসীনতা ও অবজ্ঞার এই মনোভাবকে ঝেড়ে ফেলেই একজন তরুণ বামপন্থি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন। কিন্তু যে-শ্রমজীবীর শাসনপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর সগ্রামে নামা, তাদের জীবনযাপন সম্পর্কে অজ্ঞতা কাটানো সহজ কাজ নয়। বই পড়ে, নিজেদের দেখাশোনা ও বুদ্ধিবিবেচনার সাহায্যে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর নিদারুণ অভাব সম্বন্ধে তার ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট। তিনি জানেন যে, আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা খেয়ে প্রাণধারণ করেন, আমাদের এই দেশের অতি অল্প কিছু লোকের কুকুরও এর চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খায়। তিনি জানেন যে, আমাদের দেশের কৃষিশ্রমিকদের অধিকাংশই বছরের দীর্ঘ একটি সময় প্রায় অনাহারে দিন কাটান এবং না-খেয়ে না খেয়ে তার পাকস্থলীর কাঠামো এমন দুর্বল হয়ে পড়ে যে হঠাৎ একটু বেশি খেলে পেটে অসুখ হয়ে তিনি মারা পড়েন। তিনি জানেন যে চিকিৎসা হল তাদের কাছে পরম বিলাসের বন্ধু। আমাদের এই নদীমাতৃক দেশে গ্রামের শ্রমজীবীরা গ্রীষ্মকালে যে-পানি খান, এই সোনার দেশেরই ভদ্রলোকেরা তা-ই দিয়ে শৌচকার্য করার কথাও কল্পনা করতে পারেন না। বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী এসব কথা জানেন। কেবল জানেন না, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন বলে উঁচু জাতে ওঠার দৌড়ে -নেমে রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন।
শ্রমজীবী মানুষের দারিদ্র বহু শতাব্দীর নিদারুণ শোষণের ফল। ইতিহাসের যতদূর দেখা যায়, বাংলার নিম্নবিত্তের সচ্ছল ছবি পাই না। এক হাজার বছর আগেকার বাংলা কবিতায় মানুষের নিত্যউপবাসের খবর আছে।
কিন্তু এই পারি দিয়েই নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীকে সম্পূর্ণ চেনা যায় না। তার জীবনযাপনে মানবিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ আছে এবং হাজার হাজার বছরের শোষণ তার সুকুমার বৃত্তিকে উপড়ে ফেলতে পারেনি। তাই তার যথার্থ পরিচয়লাভের জন্য তার সংস্কৃতিকে জানা একেবারে প্রথম ও প্রধান শর্ত।
মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা রাজনৈতিক কর্মীর কাছে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর প্রধান ও একমাত্র পরিচয় এই যে, লোকটি অসম্ভব রকমের গরিব। একথা ঠিক যে, দারিদ্র্য যে-জীবনযাপন করতে তাঁকে বাধ্য করে তা মানবেতর। কিন্তু পত্র মতো জীবনযাপন করলেও তিনি যে মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করা দরকার। নইলে শ্রমজীবীর মানবোচিত জীবনের মান অর্জন করার সংগ্রামে সর্বশক্তি প্রয়োগ করা রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে সম্ভব নয়।
দারিদ্র্য যতই ভয়াবহ ও প্রকট হোক, কেবল তা-ই দিয়ে কাউকে শনাক্ত করা হলে তাকে মর্যাদা দেওয়া হল না। যাকে সম্মান করতে পারি না, তার সমস্যাকে অনুভব করতে পারব না। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী যত গরিব হোন না, তিনি একজন মানুষ। তিনি একজন ব্যক্তি, একটি পরিবারের প্রধান, কারও স্বামী, কারও ভাই, কারও ছেলে এবং নিজের ছেলেমেয়ের বাপ। পরিবারের যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাকেই। তার মতো না খাওয়া ও আধপেটা-খাওয়া মানুষের সমাজ আছে, সেখানেও তার কিছু-কিছু দায়িত্ব থাকে। দারিদ্রের সঙ্গে একটি ধর্মবিশ্বাসও তিনি বাপ-দাদার কাছ থেকে বহন করে এনেছেন, যদিও ধর্মচর্চার ব্যাপারে ভদ্রলোকদের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ মিল নেই। ঈদে-পার্বণে নতুন জামাকাপড়ের খোঁজে তাকে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে হয়। বেশির ভাগ সময় কিছুই। মেলে না, তবু তৎপর তো হতেই হয়। পাড়ার বা সমাজের লোকের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহেও তার ভূমিকা থাকে। সর্বোপরি তার পেশা বা জীবিকা তাঁকে ব্যস্ত রাখে। কাজ যখন থাকে না কাজ দেওয়ার মালিকদের কাছে পাত্তা না-পেলেও পরিবারের দায়িত্ব থেকে তিনি রেহাই পান না। তখন নিজের এবং ঝে-ছেলেমেয়ের পেট ঠাণ্ডা রাখার চিন্তায় মাথাটা তার গরম হয়ে থাকে।
এইসব ব্যস্ততা, তৎপরতা ও কাজ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, চিন্তা ও দুশ্চিন্তা এবং উদ্বেগ ও উত্তেজনা নিয়ে নিরক্ষর ও কপর্দকশূন্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী একজন আস্ত মানুষ। আস্ত একজন। মানুষ কখনো সংস্কৃতিশূন্য জীবনযাপন করতে পারে না। যার চিন্তাভাবনা আছে, দুঃখ শোক, আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ-বিরক্তি ও ক্ষোভপ্রকাশের জন্য যিনি ভাষা ব্যবহার করতে পারেন সংস্কৃতিচর্চা না-করে তার উপায় নাই। তার সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে পরিচিত হতে না পারলে তাকে অন্তরঙ্গভাবে চেনা খুব কঠিন, অসম্ভব বললেও চলে। কিন্তু শিক্ষিত বামপন্থি বেশির ভাগ সময় ব্যাপারটি খেয়াল করেন না। তারা মনে করেন যে, সংস্কৃতিচর্চা সীমাবদ্ধ কেবল মধ্যবিত্তের মধ্যে। বর্তমান সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলবার পক্ষে একটি প্রধান যুক্তি হল এই যে, সমাজের অধিকাংশ মানুষ কেবল খাওয়া-পরা থেকে বঞ্চিত নন, সংস্কৃতিশূন্য একটি জীবনযাপন করতে তারা বাধ্য হচ্ছেন।
একথা ঠিক যে, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চায় বিকাশ ঘটছে না, একটি বিশেষ পর্যায়ে এসে তার বিবর্তন প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। দারিদ্র্য যেমন শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁদের একই মানের জীবনযাপন করতে বাধ্য করে, সংস্কৃতিচর্চাও তাদের একটি পর্যায়ে থেকে নতুন ধাপে উঠতে হোঁচট খাচ্ছে। কিন্তু নিম্নমানের জীবনযাপন সত্ত্বেও জীবনধারণ তো আটকে থাকে না, যে-করে হোক তারা বাঁচেন। তেমনি যে-মানেরই হোক বা একই জায়গায় স্থির হয়ে থাকুক, নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিচর্চা তার জীবনে অনুপস্থিত নয়। বরং এই সংস্কৃতিচর্চা তার জীবনের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত, বাঁচার জন্য এটা তার জীবনে অপরিহার্য।
পক্ষান্তরে, মধ্যবিত্তের সংগঠিত সংস্কৃতিচর্চা অনেকটাই শৌখিন। এখানে কবি বা শিল্পীর কথা বলা হচ্ছে না। একজন যথার্থ কবি কী গায়ক কী চিত্রশিল্পী কী অভিনেতা কী চলচ্চিত্রকার তার সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে উত্তীর্ণ করেন শিল্পে। সৎ ও নিষ্ঠাবান শিল্পী তার শিল্পচর্চার মাধ্যমে মধ্যবিত্ত সংকীর্ণতা ও আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে ফেলার সাধন করে। যান। সেটা মধ্যবিত্ত প্লানি ও ক্লেদ প্রকাশের মধ্যেও হতে পারে, নতুন সুস্থ জীবনের। সম্ভাবনার দিকে ইঙ্গিত দিয়েও হতে পারে। কিন্তু গড়পড়তা মধ্যবিত্ত যে-সংস্কৃতিচর্চা করেন। তা তাঁর জীবিকা ও দৈনন্দিন জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পর্কহীন। একই ব্যক্তির মধ্যে যখন ধ্রুপদ সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, ডিসকো গান ও পপগানের প্রতি সমান ভক্তি দেখা যায় তখন বোঝা যায় যে সংগীত জিনিসটা তার ভেতরে ঢোকে না, গানের ব্যাপারে তার ভালোলাগা বলে কিছু নেই, এটার সাহায্যে সমাজে তিনি রুচিশীল ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হতে চান। সিক্স মিলিয়ন ডলার ম্যান বা বায়োনিক উওম্যান সিরিজের ছবি দেখার জন্য উগ্রীব ব্যক্তি একুশে ফেব্রুয়ারি কী পয়লা বৈশাখে কারুকাজ-করা-পাঞ্জাবি পরে বাংলা-প্রেম দেখাতে বের হন। অর্থাৎ, কোনোটাই তার স্বভাবের অন্তর্গত হতে পারেনি। কুলা, শিকা বা শীতলপাটি দিয়ে একজন আমলা কী ইঞ্জিনিয়ার কী অধ্যাপকের ড্রয়িংরুম সাজানো হলে বোঝা যায় যে তাঁর জীবিকার সঙ্গে সম্পর্কহীন এইসব বন্ধু তার কাছে গৃহসজ্জার অতিরিক্ত কোনো মূল্য বহন করে না।
নিম্নবিত্ত শ্রমজ্জীবীর সংস্কৃতিচর্চার উৎস হল তাঁর জীবিকা। তার শ্রমের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন বলে তার সংস্কৃতিকে উপরিকাঠামোর পর্যায়ে ফেললে ভুল করা হবে। সংস্কৃতিচর্চা তাঁর কাছে কেবল মনোরঞ্জনের ব্যাপার নয়। কৃষক যখন গান করেন তখন মন হালকা করার উদ্দেশ্যে। করেন না। পান না-করলে তাঁর শ্রম অব্যাহত রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় বলেই তাকে গাইতে হয়। শরীরের সঙ্গে গানও তাকে জমিতে খাটতে সাহায্য করে। মাঝির গান তার নৌকা বাইবার প্রেরণা। শুধু প্রেরণা বললে কম বলা হয়। উত্তাল নদী অতিক্রম করার জন্য। তার হাত দুটোর সঙ্গে গানের ভূমিকাও কম নয়। তার কাজের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সংগতি রেখে গানের বাণী ও সুর সৃষ্টি হয়েছে। এখানে তাকে কীর্তন কী রবীন্দ্রসংগীত কী নজরুলগীতি কী কাওয়ালি এমনকী ভাওয়াইয়া গাইতে হলেও নৌকা চালাবার কাজে তার বিঘ্ন ঘটবে। উত্তর বাংলার যে-মানুষ গোরুর গাড়ি চালিয়ে পাড়ি দেন বিশাল প্রান্তর, তার শরীরের শক্তি ভাওয়াইয়া। আধুনিক গান কী পপ তো দূরের কথা, ভাটিয়ালি গানও তাঁর জন্য অপ্রয়োজনীয় ও শৌখিন। ছাপেটার সময় শ্রমিক যে-গান করেন, ভারী কোনো জিনিস। ঠেলে তুলবার সময়কার গান থেকে তা আলাদা। উঠানে ধানঝাড়ার সময় চাষি মেয়েরা যে-গান করেন, কেঁকিতে ধান ভাবার সময় ঐ গান গাইতে গেলে তা ঐ সময় শিবের গীত। গাওয়ার মতো অপ্রাসঙ্গিক হবে। ‘ধান ভানতে শিবের গীত’ কথাটা মিছেমিছি প্রচলিত হয়নি।
শুধু গান নয়, নৌকার গলুই, লাঙলের জোয়াল, দায়ের ফলা, কাস্তের গা প্রভৃতি জায়গায় যেসব কারুকাজ করা হয় তার প্রত্যেকটির উৎস কিন্তু শ্রম, জীবিকার শ্রমকে সহজ করে তোলা। এইসব কারুকাজ মধ্যবিত্তসমাজের নামকরা শিল্পীর দ্বারা সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তসমাজে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য সৌন্দর্যটি। এমনকী অতিউৎসাহী বামপন্থি কোনো শিল্পী হয়তো কারুকাজের মধ্যে শ্রেণীসগ্রামের ছবি আঁকলেন। কিন্তু এর ফলে নানা ধরনের অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। নৌকার গলুইতে এই ছবি খোদাইয়ের ফলে গলুই অতিরিক্ত ভারী বা পাতলা হয়ে যেতে পারে, যার ফলে নৌকার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন নৌকা চালাতে মাঝি অসুবিধা বোধ করতে পারেন। দ্বিতীয়ত, কারুকাজের মান ও নৈপুণ্য উন্নত হলেও মাঝির জীবিকার সঙ্গে তার সম্পর্ক না-থাকায় শ্রমসম্পাদনে তা তার কোনো কাজেই লাগবে না। তা হলে দুদিন পর এই কারুকাজের ব্যবহার উঠে যেতে বাধ্য।
ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর বৈশিষ্ট্য মনোযোগর সঙ্গে লক্ষ করা দরকার। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোতে প্রধানত আঞ্চলিক ভাষাই ব্যবহার করা হয়, এমনকী বড় শহরগুলোতেও এর ব্যতিক্রম তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর ভাষা তো অবশ্যই আঞ্চলিক। কিন্তু মধ্যবিত্তের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে তার পার্থক্য অনেক। যতই দিন যাচ্ছে মধ্যবিত্তের শিক্ষা ও চির পরিবর্তনের সঙ্গে এই পার্থক্য ততই প্রকট হয়ে উঠছে। বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ মধ্যবিত্তের প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে গ্রামের এমনকী শহরের নিম্নবিত্তের প্রকাশভঙ্গি অনেকটা আলাদা।
নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীদের কথায় প্রবাদ ও উপমা ব্যবহার করার প্রবণতা অনেক বেশি। প্রবাদ, শ্লোক, ছড়া, আর্যা ও উপমার সাহায্যে তারা নিজেদের বাক্য অলংকৃত ও আকর্ষণীয়। করে তোলেন। সরাসরি সরলবাক্য দিয়েও বক্তব্য প্রকাশ করা চলে, কিন্তু প্রবাদ-শ্লোক-ছড়া-উপমা প্রভৃতি বক্তব্যকে একই সঙ্গে তীব্র ও আকর্ষণীয় করে। মধ্যবিত্তের চির সঙ্গে। এসব প্রায়ই খাপ খায় না, তাদের কাছে এইসব প্রবাদ বা শ্লোক বা ছড়া, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাচনভঙ্গি পর্যন্ত অশ্লীল বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু এই প্রকাশ তাদের জীবনযাপন ও চেতনার এত গভীর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে যে শ্রমজীবীদের কাছে এসবের গীল অশ্লীলতার প্রশ্নটি একেবারে গৌণ। আর মধ্যবিত্তের রুচিরও বলিহারি! টিভি ও সিনেমায় অভিনয়ের নামে স্বদেশি-বিদেশি মেয়ে-পুরুষদের চোখমুখ ও কণ্ঠের ন্যাকামি ও স্থাবলামি দেখে এরা অভিভূত, আর নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর মুখের ভাষা গুনে এদের কান একেবারে লাল হয়ে ওঠে। বুদ্ধিজীবীরা সেখানে ব্রাহ্মসমাজসুলত সুরুচি ও সুনীতির বচনে মুখর। এইসব ব্যাপারে বামপন্থি বুদ্ধিজীবীরাও শুচিবায়ুগ্রস্ত। শ্রমজীবীর জীবনযাপনের সঙ্গে তার ভাষা সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাজার হাজার বছর ধরে প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলে আবেগ অনুভূতির রাখোটাকো-মার্কা প্রকাশ তাদের স্বভাবের বাইরে। তাদের প্রেম-ভালোবাসা বা স্নেহ-বাসল্যের প্রকাশের ভাষাও মধ্যবত্তিসুলত তুলতুল মার্কা মিষ্টি হতে পারে না। ভাষাকে তারা অলংকৃত করেন, কিন্তু সঁতসেঁতে করেন না। নিরক্ষর শ্রমজীবীর হাতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না হওয়া সম্ভব নয়। ভাষায় অলংকার ব্যবহার করে এঁরা সাহিত্যচর্চার ক্ষুধা মেটান। এতে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না, কিন্তু এটা তাদের সংস্কৃতিচর্চার অংশ।
লেখক ও শিল্পীর হাতে নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতি উঁচুদরের শিল্পে পরিণত হয়। উত্তর। ভারতের লোকগীতির সুর বড় বড় শিল্পীর হাতে বিবর্তিত হয়ে রাগ-রাগিণীর পর্যায়ে উঠেছে। লোকের মুখেমুখে প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলো। আধুনিক কালে শিল্প ঠিক প্রাকৃতিক নিয়মে গড়ে ওঠে না, শিল্পীর সচেতন ভাবনা ও তৎপরতার ফল আধুনিক শিল্প-সাহিত্য। বিটোফেন, ভাগনার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য সংগীতরচয়িতার শিল্পকর্মের উৎস হল ইউরোপের গ্রামের প্রকৃতি, গ্রামের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি। এঁদের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহ সচেতন প্রয়াসের ফল।
শ্রমজীবীর কাজের মধ্যে যে-ছন্দ ও গতি, নৃত্যে তারই মার্জিত ও সংগঠিত রূপ হল তাল ও মুদ্রা। শুধু তা-ই নয়, এই ছন্দ ও গতিকে একজন যথার্থ শিল্পী মানুষের মনোরঞ্জনে সীমাবদ্ধ রাখেন না। এর সাহায্যে তিনি তার উপলব্ধি ও বক্তব্যকে জ্ঞাপন করেন। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতি শিল্পীর হাতে নতুন ব্যঞ্জনা পায়, এই সংস্কৃতি শিল্পে উত্তীর্ণ হয়ে সর্বজনীনতা লাভ করে। শ্রমজীবীর ব্যবহৃত গান ও ছড়া, প্রবাদ বা প্রবচনকে লেখক উঁচুস্তরের চিন্তাপ্রকাশের জন্য ব্যবহার করে তাকে নতুন মাত্রা দেন। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চায় এরকম পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে। মধ্যবিত্তের সৃষ্টিতে শ্রমজীবীর জীবন আজকাল প্রায়ই পাওয়া যায়। বাংলা নাটক ও চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে নিম্নবিত্তের জীবন প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তাদের সাংস্কৃতিক জীবন সংগঠিত শিল্প-সাহিত্যে অনুপস্থিত বললেই চলে। যেটুকু আছে বাংলা ভাষার বিশাল ও সমৃদ্ধ সাহিত্য ও ব্যাপক সংস্কৃতিচর্চার তুলনায় তা একেবারেই কম ও তাৎপর্যহীন।
কয়েকটি সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের উপজীব্য নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী সম্প্রদায়। এদের দাবি ও বঞ্চনার কথাও কারও কারও লেখায় সার্থকভাবে এসেছে। কবিতায় নিম্নবিত্তের শোষণ ও শোষণমুক্তির সংগ্রামে অংশ নেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়েছে। এইসব সাহিত্য ও শিল্পকর্ম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অনেক ছেলেকে উদ্বুদ্ধ করেছে মধ্যবিত্ত সংস্কার ও খাটো বাসনা ঝেড়ে ফেলে বামপন্থি রাজনীতির বন্ধুর পথে তাঁদের পদচারণা ঘটেছে। কিন্তু ঐসব সাহিত্য ও শিল্পকর্মে নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয় না। তা হলে এসব ক্ষেত্রে প্রতিফলিত নিম্নবিত্তের জীবনকে স্থিরচিত্রের বেশি মর্যাদা দিই কী করে? শ্রমজীবীর জীবনযাপন, তাঁর ভুলভাল বা ঠিকঠাক বিশ্বাস, তার সংস্কার ও কুসংস্কার, তার পছন্দ-অপছন্দ, তার রুচি, তার ভাষা ও প্রকাশ, তার শক্তি ও দুর্বলতা, তার ভালোবাসা ও হিংসা–এসব নিয়েই তো তার সংস্কৃতিচর্চা, তার সংস্কৃতির এই পরিচয় বাংলা সাহিত্যে কোথায়?
সাম্প্রতিককালে আফ্রিকান উপন্যাসে আমরা অন্যরকম দৃষ্টান্ত পাই। নাইজিরীয় লেখক চিনুয়া আটিবির উপন্যাসে নাইজিরিয়ার গ্রাম্যজীবনের গভীর ভেতরে ঢোকার সফল প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। সেখানকার মানুষের জীবনযাপনের পরিচয় তো আছেই, উপরন্তু সেই জীবনযাপন জীবন্ত হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার প্রবাদ-প্রবচন, শ্লোক এবং তাদের বিশ্বাস ও সন্দেহ, সংস্কার ও কুসংস্কারের অপূর্ব ব্যবহারের ফলে। এই উপন্যাসগুলো ইংরেজিতে লেখা। অথচ সম্পূর্ণ আলাদা–সবদিক থেকেই আলাদা–ভিন্ন মহাদেশীয়, ভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন করি, ভিন্ন সংস্কৃতির একটি ভাষায় নাইজিরিয় সংস্কৃতি উঠে এসেছে তার অস্থিমজ্জা নিয়ে। এখানে ব্যবহৃত অনেক কথা ও প্রবাদ, ফী ছড়া ও শ্লোক, ইংরেজি কী পাশ্চাত্য এমনকী আধুনিক মধ্যবিত্ত বাঙালি রুচি অনুসারে অশ্লীল ও স্থূল। কিন্তু নাইজিরিয়ার পাশ্চাত্য শিক্ষাবর্জিত গ্রাম্য মানুষের সর্বাঙ্গীণ ও জীবও কপায়ণের জন্য লেখক সেগুলোকে তুলে এনেছেন অপরিবর্তিত অবস্থায় এবং একই সঙ্গে তাকে নতুন মাত্রা দিয়ে তাকে তার উন্নত দার্শনিক চিন্তার বাহনে পরিণত করেছেন।
চিনুয়া আচিবির মানের লেখক বাংলা সাহিত্যেও পাওয়া যাবে, দক্ষতা ও নৈপুণ্য তাদের কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু গল্পের জায়গাজমি ও মানুষের জন্য যে-মুরীদবোধ ও দায়িত্ববোধ নাইজিরীয় লেখককে উপন্যাসনায় উদ্বুদ্ধ করে তার শোচনীয় অভাবে মাতৃভাষায় লিখেও আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ বাংলা ভাষার প্রবাদ প্রবচন, শ্লোক, হড়া এবং সামগ্রিকতাবে লোকসংস্কৃতির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারেন না।
এর মানে কিন্তু এ নয় যে লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যে প্রদর্শনী ও আলোচনায় কিছুমাত্র ভাটা পড়েছে। ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, কীর্তন ও বাউলের জনপ্রিয়তা শহরের মধ্যবিত্তের মধ্যেও খুব লক্ষ করা যাচ্ছে। মেলা বড় বড় প্রতিষ্ঠান ও পতি অধ্যাপকগণ লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির সগ্রহ ও সংরক্ষণে অত্যন্ত উৎপর। এতে আপত্তির কী আছে? এর সাহায্যে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যদি গ্রামবাসী নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতির সামান্যতম অংশের পরিচয় পান তো তাতে পরস্পরের ব্যবধান কমে আসে। কিন্তু সেরকম পরিচয় তো মার্কিন কোটিপতিদের সজির সঙ্গে প্রত্যেক দিনই ঘটছে টেলিভিশনের পর্দায় দিকে একটু কষ্ট করে তাকালেই চোখ ভরে সেই সতিচর্চা দেখা যায়। আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সংস্কৃতি আমাদের কাছে আজ কেবল প্রদর্শনীর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সঙ্গতি যদি আধুনিক ডিঙ্গিসম্পন্ন শিল্পীর হাতে নতুন ব্যঞ্জনা না-পায়, তার শিল্পকর্মে শিল্পী যদি এর নতুন মাত্রা দিতে না-পারেন, আধুনিক শিল্পী ও লেখক যদি সেমিনারে-সেমিনারে তাকে প্রশংসাই করে চলেন, কিন্তু নিজের শিল্পচর্চাকে তার থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে দেন তো নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতির প্রাণশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং তার বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। এবং একই সঙ্গে মধ্যবিত্তের আধুনিক শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা দেশের সংস্কৃতিচর্চার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয় উদ্ভব ও নিষ্প্রাণ ব্যায়ামে।
নিষ্ঠাবান শিল্পী এবং বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সংস্কৃতিকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনবেন কী উপায়ে? নিম্নবিত্ত শ্রমজীবীর সঙ্গে কেবল মেলামেশা করলেই এই পরিচয় সম্পন্ন হয় না, মানুষের প্রতি গভীর মর্যাদবোধ–কেবল ভালোবাসা নয়–জাতীয় মর্যাদাবোধই তাকে উদ্ভুদ্ধ করবে শ্রমজীবীর সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে।
বুদ্ধিজীবী ও বামপন্থি রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেই, বোধহয় অধিকাংশই, মানুষের প্রতি এই মর্যাদাবোধের পরিচয় দেননি। দফায়-দফায় বন্দুকের মাথায় যারা ক্ষমতায় আসে তারা হল পেশাদার খুনি। মানুষ তাদের কাছে চমৎকার গেম, শিকার-মাত্র। পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদদের কাছে শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র পরিচয় ভোটার হিসাবে। ছলে-বলে কৌশলে মহামূল্যবান ভোটটি নিংড়ে নিয়ে পার্লামেন্টারি রাজনীতিবিদ শ্রমজীবী নিম্নবিত্তকে ছিবড়ের মতো ছুঁড়ে ফেলেন। বামপন্থি রাজনীতিবিদের কাছে শ্রমজীবী মানুষ হল আন্দোলনের হাতিয়ার। তাঁকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারলেই বামপন্থি রাৰ্জনীতিবিদদের অনেকেই নিজেদের সফল বিপ্লবী ভাবেন। কিন্তু বামপন্থি রাজনৈতিক আন্দোলন তো পরিচালিত হয় শ্রমজীবীর শাসনপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। তা হলে তাদের কেবল হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার অধিকার রাজনীতিবিদরা পান কোত্থেকে শ্রমজীবীকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়ে বামপন্থি রাজনীতিবিদদের মাঠে নামবার আর দরকার নেই। শ্রমজীবীর প্রতি মর্যাদাবোখ না-থাকলে বামপন্থি আন্দোলন চালাবার উৎসাহ কি শেষ পর্যন্ত টেকে? বরং তাদের প্রতি এই মর্যাদাবোধ নিয়ে এলিয়ে এলে বামপন্থি রাজনীতিবিদ বা কর্মী ইতিহাসের সকল ধারায় নিজেকে প্রয়োগ করার সুযোগ লাভ করবেন। মানুষ শুধু ইতিহাসের উপাদান নয়। কিংবা কোনো তত্ত্বপ্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ কেবল প্রয়োজনীয় উপকরণমাত্র নয়। শ্রমজীবী মানুষ ইতিহাসের নির্মাতা। তাঁদের জীবনযাপনকে তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না এবং শ্রমজীবীর জীবনযাপন ও সংস্কৃতিচর্চার মধ্যে জীবনের গভীর সত্যকে অনুসন্ধানের ভেতর শিল্পচর্চার অর্ধময়তা নির করে। তরে ভেতর যে-সত্য আছে, তাও উন্মোচিত হবে এই অনুসন্ধানের ফলেই। শিল্পসাহিত্যে প্রমাণ করার কোনো বিষয় থাকে না, অনুসন্ধান ও সিদ্ধান্তু সেখানে পাশাপাশি চলে, পরস্পরের সঙ্গে তারা সংলগ্ন, একটি থেকে আরেকটিকে ছিঁড়ে দেখানো চলে না। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে শিল্পী যদি বিন্নি হল তো এই অনুসন্ধানে তাৎপর্যময় মাত্রা থাকে না, এটা ক্রমেই নিস্তেজ ও পানসে অভ্যাসে পরিণত হয়। শিল্পচর্চার প্রাণ ও গতিরক্ষার জন্য এই বিচ্ছিন্নতা দূর করা একেবারে অপরিহার্য, নইলে মধ্যবিত্তের শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা তো বটেই তার গোটা জীবনযাপন ভিত্তিহীন ও শূন্যতার ওপর এমনভাবে ঝুলবে যে তাকে সংস্কৃতিচর্চা এবং জীবনযাপনের ক্যারিকেচার বলে শনাক্ত করতে হবে।
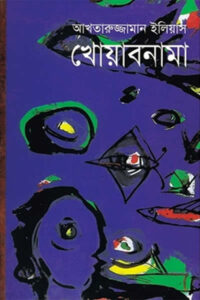




Leave a Reply