শাশ্বত বঙ্গ – কাজী আবদুল ওদুদ
শাশ্বত বঙ্গ – কাজী আবদুল ওদুদ
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা প্রয়োজনীয় নতুন বইয়ের প্রকাশ ও দুপ্রাপ্য পুরানো বইয়ের পুনর্মুদ্রণের যে কর্মসূচি নিয়েছে তারই অংশ হিসেবে কাজী আবদুল ওদুদের ‘শাশ্বত বঙ্গ’ বইটির পুনর্মুদ্রণ করা হলো। সংস্থা উদ্যোগ নিয়েছে, কিন্তু এই পুনর্মুদ্রণের মূল কৃতিত্ব বাংলাদেশ রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট কমিটি (ব্র্যাক)-এর। এ ধরনের গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের এটিই প্রথম পদক্ষেপ, আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাই এবং তাদের ক্রমবর্ধমান সাফল্য কামনা করি।
‘শাশ্বত বঙ্গ’ বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৫১ সালে। এর দ্বিতীয় কোনো সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। এ বইয়ের নাম অনেকে শুনেছেন কিন্তু প্রথম মুদ্রণ বহু পূর্বেই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দরুণ পড়বার সুযোগ পাননি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কাজী আবদুল ওদুদ পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাঁর রচনাবলী সংগ্রহ করা বহু ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষেই সম্ভবপর হয়না। আমরা তাই আশা করবো যে, ‘শাশ্বত বঙ্গ’-র এই দ্বিতীয় মুদ্রণ বহু উৎসাহী ও কৌতূহলী পাঠকের প্রয়োজন মেটাবে।
বইটির গুরুত্ব একাধিক কারণে। প্রথম কথা এর ঐতিহাসিক মূল্য। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ঢাকায় ‘বুদ্ধির মুক্তি’ নামে যে একটি আন্দোলন হয়েছিল তরুণ অধ্যাপক ও ছাত্রদের, কাজী আবদুল ওদুদ ছিলেন তার প্রধান পুরুষ। বিচার-বুদ্ধিকে মুক্ত ও সবল করবার সেই প্রচেষ্টায় যে সকল চিন্তা ও বক্তব্য নিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ ও তাঁর সহকর্মীরা অগ্রসর হয়েছিলেন শ্বাশ্বত বঙ্গ’ তার একটি মূল্যবান দলিল।
সেই সংগে বইটি মূল্যবান তার প্রাতিস্বিক মূল্যে। এ বইতে কাজী আবদুল ওদুদ একজন উদারনৈতিক শিক্ষাবিদ, নিজের সমাজ ও সম্প্রদায়ের দৈন্য তাকে পীড়া দিয়েছে। পরিবেশের সংগে তার সম্পর্ক গভীর ভালোবাসার, ‘প্রেম’ তাঁর বক্তব্যের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। ‘শাশ্বত বঙ্গ’ তাই স্বাদেশিকতায় প্রাণবন্ত। কাজী আবদুল ওদুদের ‘শাশ্বত বঙ্গ’ কোনো অনৈতিহাসিক সোনার বাংলা নয়, দেশ নয় কোন আদর্শায়িত রূপকথার। বরঞ্চ এই বঙ্গে মানুষের জীবন দীনহীন ও সংস্কার পীড়িত। অনগ্রসরতার গ্লানি তার নিত্য সংগী। কিন্তু তবু দীনতাকেই একমাত্র সত্য বলে মানেন না ‘শাশ্বত বঙ্গের’ লেখক। তার বঙ্গ সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি যে আত্মজীবনী লিখছিলেন তার নাম দিয়েছিলেন একজন খাঁটিয়ে সাহিত্যিকের কথা। যে শ্রমে তিনি বিশ্বাস করতেন তা সৃজনশীল। তার বঙ্গ সৃষ্টিশীল বঙ্গ।
কাজী আবদুল ওদুদের স্বাদেশিকতায় কূপমণ্ডুকতা নেই। তিনি উনিশ শতকের ইউরোপীয় উদারনীতির ভক্ত। পশ্চিমের উন্নত চিন্তাকে তিনি গ্রহণ করতে চান। উনিশ শতকে বঙ্গদেশে একটি রেনেসাস সংঘটিত হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন, সেই নবজাগরণের আদর্শ মানুষ হচ্ছেন রামমোহন-তার দৃষ্টিতে। রামমোহনের উত্তেজনাবিহীন সাহসী যুক্তিবাদিতাকে অত্যন্ত উচ্চমূল্য দেন তিনি, তুলনায় এমনকি বঙ্কিমচন্দ্রের যে অংশ ভাবালু তাকে অবিশ্বাস করেন। রামমোহনের লেখার রীতির প্রতি অনুরাগ কাজী আবদুল ওদুদের নিজের রচনারীতির মধ্যেও প্রতিফলিত। তিনি কথা বলেন চিন্তা করে, আলো চান, আগুন চাননা।
কাজী আবদুল ওদুদ ছাত্র ছিলেন অর্থনীতির, কিন্তু তার আস্থা ছিল সাহিত্যে। বুদ্ধির মুক্তি’ মূলমন্ত্রের উদাতা : মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ সাহিত্যের চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন কোনো সৃষ্টি নয়। কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যবিচার নান্দনিক নয়; সাহিত্যকে তিনি বিচার করেন প্রধানত উপযোগিতা ও বক্তব্যের মূল্য দিয়েই।
আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যে কাজী আবদুল ওদুদের রচনার স্থান সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য এ বই পড়তে হয়, যেমন পড়তে হয় একটি চিন্তা উদ্রেককারী আনন্দঘন অভিজ্ঞতা লাভের জন্যও।
পুনর্মুদ্রিত শাশ্বত বঙ্গের পরিশিষ্ট হিসেবে আমরা কাজী আবদুল ওদুদের জীবনের একটি ঘটনাপঞ্জী ও তাঁর রচনাবলীর পরিচয় যোগ করেছি। এটি তৈরি করে দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর রহমান। তাঁকে ধন্যবাদ।
আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কাজী আবদুল ওদুদের জামাতা শামসুল হুদা ও তার কন্যা বেগম জেবুন্নিসার কাছে, যাদের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে এই বই পুনর্মুদ্রণ সম্ভবপর হতো না।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১০ আগস্ট, ১৯৮৩
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
কাজী আবদুল ওদুদ একজন মহৎপ্রাণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। যারা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তারা সবাই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপনা করেছেন, যারা তার ছাত্র ছিলেন তারা তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; ক্লাশ রুমের বাইরে যাঁরা তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা তাঁকে ভুলতে পারেন নি। জ্ঞানের প্রতি তার আগ্রহ ছিল গভীর ও সর্বজনবিদিত। আবার তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল যেমন আকর্ষণীয় তেমনি দৃঢ়। চাকরির উন্নতির জন্য তিনি নিজে কোনো চেষ্টা করেন নি, উল্টো তার উন্নতি হচ্ছে না দেখে অন্যরা বিব্রত হয়েছেন। আবদুল ওদুদের কথা ও কাজের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। পাকিস্তানে তিনি বিশ্বাস করতেন না, তাই শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। অন্যরা চলে এসেছেন, তিনি আসেন নি। অথচ বাড়ি তার পূর্ববঙ্গেই। বন্ধুবান্ধবদেরও অধিকাংশই ঢাকাতেই থাকতেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগদানের জন্য প্রস্তাবও পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অনড় ছিলেন তাঁর অবস্থানে। দেশভাগের পর কলকাতাতে তাঁর অবস্থান সুখের হয় নি, এমন কি তাকে পাকিস্তানের চর বলেও সন্দেহ করা হয়েছে, একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গে সরকারের চাকরি ছেড়ে দিতে চেয়েছেন, পরে সহকর্মীদের অনুরোধে নিবৃত্ত হয়েছেন, কিন্তু এ নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। তার ভেতর হীনমন্যতা বোধের বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখা যায় নি। দাপটের সঙ্গে নিজেকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিতেন; মুসলমান সমাজের দুর্দশায় অত্যন্ত কাতর ছিলেন, প্রতিকারের জন্য লিখতেন; অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অগ্রসর মানুষদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। আচরণে ছিলেন তুলনাবিহীনভাবে ভদ্র এবং সবদিক দিয়ে অত্যন্ত সংস্কৃতিবান। তবে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার সাহিত্যচর্চার জন্যই। নিজের পরিচয়ও তিনি সাহিত্যিক হিসেবেই দিতেন। তাঁর আত্মপ্রকাশ কথাসাহিত্য রচনার পথেই। প্রথম বই ছোটগল্পের সংকলন ‘মীরপরিবার প্রকাশিত হয় তার ছাত্রাবস্থাতে। দ্বিতীয় প্রকাশনা
নদীবক্ষে’ নামে উপন্যাস, যেটি সমাদৃত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ যার প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তীতে উপন্যাস, নাটক, এমন কি কবিতাও লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রবন্ধকেই তার মত ও মেধা প্রকাশের বাহন হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তার মতো সুন্দর প্রবন্ধ তাঁর কালে অন্যকোনো মুসলমান লেখক লেখেন নি। কাজী আবদুল ওদুদ সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন পূর্বপ্রস্তুতি নিয়েই। তাঁর ভাষারীতি একেবারে নিজস্ব, যুক্তিসমৃদ্ধ এবং প্রবহমান। যে রামমোহন রায়কে তিনি আদর্শ মনে করতেন, তিনি পর্যন্ত কখনো
কখনো উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন, কিন্তু আবদুল ওদুদ সবসময়েই ছিলেন সংযতবাক। তার প্রবন্ধ পাঠ করা সাহিত্য পাঠের মতোই আনন্দদায়ক। শাশ্বত বঙ্গ’ তাঁর প্রবন্ধ সঙ্কলন। এটি পড়তে গেলে মনে হয় উপন্যাস পড়ছি। রচনায় আড়ম্বর নেই, মেদবাহুল্যের প্রশ্নই ওঠে না, আবার আড়ষ্ট নন তিনি কখনোই। ছাত্র ছিলেন রাজনৈতিক অর্থনীতির, এমএ ডিগ্রি ওই বিষয়েই, কিন্তু কর্মজীবনের একেবারে শুরুতেই নিযুক্তি যে পেলেন সরকারি কলেজের বাংলার প্রভাষক হিসেবে সেটা সাহিত্যরচনার ফলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন বলেই। সত্য বটে পদটি একজন মুসলমান প্রার্থীর জন্যই সংরক্ষিত রাখা ছিল, তার কারণ ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গরদের ‘সান্ত্বনা হিসেবে মুসলমানদেরকে কনসেশন দিচ্ছিল যার বড় নিদর্শন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, এবং এটাও মিথ্যা নয় যে, বাংলা সাহিত্যে এমএ পাশ করা কোনো যোগ্যপ্রার্থী তখন পাওয়া যায় নি। তবু মানতেই হবে যে, রাজনৈতিক অর্থনীতির এমএ কাজী আবদুল ওদুদ যে বাংলার প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন সেটি তার সাহিত্যচর্চার কারণেই। সাহিত্যই ছিল তার প্রধান আগ্রহের বিষয় এবং তার কর্মজীবনের সবটা জুড়েই তিনি নিয়োজিত ছিলেন সাহিত্যচর্চায়। অন্যদিকে সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তিনি তার অসাধারণত্বের যে প্রমাণ দিয়েছেন, তা কেবল তাঁর ছাত্রদের স্বীকৃতিতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতেও সেটি উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। নিজের সাহিত্যিক পরিচয় সম্পর্কে আবদুল ওদুদ লিখেছেন এভাবে, ‘আমি সাহিত্যিক। জনতায় বাসা বাধা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। থাকি জনতা থেকে দূরে। কিন্তু তাই বলে সম্পর্কশূন্য নই জনতার সঙ্গে। তাকিয়ে আছি জনতার দিকে, কেননা মানুষকে ভালবাসা আমার ধর্ম।’ (মহৎ সংবাদ’) এটি লিখেছেন ১৯৪৭-এ, ততদিনে দেশ ভাগ হয়ে গেছে। এই বক্তব্যে তিনি নিজেকে কীভাবে দেখেছেন সেটা বোঝা যায়। তিনি সাহিত্যিক, জনতা থেকে দূরে থাকেন, কিন্তু জনতার সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে। কারণ মানুষকে ভালবাসাই তার ধর্ম। এই ভালবাসার ব্যাপারটা আমরা তাঁর ভেতর সবসময়েই দেখতে পাই। মানুষকে, বিশেষভাবে নিজের দুঃস্থ ও ব্যধিগ্রস্ত মুসলমান সমাজকে তিনি ভালবাসেন। কিন্তু জনতা থেকে কিছুটা দূরে থাকেন, কেননা চরিত্রগত ভাবেই জনতা হচ্ছে অস্থির, উদ্ধৃঙ্খল। তারা আবেগের বশে চলে। তিনি নিজে চালিত হতে চান বুদ্ধির দ্বারা। ঢাকাতে তারা যে বুদ্ধির মুক্তির একটি গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন তাদের বক্তব্য ছিল, ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।’ জ্ঞান, বুদ্ধি, মুক্তি এগুলোই ছিল আগ্রহ ও বিবেচনার বিষয়। ওই যে বললেন মানুষকে ভালবাসাই তাঁর ধর্ম সেটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ; তাঁর সকল রচনাই ওই ভালবাসার ফল। আর ‘ধর্ম’ কথাটি যে ব্যবহার করেছেন সেটাও তাৎপর্যহীন নয়। এ বিষয়ে আমাদেরকে পরে আবার ফিরে আসতে হবে।
বুদ্ধির চর্চাকে তিনি যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন তাতে তাঁকে বুদ্ধিজীবী বলতে আগ্রহ জন্মে। বুদ্ধিজীবী তারাই যারা পৃথিবীটাকে নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে বুঝতে চান, সেই উপলব্ধিকে অন্যদের ভেতর সংক্রমিত করতে সচেষ্ট থাকেন, এবং পৃথিবীটাকে বদলাবার ব্যাপারে আগ্রহী হন। এসব গুণ কাজী আবদুল ওদুদের ভেতর প্রচুর পরিমাণে ছিল, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে তাঁর অবস্থানটা যতটা না বুদ্ধিজীবীর তার চেয়ে বেশি একজন চিকিৎসকের। সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত, সমাজের চিকিৎসা প্রয়োজন, চিকিৎসার কাজটি করতে তিনি আগ্রহী, মানুষের প্রতি ভালবাসার টানে। চিকিৎসকের দু’টি দায়িত্ব থাকে। এক, সঠিকভাবে রোগনির্ণয়; দুই, নিরাময়ের জন্য ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। আবদুল ওদুদ উভয় দায়িত্বই পালন করেছেন। মুসলমান সমাজের ব্যধির উৎস তিনি বিশেষভাবে দেখেছেন অন্ধ শাস্ত্রানুগত্য ও সংস্কারে, যে জন্য তিনি জ্ঞানের চর্চা ও বুদ্ধির মুক্তিকে নিরাময়ের উপায় বলে গণ্য করেছেন। তার এই রোগনিরূপণ ও নিরাময় ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে আমাদের বলবার থাকবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এবং আমরাও মানতে বাধ্য যে, কাজী আবদুল ওদুদদের চিকিৎসা কার্যকর হয় নি, রোগের নিরাময় ঘটে নি। এর প্রধান কারণ রোগটা ছিল আরো গভীরে। আর তার জন্য প্রধানত দায়ী ছিল রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা। পরাধীন ভারতের মানুষের জন্য প্রধান দ্বন্দ্বটা ছিল রাষ্ট্রের সঙ্গে। রাষ্ট্র ছিল শত্রুপক্ষ। রাজনৈতিক অর্থনীতির ছাত্র ও ইতিহাসের পাঠে উৎসাহী আবদুল ওদুদ সেটা যে দেখেন নি তা নয়, কিন্তু সেটিকে বড় সমস্যা বলে মনে করেন নি। দেশের মানুষের জীবনে প্রধান সমস্যাটা ছিল অর্থনৈতিক, সে সমস্যা সৃষ্ট হচ্ছিল রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে। এই বাস্তবতাটাকে মেনে না নিয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন মানুষের মনের মুক্তির ওপর। মনের মুক্তি তো অবশ্যই দরকার। কিন্তু যে-মানুষ অভাবগ্রস্ত, দাঁড়াবার জন্য যার স্থানের অসঙ্কুলান, তার মন তো স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়ে থাকবে, ওই মনকে সে মুক্তই বা করবে কোন শক্তিতে। রোগের বড় কারণটিকে বিবেচনায় না নেওয়ার দরুন চিকিৎসা যথার্থ হয় নি; যদি নিতেন তা হলে তাঁর রচনা ভিন্নধর্মী হতো, এবং তাদের আবেদন ও প্রভাব দুটোই গভীরতা পেতো। তেমনটা যে ঘটে নি তা তিনি নিজেই দেখতে পেয়েছেন। ১৯৪৫-এ লিখিত ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ প্রবন্ধে ওদুদ নিজেদের সংগঠন মুসলিম সাহিত্য সমাজের কাজ সম্পর্কে লিখেছেন,
কিন্তু অচিরে এর প্রতি বিরোধিতা এত প্রবল হলো যে যোগ্যভাবে কাজ করবার সুযোগ এর লাভ হলো মাত্র পাঁচ বছরের জন্য। […] ব্যাপক ভাবে ওঁদের ‘বুদ্ধির মুক্তি’র মন্ত্রের পরিবর্তে বাংলার মুসলমান সমাজ নিতে চাচ্ছে আত্মনিয়ন্ত্রণের মন্ত্র।
যাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের মন্ত্র বলছেন সেটা আসলে স্বাধীনতার দাবি। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা জরুরি ছিল বৈকি, নইলে মানুষ তার অবস্থার উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ নেবে কী করে? সংগঠন যেমন জনপ্রিয় হয় নি, আবদুল ওদুদদের লেখাও প্রত্যাশিত জনপ্রিয়তা পায় নি। ‘শাশ্বত বঙ্গ’ তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সঙ্কলন, এতে তার স্বনির্বাচিত প্রবন্ধ, ভাষণ, অভিভাষণ, চিঠি, এমন কি কবিতাও স্থান পেয়েছে, কিন্তু অনুমান করা যায় যে, দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে এ বইয়ের জন্য কলকাতায় কোনো প্রকাশক পাওয়া যায় নি, যে জন্য নিজস্ব উদ্যোগেই এটিকে প্রকাশ ব বতে হয়েছে, এবং ১৯৮৩’তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্যোগ নেওয়ার আগে এটি পুনর্মুদ্রিত হয় নি।
স্বাধীনতার কথা জাতীয়তাবাদীরা বলেছেন, শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষই স্বাধীনতার জন্য অস্থির ছিল, তর সইছিল না, তাদের হৃদয় ছিল উনুখ, জাতীয়তাবাদীদের উদ্দীপক আবেদনে তারা সাড়া দিয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা ছিল দুইভাগে বিভক্ত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ। বিভাজনটি সাম্প্রদায়িক রূপ নিয়েছে এবং পরিণতিতে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে গেছে।
সাম্প্রদায়িকরা ধর্মকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু ঘটনাটা মোটেই ধর্মীয় ছিল না। ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক। পেছনে ছিল ব্রিটিশের উস্কানি। ওদুদ কিন্তু সেটা মানতে চান নি। ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত ‘হিন্দু মুসলমানের বিরোধ’ নাম দিয়ে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বলেছেন যে হিন্দু-মুসলমান বিরোধটা নতুন নয়, ব্রিটিশের আগমনের আগেও সেটি ছিল, তাই এর জন্য ব্রিটিশের ঘাড়ে দায়চাপানোটা ঠিক নয়। তিনি জানতেন যে, একসময়ে রবীন্দ্রনাথেরও ওই ধারণা ছিল, কিন্তু তিনি দেখতে পাচ্ছেন,
সম্প্রতি তাঁর মতের পরিবর্তন হয়েছে মনে হয়। অন্তত তাঁর ‘রাশিয়ার পত্রে’ এই কথাই বিশেষভাবে বলা হয়েছে যে ভারতের সাম্প্রদায়িক বিরোধের জন্য মুখ্যত দায়ী ভারতবর্ষের শাসকবর্গ।
মনে হয় তিনি দুঃখিত হয়েছেন, যে জন্য বক্তৃতাকালে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতেই কথাটা বলেছেন, এবং অন্যমনস্কভাবে ‘রাশিয়ার চিঠি’কে ‘রাশিয়ার পত্র’ বলে ফেলেছেন।
ওদুদ ব্রিটিশকে দূষবেন না, ফলে ব্রিটিশ বিতাড়ন যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিরসন তথা জনগণের মুক্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় সেটা মানবেন না। এই অস্বচ্ছতার দরুন কি করে যে দুই সম্প্রদায়কে মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করা যাবে তার পথ তিনি খুঁজে পান না। পথ অবশ্য ছিল, সেটা হলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনকে বেগবান করা, যে কাজটা সমাজতন্ত্রীরা করতে চেয়েছেন, কিন্তু আবদুল ওদুদতো সমাজতন্ত্রী নন, বরং সমাজতন্ত্রীরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন তার ঘোরতর বিরোধী। পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে ব্যক্তির কাছে যেতে হয়, নির্ভর করতে হয় বিকাশধর্মীসেইসব মানুষের ওপর যারা ‘সমাজজীবনে অক্লান্তভাবে সৃষ্টিশীল’। ব্যক্তির ক্ষমতার ওপর এই আস্থাটা ছিল তাঁর চিন্তাধারার কেন্দ্রে অবস্থিত। বলাবাহুল্য, ব্যক্তির ভূমিকায় এই নির্ভরশীলতাটা কোনো সমাধান ছিল না। প্রয়োজন ছিল সঠিক ও সমষ্টিগত কাজের।
কাজী আবদুল ওদুদের লেখায় আমরা জ্ঞানবর্ধক ও চিন্তাউদ্রেককারী অনেক ধারণাই পাই, কিন্তু পাই না অতিপ্রয়োজনীয় সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা।
সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ধর্মনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেয় নি, দিতে পারে নি। কংগ্রেস যখন ভারতবর্ষকে এক জাতির দেশ বলেছে, মুসলিম লীগ তখন সন্দেহ করেছে যে ওই একজাতি হচ্ছে হিন্দু জাতি; ভয় পেয়ে মুসলিম লীগ দ্বি-জাতি তত্ত্বকে সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাদের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হবার প্রশ্নই ওঠে নি। দুঃখের ব্যাপার এটা যে কাজী আবদুল ওদুদের মতো অসাম্প্রদায়িকেরাও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গুরুত্ব দেন নি।
আবদুল ওদুদের লেখায় বরং ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার ধর্ম অবশ্য সাম্প্রদায়িক কুসংস্কারচ্ছন্নদের ধর্ম নয়, ধর্ম বলতে তিনি ধর্মবোধকে বুঝিয়েছেন; কিন্তু ধর্মের কথা বার বার বলতে গিয়ে তিনি নিজের জন্য এবং সমাজে যারা পরিবর্তন আনতে চান তাদের জন্যও দু’টি অসুবিধা তৈরি করেছেন। প্রথমত, ধর্মবোধ বা ধর্মভাব যে কীভাবে ধর্মীয় সংস্কার থেকে আলাদা সেটা পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে অসমর্থ। হয়েছেন, ফলে ধর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, তৎকালীন রাজনীতির পক্ষে যে-বুদ্ধিটা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মভাবকেই বা তিনি কেন অতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন তাও বোঝা যায় না। যেমন ‘জ্ঞান ও প্রেম’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন, ‘ধর্মের আনুষ্ঠানিক অংশ বাদ দিলে যাকে বলা যায় ধর্মভাব তাকে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দেওয়ার দরকার ছিল না, তাকে ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে যার যার ধর্মভাব তার তার বলে দিলেই ব্যাপারটা মঙ্গলজনক হতো। যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করি না কেন ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসের ব্যাপার, সেখানে যুক্তির প্রবেশ মোটামুটি নিষিদ্ধ, যারা যুক্তিতে আস্থাশীল তারা কেন ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওই ব্যাপারটাকে সমষ্টিগত স্বার্থের জগতে নিয়ে এসে বিরোধ সৃষ্টির সুযোগটাকে বাড়িয়ে দেবেন? তাছাড়া ধর্মভাব যে কী তাও কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি। যেমন এই প্রবন্ধেই তিনি লিখেছেন ধর্মভাবের অর্থ হচ্ছে। ‘জীবনকে গভীরভাবে নেওয়া, মানুষের বা জগতের প্রতি প্রেম-পরায়ণ হওয়া। এখানে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠবে ‘মানুষ বা জগৎ’ এই কথাটার মানে কি? মানুষ ও জগতের ভেতর পার্থক্যটা কোথায়? মানুষের জগৎ নিয়েই আমাদের সব কথাবার্তা, অন্যকারো জগৎ নিয়ে তো নয়, তা হলে ওই ‘বা’ শব্দটি আসে কেন?
দ্বিতীয়ত, ধর্ম নিয়ে যারা মাথা ঘামান না তারা কি জীবনকে গভীরভাবে নিতে বা মানুষের প্রতি প্রেমপরায়ণ হতে ব্যর্থ হয়েছেন? ব্যর্থ না হয়ে থাকলে ধর্মের ভাষায় কেন কথা বলা, কেন ধর্মকে এমনভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা? ধর্মের প্রসঙ্গ এলে মন্ত্রও আসে, এবং কাজী আবদুল ওদুদ নানা প্রসঙ্গে মন্ত্র’ শব্দটির ব্যবহার করেছেন, আদর্শের কথা বোঝাতে; যে-কাজটা, আবারো বলতে হয়, কেবল অপ্রয়োজনীয় নয়, বিপজ্জনকও বটে। মন্ত্র তো মুক্তবুদ্ধির অনুষঙ্গ নয়, অনুষঙ্গ অন্ধবিশ্বাসের। তাছাড়া ওই ধর্মবোধকে তিনি অতটাই বা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? যে জন্য বলছেন, জীবনের সার্থকতা, ধর্মবোধে, অর্থাৎ সত্যে অথবা কোনো আদর্শে সমর্পিতচিত্ততায়’? (হিন্দু মুসলমানের বিরোধ’)? ধর্মবোধ বলতে সত্যে বা কোনো আদর্শে সমর্পিতচিত্ততাই যদি বোঝায় তা হলে অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর ধর্মবোধকে টেনে না এনে সত্য ও আদর্শবোধের উল্লেখ করলেই তাঁর বক্তব্য অধিকতর স্পষ্ট হতো, এমন সম্ভাবনা। এটাও বলতে হয় যে, সত্যের কথা তিনি খুব জোর দিয়ে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে বলেছেন, কিন্তু সত্যের ভেতর যে আপেক্ষিকতা রয়েছে সেটা স্মরণে রাখেন নি। সেই অতিপরিচিত উপমাটি ব্যবহার করে তো বলা যায় যে, ঘোড়ার জন্য যা সত্য ঘোড়সওয়ারের জন্য তা সত্য নয়, কেননা তাদের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী। আর এটাও তো জিজ্ঞাস্য থাকে যে সত্য এবং কোনো আদর্শ সমার্থবোধক হয় কি করে? যে বাক্যটি ওপরে উদ্ধৃত করেছি সেটির পরপরই কাজী আবদুল ওদুদ যখন প্রশ্ন উত্থাপন করেন, প্রত্যেক ধর্ম-সম্প্রদায়কে মোহ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত-ধর্মপ্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই কি দেশের চিন্তাশীল ধর্মীদের শ্রেষ্ঠ কাজ নয়?’ জবাব হচ্ছে, মোটেই না। কেননা কোনটা মোহ কোনটাই বা প্রকৃত-ধর্মপ্রীতি ওঠা নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন। এবং সেটা যে কঠিন তা তো ওদুদ এবং তাঁর সহযোদ্ধা আবুল হুসেন মর্মান্তিক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রত্যক্ষ করেছেন। মওলানা আকরম খাঁর দল তাঁদেরকে নির্মম ভাষায় আক্রমণ করেছেন, এবং তাঁদের লেখা পড়ে মর্মোদ্ধার করা যাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, ঢাকার সেই জমিদার ও নবাবদের কাছে প্রমাণ করতে হয়েছে যে তারা কাফের নন, ধার্মিক মুসলমান বটে। এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যদি সমাজকে ইহজাগতিক এবং রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ করার ব্যাপারে সাহায্য করতেন, তা হলে ওই সাম্প্রদায়িক শক্তি হয়তো কিছুটা হলেও দুর্বল হতো, আর দেশভাগের বিয়োগান্ত ঘটানোর ব্যাপারে তারা যতটা শক্তি হারাতো ততটাই দেশবাসীর উপকার ঘটতো। ধর্মের বৃত্তের বাইরে না-গিয়ে তাঁরা তাঁদের নিজেদের ক্ষমতার কিছুটা হলেও অপচয় ঘটিয়েছেন, এবং কেবল নিজেদের জন্য নয় দেশবাসীর জন্যও বিপজ্জনক যে সাম্প্রদায়িক শক্তির দাপট বৃদ্ধি পাচ্ছিল নিজেদের অজান্তেই তাকে সাহায্য করেছেন।
দেখা যাচ্ছে যে, এমন কি সাহিত্যের ব্যাপারেও ওদুদ ধর্মকে নিয়ে আসতে অপছন্দ করেন না। সাহিত্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের যে যুদ্ধ তাকে তিনি বলতে চান ‘ধর্মযুদ্ধ’ (পরিবেশের সঙ্গে প্রেমের যোগ’)। যে-শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলতে দ্বিধা করেন নি, তাঁর সম্পর্কেও তিনি বলেন যে মানুষের অন্তরতম মাহাত্মে শরৎচন্দ্রের যে আস্থা সেটি তার ধর্ম বিশ্বাস’। (শরৎ-প্রতিভা’) যে-দেশটি আবদুল ওদুদের কাঙ্ক্ষিত সেখানে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না, এটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যোগ করেন যে, একান্ত বীভৎস না হলে কোনো সমাজেই ধর্মাচার অশ্রদ্ধেয় বিবেচিত হবে না। (সংস্কৃতি, কথা’) তা হলে কী ধরে নিতে হবে যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে তিনি কেবল পাশ কাটিয়েই যান না, রীতিমত সন্দেহের চোখে দেখেন? তিনি গান্ধীর নেতৃত্বে আস্থা রাখেন, যদিও নিজাম বক্তৃতা’তে তিনি স্বীকার না-করে পারেন না যে গান্ধী যে-ভাবে সবাইকে স্বধর্মে নিষ্ঠাবান হতে বলেছেন তাতে ‘প্রকৃত ধর্মভাব নয় ধর্মমোহই দেশে প্রবল হবার সুযোগ পেয়েছে, এবং মেনে নিয়েছেন এটাও যে, এ কালের বিবর্ধিত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের জন্য গান্ধী আংশিকভাবে হলেও দায়ী। তা হলে? রাজনীতিতে ধর্ম নিয়ে নাড়াচাড়া করাটা যে বিপজ্জনক সেটা তো বোঝা যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ইংরেজিতে যাকে সেকুলার রাষ্ট্র বলা হয় বাংলায় যে তাকে ইহজাগতিক না-বলে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ বলতে আমরা বাধ্য হচ্ছি তার কারণ একটাই, ধর্মকে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলার জাতীয়তাবাদী প্রবণতা। ইতিহাসের পাঠ ‘শাশ্বত বঙ্গে’র একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ। তিনি স্মরণ করেন যে, ইংরেজের ইতিহাসে পিউরিটান যুগ যে কেবল মানুষের সুকুমার বৃত্তির নির্যাতনের যুগই ছিল তা সত্য নয়, সেটি নবসৃষ্টির যুগও ছিল। প্রসঙ্গটা এসেছে আমাদের দেশের আলেমদের কাজকর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে গিয়ে। পিউরিটানরা বিশুদ্ধতাবাদী, আমাদের আলেমরাও তা-ই; কিন্তু আমাদের আলেমদের প্রচেষ্টা থেকে এমন একটা ফল আশা করা কতকটা বালির কাছ থেকে হে পদার্থ আশা করার মতো।’ (অভিভাষণ’) এ উক্তি অবশ্যই যথার্থ। কিন্তু এখানে সেটা বিবেচনায় আনা প্রয়োজন, এবং যা তিনি আনেন নি, সেটা হলো এই যে, পিউরিটানদের সৃষ্টিশীল কাজটা আপনা আপনি ঘটে নি, তার পেছনে ছিল ক্রমওয়েলের বিপ্লব, যা সাময়িকভাবে হলেও রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়েছিল, এবং যার ফলে রাজতন্ত্র পুরাতন চরিত্রে আর ফিরে আসে নি, দেশে বুর্জোয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। বুর্জোয়া গণতন্ত্র আর যাই হোক ধর্মনির্ভর নয়। পিউরিটান ধর্মের বিশুদ্ধতার চেয়ে অধিক সৃজনশীল ছিল পিউরিটানদের ওই রাষ্ট্র বিপ্লব।
বিপ্লবের ব্যাপারটাকে ধর্তব্যের মধ্যে মনে না-করার অবশ্য কারণ আছে, সেটা হলো বিপ্লবে ভয়। কেবল ভয় নয়, বিরোধিতাই আসলে। তরুণ আবদুল কাদিরের চিঠির জবাবে আবদুল ওদুদ তো স্পষ্ট করেই তার অবস্থানটি ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, বিপ্লব হলো মানুষের সমাজের এক ব্যাধি, সুতরাং মানুষের জন্য কাম্য নয়।’ বিপ্লব বলতে তিনি বোঝেন বিশৃঙ্খলা। তিনি আরো বলেন, বিপ্লবের মতো এক সর্বব্যাপী বুদ্ধিনাশের চর্চার ভিতর দিয়ে মানুষের সমাজের কোনো শ্রেয় লাভ হতে পারে এ-তত্ত্ব আমার জন্য বাস্তবিকই দুরধিগম্য। এবং
হিংসাকেই মানব-সমাজে কার্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন রূপে গণ্য করলে মানুষকে পশু ভিন্ন আর কিছু তেমন মনে করা হয় না। আর মানুষ যদি পশুই হয় তবে বিপ্লবের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান কিইবা প্রয়োজন। (‘বিপ্লব’)
এই বিপুবভীতিই তাঁকে গান্ধীর অহিংসা, সত্যাগ্রহ ও চরকার কাছে প্রেরণ করে, যদিও তিনি গান্ধী নেতৃত্বের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে যে অনবহিত তা নন। আমাদের স্মরণে আছে যে, চরকার অভিনবত্বে নজরুল ও শরৎচন্দ্র এক সময়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু চরকার ঘূর্ণিতে তাড়িত-হয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে পালাবে এমন বিশ্বাস তারা ধরে রাখতে পারেন নি। তুলনা সব সময়েই অপ্রীতিকর, তবু বলা যায় চরকা ঘুরিয়ে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন আর একাত্তরে আমরা অনেকেই যে মনে করছিলাম পাখি শিকারের বন্দুক দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের ট্যাঙ্ক ও কামানকে পরাভূত করবো সেই আশা খুব যে পরস্পর দূরবর্তী তা নয়।
কাজী আবদুল ওদুদ’রা আলো চান, প্রদীপ শিখাও তাদের কাম্য, কিন্তু তারা আগুনকে মোটেই বিশ্বাস করেন না। অথচ রাষ্ট্রীয় অবিচার ও সামাজিক বৈষম্যের আগুনে মানুষ তখনো দগ্ধ হয়েছে, এখনো হচ্ছে। মুক্তির জন্য নয়, ধ্বংস চাই সৃষ্টির প্রয়োজনে, তবে সে রকমের সৃষ্টি বিপ্লব ছাড়া কোনো দেশে আসেনি, যেমন আসেনি আমাদের দেশেও। ওই বিপ্লবের যথার্থ নাম সামাজিক বিপ্লব। যেটি ঘটেনি। আর ঘটেনি বলেই। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ব্রিটিশের অনুগত কংগ্রেস ও লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর মাত্র রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেনি। সমাজবিপ্লব তো অনেক দূরের কথা। সাতচল্লিশের পরে বাংলাদেশে আমরা স্বাধীনতা নয়, মুক্তির জন্য লড়েছি, কিন্তু মুক্তি আসেনি, কেননা সমাজবিপ্লব ঘটেনি। মুক্তি তো পরের ব্যাপার, যে-ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো, সেখানে এমন কি ধর্মনিরপেক্ষতাও রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে নি। এ ব্যাপারে বুদ্ধিজীবীরা আমাদেরকে সাহায্য করেন নি।
বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই শিক্ষিত মানুষদের জন্য লিখেছেন। আবদুল ওদুদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি; তার কথোপকথন ভদ্রলোকদের সঙ্গে, এবং ভদ্রলোকদের জন্যই, অশিক্ষিত সাধারণ মানুষের পক্ষে যারা সংগ্রাম করেন তাদের জন্য নয়। ফলে তাঁর লেখায় শ্রেণীর প্রসঙ্গ আসে কদাচিৎ। যে নদীবক্ষ’ উপন্যাসে তিনি একজন গরীব কৃষকের কথা লিখেছেন, সে-মানুষটি একটি ব্যক্তিই, তার শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়। অথচ শ্ৰেণীবৈষম্য ছিল সমাজে বিদ্যমান অর্থনৈতিক দৈন্যের প্রধান কারণ। তাই সমাজ পরিবর্তনে আগ্রহী যে তরুণ, তাদের কাছে কাজী আবদুল ওদুদের বিদগ্ধ প্রবন্ধ তেমন কোনো আবেদনের সৃষ্টি করতে পারেনি। ওদিকে আবার তাঁর রচনার লক্ষ্য মূল পাঠকের হৃদয় নয়, তার বুদ্ধি। পাঠকদের বুভুক্ষু হৃদয় চলে গেছে জাতীয়তাবাদীদের আবেগ-উদীপ্ত বক্তব্যের কাছে, যারা সমগ্র জাতির কথা বলেছেন, নিজেদেরকেই জাতি মনে করেছেন এবং জনগণকে কথিত ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের (অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার) ভিত্তিতে দেশের মানুষকে খাড়াখাড়ি ভাগ করে ফেলেছেন। জাতীয়তাবাদীদের তৎপরতায় দেশভাগের কাজটা ত্বরান্বিত হয়েছে। দেশভাগ হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রের পীড়নকারী চরিত্রে কোনো পরিবর্তন আসেনি এবং সমাজ আগের মতোই শ্রেণীবিভক্ত রয়ে গেছে। বৈষম্য কমবে কি উল্টো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।
ধর্মের ভাষা ও ভঙ্গির ভেতরে যে শক্তিটা নিহিত থাকে তার শক্তি সম্পর্কে আবদুল ওদুদ নিজেকে অবহিত রাখেননি। দেশভাগের পরে, ১৯৪৯-এ লিখিত ‘শতবর্ষ পরে রামমোহন’ প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছেন যে, ধারণা করা হয় যে জাতির হৃদয়-সিংহাসন শক্তিমান ও খ্যাতিমান রামমোহনের কাছে নয় চলে গেছে অন্যদের, বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও রামমোহন-বিবেকানন্দদের কাছে। তার ধারণা এর কারণ তাদের ধর্মবোধের মনীষা বা মহাপ্রাণতা নয়, বরং এর মূলে আছে তাদের কোনো কোনো কথায় ও আচরণে দেশের শিক্ষিত সমাজের এবং কখনো কখনো অশিক্ষিতদের ‘আত্মঅভিমান’ লালিত হবার সুযোগ। এখানে বোধ করি কিছুটা ভ্রান্তি রয়েছে। কেননা যে আত্মঅভিমানের কাছে জনপ্রিয় ওই মনীষীরা আবেদন জানিয়েছেন, সেটা যতটা না ইহজাগতিক ছিল তার চেয়ে অধিক ছিল ধর্মীয়। তদুপরি ওঁদের ভাষা ও উপস্থাপনায় ধর্মের উপস্থিতি ছিল। আসলে এরা ধর্মীয় অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলাতেই আগ্রহী ছিলেন এবং তারা সফলও হয়েছেন।
ওদুদ প্রগতিপন্থী এবং চিন্তশীলদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সেজন্য তার কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অধিক। কিন্তু তার ভাবনাগুলোর প্রভাব যে কেবল ইতিবাচক হয়েছে তা নয়, কোথাও কোথাও নেতিবাচকও হয়ে পড়েছে। যেমন ধরা যাক দেশবিভাগের ব্যাপারটাই। পলাশীর যুদ্ধের পরে আমাদের জন্য এত বড় বিপর্যয় তো আর ঘটেনি। ওদুদ অবশ্যই দেশভাগের ঘোরতরবিরোধী। দেশভাগ প্রতিরোধের উপায় ছিল, আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনকে বেগবান করার মধ্যে। সে-আন্দোলন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজতান্ত্রিক হতো, জনমানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে, এবং মানুষের মুক্তির পথকে প্রশস্ত করে দিতো। ওই আন্দোলনের পক্ষে থাকাটা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে-চেষ্টা তিনি করেনও নি। কারণ তিনি ধর্মের ওপর আস্থা হারান নি, ভারতবর্ষ যে একটি নয়, বহু জাতির দেশ সেটা মানতেন না, এবং সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিলেন। ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর পরিচয়টা দাঁড়াল একজন জাতীয়তাবাদী ভারতীয় মুসলমানের। মুসলমান সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা পেলো না। সেই সঙ্গে পরোক্ষে তিনি জায়গা করে দিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদের জন্য।
উগ্র জাতীয়তাবাদীদের কাছে যেমন বঙ্কিম অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন, মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের কাছে তেমনি বিশেষভাবে আদরণীয় হয়ে দেখা দিলেন পাঞ্জাবের কবি ইকবাল। শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানদের ভেতর যে হীনমন্যতা বোধ ছিল ইকবাল সেখানে ইসলাম ধর্মের গৌরবের দিকটা তুলে ধরে তাদের মুসলমান পরিচয়টিকে গর্বের বিষয় করে তুলতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। অন্যদিকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন কিন্তু বাঙালি মুসলমানকে না সাহায্য করলো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিতে, না হীনমন্যতা বোধ কাটিয়ে উঠতে। হীনমন্যতা বোধের মধ্যেই কিন্তু ছিল পাকিস্তান দাবির লালনভূমি।
ওদুদের লড়াইটা ছিল মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে, কিন্তু ওই লড়াইতে সুবিধা হলো না সামাজিক বিপ্লব বিরোধিতার কারণে। বিপ্লবকে বিশৃঙ্খলতা মনে করতেন বলেই তাঁর লেখায় ফ্রয়েড আসেন কিন্তু মার্কস ও লেনিন একবারও আসেন না, যদিও রুশ বিপ্লব তাঁর কাছে মোটেই অপরিচিত নয়।
২
কাজী আবদুল ওদুদকে বোঝার জন্য সুবিধা হবে আমরা যদি তার চিন্তার কাঠামোটাকে জেনে নিই। এটি হচ্ছে উদারনীতি। উদারনীতি ব্যক্তির ভূমিকায় বিশ্বাস করে, সমষ্টির হাত থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করতে চায়, সংস্কার চায়, কিন্তু বিপ্লবকে ভয় পায়। কেবল বিপুব নয় সংঘবদ্ধতাতেও উদারনীতির অনাস্থা। ওদুদের অবস্থান এই কাঠামোর ভেতরেই। যে জন্য তিনি গান্ধীর ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও চরকাকে উচ্চমূল্য দেন, যদিও উভয় বস্তুই বিচ্ছিন্নতাকে উৎসাহিত করেছে। ১৯৪৯-এ গান্ধীর মৃত্যুর পরপরই লিখিত ‘জয়তু গান্ধী’ প্রবন্ধে তার একটি মন্তব্য বিস্ময়কর। তিনি বলেছেন, এ যুগের বিভীষণ। সংঘবদ্ধতার মারাত্মকতা প্রশমনের এক বিশিষ্ট উপায় নিহিত রয়েছে […] চরকায়, অর্থাৎ কটীরশিল্পের মধ্যে’। বিস্ময়কর এই জন্য যে, অন্যত্র তিনি সংঘবদ্ধতাকে মেনে নিয়েছেন। চরকাকে তিনি কুটীর শিল্প বলছেন; চরকা কিন্তু তা মোটেই কুটীর শিল্প নয়, ঘরে বসে শ্রমশক্তি বিক্রি করা। তবে হ্যাঁ, কুটীর শিল্প ছিল, ছিল তাত ও তাঁতী, ইংরেজ এসে উভয়কে ধ্বংস করেছে, সেই কুটীর শিল্পকে চরকায় তৈরি সুতো দিয়ে বেঁধে জীবন্ত করা যাবে এমন আশা অলীক। ওদুদ রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত যৌক্তিক চরকাবিরোধিতায় অস্বস্তিতে পড়েছেন। আর দশজনের বিরোধিতা তিনি বুঝতে পারেন, রবীন্দ্রনাথেরটা বুঝতে পারেন না। তিনি লিখেছেন,
রবীন্দ্রনাথ, আজীবন স্বাধীনতাপিয়াসী রবীন্দ্রনাথ, সত্যের অনন্তরূপের পূজারী রবীন্দ্রনাথ যে কেন চরকার ওই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করলেন না, তড়িঘড়ি ভেবে নিলেন যে ওটা আর দশটা ছোটখাটো কাজেরই এক কাজ, এ ব্যাপারটা আমাদের কাছে এক হেঁয়ালির মতোই রয়ে গেল। (“গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ’)।
আমরা কিন্তু বরং বিস্মিত হই এ ব্যাপারে ওদুদের বিস্ময় দেখে।
উদারনীতিকেরা ব্যক্তির উন্নতি চান, কিন্তু তাই বলে ব্যক্তি নেতৃত্বের ওপর পরিপূর্ণ আস্থা যে রাখেন তা নয়। কারণ নেতা যখন বীর হয়ে যান তখন তাঁর প্রবণতা থাকে স্বেচ্ছাচারী হবার। ওদুদ কিন্তু নেতা ও বীর উভয়ের ওপরই আস্থা রাখেন। যে জন্য তিনি ম্যাথু আর্নল্ডের সৌন্দর্য ও জ্ঞান প্রীতির সঙ্গে কালাইলের বীরপূজার সমন্বয় ঘটাতে অস্বস্তি বোধ করেন না।
তবে সংঘবদ্ধতাকে না-মেনেও উপায় থাকে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে তো স্বীকার করতেই হবে, তিনিও করেন। কিন্তু ব্রিটিশের রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনটাকে মোটেই গুরুত্ব দেন না। অথচ রামমোহন কিন্তু মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা, কৃষকের অধিকার, ভারতবাসীর জন্য সুবিচারের প্রয়োজনীয়তা, রাজনীতিতে ডমিনিয়ন স্ট্যাটাস পাওয়া, এসব প্রশ্নে রাষ্ট্রের সঙ্গে দরকষাকষি করেছেন। ওদুদ রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। ১৯০৫ সালের একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘আমাদের হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। এই বক্তব্যে ওদুদ আপত্তি করেছেন। তবে আপত্তিটা এখানে নয় যে, রবীন্দ্রনাথ ‘হিন্দু সভ্যতাকে ভারতীয় সভ্যতা থেকে আলাদা করে দেখেছেন। বস্তুত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলমান যুগ ও ব্রিটিশ যুগে ভাগ করে ইংরেজরা ইতিহাসপাঠে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছিল ওদুদ সেটাকে মেনে নিয়েছেন; তিনি এমনটা বলেন নি যে, ওই বিভাজনে সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। তার আপত্তি অন্যত্র। তিনি মনে করেন, ‘বাস্তবিক সমাজ ও রাষ্ট্রের পরস্পরবিরোধিতা কল্পনাই করা যায় না। রাষ্ট্র সমাজের প্রাণ।’ আরো বলেছেন, জীবনের অর্থ। সংঘবদ্ধতা, একথা সব ভাগ্যবান দেশের লোকে জেনেছে, ভারতবাসীদেরও জানতে হবে। আমরা তো জানি রাষ্ট্র আসলে সংঘশক্তিরই একটি উৎকট প্রকাশ, তার কাজ শাসক শ্রেণীর স্বার্থ দেখা। রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের বিপুলসংখ্যক মানুষের বিরুদ্ধতা যে একেবারেই অনিবার্য সেটা ওদুদ জানেন না মনে করবার কারণ নেই। জানেন কিন্তু মানেন না।
১৯৪৬-এ লিখিত ‘গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে’ প্রবন্ধে তিনি মেনে নিচ্ছেন ভারতবর্ষে যে গৃহযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছে, তার সমাধান হচ্ছে মিলে মিশে থাকার চর্চার মাধ্যমে নতুন এক ‘সম্মিলিত ভারত’ গঠন যার ভিত্তি হবে সাম্যবাদ, এবং যেখানে ধর্ম হবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। বলা বাহুল্য, এমন সমাধানের কথা তিনি আগে ভাবেননি। কিন্তু সমাধানের কাছাকাছি এসেও তার দ্বিধা থাকে। প্রথম কথা, তিনি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে বিশ্বাস করেন না, যেটি গণতন্ত্রের একটি ভিত্তি। ওদুদ ফেডারেল নয়, এককেন্দ্রিক ভারত চান। আর ওই এককেন্দ্রিকতাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রধান সমস্যা। ভারতীয় মুসলমানদের ভয় ছিল এককেন্দ্রিক ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতা চলে যাবে কংগ্রেসের হাতে, যার দরুন মুসলমানরা চিরকালের জন্য হিন্দু-আধিপত্যের নিচে পড়ে থাকবে। দ্বিতীয় কথা, এই পর্যায়ে পৌঁছার পর দেখা যাচ্ছে তিনি সাম্যবাদ মানেন, ধর্মনিরপেক্ষতাও মেনে নিচ্ছেন, কিন্তু বলশেভিজম মানেন না। বলশেভিজমকে তিনি নাৎসীবাদের তুলনায় বেশি কার্যকর হতে পারে বলে মনে করেন ঠিকই, কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশে ‘ওই জিনিস’ চলবে বলে মনে করেন না। কারণ রাশিয়ার মতো আমাদের সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি নেই। তাই বলশেভিজম প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ‘জবরদস্ত’ বন্ধুদের কাছে তাঁর বিনীত নিবেদন–
ধীরে বন্ধু ধীরে! নগরকে আলোকমালায় উজ্জ্বল করা আর তাতে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো এক কথা নয় কোনো দিন। অগ্নিকাণ্ড অল্পকালেই ঘটানো যায় সন্দেহ নেই, কিন্তু আলোকমালায় সজ্জিত করার জন্য চাই পর্যাপ্ত আয়োজন।
ইতিমধ্যে ভারতবাসী যে অগ্নিগদ্ধ হতে থাকবে তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তার অভাব।
বলশেভিজম প্রসঙ্গে আবুল হুসেনের অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। তিনি বাংলার বলশই’ নামে ছোট একটি বই লিখেছেন। তাতে বলশেভিজমের সমর্থন করেন নি বটে, কিন্তু জমিদারদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে কৃষকদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার তারা চালাচ্ছে, তা থেকে নিবৃত্ত না হলে বাংলায় বলশেভিক বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়বে। কৃষকের দুঃখে ওই কাতরতাটা আবদুল ওদুদের লেখাতে নেই। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে আবুল হুসেন ও তিনি একসঙ্গে কাজ শুরু করেছিলেন। মিল অবশ্যই ছিল, তাদের শিক্ষাগত পটভূমিটাও অনেকটা একই ধরনের, উভয়েই প্রেসিডেন্সি কলেজে রাজনৈতিক অর্থনীতি পড়েছেন, কিন্তু পার্থক্য যে ছিল না তাও নয়। বলা হয়ে থাকে যে ওদুদ ছিলেন ভাবযোগী, হুসেন কর্মযোগী। সেটা সত্য। সাংগঠনিক কাজ আবুল হুসেনই করতেন, তরুণপত্র’, ‘শিখা’, ‘জাগরণ এসব পত্রিকা তাঁর উদ্যোগে ও সম্পাদনাতেই বের হয়েছে, ঢাকা শহরে তিনি একটি বইয়ের দোকানও খুলেছিলেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলায় অভিমান করে জেদের বশে তিনি প্রথমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে ঢাকাতেই আইনজীবী হিসেবে নিজেকে কর্মনিযুক্ত করেন। তারপর কলকাতায় গিয়ে আইন শাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে আইনজীবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। নানা বিষয়ে লিখেছেন, অর্থনীতির গুরুত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তিনি বেঁচে ছিলেন মাত্র একচল্লিশ বছর। তার অগ্রসরমানতা দেখে ধারণা করা অন্যায় নয় যে, দীর্ঘজীবন লাভ করলে তিনি হয়তো বলশেভিজমের পক্ষেই চলে যেতেন, যেমনটি তার সর্ব কনিষ্ঠভ্রাতা ডা. মারুফ হুসেন গেছেন। আবুল হুসেনকে সমাজের চিকিৎসক বলা সঙ্গত নয়, তিনি একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন।
৩
‘বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তার আদর্শ’ প্রবন্ধে ওদুদ বলছেন যে, ‘শাসক ও শাসিতকে কাছে আনতে হবে এই উপলব্ধিতে যে দেশে অভুক্ত ও কর্মহীন কেউ থাকবে না। কিন্তু সে লক্ষ্য কীভাবে অর্জিত হবে ওদুদ তার সন্ধান দিতে পারছেন না। গান্ধীর মতো শাসকদের হৃদয় পরিবর্তনে যে আস্থা রাখবেন তা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সাহায্য করবেন তাও মনে হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ বলছেন বটে যে, দেশের রাজশক্তিকে যেমন করেই হোক দেশের সম্পদবৃদ্ধির কাজে লাগাতে হবে, না পারলে দেশের ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের উন্নতি বাস্তবিকই অসম্ভব।’ কথাগুলো ঠিক রবীন্দ্রনাথের নয়, ওদুদ যেভাবে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উপলব্ধি করেছেন এটি তারই প্রকাশ। যেমন করেই হোক, সেটা তো বোঝা গেল, সেই যেমন করেই হোকটা কি তা তো জানা গেল না। তাছাড়া ওদুদ যে বলছেন রবীন্দ্রনাথ দেশের ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকের উন্নতির কথা ভাবছেন তারই বা অর্থ কি, দেশ এবং দেশের লোক কি তা হলে আলাদা বস্তু? তৃতীয় জিজ্ঞাসা এটা যে, দেশের সম্পদবৃদ্ধি ঘটলেই কি দেশের মানুষের উন্নতি ঘটে যাবে, নাকি সেই সম্পদের যথার্থ বিতরণেরও ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে কেউই অভুক্ত ও কর্মহীন না থাকে। এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, যে-কোনো পাঠকই লক্ষ্য করবেন যে ওদুদের বা’ এবং ‘অথবাগুলো অনেক সময়েই বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।
প্রবন্ধটিতে ওদুদ বাংলাসাহিত্যে ‘জাতীয়তা’র আদর্শের কথা বলছেন। কিন্তু কোন জাতীয়তার কথা ভাবছেন তিনি, ভারতীয় না বাঙালি; এদু’টি তো মোটেই এক নয়, ক্ষেত্রবিশেষ পরস্পরবিরোধী। নিজাম বক্তৃতাতে তিনি বলছেন, ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় না হয়ে ভারতবাসীর পরিত্রাণ নেই। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। ভৌগোলিক পরিস্থিতিই যদি নিয়ামক হবে তবে ইউরোপের ভৌগোলিক পরিস্থিতি ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান, স্পেনীয় সবাইকে এক জাতিতে পরিণত করেনি কেন? করেনি এই জন্য যে, ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন, এবং ভারতবর্ষকে যে এক জাতির দেশ হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে সেটা ভারতবর্ষীয়রা নিজের করেন নি, বিদেশী শাসকেরা এসে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের স্বার্থে ওটি ঘটিয়েছে।
ইউরোপে যেমন ভারতবর্ষেও তেমনি, বহুজাতির বসবাস এবং ওই জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, ভাষা বটে। ওদুদ অবশ্য সেটা না-মেনে পারেন নি, যে জন্য তিনি বলেছেন, ‘তবু আপাতত বাঙ্গালী, মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবী হওয়াই বেশি ভাল মনে হয়, কেননা তা বেশি স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য। মানছেন আবার মানছেনও না, পরিষ্কার করে বলছেন না যে, ওই কাজটা স্বাভাবিক ও কম কষ্টসাধ্য এই জন্য যে, জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। তদুপরি দেখা যাচ্ছে যে, তার দৃষ্টিতে যা ভাষাভিত্তিক প্রাদেশিক জাতীয়তা, সেটাকে তিনি মানতে রাজি হলেও ওটি যাতে ভারতীয়ত্বের বিরোধী না হয় সেটা দেখতে চান।
অখণ্ড ভারতীয়তার অবাস্তবিক জাতীয়তাবাদে তিনি যে প্রত্যাখ্যান করেননি তার প্রমাণ ওদুদের ওই বক্তৃতাতেই রয়েছে। বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে ইসলামের দেহ ও বেদান্তের মস্তিষ্ক সেই বক্তব্যকে সংশোধন করে এবং ভারতীয় জাতীয়ত্বকে মেনে নিয়ে তিনি ধারণা করেছেন যে, ভারতীয় জাতীয়ত্বের রূপ হবে পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ ও পূর্ণাঙ্গ মানবমস্তিষ্ক, সৃষ্টিশক্তির প্রকাশ যার ভেতর হবে অবাধ। অন্যদিকে আবার গৃহযুদ্ধের প্রাক্কালে’ প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের নব-নেতাদেরকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তাদেরকে গভীর ভাবেই ভাবতে হবে যে বাংলার মুসলমানের সঙ্গে পাঞ্জাবের মুসলমানের অঙ্গাঙ্গী যোগ ঘটাতে গিয়ে দু’য়েরই বিকাশ ব্যাহত করার মতো মহা অনর্থ তারা ঘটাবেন কি না।’ তা মহা অনর্থ শেষ পর্যন্ত তারা ঘটিয়েছেন বৈকি, কিন্তু কাজী আবদুল ওদুদ তো তাঁদের প্রতিপক্ষকে, অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে একথাটা বলতে পারেননি যে, সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ বলে আসলেই কিছু নেই, আছে বাঙালি পাঞ্জাবী ইত্যাদি জাতীয়তা। তারা সবাই অবশ্য তা শুনতো না, কিন্তু ভবিষ্যদ্রষ্টা হিসেবে সতর্কবাণীটি উচ্চারণ করলে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের সত্যটা জোরদার হতো।
ওদুদ ধীর চান। ১৯২৬ সালের ডায়েরির পাতায় তিনি লিখেছেন, দেশের মঙ্গলের জন্য এমন গগনচুম্বী হিমাদ্রি চাই- যারা আকাশের নিরন্তর বর্ষণশীল প্রাচুর্যের ভাণ্ডারী হয়ে সমতলে তা সহস্র ধারায় ছড়িয়ে দিতে পারে। এমন হিমাদ্রির সন্ধানে তিনি রামমোহনের কাছে গেছেন, রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছেন, গান্ধীকে নেতা বলে মেনেছেন, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দও বাদ পড়েন নি। স্পষ্টতঃই তিনি সমন্বয়বাদী। সংস্কৃতিকে তিনি গুরুত্ব দেন, এবং সমম্বয়কে সংস্কৃতির বড় গুণ বলে মানেন; কিন্তু যেভাবে পরস্পর বিরুদ্ধ আদর্শের নেতাদেরকে তিনি একত্র করেন তাতে অগ্রগতির জন্য অত্যাবশ্যক যে ঐক্য সেটা কীভাবে যে গড়ে তা বোঝা দুষ্কর। রামমোহনকে আলাদা রেখে অন্যসকলেরই সমালোচনা তার লেখায় দেখতে পাই, কিন্তু কারো ভাবমূর্তিই তিনি ভেঙে ফেলেন না। স্মরণ করিয়ে দেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ম্যএকদা ‘সাম্য লিখেছিলেন, কিন্তু বলেন না যে সেই বই তিনি প্রত্যাহারও করে নিয়েছিলেন। রাজনীতিবিদদেরকে তিনি বিশ্বাস করতে চান না। মন্তব্য করেন যে, আমাদের এই ভারতে আজ যদি রাজশক্তি দেশের লোকের হাতে আসে তা হলে গো রক্ষা, মন্দির ও মসজিদ ইত্যাদি সংক্রান্ত আইন পাশ করার দিকেই রাজনৈতিক নেতাদের খেয়াল বেশি করে জাগবার কথা। (জ্ঞান ও প্রেম’) কিন্তু এমনটা যাতে না ঘটে তার জন্য কী করা প্রয়োজন তা বলেন না। যেন বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই বলতে চান আমরা একটি পরাধীন জনগোষ্ঠী, আমরা অনেক কাল পরাধীন থাকবো; এবং আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নই, কেননা তাতে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ঘটার আশঙ্কা। মুসলমান সমাজের তরুণরা কামাল আতাতুর্কের দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ওদুদ বলছেন, বুদ্ধির মুক্তির দল উদার দৃষ্টিতে তাঁর পানে চেয়ে আছেন। কিন্তু কামাল পাশার ভেতরে যে একটা সমাজবিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সত্তা ছিল, এবং সেখানেই যে তাঁর মহত্ব সেটা নজরুল ইসলাম যেভাবে অনুধাবন করেছেন এঁরা সে ভাবে করেন নি।
৪
সাহিত্যকে তিনি অত্যন্ত অধিক মূল্য দিয়েছেন। যে রামমোহনের প্রতিভা ও আগ্রহ ছিল বহুমুখী আবদুল ওদুদ তাঁকে তাঁর নিজের মতো করেই দেখেন, এবং বলেন, “আমার তো মনে হয় রামমোহনের অলোকসামান্য মানসজীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সাহিত্যের ভিতরেই সঞ্চিত রয়েছে। যেমন, অন্যান্য সাহিত্যিকের বেলায় ঘটে।’ (‘রামমোহনের বিরুদ্ধপক্ষের যুক্তি’) রামমোহনকে একজন সাহিত্যিক হিসেবে দেখার ব্যাপারে অন্যদের অবশ্যই আপত্তি থাকবে, ওদুদের নেই।
সাহিত্যের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদের সাহিত্যবিচার নিজস্বতার গুণে গুণান্বিত, এবং তা পাঠ করা আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা। সাহিত্যকে তিনি যে শিক্ষকের মতো বিচার করেন তা নয়, তার লক্ষ্য সাহিত্যপাঠে তাঁর নিজের আনন্দকে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সে জন্য তিনি রচনার ভাষা, উপমা, রূপক ইত্যাদির বিশ্লেষণে যান না, একজন পাঠক হিসেবে তার নিজের ভেতর যে অনুভূতি ও ধারণা সৃষ্টি হয় তাঁর কথাই লেখেন। ওদিকে সাহিত্যসৃষ্টিকে তিনি সাহিত্যিকের প্রতিভার প্রকাশ বলে মনে করেন, যে জন্য সাহিত্যিকের প্রতিভার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য বিচারের বিষয়টা প্রধান হয়ে ওঠে। সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে তার একটি বড় কাজ জার্মান কবি গ্যেটের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। তার আগে এই কাজটি এমন সুচারুভাবে আর কেউ করেন নি।
তাঁর প্রধান আগ্রহ রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান সমাজ’ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। একজন প্রকৃত কবির যেসকল গুণ থাকা আবশ্যক সেগুলোর সবকটিই তিনি রবীন্দ্রনাথের ভেতর লক্ষ্য করেছেন। সেখানে রয়েছে তীক্ষ্ণ অনুভূতি, সন্ধানপরতা, এবং সেই সঙ্গে রহস্যময়ের পূজা। তার বিচারে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক প্রতিভা নন, যুক্তি বা বুদ্ধি তার ভেতরে প্রধান নয়, যদিও প্রবল। ‘অনুভূতি তার চেয়েও বড় সম্বল।
রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনদেবতা’ সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, ওদুদ মনে করেন ওটি আসলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা। রবীন্দ্রনাথকে যে বিশ্বকবি বলা হয় সে-বলার পেছনে যে যুক্তিটি ওদুদের কাছে গ্রাহ্য বলে মনে হয়, সেটি হলো কবির বিশ্বভাব; রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিশ্বভাবের কবি।
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃতির ভেতর একটি ঔদ্ধত্য ছিল, আর ছিল একটি সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব; একদিকে তিনি জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের পূজারী অপরদিকে তেমনি আবার প্রবলভাবে হিন্দুত্বের প্রচারক। ওদুদ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভারতের হিন্দু মুসলমানের কয়েক শতাব্দীব্যাপী রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষি কালে হয়ত অতিঅদ্ভুত ঘটনা বলে মানুষের মনে হবে। তখন জ্ঞানী ও শক্তিমান বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ ভালবাসতে পারবে সন্দেহ নেই, কিন্তু অসহিষ্ণুতা হবে তাদের জন্য পরম কৌতুকাবহ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এমনটা ঘটেনি। তার কারণ সাম্প্রদায়িকতার অবসান না-ঘটা, এবং জাতীয়তা ও শ্রেণী সমস্যার সমাধানে উপমহাদেশের মানুষের ব্যর্থতা।
দেশপ্রেমের ধারণার ব্যাপারে বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের ভেতর যে ব্যবধান সেটিকে ওদুদ চমৎকার ভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখাচ্ছেন যে, বঙ্কিম যেখানে বলতেন সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না’; সেখানে রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ স্বজাতিকে উচ্চ করতে হবে ঠিকই, তবে দেশের কাছে মানুষকে ছোট করা যাবে না, ক্ষুদ্র জনকে বীর্য দিতে হবে যাতে সে নিজেকে হীন জ্ঞান না করে এবং বলের জ্ঞানে লুটিয়ে না পড়ে।
ওদুদ কিন্তু অসুবিধায় পড়েন মধুসূদনকে নিয়ে কিছুটা এবং নজরুলকে নিয়ে অনেকটাই। মধুসূদনকে তিনি অবশ্যই গুরুত্ব দেন। তার ভেতরে যুগচেতনা ও উদার গ্রহণশীলতা তিনি লক্ষ্য করেন, দেবতার প্রতি কবির বিতৃষ্ণার কথাও উল্লেখ করেন, কিন্তু মধুসূদনের বিপ্লবী সত্তাটাকে ধরতে পারেন না, যে জন্য মধুসূদনের মহাকাব্যে জাতীয়তাবাদের আর্ত হৃদয় যে ক্রন্দন করছে, সেটা তাঁর পক্ষে শোনা সম্ভব হয় না। অপরদিকে নজরুলকে তিনি মাপতে যান রবীন্দ্রনাথের মানদণ্ডে, যে জন্য রবীন্দ্রনাথ যে-নজরুলকে কবি বলে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি, ওদুদ তার ভেতর ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা দেখতে পান। নজরুল রবীন্দ্রনাথ নন, তিনি স্বতন্ত্র, এবং তার স্বাতন্ত্রের একটি বড় কারণ হচ্ছে নজরুলের অন্যান্য গুণের মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর বিপ্লবী চেতনা। এই চেতনাকে বুঝতে না পেরে তিনি নজরুলকে প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং জসীমউদ্দীনের সঙ্গেও তুলনা করে ফেলেন। নজরুলের মধ্যে আত্মঅভিমান বোধ রয়েছে ঠিকই, যেটির তিনি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু নজরুল যে সমাজ বিপ্লব চেয়েছিলেন সেটাকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেননি। তাঁর মনে হয়েছে নজরুল পুরোপুরি সাম্যবাদী নন। নজরুলের ওপর ওদুদের একটি বই আছে, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এটা মানছেন যে, নজরুল বিংশ শতাব্দীর বাংলার তথা ভারতের এক স্মরণীয় কবি’, এবং একালে দেশের যে গণশক্তির উত্থান তার মূলে নজরুল প্রতিভা বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়েছে। তিনি বলেন, যেমন করেই হোক’ নজরুল ‘স্বদেশী আন্দোলনের সমস্ত বীর্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছেন। যেমন করেই হোক’ এর রহস্যটা হচ্ছে নজরুলের বিপ্লবী চেতনা, ওদুদ যেটাকে গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন।
কবি ইকবাল সম্পর্কে ওদুদের বক্তব্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। ইসলাম বলতে ইকবাল যে বুঝতেন শক্তিমত্তা, ওদুদের এ বক্তব্য ইকবালকে বুঝতে সাহায্য করে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে মুসলমানদের পতনের বিষয় ইকবালের যে কাব্যগ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে সেটির তুলনায় যে, কাব্যগ্রন্থে কবি প্রতিকারের কথা বলছেন কাব্য হিসেবে তা নিকৃষ্টতর। সাহিত্যে এটাই নিয়ম; সেখানে দুঃখের কাহিনী গম্ভীর হয়, সুন্দরও হয়, আশার বাণীর তুলনায়। এটি কাজী আবদুল ওদুদের নিজের লেখা সম্পর্কেও সত্য; সেখানেও দেখি যখন তিনি সমস্যা, সঙ্কট ও দুঃখের কথা বলেন, তখন তা অনেক বেশি হৃদয়স্পর্শী ও গ্রহণযোগ্য হয় যেসকল সমাধান তিনি উপস্থিত করেন তাদের তুলনায়। ইকবালের বাগবৈদগ্ধে উর্দু সাহিত্যের যে বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত সেটাও তিনি দেখিয়েছেন। ওদুদ ধর্মকে গুরুত্ব দেন; সাহিত্য অবশ্য ধর্মের চেয়েও ততোধিক গুরুত্ববাহী, তবে তাঁর প্রধান বিবেচনা সংস্কৃতি। একালে ধর্মের চেয়েও সংস্কৃতি যে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সে-বিষয়টিকে তিনি বিবেচনায় নিয়ে এসেছেন। সংস্কৃতিকে তিনি দেখেন এক বিশেষ ধরনের সমন্বয় হিসেবে। সমন্বয়ে বিশ্বাসী ওদুদ-চিন্তায় তাই সংস্কৃতি বিশেষভাবেই মূল্যবান হয়ে ওঠে। তদুপরি সংস্কৃতি অতীতের শ্রেষ্ঠ ভাবসম্পদকে সাদরে গ্রহণ করে। সংঘবদ্ধতাকে তিনি সন্দেহের চোখে দেখেন ঠিকই, কিন্তু সংস্কৃতির বেলাতে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ইউরোপে সাংস্কৃতিক জীবন মোড় ফিরেছে। ‘সামাজিকতা’র দিকে, যার কারণ ইউরোপে সংঘবদ্ধ জীবন অনেক বেশি সক্রিয়। (সংস্কৃতির কথা)
৫
কাজী আবদুল ওদুদের উপমাগুলো সুন্দর। তাঁর কোনো কোনো উক্তি মনে রাখবার মতো। যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্পর্কে তিনি বলছেন, ‘মোহ আর মোহমুক্তির ধস্তাধস্তি সে-কালে উৎকট আকার ধারণ করেছিল। অন্যত্র, ‘তাজী ঘোড়াকে জীর্ণ আস্তাবলে পোরায় যে বিপদ বাংলার মনীষীদের নব-জীবন ও নব-মানবতার সাধনা হয়তো সেই বিপদের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই ঘোড়া বিদায় দিয়ে জীর্ণ আস্তাবলটি যে অটুট রাখার চেষ্টা হবে সে সময়টি তো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সত্য সম্পর্কে ‘শাশ্বত বঙ্গ’ বইতে অনেক উক্তি আছে। তাদের মধ্যে একটিতে আশার ধ্বনিটা শুনতে পাই, যেটিতে তিনি বলেন, যা আছে শুধু তাইই সত্য নয়, যা হওয়া উচিৎ তাইই মানুষের জন্য বিশেষভাবে সত্য।’ যে বিবেকানন্দকে তিনি বীরের কাতারে রাখেন তার সম্পর্কে একটি উক্তি যেমনি যথার্থ তেমনি উজ্জ্বল; বিবেকানন্দের অপূর্ব আবিষ্কার “দরিদ্র নারায়ণ”- তাঁর অগণিত দেশবাসীর জন্য এটি হলো একটি সুন্দর কথা মাত্র; সে-প্রমাণ তারা নিঃশেষে দিল পঞ্চাশের মন্বন্তরে। অপূর্ব আবিষ্কার, কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ! ব্যক্তিকে চিনবার উপায় সম্পর্কে তার একটি উক্তিও চিন্তার উদ্রেককারী; ‘ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে তার গুণে তেমন নয় যেমন তার দোষে।
এ ধরনের বহু উক্তি তাঁর লেখায় আমরা পাবো, যেগুলো তাঁর সম্পর্কে সেই সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে যে তিনি একজন সাহিত্যিক। আমরা এটাও স্বীকার করবো যে তিনি ঠিক সমাজ-সংস্কারক নন (জ্ঞান ও প্রেম’); কিন্তু এটা বলতেই হবে যে পুরোপুরি সাহিত্যবিষয়ক রচনাগুলো ছাড়া তার সব প্রবন্ধেই রুগ্ন সমাজের রোগের বিবরণ ও ব্যাখ্যা এবং নিরাময়ের উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে, যে জন্য তাকে ভালবাসার দ্বারা অনুপ্রাণিত একজন সমাজচিকিৎসক হিসেবে বিবেচনা করেছি। শিক্ষক নয়, চিকিৎসকই।
তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি আমাদেরকে মূল্যবান রচনা উপহার দিয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধগুলো কেবল তাকে নয়, তার সময় এবং উদারনীতির যে চিন্তা-কাঠামোর ভেতরে থেকে তিনি ব্যাধি ও প্রতিকারের কথা বলেছেন, সেই উদারনীতির গুণ ও সীমাকে বুঝতে সাহায্য করে। উদারনীতি পরমতসহিষ্ণু এবং মার্জিত, তার সীমা হচ্ছে বিপ্লবভীতি। কাজী আবদুল ওদুদের প্রবন্ধ আমাদেরকে চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে, তার সঙ্গে আমরা তর্কে লিপ্ত হতে পারি, কিন্তু সেটি একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা বটে।
ওদুদ বিশ্বাস করেন সৃষ্টিশীলতায়। যাকে তিনি শাশ্বত বঙ্গ বলছেন সেটি হচ্ছে আমাদের সৃষ্টিশীলতার ইতিহাস। অন্যদিকে তিনি তাঁর দেশবাসীকে জাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তাঁর নিজের জন্য তো বটেই, তাঁর সময়ের জন্যও মীমাংসেয় খুব বড় ও জরুরি প্রশ্ন ছিল দু’টি, একটি জাতীয়তার অপরটি শ্রেণীর। প্রশ্ন নয়, বলা যায় সমস্যা। এই দুই সমস্যার কোনোটারই মীমাংসা ব্রিটিশ যুগে হয়নি। জাতীয় সমস্যার যদি সমাধান করা যেতো, যদি মেনে নেওয়া হতো যে, উপমহাদেশ একটির নয়, আসলে ভাষাভিত্তিক অনেক ক’টি জাতির বসবাস, তা হলে ভারতবর্ষ হয়তো দ্বিখণ্ডিত হতো না। আর জাতি সমস্যার সমাধান হলে শ্রেণী সমস্যা অবশ্যই সামনে আসার সুযোগ পেতো, এবং প্রবলভাবে সমাধানের দাবি জানাতো। তেমনটি ঘটেনি।
কাজী আবদুল ওদুদ যা দিয়েছেন তা মূল্যবান, আর যা দেননি সে-বিষয়ে তিনি আমাদের পরোক্ষে হলেও সচেতন করেছেন। তার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আনন্দদানের পাশাপাশি তিনি আমাদের অতীতকে বুঝতে সাহায্য করেন এবং ভবিষ্যৎ গড়বার জন্য কী করণীয় সে-ব্যাপারেও সজাগ করেন। তাঁর কাছ থেকে আমাদের প্রাপ্তিটা খুবই বড়।
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
.
নিবেদন
‘শাশ্বত বঙ্গের অনেকগুলো লেখা পূর্বে বেরিয়েছিল এইসব বইতে ও নবপর্যায় (১৩৩৩ সাল), রবীন্দ্রকাব্যপাঠ (১৩৩৪ সাল), নব-পর্যায় দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৩৬ সাল), সমাজ ও সাহিত্য (১৩৪১ সাল), হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ (১৩৪৩ সাল), আজকার কথা (১৩৪৮ সাল), নজরুল-প্রতিভা (১৩৫৫ সাল)। সূচিপত্রে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ দেখতে পাওয়া যাবে। এর প্রথম ৭৯ পৃষ্ঠার লেখাগুলো এর পূর্বে বই আকারে বেরোয়নি, তবে তার অল্প কয়েকটি দিয়ে কয়েক মাস পূর্বে ‘স্বাধীনতা-দিনের উপহার’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর শেষের দিকের ‘গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ লেখাটিও পূর্বে কোনো বইতে প্রকাশ করা হয়নি। দেশ-বিভাগের পরের লেখাগুলো বইয়ের প্রথম দিকে দেখতে পাওয়া যাবে।
এর অন্তর্ভুক্ত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ’ ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতীতে প্রদত্ত নিজাম-বক্তৃতা-স্বত্বাধিকার বিশ্বভারতীর। এটি শাশ্বত বঙ্গে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ লেখককে অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন। রস ও ব্যক্তিত্ব’ লেখাটি এর অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়ে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কর্তৃপক্ষও তুল্যরূপে লেখকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।
১৩৩২ সালে-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের সূচনায়-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলে ‘মুসলিম সাহিত্য-সমাজ’ নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূলমন্ত্র ছিল বুদ্ধির মুক্তি’। কয়েকজন মুসলমান অধ্যাপকের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল এর পরিচালনার ভার-শাশ্বত বঙ্গের লেখক তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধির মুক্তি, অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান-বাংলার মুসলমান-সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুসলমান-সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিনে বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপরে এর প্রভাব-একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তফা কামালের উদ্যম থেকে, কিন্তু তারও চেয়ে গূঢ়তর যোগ এর ছিল বাংলার বা ভারতের একালের জাগরণের সঙ্গে আর সেই সূত্রে মানুষের প্রায় সর্বকালের উদার জাগরণ-প্রয়াসের সঙ্গে। শাশ্বত বঙ্গের অনেক লেখায় রয়েছে সেই স্মরণীয় দিনগুলির স্বাক্ষর, বিশেষ করে বুদ্ধির মুক্তি’ আর তার আনুষঙ্গিক ব্যাপক মানব-হিত মানুষের সভ্য জীবনের এই মহাপ্রয়োজনের কষ্টিপাথরে বারবার সেসবে যাচাইয়ের চেষ্টা হয়েছে। বাংলার ও ভারতের একালের জাগরণের মূল্য ও মর্যাদা, আর বারবার আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে দেশের শিক্ষিত-সমাজের অনবধানতার জন্য সেই অমূল্য প্রচেষ্টার বিড়ম্বনা-ভাগের সম্ভাবনা সম্বন্ধে।
দুর্ভাগ্যক্রমে এই আশঙ্কিত বিড়ম্বনা-ভোগ এড়িয়ে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নি। দেশের একালের জাগরণের এক পরিণতিরূপেই আমাদের লাভ হলো রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কিন্তু সেই স্বাধীনতা-লাভের পুণ্যক্ষণে দেশের (ভারতবর্ষের ও পাকিস্তানের) অগণিত লোকের যে আত্মিক অপঘাত ঘটলো তাতে সেই অশেষপ্রতিশ্রুতিপূর্ণ স্বাধীনতাও আজো হয়ে আছে রাহুগ্রস্ত।
তবে এমন লাঞ্ছনা শুধু আমাদের দেশের ভাগ্যেই ঘটেনি, বৃহত্তর জগতেও একালে চলেছে এক অদ্ভুত বিপর্যয়, যার ফলে দেশে দেশে ব্যাপক প্রবণতা জেগেছে কঠিন অপ্রেম আর সংঘর্ষের দিকে; একালের বুদ্ধিজীবীদেরও অনেকের পক্ষপাত সংঘবদ্ধতা, অধিকার-ঘোষণা, আর প্রচারবহুলতার দিকেই-বিচার, প্রেমপ্রীতি, আত্মবিকাশ, এসব আজ তাদের চোখে অনেকখানি অবিশ্বাস্য চিন্তাধারা।
এই পরিবেশে ‘বুদ্ধির মুক্তির কথা সমাদৃত হবে, সে সম্ভাবনা অল্প। আজ বরং মুষ্টিমেয়ের বুকে অনির্বাণ থাকুক এই প্রত্যয় যে তাই-ই মানুষের জন্য পথ, চিরন্তন ধর্ম, যা পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী আর সবার জন্য কল্যাণবাহী, আর সব বড়জোর আপদ্ধর্ম, অন্য কথায়, বিপথ। মানুষ অপ্রেম ও চিন্তার আবিলতা থেকে রক্ষা পাক, এই হোক আজ প্রত্যেক দায়িত্ববোধসম্পন্ন নর ও নারীর অন্তরতম প্রার্থনা।
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮
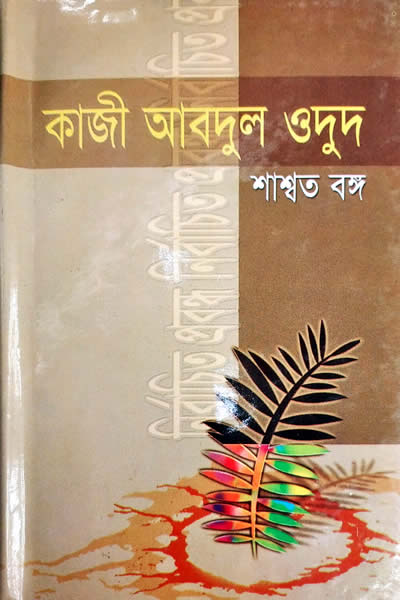

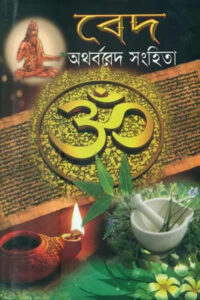

Leave a Reply