বিশ্বমনা: রবীন্দ্রনাথ – সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
সংকলন ও সম্পাদনা – বারিদবরণ ঘোষ
কবিগুরু ও ভাষাচার্যের অনুরাগী পাঠককে
.
ভূমিকা
ত্রিপুরার আঞ্চলিক রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী সমিতির পক্ষ হইতে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বসু প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহী সাহিত্যিক ও অন্যকর্মীর চেষ্টা ও যত্নে প্রস্তুত এই বইখানিকে বাঙলা সাহিত্যের ও বঙ্গদেশের সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অপূর্ব গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই যুগের এক বিরাট যুগন্ধর মহাপুরুষ ছিলেন, এবং নানা দিক দিয়া বিচার করিয়া বলিতে হয় যে, তাঁহার জীবনে প্রায় আশি বৎসর ধরিয়া বাঙলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি যেন মূর্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সমগ্র রূপটি জানা তো সম্ভবপর নহে—কর্মবিপুল রবীন্দ্রজীবনের বহু ঘটনা, বহু তথ্য আমাদের কাছে এখনও ধরা দেয় নাই। সূর্যের মতোই তিনি যেখানেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন সেখানেই তাঁহার জ্যোতির্ময় স্বরূপের কিছু না কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার পূর্ণ সংগ্রহ ও সংগ্রথন দুঃসাধ্য, হয় তো বা অসাধ্য।
রবীন্দ্রনাথ অন্য নানা দেশ ও স্থানের মতো ত্রিপুরাতেও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-রচনাবলী-র মধ্যে ত্রিপুরার সহিত তাঁহার এই সংযোগ এবং এ বিষয়ে ত্রিপুরার দান একটি লক্ষণীয় ও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠক ও আলোচক সে-সম্বন্ধে সচেতন আছেন। কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে, বিশেষ করিয়া ত্রিপুরার রাজবংশের কতকগুলি অভিজাত ব্যক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে নিবিড় আত্মীয়তা ঘটিয়াছিল, যেভাবে তাঁহারা সুদূরপ্রসারী দিব্যদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক ও অন্যবিধ মহত্ত্ব দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে-সমস্ত কথা এতদিন বিলুপ্তির গর্ভে যাইতে বসিয়াছিল। ত্রিপুরার রাজবংশের অশীতিবর্ষদেশীয় শ্রদ্ধেয় মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (লালকর্তা) প্রমুখ রবীন্দ্রগোষ্ঠীর কতকগুলি অন্তরঙ্গ গুণজ্ঞের সহায়তায়, ত্রিপুরার রাজবংশের সহিত রবীন্দ্রনাথের যে পত্র ব্যবহার ছিল তাহা উদ্ধার করিয়া, রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরার সংযোগের এই আশ্চর্য ইতিহাস সংকলিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের নানামুখী প্রতিভার ও ব্যক্তিত্বের একটি লক্ষণীয় দিক আমাদের সমক্ষে উদঘাটিত হইয়াছে, এবং তাহার ফলে রবীন্দ্রনাথের জীবনের, তাঁহার মনন ও কর্মপ্রচেষ্টার একটি অজ্ঞাতপূর্ব রূপ আমরা দেখিতে পাইতেছি, বঙ্গদেশ ও ত্রিপুরার আত্মিক যোগেরও পরিচয় পাইতেছি।
এই পুস্তকগুলি, রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী হইয়াছে। মূলপত্রাদির পাঠ ও প্রতিলিপি ইহাতে প্রমাণপঞ্জীরূপে উদ্ধৃত হওয়ায়, এবং কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য চিত্র এই পুস্তকে প্রথম প্রকাশিত হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও অসাধারণ হইয়াছে।
এইবার ত্রিপুরায় আসিয়া এই পুস্তকের সংকলন ও প্রকাশনের আয়োজন দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। আমি এইজন্য ত্রিপুরা রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সমিতির সদস্যগণ ও তাঁহাদের সহায়কগণের নিকট আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি, এবং বাঙলা সাহিত্য ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই পুস্তকের স্বাগত করিতেছি।
ইতি—
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
আগরতলা ৫ই বৈশাখ ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ
১৮ই এপ্রিল ১৯৬১
আগরতলা, ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী সমিতি কতৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরা স্মারক গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রচিত।
.
অবতরণিকা
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ নভেম্বর; রবীন্দ্রনাথের জন্ম আমাদের সবারই জানা ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ, সঠিক ইংরেজি তারিখটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে। অঙ্কের হিসেবে সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে মোটামুটি ২৯ বছরের ছোটো। রবীন্দ্রনাথ চলে যান ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে, সুনীতিকুমার ১৯৭৭-এ। কবিপ্রয়াণের পরে সুনীতিকুমার বর্তমান ছিলেন মোটামুটি ছত্রিশ বছর। সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথকে কবে প্রথম দেখেন—এ নিয়ে ‘পাথুরে’ প্রমাণ দিতে পারব না, কিন্তু শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য আশ্রমের একদা ছাত্র গৌরগোবিন্দ গুপ্ত ওরফে গোরা যখন মতিলাল শীলস ফ্রি স্কুলে সুনীতিকুমারের সহপাঠী হয়ে তাঁকে প্রথম রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনান, সেইদিনই সুনীতিকুমারের চোখের সামনে রবীন্দ্রভবনের সিংহদ্বারটি খুলে গিয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কল্পনা ‘চোদ্দ বছরের ছেলে’ সুনীতিকুমারের ‘হৃদয়কে মনকে’ আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের ‘জীবন-দেবতা’ বোধ নিয়ে সুনীতিকুমার যতবার ভেবেছেন, অন্য কোনো রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ তাঁকে ততবার গ্রাস করেনি। এই বোধই তাঁকে ক্রমশ রবীন্দ্র-সন্নিবিষ্ট করেছিল। তবে সংবাদ হিসেবে জানাতে পারি, ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কোনো সূত্রে রবীন্দ্রদর্শন সম্ভব হলেও ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে বি এ পাস করার পরই তিনি প্রথম রবীন্দ্র-সংস্পর্শে আসেন। তারপর থেকেই তিনি রবীন্দ্রনাথকে তাঁর জীবনের মর্মমূলে আসীন রেখেছিলেন।
অন্যদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়ে আগ্রহী এবং শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে—যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর Origin and Development of the Bengali Language বইটি প্রকাশ করেন। বাস্তবিকই বছর ছত্রিশের তরুণটিকে পঁয়ষট্টি বছরের এক চিরতরুণ শ্রদ্ধার পাত্রই ভেবেছিলেন। ততদিনে স্নেহের স্তরটি তিনি অতিক্রম করেছিলেন। এই স্নেহবশতই ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই প্রমথ চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:
সুনীতি আমার কাছে আসবার আগেই অজিত [কুমার চক্রবর্তী] আমার কাছ থেকে সার্টিফিকেট আদায় করে নিয়ে গেছে। কিন্তু তবু সুনীতিকে কিছু না-দিয়ে পারলুম না—কেননা ওর যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নেই।
সেই ‘যোগ্যতা’ই কবির শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করে নিতে পেরেছিল একেবারে তাঁর ভ্রমণসঙ্গী হবার দুর্লভ অবকাশ পাওয়ার সূত্রে। এ কথা বলার আগে এর আগের কথা একটু বলে নিই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি চাক্ষুষ করেছিলেন ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে—আগেই তার ইঙ্গিত দিয়েছি। এ বিষয়ে তাঁরই একটি সাক্ষ্য উদ্ধার করে চক্ষু-কর্ণ সার্থক করি।
রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রথম চাক্ষুষ দেখি স্বদেশি আন্দোলনের গোড়ার দিকেই—বোধহয় ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে, তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে (এখনকার বিদ্যাসাগর কলেজে) ‘ডন সোসাইটি’ নামক কলেজের যুবকদের একটি ক্লাব বা সভায় (যে-সভা থেকে তখনকার দিনের পক্ষে খুবই উচ্চকোটির একখানি সংস্কৃতিমূলক ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হত—The Dawn Society’s Magazine; অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ডন সোসাইটির পরিচালক ছিলেন) বক্তৃতা দিয়েছিলেন; বিষয়টি ছিল, যতদূর মনে হচ্ছে, ‘দেশের অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে শিক্ষা বা অক্ষর পরিচয় প্রচারের জন্য যুবকদের কর্তব্য।’ পরে কলেজে পড়তে পড়তে কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে একদিন রবীন্দ্রনাথের দর্শনলাভ হয়—এটি দ্বিতীয় দর্শন—কী একটা সভায় রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। সেখানে স্বর্গীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নির্বন্ধে তিনি একটি গান গেয়েছিলেন, সে গানটি তখন থেকেই আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল—‘তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি’—এই গানটি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যেবার তিনি ‘আত্মপরিচয়’ বলে প্রবন্ধটি পড়েন, সেবারও তাঁর দর্শনলাভ ও পাঠ-শ্রবণ ঘটেছিল। তারপরে এম এ পাস করবার পরে শান্তিনিকেতনে যাই, সেখানে তাঁর সঙ্গে বাঙলা ভাষা নিয়ে প্রথম আলোচনা করি; তখন আমি বাঙলা ভাষার ইতিহাসের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করার আশঙ্কা নিয়ে পড়াশুনা করতে আরম্ভ করেছি মাত্র। …‘বিচিত্রা’ আলোচনী সভা কবির চেষ্টায় ঠাকুরবাড়িতে স্থাপিত হয়, তাতে আমন্ত্রণ পাই,—কবির ‘ডাকঘর’ আর ‘ফাল্গুনী’র অপূর্ব অভিনয়ও দেখি। এইরূপে আস্তে আস্তে দেশে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতা (২২, শঙ্কর ঘোষ লেনে) প্রদান করেন—সেটি প্রদত্ত হয় ৫ নভেম্বর ১৯০৫, রবিবার বিকেলে। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের যে-সভায় সুনীতিবাবু রবীন্দ্রনাথকে দ্বিতীয়বার দেখেন সেটি ছিল সংগীতজ্ঞ এনায়েৎ খানের বক্তৃতাসভা। রবীন্দ্রনাথ সেখানে সভাপতিত্ব করেন। স্যার গুরুদাসের অনুরোধে তিনি যে-গানটি শোনান—The Bengalee পত্রিকার ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তারিখের বিবরণে সেটি ‘which was of course listened to with rapt attention’ বলে উল্লিখিত। সভায় উপস্থিত অধ্যাপক সুখরঞ্জন রায় লিখেছেন (তাঁর রবীন্দ্র কথা-কাব্যের শিল্পসূত্র গ্রন্থের পূর্বকথা অংশে) যে, গানটি ছিল ‘তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী।’ সভাটি সম্ভবত ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
লণ্ডনে পড়াশুনোর জন্যে সুনীতিকুমারকে সেখানে থাকতে হয় ১৯১৯-’২১ কালপর্বে। রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে যান ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে তাঁকে YMCA সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে ১২ জুন তারিখে, তাতে সুনীতিকুমার উপস্থিত ছিলেন। ‘লণ্ডনে রবীন্দ্রনাথ’ নামের একটি প্রবন্ধে তিনি সভার একটি সরস বর্ণনা দিয়ে গেছেন। সেটি সমগ্রতই উদ্ধার্য—তবুও আমি অংশবিশেষ উল্লেখ করছি :
রবীন্দ্রনাথ কোন তারিখে লণ্ডনে এসে পৌঁচেছিলেন তা মনে নেই। তাঁর বাসার সন্ধান না পাওয়ায় প্রথমেই তাঁর কাছে গিয়ে উঠতে পারিনি। জুন মাসের গোড়ায় শুনলুম, রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার জন্য ১২ জুন তারিখে YMCA দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ছাত্রাবাসে আর ক্লাবে একটি সভা হবে। ওই সময়ে ১০ জুন ছিল আমার একটা পরীক্ষা, পরীক্ষার জন্য একটু ব্যস্ত থাকায়, আর ঠিক ওই সময়ে আমাদের ইউনিভার্সিটি কলেজের ফনেটিক্স বিভাগে ক্যোপন-হাগনের বিখ্যাত অধ্যাপক অটো য়েস্পরসেন আসায়, তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা আর তাঁর সম্মাননার জন্য ডিনারের আয়োজন থাকায়, আমি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি। পরীক্ষা চুকল ১২ দুপুরে, আর সন্ধ্যায় ছিল ভারতীয় ছাত্রাবাসে, গাওয়ার ষ্ট্রীটের তখনকার দিনের বিখ্যাত কাঠের বাড়ি শেকসপিয়র-হাট-এ রবীন্দ্র-স্বাগত-সভা। ইতিপূর্বে বাঙালি ছাত্রেরা সকলকে অনুরোধ করেছিল, ভারতীয় ছাত্রেরা যেন ভারতীয় পোশাক পরেই সেই সভায় হাজির হন। তদনুসারে আমি ধুতি পাঞ্জাবি শাল ব্যাগে করে সভার স্থল ছাত্রাবাসে নিয়ে যাই, সেখানে একটি বাঙালি বন্ধুর ঘরে বিলিতি কাপড়-চোপড় ছেড়ে সেগুলি পরে নিই। সভাস্থলে গিয়ে দেখি, যেন দেশেরই কোনো সভা; ইংরেজ আর অন্য ইউরোপীয় মেয়ে-পুরুষ অনেক আছে, কিন্তু ভারতীয়েরা সকলেই প্রায় ‘ভারতীয় পোশাকে’, অর্থাৎ কোনো-না কোনো রকমের প্রাদেশিক ভারতীয় পোশাক পরে এসেছে। মারাঠী জরির আঁচলা বা পাড়ওয়ালা লাল রেশমের বাঁধা পাগড়ি, তিলক গোখলে এঁরা যেমন পরতেন; জবরদস্ত শিখ পাগড়ি, লুঙ্গি আর কুলহা মিলিয়ে পাঞ্জাবি পাগড়ি, রাজপুতানার রঙীন সাফা, মাদ্রাজি জরিপাড় সাদা পাগড়ি ভারতীয় মুসলমানের তুর্কি ফেজ, উত্তর-ভারতের আর গুজরাটের হিন্দুর গোল ফেল্টক্যাপ—এইসব রকমারি শিরস্ত্রাণ; তারপরে আচকান, গলা-আঁটা কোট, গলা-খোলা কোট, কোর্তা, পাঞ্জাবি; রঙীন চাদর, জরিপাড় চাদর, শাল; ধুতি, যোধপুরী পাজামা, ঢিলে ইজের; বিলিতি জুতো, নাগরা, মারাঠী চটি; খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত মোজা; সব ছিল। একজন পরিচিত ইংরেজ ছোকরা, একটু বেশিরকম চালাক, এই হরেক রকম ভারতীয় পোশাকের পসার দেখে আমায় চুপিচুপি বললে—‘A brave and varied display’। যা হোক, সকলে তো সভায় উপস্থিত হয়ে জাঁকিয়ে বসল; ছাত্রদের মধ্যে যারা কর্মকর্তা, তারা ঘোরাফেরা করতে লাগল; রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় আমরা সভাগৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে রইলুম; রকমারি দেশি পোশাক পরা এতগুলি ভারতীয়কে রাস্তার ধারে অপেক্ষা করতে দেখে, স্থানীয় পথচলতি মেয়ে-পুরুষ ইংরেজদেরও একটা ভীড় জমে গেল। রবীন্দ্রনাথ এলেন, সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ; অনেকেই আমরা তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলুম, স্মিতহাস্যে কারুকে দুই-একটি কুশল জিজ্ঞাসা করতে-করতে তিনি আমাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসলেন। সব ‘Indian style’-এ করবার চেষ্টায়, তাঁকে চেয়ারে না বসিয়ে, ক্লাবের কাঠের মেঝের উপরে গালচে পেতে ভারতীয় ধরনে আসর করা হয়েছিল। গ্রীষ্মের দিন, অগ্নিকুন্ডে আগুনের দরকার হয়নি, মেঝেয় বসে ঠান্ডা লাগবার ভয় ছিল না; আর চমৎকার পারস্যদেশীয় গালচে সভার জন্য সংগ্রহ করে আনা হয়েছিল। আমরা জনকতক তাঁর সঙ্গে মাটিতে ফরাসের উপরে বসলুম, বাকি সব দর্শকেরা—বেশির ভাগ লোক—তিনদিক ঘিরে চেয়ারেই বসল। অনেক দিনের কথা, সমস্ত কার্যক্রম মনে নেই, তবে কতকগুলি ব্যাপার যা মনে আছে তা বলছি। আমরা কবির কাছেই বসতে পেরেছিলুম, কারণ আমরা ক’জন, দেখলুম, কবির পূর্ব-পরিচিত। দিলীপ রায় ছিলেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—আরও জনকয়েক ছিলেন। ছাত্রাবাসের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন কতকগুলি মহীশূরের ধূপকাঠি যোগাড় করে এনেছিল, কিন্তু সেগুলি জ্বালিয়ে দেখা গেল যে, ধূপদান নেই। কবির সামনে ধূপ জ্বালাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু ধূপকাঠি কীসের মধ্যে রাখা হবে সে বিষয়ে কেউ ভাবেনি। একটি বুদ্ধিমান ছেলের পরামর্শে তখন একখানা সাবান যোগাড় ক’রে তাতে ধূপকাঠিগুলি বিঁধিয়ে একটি রেকাবির উপরে রেখে রবীন্দ্রনাথের সামনে বসানো হল; গৃহস্থঘরের পূজায় যেমন একটা কলায় বা এক টুকরো শশায় ধূপ বিঁধিয়ে রাখা হয়। প্রোগ্রামের মধ্যে মুখ্য কার্য ছিল রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত করা; ছাত্রদের তরফ থেকে দু-একজন বক্তৃতা দিয়ে তাঁর প্রশস্তি করে কার্য সমাধা করলে, তার মধ্যে বিশেষ লক্ষণীয় কিছু ছিল না; আর কবিও উত্তর দিলেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ মনোহর ভাবে আস্তে-আস্তে তিনি কিছু বললেন। এই দুই প্রধান কার্যের পূর্বে আর পরে অন্য কতকগুলি ব্যাপার ছিল—তার মধ্যে আমার বেশ মনে আছে, প্রথমদিকে ছিল কতকগুলি কবিতা পড়া, আর শেষের দিকে দিলীপের গান। একটি গুজরাটি মুসলমান ছেলে, তখনকার দিনে সে শেকসপিয়র-হাটের আড্ডায় একজন মাতব্বর ছিল, বহুকাল ধরে অধ্যবসায়ের সঙ্গে কেমব্রিজ আর লণ্ডনে অধ্যয়ন করছে, পাস আর তার করা হচ্ছে না, সে ছোকরা তার স্বরচিত এক ইংরেজি কবিতা পড়লে; কবিতার একটি অপূর্ব লাইন এখনও মনে আছে, তবে তার অর্থটা এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি—Tagore, O Tagore, Launch thy boat ashore। আর একটি মধ্যপ্রদেশের ছাত্র—হিন্দীভাষী—তারস্বরে সুর ক’রে তার হিন্দী কবিতা শোনালে—প্রত্যেক ছত্রটি দুবার করে করে ‘দোহরাইয়া’ পড়লে, পাছে আমরা রস-গ্রহণ করতে না পারি সেই আশঙ্কায়। কবিতাটির আরম্ভটা মনে আছে, সেটা এই রকমের—‘‘স্বস্তি শ্রীরবি-ইন্দ্রনাথ, স্বাগত তুম হো ইস শেকসপিয়র-হাট্ট মে’’—এক ‘ইস’ ছাড়া সব শব্দগুলি স্বরান্ত করে পড়া হল। কবিতাটির মধ্যে একটি জোরালো লাইন ছিল; ছোকরা সেটিকে যথারীতি দুবার পড়ে ‘দোহরালে,’ তিনবার পড়ে ‘তেহরালে,’ চারবার পড়ে ‘চৌহরালে,’ কিন্তু দেখলে যে তার কৃতিত্বের অন্তর্নিহিত ভাবটুকু কেউ ধরতে পারলে না—তার পক্ষে চার-চারবার লাইনটি পড়া ‘অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম’ হল; লাইনটি এই—‘তুম-নে ইনকে সর-পর লাত মারা।’ শেষটায় মরিয়া হয়ে কবিটি নিজেই হিন্দী ভাষায় ভাষ্য করলে—‘‘ইস লাইন কো সোচ কর দেখিয়ে; ‘সর’ য়হ শব্দ দো অর্থ-মেঁ হৈ; চাহে ইসে ইংলিশ ‘সর’ সমঝিয়ে, চাহে figurative অর্থ-মেঁ লীজিয়ে।’’ অর্থাৎ লাইনটির মানে—তুমি এদের সর-এর উপর লাথি মেরেছ; সর—ইংরেজি sir, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যে ব্রিটিশরাজ-দত্ত ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ ক’রেছেন, সেই অর্থে লাইনটি নেওয়া যায়; আর ‘সর’ মানে মাথা; দ্বিতীয় অর্থটি খুব যে উচ্চ ভাবের পরিচায়ক, তা নয়। যা হোক লেখকের নিজের ভাষ্যে যখন হিন্দী আর উর্দু-ওয়ালাদের কাছে অর্থটি সুপরিস্ফুট হল, আর আমাদের মত অহিন্দুস্থানী বাঙালি মারাঠী গুজরাটিদের কাছেও, তখন একটা উৎসাহের ঢেউ খেলে গেল, জালিয়ানওয়ালাবাগের পরে রবীন্দ্রনাথ যে ‘স্যর’ উপাধি ত্যাগ করেছিলেন সে কথা স্মরণ করে দেশাত্মবোধের হাওয়ার একটা হিল্লোল এসে সমবেত ভারত-সন্তানদের হৃদয়কে আলোড়িত করে দিয়ে গেল—তারস্বরে সকলে এই লাইনের তারিফ করে আর খুশীর সঙ্গে গর্বপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে ‘বন্দে মাতরম’ আর ‘রবীন্দ্রনাথ-কী জয়’ করে উঠল। পরিচিত একজন ইংরেজ ভদ্রলোক পিছন থেকে এসে কানে-কানে জিজ্ঞাসা করলে, ‘কী ব্যাপার? কবিতা-পাঠে এতটা উৎসাহ কেন? জাতীয় কবিতা বুঝি?’ কী উত্তর দিই? বললুম, ‘It is all for a pun, which is thought to be rather neat.’ কবিটি তো তখন উৎসাহের সঙ্গে আরও দুবার তার এই লাইন শোনালে; রবীন্দ্রনাথ কিন্তু অধোবদন হয়ে রইলেন। শেষটায় বোধ হয় দিলীপের গান হল। ঠিক মনে নেই, তবে যেন তিনি তাঁর পিতার ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’ গেয়েছিলেন, আর পরে তাঁর অনুরাগী বন্ধুদের অনুরোধে তিনি এই গানটির ইংরেজি অনুবাদ (বাঙলা গানটির-ই সুরে) গেয়েছিলেন। এই সহজ সুরের গানটিতে তাল দেওয়া নিতান্ত আনাড়ি তাল-কাণা লোকের পক্ষেও কঠিন নয়; ইংরেজিতে গানের মানে ধরতে পেরে, যারা চেয়ারে বসেছিল সেইসব ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে কাঠের মেঝেয় পা ঠুকে-ঠুকে তাল দিতে লাগল।
পরে কবির সঙ্গে, তাঁর এই সংবর্ধনা কেমন লেগেছিল সে-সম্বন্ধে কথা হয়েছিল। ‘তুম-নে ইন-কে সর-পর’—এই লাইনের কথাও তুলেছিলুম। তিনি খালি বলেছিলেন, ‘সব রকমই শুনতে হয়, যেতে দাও। তবে ভাবি, এত খরচপত্র করে এরা এতদূর আসে কেন।’
এই স্মৃতিকথায় তিনি আরও লিখেছিলেন :
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করতে যেতুম। দুই-একবার তিনিও আমাকে আসবার জন্য খবর দিয়েছিলেন। তিনি লণ্ডনে মাসকয়েক থেকে, একবার আমেরিকা ঘুরে এলেন। লণ্ডনে তিনি থাকতে-থাকতে আমরা জনকয়েকে মিলে ছুটির মধ্যে স্কটল্যাণ্ড আর লেক-ডিস্ট্রিক্ট বেড়িয়ে এলুম। আমেরিকা থেকে ফিরে আসবার পরেও তাঁর সঙ্গে খুব দেখা করতে যেতুম। এই কয়মাসের মধ্যে তাঁকে প্রথম একটু অন্তরঙ্গভাবে জানবার সুযোগ আমার হয়েছিল। তখন আমার বয়স তিরিশ; বিলেতে পড়তে গিয়েছে এমন ভারতীয় ছাত্রেরা বেশির ভাগ আমার চেয়ে বয়সে ছোটো; সুতরাং তাঁর সঙ্গে গুরুগম্ভীর বিষয়ে আলাপের সুযোগ সহজেই তিনি আমায় দিয়েছিলেন; আর সেটা আমার জীবনে একটা পরম লাভের বস্তু হয়েছিল। কত না বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা, ক্কচিৎ তর্ক জুড়ে দিয়ে, আমার নিজের মনন-শক্তিকে আমি আগের চেয়ে নির্মল আর স্থূলতাবর্জিত করতে পেরেছি। তাঁর কাছে অনেক বড়ো-বড়ো লোক আসতেন। প্রথমবার তিনি ছিলেন Kensington Palace Mansion বলে একটি হোটেলে; দ্বিতীয়বার ছিলেন আমাদের বাঙলাদেশের চট্টগ্রামবাসী একটী বাঙালী ভদ্রলোকের পরিচালিত আর স্বত্বাধিকারী হিসাবে তাঁর নিজস্ব, Regina Hotel নামে হোটেলে। পরিচয় হয়েছিল অনেকের সঙ্গে; কিন্তু কারো সঙ্গে সে আলাপ জীইয়ে রাখতে পারিনি, কারণ মানসিক চর্চায় বা আলোচ্য বিষয় নিয়ে সকলেই আমার সমানধর্মা ছিলেন না। তবে শান্তিনিকেতনের পিয়ারসন সাহেব, আর দীনবন্ধু চার্লস এফ আন্ড্রুস, এঁদের বেশ লেগেছিল। কবিরই বাসায় লরেন্স বিনয়ন, উইলিয়ম রটেনষ্টাইন, লর্ড সিংহ, স্যর কে জি গুপ্ত—এঁদের দেখি; কবির সঙ্গে রটেনষ্টাইনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বা পারিবারিক সান্ধ্য সম্মিলনে যাই, সেখানে আয়ারল্যাণ্ডের কবি ইয়েটসকে দেখি; রটেনষ্টাইনের বাড়িতে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে পরম ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত দেখত; মনে আছে, ওই দিন কবি তাঁর ইউরোপীয় বন্ধুদের অনুরোধে দুটি বাঙলা গান গেয়েছিলেন, তার মধ্যে ‘দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে’ গানটি ছিল। ইয়েটস ছিলেন একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার লোভ হলেও তেমন সাহস আমার হয় নি, কারণ সাহিত্যরস-রসিক আমি মোটেই ছিলুম না—তাঁর মত লোকের সঙ্গে কথা কইবার যোগ্যতা আমার ছিল না।
বিখ্যাত রুশ শিল্পী নিকোলাই র্যোরিখ ইংল্যাণ্ডে নির্বাসন যাপন করছিলেন। ইনি ছিলেন সোভিয়েট বা বলশেভিক তন্ত্রের বিরোধী, সেইজন্য এঁর বিশাল প্রাসাদ, প্রাচীন বস্তুর সংগ্রহ, সব ছেড়ে দিয়ে, দেশ ত্যাগ করে বাইরে এসে এঁকে থাকতে হ’য়েছিল। এঁর দুই ছেলের মধ্যে বড়ো ছেলে য়ুরি বা জ্যরজ লণ্ডনের স্কুল-অব-ওরিয়েন্টাল স্টাডিস-এ পড়তেন, য়ুরির আলোচ্য ছিল তিব্বতী আর সংস্কৃত। আমিও সেই স্কুলের ছাত্র ছিলুম; সেই সূত্রে য়ুরি র্যোরিখ-এর সঙ্গে ভাব হয়, পরে তিনি তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর বাপ-মা আর ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এঁদের বাড়ীতে মাঝে-মাঝে যেতুম। এঁরা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ অক্সফোর্ড থেকে লণ্ডনে আসতেই, তাঁর সঙ্গে র্যোরিখের পরিচয় করিয়ে দেবার কর্তব্য সহজেই আমার উপর পড়ল। র্যোরিখ নিজে একদিন আমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে এলেন—ছেলেরাও তাঁর সঙ্গে এল; আমি কবিকে আগেই এঁর কথা বলে রেখেছিলুম। ইনি কবিকে নিজের আঁকা একখানি ছবি উপহার দিলেন, কবির একটি কবিতার রুশ ভাষায় অনুবাদ (‘ওগো মা, রাজার দুলাল যাবে…’ এই কবিতাটি) পড়ে শুনিয়ে, ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করলেন—‘এখন আপনার নিজের লেখা বুঝতে পারলেন?’ দুজনে খুবই হৃদ্যতা জমে উঠল। কবিও একদিন নিমন্ত্রিত হয়ে র্যোরিখের বাসায় গেলেন, র্যোরিখ-গৃহিণী খুব শ্রদ্ধা আর সম্মানবোধের সঙ্গে কবিকে স্বাগত করলেন। এঁদের মধ্যে তার পরে মাঝে-মাঝে দেখাসাক্ষাৎ হত। আমি আমার পরিচিত সতীর্থ কতকগুলি ইংরেজ আর অন্যদেশীয় ইউরোপীয় ছাত্র, যারা কবির কাব্য পড়ে তাঁর অনুরাগী হয়েছে, তাদের বারকতক কবির কাছে নিয়ে গিয়েছিলুম। কবি বেশ খুশি মনে দিলখোলা ভাবে এই বিদেশি তরুণদের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন; এই আলাপের স্মৃতি তাদের মনে নিশ্চয়ই চিরকাল ধরে জাগরূক থাকবে। আমার মনেও এদের নিয়ে যাওয়া আর কবির সঙ্গে এদের কথাবার্তার অনেক কিছু এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। বেশি উৎসাহ দেখতুম কন্টিনেন্টাল ছাত্রদের মধ্যে। এখন একদিনকার কথা বেশ মনে পড়ছে। কবি কথায়-কথায়, বইয়ের মারফৎ বড়ো কবির কাব্য বা মহাপুরুষের বাণী ভবিষ্যৎ যুগের লোকেদের কাছে শোনানোর চেয়ে কোনও রকমে তাঁদের মুখের কথায় সেই বাণী তাদের ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে’ পৌঁছানোর বেশি উপযোগিতায় তাঁর বিশ্বাস আছে, এই মন্তব্য করলেন। তাতে এই মন্তব্য নিয়ে আলোচনা চলল; সে কী ক’রে করা যায়? কবি বললেন, কেন, গ্রামোফোন রেকর্ডে করে; এই বলে এই idea বা ভাবটি তিনি একটু ফলাও করে বলতে লাগলেন—
দেখ হে, ভবিষ্যতে হয়তো লাইব্রেরিতে বইয়ের বদলে, আজকালকার যুগের পরের যুগের কবি আর লেখকদের মুখের কথা, তাদের বক্তৃতা বা পাঠের রেকর্ড তৈরি করে রাখতে হবে। কেউ লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়বে না; রেকর্ড বার করে বাজাবে, আর মনীষী আর কবিদের শিক্ষা, চিন্তা আর অনুভূতি বা সৌন্দর্য-দর্শনের কথা তারা কানে শুনে ধরতে পারবে—এইভাবে সোজাসুজি কবির বা দর্শনশীল ব্যক্তির মুখের কথা আমাদের উত্তরপুরুষদের কানের ভিতরে যাবে।
তাতে একটি ইটালীয় ছেলে বললে, আচ্ছা, তা হলে লাইব্রেরিতে একসঙ্গে পাঁচ-শ’ লোক যদি পাঁচ-শ’-খানা রেকর্ড বার করে পড়তে আরম্ভ করে, তা হলে নানা ভাষায় পাঁচ-শ’ গলায় একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হবে না? কবি তা শুনে হেসে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন:
তা হবে কেন? রেলস্টেশনে যেমন বাহিরের আওয়াজ বাঁচাবার জন্য টেলিফোনের কাচ দিয়ে ঘেরা ঘর থাকে, সেই ধরণের ঘর প্রত্যেক ‘পাঠক’ অর্থাৎ শ্রোতার জন্য হবে, তাতে সকলে নিশ্চিন্ত মনে বাণী শুনতে পারবে।
এই রকম কত বিষয়ের অবতারণা করতেন, আবার সে সবের সমাধান করতেন। প্রত্যেক বার-ই এইসব ছাত্রছাত্রী যারা আমার সঙ্গে কবির কাছে যেত, সকলেই মুগ্ধ হয়ে ফিরে আসত।
এখন আমার মনে আফসোস হয়, কেন কবির সঙ্গে কথাবার্তার খুঁটিনাটিতে পূর্ণ রোজনামচা তখন রাখি নি, তা হলে হয়তো তাঁর অনেক ক্ষণিকের উক্তি, ক্ষণপ্রভার মত উঁকি দিয়ে চলে গিয়েছে, তা ধরে রাখতে পারা যেত। কিন্তু হায়, রবীন্দ্রনাথের মত লোকোত্তর প্রতিভাকে, তার সমস্ত শক্তি আর প্রকাশভঙ্গীসমেত কে লোক-সমক্ষে সম্পূর্ণ ধরে দিতে পারে? তিনি নিজে যা দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের তাঁর বিভূতির যে অংশ তিনি স্বয়ং প্রকাশ করে গিয়েছেন, তারই প্রাচুর্য আর নানামুখিতা এক বিস্ময়কর বস্তু; কেবল তারই পূর্ণ সমাদর করতে, তার গৌরব থেকে প্রসাদ লাভ করতে, আর তা থেকে নিজেদের আত্মসংস্কৃতি আনতে আমরা যেন সমর্থ হই।
—শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৪৮
আবার আমরা পুরেনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই—কবির সঙ্গে তাঁর দ্বীপময় ভারত ভ্রমণের প্রসঙ্গে। তাঁদের উভয়ের পত্রাবলী সংগ্রহ করে সুনীতিকুমারের শতবর্ষে দেশ পত্রিকার সুনীতিকুমার সংখ্যায় (২৮ জুলাই ১৯৯০) যে-বিস্তৃত প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, তার অংশবিশেষ উদ্ধার করছি :
সুনীতিকুমার ছাড়া তাঁর সঙ্গে এই ভ্রমণযাত্রায় সঙ্গী হলেন সুরেন্দ্রনাথ কর এবং ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা প্রমুখ ব্যক্তিগণ। মাদ্রাজ থেকে জাহাজ ছাড়ল ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই তারিখে। জাভা, বালী প্রভৃতি দ্বীপ ভ্রমণের পর সিয়াম হয়ে এ বছরের অক্টোবরের শেষে কবি ফিরে এলেন দেশে। বিশ্বভারতী পত্রিকা ও প্রবাসী পত্রে এই ভ্রমণযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণ সুনীতিকুমার প্রকাশ করেন। পরে তা রবীন্দ্রসঙ্গমে দ্বীপময় ভারত ও শ্যামদেশ নামে সেপ্টেম্বর ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-সুনীতিকুমার সাহচর্যের কথা সবিশেষ জানেন। প্রকৃতপক্ষে ‘সাগরিকা’ নামে বিশেষ পরিচিত মূল ‘বালী’ কবিতাটি সুনীতিকুমারের খসড়াতেই প্রথম ধরা পড়ে, পরে রবীন্দ্রনাথ এর সংযোজন-বর্জন করেন। সুনীতিকুমার লিখেছেন—‘আজ কবি [শনিবার, ২২এ অক্টোবর ১৯২৭] আমার খাতাখানি চেয়ে নিয়ে, তাতে নকল-করা তাঁর ‘‘বালী’’ কবিতাটিকে নিজের হাতে কিছু সংশোধন ও সংযোজন লিখে দিলেন, আর তার নীচে নিজের নাম সই করে দিলেন। এইভাবে কবির এই অপূর্ব সুন্দর কবিতাটি নতুন রূপে তাঁর শ্রীহস্তের ছাপ নিয়ে আমার খাতায় শোভা পাচ্ছে।’
এই তিনমাস রবীন্দ্রসাহচর্য সুনীতিকুমারের জীবনকে কানায় কানায় পূর্ণ করে তোলে। এ সময় থেকেই উভয়ের মধ্যে পত্রালাপও চলতে থাকে। আমাদের সৌভাগ্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ চিঠি আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি, কিন্তু সুনীতিকুমারের লেখা চিঠিগুলির বেশিরভাগই উদ্ধার করতে পারিনি। সে আমাদের দুর্ভাগ্য। অথচ একসময়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে ‘জাভাযাত্রীর পত্র’-এ (৩ শ্রাবণ ১৩৩৪) নির্মলকুমারী মহলানবীশকে লিখেছিলেন :
…কিন্তু, সকলপ্রকার রচনাই স্বাভাবিক শক্তির অপেক্ষা করে। চিঠি-রচনাও তাই। আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পন্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ, আস্ত জিনিসকে টুকরো করা ও টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় করে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তালভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত সম্পূর্ণ তুলে নিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছুই নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত, একথা বলা চলে যে শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে শব্দচিত্র তাদের এলেকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলায়। কিন্তু, সুনীতির মনে সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারেনি এই বড় অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে—দেখবে এগুলো একেবারে বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম; বর্ণনা সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী ছোট বড় কিছুই তার থেকে বাদ পড়েনি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত—লিপিবাচস্পতি কিম্বা লিপিসার্বভৌম কিম্বা লিপি চক্রবর্তী। ইতি।
প্রকৃতপক্ষে সুনীতিকুমারের ‘দর্শনশক্তি’ এবং ‘ধারণাশক্তি’ ‘আগ্রহ’ এবং ‘সংগ্রহ’ সবকিছু সম্পর্কেই কবি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি যে প্রত্যাশা করেছিলেন—‘তাঁর হাতে আমাদের ভ্রমণের ইতিবৃত্ত লেশমাত্র ব্যর্থ হবে না, লুপ্ত হবে না’—তা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এই দর্শন ও ধারণাশক্তির প্রতি আস্থাবশতই একদা কবি সুনীতিকুমারকে উপন্যাস রচনায় পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিলেন (দ্রষ্টব্য: পত্রসংখ্যা-১)। সুনীতিকুমার উপন্যাস অবশ্য লেখেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বোধকরি সেই শূন্যস্থান পূরণ করে তাঁর শেষের কবিতা উপন্যাসে সুনীতিকুমারকে অমর করে দিয়ে গেছেন। অমিত রায়ের কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন:
কিছুদিন ওর কাটলো পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই পড়ে পড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাঙলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।
সুনীতিকুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নৈকট্য দুজনকে শুধুমাত্র সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেনি। সেকালের আধুনিক সাহিত্যে যে-রবীন্দ্রবিরোধিতা দেখা দিয়েছিল প্রধানত শনিবারের চিঠি-কে কেন্দ্র করে তা যেমন প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি রাজনৈতিক, সামাজিক নানা প্রসঙ্গেও উভয়ের মধ্যে মতবিনিময় হয়ে চলেছিল। দুজনই আপন আপন ব্যক্তিগত মনের জানালা খুলে দিয়ে দুজনকে চিনে নিতে পেরেছিলেন। শনিবারের চিঠি-র দলে ছিলেন সুনীতিকুমার। সেজন্য তাঁর মাধ্যমেই অনেকসময় রবীন্দ্রনাথ নিজের মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন। এমনকী এ বিষয়ে সুনীতিকুমারের ভূমিকা নিয়েও কবির ক্ষোভ ছিল। হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে তা সহজেই ধরা পড়ে রয়েছে:
আমার বন্ধু সুনীতি সজনীকান্তের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এমনকি আমার দৃঢ় বিশ্বাস শনিবারের চিঠিকে তিনি আমার বিরুদ্ধে গোপনে উত্তেজিত করতে সহায়তা করেন। ও তাতে আনন্দ বোধও করে থাকেন। সেজন্য আমি যদি সুনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতুম—তাহলে তার চেয়ে লজ্জার কথা আমার পক্ষে কিছু হতে পারত না। সুনীতির সমাজমতের সঙ্গে আমার বিরোধ থাকাতে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করেন যে আমি হিন্দু সমাজের শত্রু, অতএব কঠিন শাস্তির যোগ্য—অতএব সেই শাস্তির ব্যবস্থা করা তিনি কর্তব্য বলেই মনে করেন। শাস্তির প্রণালী ও রুচি সম্বন্ধে মানুষের স্বভাব শিক্ষাদায়িক—সে সম্বন্ধেও আমাদের আদর্শের সঙ্গে তাঁদের মিল না থাকতে পারে কিন্তু তাই নিয়ে যদি আমি বিবাদ করতে পারি তবে সেইটেই যথার্থ গ্লানির বিষয় হত।
কিন্তু ১৯৩২ সালের এই ঘটনাটিই শেষ কথা ছিল না। এই ‘কলহে’ সুনীতিকুমার কী পরিমাণ বেদনাবোধ করতেন তা কবিকে লেখা তাঁর পত্রের খসড়াটি (পত্রসংখ্যা-১৬) থেকে আমরা জানতে পারি (মূলপত্র আমাদের হস্তগত হয়নি)। রবীন্দ্রনাথ যেমন এসব কথা ভুলে গেছিলেন, সুনীতিকুমারও তেমনি তাঁর মনের ব্যাপ্তি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। তাই রবীন্দ্রধ্যানই তাঁর জীবনে শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রকবিতা পাঠ, রবীন্দ্রসংগীত শ্রবণ, নবজাতকের ‘কেন’ কবিতাটির প্রতি তাঁর গভীর আসক্তি, বলাকা-র ১৯-সংখ্যক কবিতার প্রতি দুর্নিবার আগ্রহ, শেষ লেখা-র প্রথমদিনের সূর্য-র বারংবার আবৃত্তি, পত্রপুট-এর ‘glorious sublime’ ‘আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী’—এই মন্ত্রোচ্চারণ—সুনীতিকুমারের শেষ জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাসূত্রে এবং সেখানের বানান সংস্কার সমিতির সংযোগে দুজনের মধ্যে এই সম্পর্কের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়ে চলেছিল। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে কবি তাঁর বাঙলা ভাষা পরিচয় গ্রন্থটি ‘ভাষাচার্য শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের করকমলে’ উৎসর্গ করে তাঁর অমিত স্নেহের চিরস্থায়ী অভিজ্ঞানটি রেখে গেছেন। সুনীতিকুমারও রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তাঁর বৈদেশিকী বইটি ‘বিশ্ব-মানব-সংস্কৃতি কেন্দ্র/বিশ্বভারতী/ ‘‘যত্র বিশ্বম ভবত্যেক নীড়ম’’ তৎ-প্রতিষ্ঠাতা বাকপতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ/ শ্রীচরণোদ্দেশে’ নিবেদন করে আভূমি প্রণতি জানিয়েছিলেন।
যে বানান কমিটির কথা আমরা বলে এলাম, সেই কমিটির একটি উপভোগ্য স্মৃতিচারণ লিখে গেছেন হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। সেটি অবশ্যপঠিতব্য। হীরেন্দ্রনারায়ণকে উদ্ধার করছি :
রবীন্দ্রনাথের মুখ থেকে সাহিত্য সম্পর্কে কিছু শোনার আগ্রহ ছিল। কিন্তু বাধা পড়ল সুনীতিবাবু, চারুবাবু ও বিজন ভট্টাচার্যের আগমনে।
‘তারপর কী খবর?’ রবীন্দ্রনাথ তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন।
‘বানান পরিষদের দায়িত্ব পড়েছে ঘাড়ে। তাই বাঙলা বানান সম্বন্ধে আপনার কিছু মতামত দরকার’—বলে নিজেকে একটু এগিয়ে দিলেন সুনীতিবাবু।
ক্ষণকাল মৌন থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ তো ছিল না কোনোদিন। ও পথ মাড়াইনি। আমার মতামত!’
‘আপনার মতামত ছাড়া কি বাঙলা ভাষার কোনো পরিবর্তন করা চলে! বিশেষ করে আমাদের যুগে যখন আপনাকে পেয়েছি।’ বলে সুনীতিবাবু বানানের কথা পাড়লেন। ‘কতকগুলো শব্দের মৌলিক রূপটা বজায় রাখবার জন্য চলতি বানান কিছু কিছু পরিবর্তন করতে চাইছি।’
‘যথা?’ রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।
সুনীতিবাবু বললেন, ‘যেমন গরু। আমরা বানান লিখি গরু। কিন্তু আমার মনে হয় শব্দটা গো-রূপা থেকে এসেছে। সুতরাং বানানটা গরু না হয়ে গোরু হলেই ভালো হয়।’
‘হাঁ। অন্তত কলেবর বৃদ্ধি হয়। গাইগুলো দিন দিন যেন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, কলেবর বাড়ানো ভালো নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে দুধ বাড়বার সম্ভাবনা আছে কি?’ রবীন্দ্রনাথ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ তুলতে চাইলেন। কারো পক্ষেই হাসি সংবরণ করা সম্ভব হল না।
রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সুনীতিকুমারের কত স্মৃতি। অনেকেই একটি ইংরেজি শব্দের বঙ্গায়ন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রসঙ্গ মনে রেখেছেন হয়তো—সেটি হল ‘culture’ শব্দের সঠিক বঙ্গানুবাদ নিয়ে। অনেক রূপান্তর ঘটেছিল—শেষ পর্যন্ত সংঘাতের ক্ষেত্র হয়েছিল ‘কৃষ্টি’ আর ‘সংস্কৃতি’ শব্দ দুটি। রবীন্দ্রনাথেও পছন্দ ‘সংস্কৃতি’ শব্দটিই। সুনীতিকুমার এ-বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন—
‘সংস্কৃতি’ শব্দ culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই খুশি হন। এই শব্দটি বাঙলায় এখন থেকে [১৯৭৬] ২৪/২৫ বছর আগে কেউ ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না।…
১৯২২ খ্রিস্টাব্দে দেশে ফিরে [লন্ডন থেকে] রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ করি। তিনি আগে থাকতেই এই শব্দটি পেয়েছিলেন কিনা, জানি না—সম্ভবত শব্দটি তাঁর অবিদিত ছিল না। তবে আমার বেশ মনে আছে, culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ‘সংস্কৃতি’ শব্দ সম্বন্ধে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ অনুমোদন জ্ঞাপন করেন। ‘কৃষ্টি’ শব্দ আর ব্যবহার করা ঠিক হয় না, একথাও বলেন। ‘সংস্কৃতি’ শব্দ ঋকবেদে নেই, কিন্তু ‘ব্রাহ্মণ’ গ্রন্থে আছে আর এ বিষয়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে উদ্ধৃত একটি অতি সুন্দর উক্তির প্রতি শান্তিনিকেতনের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব থেকেই এটি দেখে থাকবেন।…
আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করছি রবীন্দ্রনাথের ভাষাধিকারের একটি মনোহর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। এটি আমি স্বয়ং সুনীতিকুমারের মুখে শুনেছিলাম। লিখিত একটি প্রবন্ধেও সংক্ষেপে তিনি এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে গেছেন। আমি যেমন শুনেছিলাম—তেমনভাবেই লিখছি : শান্তিনিকেতনে তখন অফিসের কাজকর্মও বাঙলা ভাষায় করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাঙলায় বিজ্ঞপ্তিপত্র রচনা অফিসের বড়োবাবু কেন শিবেরও অসাধ্য। তাই বড়োবাবুকে প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের শরণ নিতে হয়। তিনি অফিসের সহায়ক কর্মীকে পাঠিয়ে দেন ইংরেজি বয়ানকে বাঙলায় রূপান্তর করিয়ে নেবার জন্য। একদিন ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী, বিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী মশায়রা ছাড়া সুনীতিকুমারও বসে আছেন। এমন সময় জনৈক অফিস পরিচারক এলেন একটি ইংরেজি বয়ান নিয়ে যার ওপরের দিকে লেখা ছিল—Advisory Council of The Senior Members। কবি একে একে সেন শাস্ত্রী, ভট্টাচার্য শাস্ত্রীদের এর সঠিক বাঙলা কী হবে জানতে চাইলেন। তাঁরা বিনয়াবনত হয়ে বললেন—গুরুদেব আপনি থাকতে আমরা! এবার তাকালেন সুনীতিকুমারের দিকে—‘ভাষাচার্য, তুমিই বলো।’ সুনীতিবাবু পূর্বসূরিদের পন্থাবলম্বন করে একই জবাব দিলেন।
এবার তিনি দেখলেন একখন্ড সাদা কাগজে গুরুদেব কলমে আঁকর কাটছেন—লিখেছেন ‘সুমন্ত্রসভা’। ভাষাচার্য নিম্নস্বরে বললেন, ‘Advisory Council-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ‘‘সুমন্ত্রসভা’’ ঠিকই হয়েছে—যাঁরা সু-মন্ত্রণা দান করবেন। কিন্তু এতে ‘Senior Members’ কথাটি তো ঠিক উপলব্ধ হচ্ছে না। কবি মুহূর্তে বললেন—‘কেন রামচন্দ্র বনবাসে গেলেন, দশরথ মারা গেলেন, ভরত রামচন্দ্রর খড়ম এনে বসিয়েছেন সিংহাসনে। কিন্তু খড়ম তো রাজ্যশাসন করতে পারে না। রামচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন দশরথের অতিবৃদ্ধ অমাত্য সুমন্ত্র। তাঁর চেয়ে Senior আর কে হতে পারেন?’
সুনীতিকুমার লুটিয়ে পড়ে গুরুদেবকে প্রণাম করেছিলেন।
বারিদবরণ ঘোষ
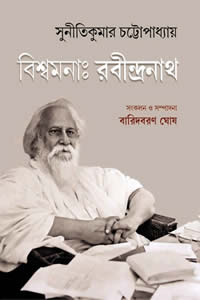

Leave a Reply