বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন – ড. অতুল সুর
Bangla O Bangalir Bibartan [an Ethno-Cultural History of Bengali] By. Dr. Atul sur Published
যে দেশের
ভূমিসন্তান হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি
সে দেশের দেশমাতৃকার চরণে
নিবেদিত হল
গৌড়চন্দ্ৰিকা
প্রাচীন বাঙলার অপর নাম ছিল ‘গৌড়’। সেজন্য বইখানার ভূমিকার নাম দেওয়া হয়েছে ‘গৌড়চন্দ্রিকা’। আর বইখানার শিরোনামে গৃহীত ‘বিবর্তন’ শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আভিধানিক অর্থে। ‘বিবর্তন’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘পরিবতর্ন’। ‘বিবর্তন’ শব্দের সঙ্গে অবনতি বা উন্নতির কোন সম্পর্ক নেই। একমাত্র সম্পর্ক হচ্ছে রূপান্তরের সম্পর্ক। সেজন্য কালের ঘূর্ণনে বিভিন্ন যুগে বাঙালী জীবনে যে রূপান্তর ঘটেছে, তারই ইতিহাস দেওয়া হয়েছে এই বইখানাতে। তবে এ ইতিহাস কোন ‘পোশাকী’ বা ‘ফরম্যাল’ ইতিহাস নয়। সম্পূর্ণভাবে এটা ‘আটপৌরে’ বা ‘ইনফরম্যাল’ ইতিহাস। এটা বিষয় – বিন্যাসের পদ্ধতি থেকেই বুঝতে পারা যাবে। এক কথায় বইখানাতে পাওয়া যাবে বাঙালী জীবনের সৃজন, বিকাশ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস।
বইখানা লেখা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে স্মরণ করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—’আমরা ইতিহাস পড়ি-কিন্তু যে ইতিহাস দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নাম লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাইরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস, তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতে পারে না।’
বাঙালির জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল মানুষের আর্বিভাবের দিন থেকে। ভূ-তাত্ত্বিক আলোড়ন ও চঞ্চলতার ফলে বাঙলা দেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে। ভূতত্ত্ববিদগণের হিসাব অনুযায়ী সেটা ঘটেছিল প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে। মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল আরও পরে, আজ থেকে পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে। তার আগেই ঘটেছিল জীবজগতে ক্রমবিকাশের এক কর্মকাণ্ড। বানরজাতীয় জীবগণ চেষ্টা করছিল বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত হয়ে নানা বৈশিষ্ট্যমূলক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হতে। এরূপ এক শাখা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল নরাকার জীবসমূহ (Primates)। এরূপ নরাকার জীবনসমূহের কঙ্কালাস্থি আমরা পেয়েছি ভারতের উত্তর-পশ্চিম শিবালিক শৈলমালা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে। বিবর্তনের ছকে তাদের আমরা নাম দিয়েছি শিবপিথেকাস, রামপিথেকাস, সুগ্রীবপিথেকাস ইত্যাদি। আরও উন্নত ধরনের নরাকার জীবের কঙ্কালাস্থি পাওয়া গিয়েছে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বে জাভা-দ্বীপে ও চীন দেশের চুংকিং-এ। এখন এই তিনটি জায়গায় তিনটি বিন্দু বসিয়ে যদি সরলরেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়, তা হলে যে ত্রিভুজ সৃষ্ট হবে, তারই মধ্যস্থলে পড়বে বাঙলা দেশ। সুতরাং, এরূপ নরাকার জীবসমূহ যে বাঙলা দেশের ওপর দিয়ে যাতায়াত করত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এসব নরাকার জীব থেকেই মানুষের উদ্ভব ঘটেছিল।
মানুষের প্রথম সমস্যা ছিল আত্মরক্ষা ও খাদ্য আহরণ। জীবন- সংগ্রামের এই সমস্যা সমাধানের জন্য, তাকে তৈরি করতে হয়েছিল আয়ুধ। আয়ুধগুলো একখন্ড পাথর অপর একখন্ড পাথরের সাহায্যে তার চাকলা তুলে হাতকুঠার ও অন্য আকারে নির্মিত হত। এগুলোকে আমরা প্রত্নোপলীয় যুগের আয়ুধ বলি। গঠনপ্রণালী ও চারিত্রিক বিশিষ্টতার দিক দিয়ে এগুলোকে আমরা কালানুক্রমিক সাতটা যুগে ফেলি। যথা (১) আবেভিলিয়ান, (২) অ্যাশুলিয়ান, (৩) লেভালয়সিয়ান, (৪) মুস্টেরিয়ান, (৫) অরিগনেসিয়ান, (৬) সলুট্রিয়ান ও (৭) ম্যাগডেলেনিয়ান। এগুলো সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান ও অনুশীলন হয়েছে পশ্চিম ইউরোপে। সেজন্যই এই সকল আয়ুধের ‘টাইপ’-এর নাম পশ্চিম-ইউরোপের অঞ্চলবিশেষের নাম অনুসারে করা হয়েছে। তবে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদগণ তাদের কাজের সুবিধার জন্য প্রত্নোপলীয় যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা— আদি, মধ্য ও অন্তিম। আয়ুধ নির্মাণ ছাড়া, প্রত্নোপলীয় যুগের মানুষের আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা ভাবপ্রকাশের জন্য ভাষার ব্যবহার, পরিবার গঠন, পশু-শিকার সুগম করবার জন্য পর্বত-গুহায় বা পর্বতগাত্রে পশুর চিত্রাঙ্কন দ্বারা ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ, ও আগুনের ব্যবহার।
মুস্টেরিয়ান যুগের আগেকার যুগের মানুষের কোন কঙ্কালাস্থি আমরা পাইনি। মুস্টেরিয়ান যুগে যে জাতির মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের আমরা নিয়ানডারথাল মানুষ বলি। তবে সে জাতির মানুষ এখন লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে জাতির মানুষ থেকে আধুনিক জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে, তাদের আবির্ভাব ঘটে আনুমানিক ৪০,০০০ বৎসর পূর্বে। তাদের আমরা ক্রোম্যানিয়ন। (Cro-Magnon) জাতির মানুষ বলি।
খুব প্রাচীনকালের মানুষের কঙ্কালাস্থি ভারতে পাওয়া যায়নি। বিখ্যাত প্রত্নাস্থিতত্ত্ববিদ স্যার আর্থার কীথ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর ‘অ্যাটিকুইটি অভ্ ম্যান’ নামক বই লেখেন, তখন তিনি বলেছিলেন— ‘প্রাচীন মানুষের সম্বন্ধে যাঁরা অনুসন্ধান করেন, তাঁরা ভারতের দিকেই আশার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন, কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁদের নিরাশ হতে হয়েছে।’ অনুসন্ধানের উদ্যোগের অভাবই এর একমাত্র কারণ। সম্প্রতি (১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে) মেদিনীপুর জেলার রামগড়ের অদূরে সিজুয়ায় পাওয়া গিয়েছে এক জীবাশ্মীভূত ভগ্ন মানব-চোয়াল। রেডিয়ো কারবন— ১৪ পরীক্ষায় এর বয়স নির্ণীত হয়েছে ১০, ৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। তার মানে প্রত্নোপলীয় যুগের একেবারে অন্তিম পর্বে, কেননা নবোপলীয় যুগ শুরু হয়েছিল ৮,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বা তার কিছু পূর্বে।
তবে প্রত্নোপলীয় যুগের প্রথম দিকের মানুষের কঙ্কালাস্থি পাওয়া না গেলেও, মানুষ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বাঙলা দেশের বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলা দেশের নানাস্থানে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ (tools) থেকে। (পৃষ্ঠা ৭০ দেখুন)। এগুলো সবই পশ্চিম-ইউরোপে প্রাপ্ত প্রত্নোপলীয় যুগের হাতকুঠারের অনুরূপ। প্রত্নোপলীয় (Palaeolithic) যুগের পরিসমাপ্তির পরই সূচনা হয় নবোপলীয় (neolithic) যুগের। এ যুগেই কৃষি ও বয়নের উদ্ভব হয়, এবং মানুষ পশুপালন করতে শুরু করে। তবে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন যা নবোপলীয় যুগে ঘটেছিল, তা হচ্ছে মানুষ তার যাযাবর জীবন পরিহার করে, স্থায়ীভাবে গ্রামে বাস করতে শুরু করেছিল। ধর্মেরও উদ্ভব ঘটেছিল। তাদের ধর্মীয় জীবন সম্বন্ধে আমি আমার ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ গ্রন্থে আলোচনা করেছি, সেজন্য এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করছি না। নবোপলীয় যুগের কৃষ্টির নিদর্শন আমরা দার্জিলিঙ থেকে মেদিনীপুর পর্যন্ত নানাস্থানে পেয়েছি। শুধু তাই নয়, নবোপলীয় যুগের অনেক কিছুই আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের দৈনন্দিন জীবন ধরে রেখেছি, যথা ধামা, চুবড়ি, কুলা, ঝাঁপি, বাটনা, বাটবার শিল-নোড়া ও শস্য পেষাইয়ের জন্য যাঁতা ইত্যাদি। এগুলো সবই আজকের বাঙালি নবোপলীয় যুগের ‘টেকনোলজি’ অনুযায়ী তৈরি করে। তা ছাড়া, নবোপলীয় যুগের শস্যই, আজকের মানুষের প্রধান খাদ্য।
জীবনচর্যাকে সুখময় করবার জন্য মানুষের জয়যাত্রা নবোপলীয় যুগেই ত্বরান্বিত হয়। কেননা, মাত্র পাঁচ হাজার বৎসরের মধ্যেই নবোপলীয় যুগের গ্রামীণ সভ্যতা তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতায় বিকশিত হয়। তাম্রাশ্মযুগের নগরসভ্যতার নিদর্শন আমরা পেয়েছি বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি ও সন্নিহিত অঞ্চলে। এই বইয়ের অন্যত্র আমি বলেছি— ‘তাম্ৰাশ্মযুগের সভ্যতার অভ্যুদয়ে তামাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিশর বলুন, সুমের বলুন, সিন্ধু উপত্যকা বলুন, সর্বত্রই আমরা সভ্যতার প্রথম প্রভাতে তামার ব্যবহার দেখি। সুতরাং আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে তাম্রাক্ষ্ম সভ্যতার উন্মেষ এমন কোন জায়গায় হয়েছিল, যেখানে তামা প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যেত। এখানে সেখানে তামা অবশ্য সামান্য কিছু কিছু পরিমাণে পাওয়া যেত, কিন্তু তা নগণ্য। বাঙলাই ছিল সে-যুগের তামার প্রধান আড়ত। তামার সবচেয়ে বৃহত্তম খনি ছিল বাঙলা দেশে। বাঙলার বণিকরাই ‘সাত সমুদ্দুর তের নদী’ পার হয়ে, ওই তামা নিয়ে যেত সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহে বিপণনের জন্য। এজন্যই বাঙলার বড় বন্দরের নাম ছিল তাম্রলিপ্তি। ওই তামা সংগৃহীত হত ধলভূমে অবস্থিত তৎকালীন ভারতের বৃহত্তম তাম্রখনি হতে।’ (পৃষ্ঠা ৭১) আমি আরও বলেছি যে এই তামার সঙ্গে বাঙালী অন্যত্র নিয়ে গিয়েছিল শিব ও শক্তিপূজার বীজ, যা বাঙলার নিজস্ব ধর্ম। বস্তুত বাঙলাদেশে যত শিবমন্দির দেখতে পাওয়া যায়, তত আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বাঙালী এখনও তার ঠাকুরঘরে ব্যবহার করে তাম্রাশ্মযুগের সম্পদ, যথা পাথর ও তামার থালাবাসন, তামার কোষাকুষি ইত্যাতি। (৩৮৪ পৃষ্ঠায় ‘সংযোজন’ দেখুন )
তাছাড়া, নিম্নবাঙলার অনেক স্থানে যেমন মেদিনীপুর জেলার তমলুক (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি), তিলদা (তমলুক থেকে ২৪ মাইল দূরে), পান্না (ঘাটাল থেকে ৪ মাইল দক্ষিণে), বাহিরি (কাঁথি মহকুমায়) ও রঘুনাথপুর (তমলুক থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে), এবং চব্বিশ পরগনার বেড়াচাঁপা বা চন্দ্রকেতুগড় (কলকাতার ২৩ মাইল উত্তরে), আটঘরা (কলকাতার ১২ মাইল দক্ষিণে), হরিহরপুর (মল্লিকপুর রেল স্টেশনের নিকটে, ) হরিনারায়ণপুর (ডায়মন্ড হারবারের ৪ মাইল দক্ষিণ) প্রভৃতি স্থানে কীলকচিহ্নাঙ্কিত প্রাচীন মুদ্রা, কুশান ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা, পোড়ামাটির নানারকম মূর্তি, মৃত্তিকা নির্মিত সীলমোহরাদি আবিষ্কৃত হয়েছে। নানারকম প্রত্নবস্তু থেকে প্রমাণিত হয় যে গ্রীক ও রোমান জগতের সঙ্গে এ অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য ছিল।
* * * *
বাঙালীকে মিশ্র জাতি বলা হয়। এ সম্পর্কে বলা প্রয়োজন যে অধুনা লুপ্ত প্রায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসিগণ ব্যতীত, জগতে এমন কোন জাতি নাই, যারা মিশ্র জাতি নয়। অনন্ত নৃতত্ত্ববিদ্গণের কাছে এমন কোন্ জাতির নাম জানা নেই যারা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। তার মানে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা যেমন মিশ্র জাতি, বাঙলীও তাই। বাঙালীর আবয়বিক নৃতাত্ত্বিক গঠনে যেসব জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে, তারা হচ্ছে অস্ট্রিক ভাষা-ভাষী বাঙলার আদিম, অধিবাসী, ও আগন্তুক দ্রাবিড় ভাষাভাষী ভূমধ্যসাগরীয় নরগোষ্ঠী ও আর্যভাষাভাষী আলপীয় (বা দিনারিক জাতিসমূহ। তবে অস্ট্রিক ভাষাভাষী বাঙলার আদিম অধিবাসী ও আলপীয় (বা দিনারিক) রক্তই প্রধান। এই শেষোক্ত জাতিই বাঙালীকে দিয়েছে তার প্রধান নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য- হ্রস্বকপাল (brachycephallic)। এখানেই উত্তর ভারতের দীর্ঘ-কপাল (dolichocephalic) জাতিসমূহ থেকে বাঙালীর পার্থক্য। (এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে ‘বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ অধ্যায়ে)।
বাঙালীর জীবনচর্যায় ‘অস্ট্রিক’ প্রভাব খুব বেশি। বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক জীবন এর বহু নিদর্শন বহন করে। বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ এ.সি. হ্যাডন তাঁর ‘রেসেস অভ্ ম্যান্’ বইয়ে বলেছেন যে ‘অস্ট্রিক’ ভাষাভাষীরা এক সময় পঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরে অবস্থিত ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বাঙলী জীবনে ‘অস্ট্রিক’ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয় বাঙালীর লৌকিক জীবনে। সে জন্যই বাঙালীর লৌকিক জীবনের একটা পরিচয় আমি দিয়েছি বইখানার গোড়ার দিকে। বস্তুত ‘অস্ট্রিক’ জীবনচর্যার ওপরই গঠিত হয়েছে বাঙালীর জীবনচর্যার বনিয়াদ। সেই বনিয়াদের ওপর স্তরীভূত হয়েছে দ্রাবিড় ও আলপীয় উপাদান। তবে আলপীয়রা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বলেই, এই তিনজাতির মহাসম্মিলনে যে জীবনচর্যা গড়ে উঠেছিল, তা আলপীয় ‘অসুরদের (পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫ ও ৮১-৮২ দেখুন)। নাম অনুসারে অসুর জাতির জীবনচর্যা নামে পরিচিত হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন সাহিত্য এটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে। মহাভারতের আদিপর্ব অনুযায়ী অসুররাজ বলির পাঁচ পুত্রে নাম থেকে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র ও সুহ্ম রাজ্যের নামকরণ হয়েছে। ‘আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প’ নামে এক প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থেও বাঙলা দেশের ভাষাকে ‘অসুর’ জাতির ভাষা বলা হয়েছে। (অসুর নাম্ ভবেৎ বাচ গৌড্রপুন্ড্রোদ্ভব সদা’)। মাত্র আবয়বিক গঠন ও ভাষার দিক দিয়েই নয়, অসুরজাতি সমগ্র জীবনচর্যাটাই উত্তরভারতের “ নর্ডিক নরগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যগণের জীবনচর্যা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই জীবনচর্যার পার্থক্যের জন্যই বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের ‘অসুর’ জাতিভুক্ত লোকদের তির্যকদৃষ্টিতে দেখতেন। আর্যদের সঙ্গে অসুরদের বিরোধের এটাই ছিল কারণ। (লেখকের ‘ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়’ দ্রঃ)।
আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন উত্তর ভারত এক জনহীন শূন্যদেশ ছিল না। সেখানেও লোকের বসতি ছিল। তারা কারা? আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ হ্যাডনের উপলব্ধি অনুযায়ী ‘অস্ট্রিক’ ভাষাভাষী জাতিসমূহই পঞ্জাব থেকে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বস্তুত আর্যরা যখন পঞ্চনদের উপত্যকাকে পাদমঞ্চ করে পূর্বদিকে তাদের জয়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন তাদের এই ‘অস্ট্রিক’ ভাষাভাষী গোষ্ঠীরই সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তখন ‘অস্ট্রিক’ গোষ্ঠীসমূহের সঙ্গে অসুররা ছিল না। কেননা, আবয়বিক নৃতত্ত্বের পরিমাপ অনুযায়ী অসুর বা আলপীয় গোষ্ঠী বিহারের পশ্চিম সীমানা পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল। সে কারণেই একাকী ‘অস্ট্রিক’ গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে অসম্ভব ছিল আর্যদের অশ্ববাহিত জঙ্গীরথকে প্রতিহত করা। কেননা, অশ্ব ভারতের জন্তু নয়। সিন্ধুসভ্যতার কোন কেন্দ্রেই অশ্বের কঙ্কালাস্থি পাওয়া যায়নি। পণ্ডিতমহলে আজ এটা সর্ববাদিসম্মতরূপে স্বীকৃত হয়েছে যে, আর্যরাই মধ্য এশিয়ায় ঘোড়াকে পোষ মানিয়েছিল, এবং অশ্ববাহিত জঙ্গীরথে করেই তারা ভারতে প্রবেশ করেছিল। ভারতে পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত হত বলীবর্দ। বলীবর্দকে এদেশের লোক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখত, কেননা বলীবর্দ ছিল শিবের বাহন; অপর পক্ষে আর্যরা বলীবর্দকে হত্যা করত ও তার মাংস ভক্ষণ করত। যাই হোক, অশ্ববাহিত জঙ্গীরথের সুবিধা থাকার দরুনই আর্যরা তাদের বিজয় অভিযানে সাফল্য অর্জন করেছিল। এই সাফল্য মিথিলা বা বিদেহ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সেখানে এসেই আর্যদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল ‘অসুর’ জাতি এবং অপর এক জন্তুর নিকট। সে জন্তু হচ্ছে হস্তী। হস্তীকে প্রথম পোষ মানিয়েছিল প্রাচ্যদেশের এক মুনি, নাম পালকাপ্য (পৃষ্ঠা ৬৮ দেখুন)। বাঙলার রণহস্তী যে মাত্র আর্যদেরই ঠেকিয়ে রেখেছিল তা নয়। এই রণহস্তীর সমাবেশের কথা শুনেই গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রাচ্যভারতের আর্যদের বিজয় অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল, আর এক কারণে। সে কারণ বিবৃত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে। সেখানে বলা হয়েছে— ‘অসুরগণের সঙ্গে দেবগণের (আর্যদের) লড়াই চলছিল। প্রতিবারই অসুররা আর্যদের পরাহত করছিল। তখন দেবগণ বলল, অসুরদের মত আমাদের রাজা নেই (‘অরাজতয়’), সেই কারণেই আমরা হেরে যাচ্ছি। অতএব আমাদের একজন রাজা নির্বাচন করা হউক। (“রাজানম্ করবমহ ইতি তথেতি’)।’ অথর্ববেদেও বলা হয়েছে ‘একরাট’ মাত্র প্রাচ্যদেশেই আছে। ‘একরাট’ মানে সার্বভৌম নৃপতি ইতিহাসও তাই বলে।
* * * *
প্রাচ্যদেশেই প্রথম সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এটা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু তিনি উত্তর ভারতের ‘নডিক’ নরগোষ্ঠীভুক্ত বৈদিক আর্যদের কাছে নতি স্বীকার করেননি। মৌর্যরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। গুপ্ত-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কাল পর্যন্ত বাঙলায় বৌদ্ধ-ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। গুপ্তসম্রাটগণের আমলেই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর্য-ঐতিহ্যমণ্ডিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম নয়। যে সকল ব্রাহ্মণ দলে দলে বাঙলায় এসেছিল, তারা নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, আর্যের সমাজের কাহিনী-সমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরাণাশ্রিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোতে। সে ধর্ম বৈদিক ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সে ধর্মে ইন্দ্র, বরুণ, প্রভৃতি বৈদিক দেবতাসমূহের প্রাধান্য ছিল না। তারা সম্পূর্ণ পশ্চাদ্পটে অপসারিত হয়েছিল। তৎপরিবর্তে এক নতুন দেবতাশ্রেণী সৃষ্ট হয়েছিল, যার শীর্ষে অবস্থিত ছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আবার তাঁদেরও শীর্ষে ছিলেন এক নারী দেবতা, শিবজায়া দুর্গা। শিব অনাৰ্য দেবতা। ব্রহ্মা অবৈদিক দেবতা। আর বিষ্ণু বৈদিক দেবতা হলেও তাঁর রূপান্তর ঘটেছিল আর্যেতর সমাজের কল্পনার দ্বারা। এটা প্রকাশ পেল যখন অবতারবাদের সৃষ্টি হল। অবতারমণ্ডলীতে বিন্যস্ত মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি অস্ট্রিক সমাজের টোটেম-ভিত্তিক কল্পনা থেকে গৃহীত। আর বুদ্ধ তো বেদবিদ্বেষের প্রবক্তা। এঁরা সকলেই কল্পিত হলেন বৈদিক বিষ্ণুর অবতাররূপে। শুধু তাই নয়। বিষ্ণুর সহধর্মিনী হলেন অনার্য দেবতা শিব- কন্যা লক্ষ্মী। পুরাণসমূহ রচনা করেছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। মহাভারত ও তাঁর রচনা। বেদসঙ্কলনের ভারও তাঁর ও পর ন্যস্ত হয়েছিল। এ সম্পর্কে বহুদিন পূর্বে আমি একটা প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু তার কোন সদুত্তর আজও পাইনি। প্রশ্নটা হচ্ছে—’তথাকথিত বৈদিক আর্যগণের মধ্যে বড় বড় পণ্ডিত থাকা সত্ত্বেও বেদ-সংকলন, মহাভারত ও পুরাণসমূহ রচনার ভার, কেন একজন অনার্যরমণীর জারজ-সন্তানের ওপর ন্যস্ত হয়েছিল?’
গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর শশাঙ্ক বাঙলার রাজা হন। তিনিই বাঙলার প্রথম স্বাধীন নৃপতি যিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে কান্যকুব্জ থেকে গঞ্জাম পর্যন্ত জয় করেছিলেন। তিনি শিব উপাসক ছিলেন। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে প্রশ্ন উঠেছিল— “শিব বড়, না বিষ্ণু বড়?’ এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য হরিহর মূর্তির কল্পনা করা হয়েছিল।
শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাঙলায় মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। দেশকে মাৎস্যনায় থেকে উদ্ধার করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। তিনিই প্রথম বাঙলার লোককে বৃত্তিগত জাতিতে বিন্যস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে পালবংশই একমাত্র রাজবংশ, যে বংশের রাজারা ৪০০ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। পালবংশের রাজত্বকালই হচ্ছে বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ। তাঁরা যে সাম্রাজিক অভিযান চালিয়েছিলেন, তাতে তাঁরা গান্ধার থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত ভূখন্ড জয় করেছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জসমূহের সঙ্গেও তাঁরা সৌহার্দপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তাঁদের আমলেই বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য তাদের আমলে বিশেষে উৎকর্ষতা লাভ করে। বাঙালীর প্রতিভা বিকাশের এটাই ছিল এক বিস্ময়কর যুগ।
পালেদের (Pala dynasty) পর সেনবংশের আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। বর্তমানে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা সেনযুগেই প্ৰথম দৃঢ় রূপ ধারণ করে। পালযুগের ন্যায় সেনযুগেও স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিশেষ উন্নতি ঘটে। এ যুগের বিষ্ণুমূর্তিসমূহ এক অপূর্ব নান্দনিক সুষমায় বিভূষিত। সেনবংশের লক্ষণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয় বাঙলায় বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তি ও মঠ- মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মান্তরকরণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হত না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল। এই অবলুপ্তির হাত থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করেন স্মার্ত রঘুনন্দন ও শ্রীচৈতন্য। (পৃষ্ঠা ২৪৫)।
তবে ইতিহাসের পাতায় বাঙলার মধ্যযুগ স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের স্বতঃস্ফুরণের জন্য। আর্যের সমাজের দেবতাগণের এই সময় আত্মপ্রকাশ ঘটে, এবং তাদের অবলম্বন করে এক বিরাট ‘মঙ্গলসাহিত্য’ সৃষ্ট হয়। এছাড়া, অনুবাদ সাহিত্য, পদাবলী সাহিত্য ও চৈতন্য জীবনচরিতসমূহ এ যুগের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে। তবে এ যুগে নতুন করে একটা সমাজবিন্যাস ঘটে, সে সমাজে উদ্ভুত কৌলীন্যপ্রথা সমাজে এক যৌনবিশৃঙ্খলতা আনে। রামনারায়ণ তর্করত্ন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন যে কৌলীন্যপ্রথার ফলে বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজে এভাবে দূষিত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামনরায়ণ তর্করত্ন ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রচেষ্টার ফলেই বাঙলার কুলীন ব্রাহ্মণসমাজ এই কালিমার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।
বাঙালী সমাজকে আরও বিশৃঙ্খল করে তুলেছিল যখন এদেশে বিদেশী বণিকরা আসতে শুরু করে। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজরাই প্রথম এদেশে আসে। তাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পর্যায়ে শুরু হয় নারীধর্ষণ ও অবৈধ যৌনমিলন। বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখবার ফারমান (firman ) পর্তুগীজরা পায় মুঘল দরবার থেকে। কিন্তু পর্তুগীজদের পরে ইংরেজরা যখন এদেশে আসে তখন তারা বিনা ফারমানেই বাঙালী মেয়েদের রক্ষিতা হিসাবে রাখতে শুরু করে। এসব মেয়েদের তারা ‘বিবিজান’ বলত। পুরানো কবরখানাসমূহের স্মৃতিফলকে এরূপ অনেক বিবিজানের উল্লেখ আছে। এক কথায় সমাজ ক্রমশ অবক্ষয়ের পথেই চলেছিল।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সংঘটিত হয় নবজাগৃতি (Renaisance)। নবজাগৃতির ফলে সমাজ খানিকটা সুসংহত হয়েছিল বটে, কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর যুগের সমাজে আবার প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈতিক শৈথিল্য। বাঙালীর যে প্রতিভা একদিন মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখেলকে উদ্বুদ্ধ করেছিল উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে যে ‘What Bengal thinks today, India thinks tomorrow,’ তা আজ কালান্তরের গর্ভের চলে গিয়েছে। বাঙালী আজ তার নিজ সংস্কৃতির স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। অশনেবসনে আজ সে হয়েছে বহুরূপী। আজ সে এক বর্ণচোরা জারজ সংস্কৃতির ধারক হয়েছে। বাঙালীর বিবর্তনের এটাই শেষ কথা। আজকের প্রশ্ন-বাঙালী কোন্ পথে? এই প্রশ্ন রেখেই এই ‘গৌড়চন্দ্রিকা’ শেষ করছি।
* * * *
বইখানির প্রথম প্রকাশের পর, বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে ও নতুন ঐতিহাসিক তথ্য জানা গিয়েছে, তা মূল পাঠের মধ্যেই সংযুক্ত করা হয়েছে। আর বই ছাপা হয়ে যাবার পর যা জানা গিয়েছে সে সম্বন্ধে ৩৮৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ‘সংযোজন’-এ উল্লেখিত হয়েছে।
পরিশেষে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ‘সাহিত্যলোক’ প্রকাশন-সংস্থার স্বত্বাধিকারী শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষকে, উদ্যম ও উৎসাহের সঙ্গে বইখানা প্রকাশ করার জন্য। শ্রীঅশোক উপাধ্যায় প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করেছেন এবং শ্রীঅরুণচাঁদ দত্ত বর্তমান সংস্করণের নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন, সেজন্য তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
অতুল সুর
*
প্রাক্ভাষণ
বাঙালী এক প্রতিভাশালী জাতি। তার প্রতিভা বিকশিত হয়েছিল তার ধর্মীয় চিন্তাধারা, জাতিবিন্যাস, সমাজগঠন ও সংস্কৃতির স্বকীয়তায়। নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে এই, প্রতিভাবান জাতি সমগ্র উত্তরভারতের জাতিসমূহ থেকে পৃথক। উত্তরভারতের জাতিসমূহের মধ্যে আগন্তুক আর্যভাষাভাষী ‘নর্ডিক’ নরগোষ্ঠীর লক্ষণযুক্ত উপদানেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এই উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়ে ক্রমশ ক্ষীয়মাণ ও বিলীন হয়ে গিয়েছে। এর পূর্বদিকে আমরা যে নৃত্তাত্ত্বিক উপাদান লক্ষ্য করি তা ক্রমশ বর্ধমান হয়ে বাঙলাদেশে এসে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এক কথায় এই উপাদানের আবাসস্থান হচ্ছে বাঙলাদেশ। এই নৃতাত্ত্বিক উপাদানে যাদের দেহ গঠিত, তারাই হচ্ছে বাঙালী জাতি। এরাও আর্যভাষাভাষী আর এক নরগোষ্ঠীর বংশধর। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের আল্পীয়, দিনারিক, আরমেনয়েড ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এরা পঞ্চনদের উপত্যকায় আগত নর্ডিক নৃতাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যভাষাভাষী জাতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এরা ঋগ্বেদ রচয়িতা আর্যগণের পঞ্চনদের উপত্যকায় আসবার অনেক পূর্বেই বাঙলাদেশের এসে বসবাস শুরু করেছিল। এদের ধর্ম, জাতিবিন্যাস, সমাজ ও সংস্কৃতি পঞ্চনদের উপত্যকায় বসবাসকারী আর্যগণের ধর্ম, বর্ণবিন্যাস, সমাজ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি পৃথক ছিল বলেই পঞ্চনদের আর্যগণের এদের ঈর্ষা ও ঘৃণার চক্ষে দেখত। বৈদিক সাহিত্যে এর প্রমাণের অভাব নেই। অথচ এদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর্যদের কৌতূহলও কম ছিল না। এটা আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্র থেকে জানতে পারি। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে যে বাঙলাদেশ বৈদিক আর্য-সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র আর্যাবর্তের বাইরের দেশ। অথচ বাঙলাদেশের তীর্থস্থানগুলি এমনই মহিমান্বিত ছিল যে বৈদিক আর্যসমাজগোষ্ঠীর উদার মনোভাবাপন্ন লোকেরা সেসব তীর্থে পুণ্য অর্জন করতে আসতেন। কিন্তু এরূপ উদারমনোভাবাপন্ন লোকদের আর্যসমাজ ভাল চোখে দেখতেন না। সেজন্যই আমরা বৌধায়ন ধর্মসূত্রে এরূপ উদারমনোভাবাপন্ন বৈদিক আর্যতীর্থযাত্রীর দল যাঁরা বাঙলাদেশে আসতেন, তাঁদের জন্য প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার বিধান দেখি।
বাঙলায় বসবাসকারী ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গোত্রীয় আর্যভাষাভাষীদের এক ঐহিত্যমণ্ডিত সংস্কৃতি ছিল। তারা নিজেদের সংস্কৃতিকে বৈদিক আর্যসংস্কৃতি থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করত। সেজন্য বৈদিক সংস্কৃতি যখন পূর্বদিকে তার জায়যাত্রা শুরু করেছিল, তখন প্রাচ্যদেশের প্রত্যন্তসীমায় এসে, তাদের প্রাচ্যদেশের আর্যভাষাভাষী লোকদের কাছে প্ৰচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারতে আগমনের দেড় হাজার বৎসর পর পর্যন্ত, বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু পরে যখন প্রবেশ করেছিল, তখন বৈদিক আর্যসমাজকে নতিস্বীকার করতে হয়েছিল প্রাচ্যদেশের কাছে। প্রাচ্যদেশে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের আমলেই এটা ঘটেছিল। তখন আর্যসমাজকে ভুলে যেতে হয়েছিল ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক বেদতাগণের উদ্দেশ্যে স্তুতিগান করা। তার পরিবর্তে তারা পূজা করতে আরম্ভ করেছিল পৌরাণিক দেব-দেবীসমূহকে। তাদের বৈদিক গরিমা ক্রমশ ম্লান হয়ে গিয়েছিল।
বৈদিক আর্যভাষারও রূপান্তর ঘটেছিল। বাঙলার কবিরা সংস্কৃত ভাষায় যে-সব কাব্য রচনা করতে শুরু করেছিল, তার অভিনব উৎকর্ষের জন্য, তা’ গৌড়ীয় রীতি’ নামে এক বিশিষ্ট আখ্যা অর্জন করেছিল। এই রীতিতেই রচনা করেছিলেন বাঙলার অমর কবি জয়দেব তাঁর ‘গীতগোবিন্দ’ যার সমতুল্য কাব্য-গ্রন্থ বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ।
দুই
বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি। সে ভুলে গিয়েছিল তার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য। সেজন্যই একশ বছর পূর্বে বঙ্কিম আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে বাঙালীর ইতিহাস নেই। আজ কিন্তু আর সেকথা বলা চলে না। নানা সুধীজনের প্রয়াসের ফলে আজ বাঙলার ও বাঙালীর এক গৌরবময় ইতিহাস রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ছিল রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির। বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় (১৯১২) ওই সোসাইটির পক্ষ থেকে রমাপ্রসাদ চন্দ লেখেন ‘গৌড়রাজমালা’ ও অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রকাশ করেন ‘গৌড়লেখমালা’। তারপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন তাঁর ‘বাঙলার ইতিহাস’। কিন্তু রাখালদাসের বইখানা ছিল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, বাঙালীর জীবনচর্যার ইতিহাস নয়। তিনের দশকে বাঙলার ইতিহাসের একটা কঙ্কাল ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করেন বর্তমান লেখক ‘মহাবোধি সোসাইটি’র মুখপত্র ‘মহাবোধি’তে। চল্লিশের দশকের গোড়াতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বের করে তাদের ‘হিস্ট্রি অভ্ বেঙ্গল’। এই বইটাতেই প্রথম প্রদত্ত হয় বাঙালীর জীবনচর্যার বিভিন্ন বিভাগের ইতিহাস। এর ছ’বছর পরে ড. নীহাররঞ্জন রায় অসামান্য গৌরব অর্জন করলেন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃজন তাঁর ‘বাঙালীর ইতিহাস- আদিপর্ব’ লিখে। কিন্তু বাঙলার ইতিহাসের প্রাগৈতিহাসিক যুগটা শূন্যই থেকে গেল। ষাটের দশকে বর্তমান লেখক তাঁর ‘হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অভ্ বেঙ্গল’ (১৯৬৩) ও প্রি-হিস্ট্রি অ্যাণ্ড বিগিনিংস অভ সিভিলিজেশন ইন বেঙ্গল (১৯৬৫) বই দুটি লিখে বাঙলার প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ইতিহাস দেবার চেষ্টা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বাঙলার ইতিহাসকে টেনে আনেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময় পর্যন্ত। ওই দশকেই রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত বের করেন তাঁর ‘একসক্যাভেশনস্ অ্যাট পাণ্ডুরাজার ঢিবি’ ও প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা’। এর পর (১৯৭১) ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার সম্পূর্ণ করেন চার খন্ডে তাঁর ‘বাঙলার ইতিহাস।’ অনেক আগেই। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ননীগোপাল মজুমদারের ‘ইনস্ক্রিপশনস্ অভ্ বেঙ্গল’ ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ড. বিনয়চন্দ্র সেনের ‘সাম হিস্টরিক্যাল অ্যাসপেকটস্ অভ্ দি ইনস্ক্রিপশনস্, অভ্ বেঙ্গল’ ও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ড. রমারঞ্জন মুখার্জি ও এস.কে. মাইতির ‘করপাস অভ্ বেঙ্গল ইনস্ক্রিপশনস্’। আশির দশকে ড. দীনেশচন্দ্র সরকার বের করলেন তাঁর “শিলালেখ ও তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ’. ‘পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত’ ও পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত।’ ইদানিং ব্ৰতীন্দ্ৰনাথ মুখোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখেরাও আলোকপাত করেছেন বাঙলার ইতিহাসের নানা বিভাগের ওপর।
এদিকে বাঙালীকে সম্যরূপে বুঝবার চেষ্টাও চলতে লাগল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর ‘ইন্ডো-আরিয়ান রেসেস্’ ‘বইয়ে বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্পীয় উপাদানের কথা বললেন। এর পনেরো বছর পরে ড. বিরাজশঙ্কর গুহ বাঙালীর দৈহিক গঠনে আল্পীয় রক্ত ছাড়া, দিনারিক রক্তের কথাও তুললেন। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও এ-বিষয়ে অনুশলীন করলেন। নূতন তথ্যের ভিত্তিতে বাঙালীর প্রকৃত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের একটা প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজন মেটানোর জন্য ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভার অনুরোধে বর্তমান লেখক লিখলেন তাঁর ‘বাঙালীর নৃত্তাত্ত্বিক পরিচয়’ (জিজ্ঞাসা, পুনর্মুদ্রণ ১৯৭৭, ১৯৭৯ ও ১৯৮৬)। অপরদিকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কাজ চালালেন প্রবোধকুমার ভৌমিক প্রমুখ নৃতত্ত্ববিদ্গণ।
অনেক আগেই বাঙালী সংস্কৃতির সাত-পাঁচের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি রাজ্য পরিভ্রমণ করে বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবহট্ট ভাষায় ‘সন্ধা’-রীতিতে রচিত লুইপাদের ‘চর্যাচর্য-বিনিশ্চয়’ সরোহবজ্রের ‘দোহাকোষ’ ও কাহ্নুপাদের ‘দোহাকোষ’ ও ‘ডাকার্ণব’ এই চারখানা বই আবিষ্কার করা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আরও অনেকে অনুশীলন করলেন, যথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্ববল্লভ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, তমোনাশ দাশগুপ্ত, সজনীকান্ত দাস, প্রবোধচন্দ্ৰ সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, পঞ্চানন চক্রবর্তী,অজিতকুমার ঘোষ, দেবীপদ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ দত্ত, নীলরতন সেন, উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও আরও অনেকে। তাঁদের সকলেই অনুশীলনের ফলে, আজ আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়েছি বাংলা ভাষায় উৎপত্তি ও বিকাশ, ও বাংলা ছন্দের গতিপ্রকৃতি ও বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসের সঙ্গে।
তিন
বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হয়ে গিয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় দশ থেকে পঁচিশ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয় প্লাইস্টোসিন যুগ। এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে।
যদিও প্লাইস্টোসিন যুগের মানুষের কোনও নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাঙলাদেশে পাওয়া তার ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ থেকে। এই আয়ুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে প্লাইস্টোসিন যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে-যুগের মানুষ আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করত, তার মাংস আহারের জন্য। এগুলো পাওয়া গিয়েছে বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার নানা স্থান থেকে। এগুলোকে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নোপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে। তারপর সূচনা হয় নব-প্রস্তর বা নবোপলীয় যুগের। নবোপলীয় যুগের অবসানের পর, অভ্যুদয় হয় তাম্রাক্ষ্ম যুগের। তাম্রাশ্ম যুগেই সভ্যতার সূচনা হয়। বাঙলায় তাম্রাক্ষ্ম যুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হচ্ছে সিন্ধুসভ্যতা। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে পাণ্ডুরাজার ঢিবি।
চার
বাঙলার আদিম অধিবাসীরা ছিল অস্ট্রিক ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক। নৃতত্ত্বের ভাষায় এদের প্রাক্-দ্রাবিড় বা আদি অস্ত্রাল (Proto-Australoids) বলা হয়। প্রাচীন সাহিত্যে এদের ‘নিষাদ’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, লোধা প্রভৃতি উপজাতিসমূহ এই গোষ্ঠীর লোক। এছাড়া, হিন্দুসমাজের তথাকথিত ‘অন্ত্যজ’ জাতিসমূহও এই গোষ্ঠীরই বংশধর। বাঙলায় প্রথম অনুপ্রবেশ করে দ্রাবিড়রা। এরা দ্রাবিড় ভাষার লোক ছিল। বৈদিক সাহিত্যে এদের ‘দস্যু’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। এদের অনুসরণে আসে আর্যভাষাভাষী আল্পীয়রা (Alpinoids)। মনে হয়, এদের একদল এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিমসাগরের উপকূল ধরে অগ্রসর হয়ে ক্রমশ সিন্ধু, কাথিয়াবাড়, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কুর্গ, কন্নাদ ও তামিলনাড়ু প্রদেশে পৌঁছায় এবং তাদেরই আর একদল আরও অগ্রসর হয়ে পূর্ব উপকূল হয়ে বাঙলা ও ওড়িশায় আসে। এরাই মনে হয়, বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে বর্ণিত, ‘অসুর’ জাতি। আরও মনে হয়, এদের সকলেরই সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক (tribal) ছিল। এবং এই সকল কৌমগোষ্ঠীর (tribes) নামেই পরে এক একটা জনপদের সৃষ্টি হয়।
বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের অন্তত দুটি কৌমগোষ্ঠীর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিল। একটি হচ্ছে ‘বঙ্গ’ যাদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ‘বয়াংসি’ বা পক্ষীজাতীয় বলা হয়েছে। মনের হয় পক্ষীবিশেষ (‘বিহঙ্গ’) তাদের ‘টোটেম’ ছিল। বৈদিক সাহিত্যে দ্বিতীয় যে নামটি আমরা পাই, সেটি হচ্ছে ‘পুন্ড্র’। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে তাদের ‘দস্যু’ বলে অভিহিত করা হয়েছে। মনে হয়, তাদের বংশধররা হচ্ছে বর্তমান ‘পোদ’ জাতি।
বৈদিক আর্যরা বাঙলাদেশের লোকদের বিদ্বেষপূর্ণ ঘৃণার চক্ষে দেখত। এটার কারণ দুই বিপরীত সংস্কৃতির সংঘাত। বাঙলায় আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত, তাদের মনে এই বিদ্বেষ ছিল।
পাঁচ
মহাভারতীয় যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট, সুহ্ম, প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। মহাভারতে বলা হয়েছে যে অসুর রাজার বলির ক্ষেত্রজ সন্তানসমূহ থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ড্র, ও সুহ্ম জাতিসমূহ উদ্ভূত হয়েছে।
বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থসমূহ থেকে আমরা বাঙলার প্রাক্-বৌদ্ধযুগের দুটি রাষ্ট্রের নাম পাই। একটি হচ্ছে শিবি রাজ্য ও অপরটি হচ্ছে চেত রাজ্য। এ দুটি রাষ্ট্র বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বেই বিদ্যমান ছিল। বর্ধমান জেলার অধিকাংশ অঞ্চল নিয়ে শিবি রাজ্য গঠিত ছিল। তার রাজধানী ছিল জেতুত্তর নগরে (বর্তমান মঙ্গলকোটের নিকটে টলেমি উল্লিখিত সিব্রিয়াম বা শিবপুরী)। এরই দক্ষিণে ছিল চেত রাজ্য। তার রাজধানী ছিল চেতনগরীতে (বর্তমান ঘাটাল মহকুমার অন্তর্ভুক্ত চেতুয়া পরগনা।)। এই উভয় রাজ্যের সীমান্ত কলিঙ্গ রাজ্যেরই সীমানার সঙ্গে এক ছিল। কলিঙ্গ রাজ্য তখন বর্তমান মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
সিংহল দেশের ‘দীপবংশ’ ও ‘মহাবংশ’ নামে দুটি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি যে বঙ্গদেশের বঙ্গ নগরে এক রাজার বিজয়সিংহ নামে এক পুত্র দুর্বিনীত আচারের জন্য সাত শত অনুচরসহ বাঙলাদেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে সিংহলে যায়, এবং সেখানে কুবেণী নাম্নী এক যক্ষিণীকে বিবাহ করে সিংহল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।
আলেকজাণ্ডারের (৩২৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ভারত আক্রমণের সময় বাঙলায় ‘গঙ্গারিড’ বা ‘গঙ্গরাঢ়’ নামে এক স্বাধীন রাজ্য ছিল। গঙ্গারাঢ়ীদের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদীর তীর থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।
এর অনতিকাল পরেই বাঙলা তার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। কেননা, মহাস্থানগড়ের এক শিলালিপি থেকে আমরা জানতে পারি যে, উত্তর বাঙলা মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, কারণ মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত (৩২২-২৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পুণ্ড্রবর্ধন নগরে এক কর্মচারীকে অধিষ্ঠিত করেন। মনে হয় এই সময় থেকেই আর্যসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ বাঙলাদেশে ঘটেছিল। ‘মনুসংহিতা’ রচনকালে (২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে) বাঙলাদেশে আর্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হত। কুষাণ সম্রাটগণের (৭৮-১০১) মুদ্রাও বাঙলার নানা জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে বাঙলাদেশে গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু যষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙলাদেশ আবার স্বাধীনতা লাভ করে। এই সময় ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদের নামে তিনজন স্বাধীন রাজা ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। গোপচন্দ্র ওড়িশারও ও এক অংশ অধিকার করেন। এর অনতিকাল পরে বাঙলাদেশের রাজা শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭) পশ্চিমে ক্যানকুব্জ ও দক্ষিণে গঞ্জাম পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। এরপর বাঙলাদেশে কিছুকাল অরাজকতা দেখা দেয়। সামন্তরাজগণ এখানে- সেখানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই অরাজকতার হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল (৭৫০-৭৭০)।
ছয়
অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় (৭৫০-৭৭০) থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে গোবিন্দপালের সময় (১১৬১-১১৬৫) পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। শেষ পালরাজ পলপাল রাজত্ব করেন ১১৬৫ থেকে ১২০০ পর্যন্ত। একই রাজবংশের ক্রমাগত সাড়ে চারশো বছর (৭৫০-১২০০) রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। গোপালের পৌত্র দেবপাল (৮১০-৮৪৭) নিজের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত। দেবপালের পিতা ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে গান্ধার পর্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত জয় করেছিলেন। বস্তুত পালরাজগণের রাজত্বকালই বাঙলার ইতিহাসের গৌরবময় যুগ।
পালবংশের পতনের পর বাঙলায় সেনবংশ রাজত্ব করে। এরাও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। সেনবংশের তৃতীয় রাজা লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানদের হাতে চলে যায়। এ ঘটনা ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতাব্দীর (১২০৪) শুরুতেই। তখন থেকে ষোড়শ শতাব্দীর পাদ পর্যন্ত বাঙালাদেশ স্বাধীন সুলতানদের শাসনাধীনে ছিল। পরের পঞ্চাশ বছর (১৫৩৯-১৫৭৬) বাঙলা পাঠানদের অধীনে চলে যায়। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট আকবরের (১৫৭৬) আমলে বাঙলা মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে (১৭৫৭) বাঙলা মুঘলদের হাত থেকে ইংরেজেদের হাতে চলে যায়।
সাত
বাঙলার ধর্মীয় সাধনার ও লৌকিক জীবনের আচার-ব্যবহারের একটা বিশদ চিত্র পাঠক পাবেন এই বইয়ে। এখানে কেবল বাঙলার সমাজবিন্যাস ও প্রথাসমূহের একটা রূপরেখা টানবার চেষ্টা করব। আগেই বলেছি যে, বাঙলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম খুব বিলম্বে প্রবেশ করেছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশের পূর্বে বাঙলায় চাতুর্বর্ণ্য সমাজ-বিন্যাস ছিল না। প্রথমে ছিল কৌমগোষ্ঠিক সমাজ। তারপর যে সমাজের উদ্ভব হয়েছিল, তাতে জাতিভেদ ছিল না, ছিল পদাধিকারঘটিত বৃত্তিভেদ। এটা আমরা জানতে পারি, ‘প্রথম কায়স্থ’, ‘জ্যেষ্ঠ কায়স্থ’, ‘প্রতিবেশি’, ‘কুটুম্ব’ প্রভৃতি নাম থেকে। এসব নাম আমরা পাই সমকালীন তাম্রপট্টলিপি থেকে। তারপর পাই বৃত্তিধারী গোষ্ঠীর নাম, যথা— ‘নগরশ্রেষ্ঠী’, ‘সার্থবাহ’, ‘ক্ষেত্রকার’, ‘ব্যাপারী’, ইত্যাদি। পরে পালযুগে যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ঘটে, তখন বাঙলায় বৃত্তিধারী গোষ্ঠীগুলি আর বৈবাহিক আদান-প্রদানের সংস্থা হিসাবে স্বীকৃত হয় না। তখনই বাঙলার জাতিসমূহ সঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পালরাজগণের পর সেনরাজগণের আমলে যখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে তখন বাঙলার সকল জাতিই সঙ্করত্ব দোষে দুষ্ট। সেজন্য ‘বৃহদ্ধর্মপুরাণ’-এ ব্রাহ্মণ ছাড়া, বাঙলার আর সকল জাতিকেই সঙ্কর জাতি বলে অভিহিত করা হয়েছিল ও তাদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল্ড (১) উত্তম সঙ্কর, (২) মধ্যম সঙ্কর ও (৩) অন্ত্যজ। এরপর আর একটা শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল ‘নবশাখ’ বিভাগ। নবশাখ মানে যাদের হাতে ব্রাহ্মণরা জল গ্রহণ করত। বিবাহের অন্তর্গোষ্ঠী (endogamous) হিসাবে মধ্যযুগে যে সকল জাতি বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহ পাই। এ সকল জাতি আজও বিদ্যমান ছিল, তাদের নাম আমরা মঙ্গলকাব্যসমূহে পাই। এ সকল জাতি আজও বিদ্যমান আছে। ময়ূরভট্টের ‘ধর্মপুরাণ’-এ যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : “সদ্গোপ, কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি/উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি/ যোগী ও আশ্বিন তাঁতি মালী মালাকার/ নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর/হাড়ি মুচি ডোম কলু চণ্ডাল প্রভৃতি/ মাজি বাগদী মেটে নাহি ভেদজাতি/ স্বর্ণকার সুবর্ণবণিক কর্মকার/ সূত্রধর গন্ধবেনে ধীবর পোদ্দার/ ক্ষত্রিয় বারুই বৈদ্য পোদ পাকমারা/পরিল তাম্রের বালা কায়স্থ কেওরা।” (বঙ্গীয়-সাহিত্য- পরিষদ সংস্করণ, পৃ.৮২)
মধ্যযুগের সমাজজীবনকে কলুষিত করেছিল তিনটি অপপ্রথা (১) কৌলিন্য (২) সহমরণ ও (৩) দাসদাসীর হাট। এসবের বিশদ বিবরণ আমি দিয়েছি এই বই-এ। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এ সকল প্রথম বাঙালীসমাজে প্রচলিত ছিল। রাজা রাজমোহন রায় প্রমুখ সমাজ- সংস্কারকদের প্রচেষ্টার ফলে ইংরেজ সরকার কর্তৃক সহমরণ (১৮২৯) নিবারিত হয়। তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইনসিদ্ধ (১৮৫৬) হয়। পরে অসবর্ণ বিবাহের জন্য ‘বিশেষ আইন’ প্রণয়ন হয় (১৮৭২)। এই আইনেই মেয়েদের ন্যূনতম বিয়ের বয়স করা হয় ১৪। আরও পরে (১৮৯২) বিবাহে সঙ্গমের ন্যূনতম বয়সও বর্ধিত করা হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে বিবাহের ন্যূনতম বয়সও বাড়ানো হয়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার হিন্দু বিবাহকে সুসংহত করবার জন্য ‘হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট’ (১৯৫৫) প্রণয়ণ করেন। এই আইন ও পরবর্তী সংশোধিত আইন দ্বারা ন্যূনতম বিবাহের বয়স (পাত্রের ২২, পাত্রীর ১৮) বাড়ানো হয়।
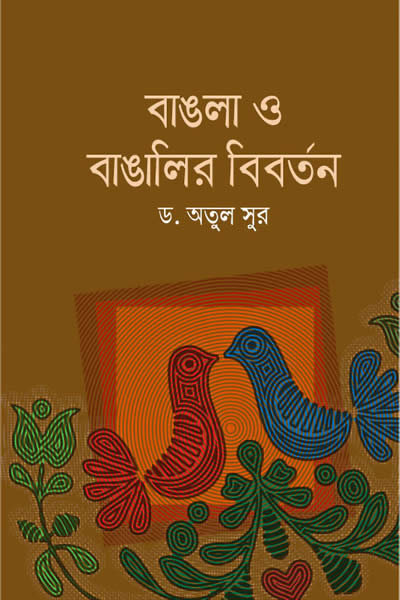
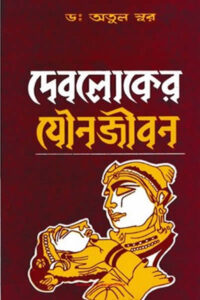

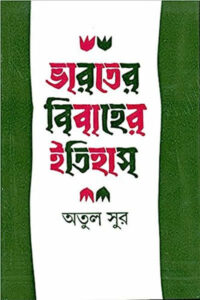


Leave a Reply