ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল – মিচিও কাকু
ফেজার, ফোর্স ফিল্ড, টেলিপোর্টেশন ও টাইম ট্রাভেলের জগতে বৈজ্ঞানিক অভিযান
ভাষান্তর – আবুল বাসার
প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪২৬, জানুয়ারি ২০২০
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
প্রচ্ছদ : সব্যসাচী মিস্ত্রী
Physics of the Impossible by Michio Kaku Translated in Bangla by Abul Bashar
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
অনুবাদকের কথা
বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকে বলা হয় ভবিষ্যতের রূপকথা। আজ যেটা বিজ্ঞান কল্পকাহিনি কাল সেটা হয়ে উঠতে পারে প্রতিদিনের বাস্তবতা। ইতিহাসে এ রকম উদাহরণ অনেক। স্মরণ করা যেতে পারে উনিশ শতকের জনপ্রিয় ফরাসি লেখক জুল ভার্নের লেখা ফ্রম আর্থ টু দ্য মুন শিরোনামের বিজ্ঞান কল্পকাহিনির কথা। এ উপন্যাসে প্রথমবারের মতো প্রায় বিজ্ঞানসম্মতভাবে রকেটে চেপে চাঁদে অভিযানের বর্ণনা দেন ভার্ন। তার প্রায় শতবর্ষ পর সত্যি সত্যিই চাঁদের বুকে পা রাখে মানুষ।
পাঠক জানেন, আজকের স্যাটেলাইট, ইন্টারনেট, স্মার্ট কার্ড, রোবট, রকেটসহ অনেক প্রযুক্তি প্রথম দেখা গিয়েছিল বিজ্ঞান কল্পগল্পের পাতায়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এসবের অনেক কিছুই স্রেফ অসম্ভব বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেকালের বাঘা বাঘা পণ্ডিত, বিজ্ঞানী ও গবেষকেরা। ধরা যাক কেলভিন স্কেলের জনক ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড কেলভিনের কথা। তিনি মনে করতেন, বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো বস্তুকে শূন্যে ভাসানো সম্ভব নয়। এমনকি রেডিওরও কোনো ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি তিনি। আর এক্স-রেকে কতিপয় লোকের ধাপ্পাবাজি হিসেবে ঘোষণা করেন কেলভিন। এদিকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আবিষ্কর্তা আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পারমাণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনাকে অবাস্তব কল্পনা বলে নাকচ করে দেন। ১৯৩০-এর দশকে তাঁর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া গিয়েছিল আপেক্ষিকতা তথা E=mc^2-র মতো বিখ্যাত সমীকরণের স্রষ্টা বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের কণ্ঠে। মজার ব্যাপার হলো, এর ১০ বছরের মাথায় আস্ত একটা পরমাণু বোমা বানিয়ে ফেলে যুক্তরাষ্ট্র।
এসব কারণেই তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মিচিও কাকু বলতে চান, অসম্ভব ব্যাপারটা আপেক্ষিক। আজ যা অসম্ভব, কাল সেটা যৌক্তিকভাবে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। আজ আমরা যেসব প্রযুক্তি ছাড়া একটি মুহূর্তও কল্পনা করতে পারি না, ১০০ বছর বা তারও আগের বিশ্বে সেটাই মনে হতো অসম্ভব কিংবা ম্যাজিক। আমরাও একই অবস্থায় পড়ি বিজ্ঞান কল্পকাহিনি-নির্ভর বই পড়তে বা মুভি দেখতে গিয়ে। স্টার ট্রেক বা স্টার ওয়ার্স কিংবা আইজ্যাক আসিমভ ও আর্থার সি ক্লার্কের বই বা এই সিনেমাগুলোতে দেখানো ভবিষ্যতের ঝাঁ- চকচকে প্রযুক্তি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। বিজ্ঞান কল্পকাহিনি লেখক তো লিখেই খালাস। কিন্তু সেগুলো কি বাস্তবে আদৌ সম্ভব? এ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় মিচিও কাকুর ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল বইয়ে।
বর্তমানে তুমুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে টাইম ট্রাভেল, টেলিপোর্টেশন, ওয়ার্মহোল, স্টার শিপ, এলিয়েন, অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতা, ফোর্স ফিল্ড বা বলক্ষেত্র, ফেজার, আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণসহ আরও অনেক কিছু। এসব প্রযুক্তি এখনো বিজ্ঞান কল্পগল্পের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। অনেক আধুনিক বিজ্ঞানী এগুলো অসম্ভব ও গাঁজাখুরি বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলোকে মোটাদাগে অসম্ভব বলতে নারাজ মিচিও কাকু। এসব প্রযুক্তি সম্ভব, নাকি অসম্ভব—তা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তিতর্ক দিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। এভাবে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি আর প্রকৃত বিজ্ঞানের সীমারেখা টেনে বাস্তবে সেগুলো সম্ভব নাকি অসম্ভব তা ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল বইয়ে খতিয়ে দেখেছেন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ মিচিও কাকু।
২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত হওয়ার পর নিউইয়র্ক টাইমস-এ ননফিকশন বিভাগে বেস্টসেলারের মর্যাদা পায় বইটি। বিজ্ঞানী, লেখক ও টিভি উপস্থাপক হিসেবে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় মিচিও কাকু। সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সাধারণ পাঠকের কাছে তুলে ধরার কারণেই তাঁর এ জনপ্রিয়তা। বই ও উপস্থাপনার সুবাদে বাংলাদেশেও তিনি বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু তাঁর ফিজিকস অব দ্য ইমপসিবল ও অন্যান্য বই ইংরেজিতে এ দেশে পাওয়া গেলেও তাঁর কোনো বইয়ের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ এখনো প্রকাশিত হয়নি। বাংলা ভাষার পাঠকের ভালো লাগলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে।
আবুল বাসার
ঢাকা, জানুয়ারি ২০২০
সূচিপত্র
লেখকের ভূমিকা
প্রথম পর্ব : প্রথম শ্রেণির অসম্ভাব্যতা
১. বলক্ষেত্র
২. অদৃশ্য হওয়া
৩. ফেজার ও মারণ নক্ষত্র
৪. টেলিপোর্টেশন
৫. টেলিপ্যাথি
৬. সাইকোকাইনেসিস
৭. রোবট
৮. মহাকাশের আগন্তুক ও ইউএফও
৯. স্টারশিপ
১০. প্রতিবস্তু ও প্রতি-মহাবিশ্ব
দ্বিতীয় পর্ব : দ্বিতীয় শ্রেণির অসম্ভাব্যতা
১১. আলোর গতি ছাড়িয়ে
১২. টাইম ট্রাভেল
১৩. সমান্তরাল মহাবিশ্ব
তৃতীয় পর্ব : তৃতীয় শ্রেণির অসম্ভাব্যতা
১৪. অবিরাম গতিযন্ত্র
১৫. ভবিষ্যৎ দেখার ক্ষমতা
শেষ কথা : অসম্ভবের ভবিষ্যৎ
পরিভাষা
লেখকের ভূমিকা
কোনো আইডিয়া শুরুতে যদি উদ্ভট মনে না হয়, তাহলে ভবিষ্যতে ওই আইডিয়ার কোনো আশা নেই।
—আলবার্ট আইনস্টাইন
দেয়ালের ভেতর দিয়ে হেঁটে কি অন্যপাশে চলে যাওয়া সম্ভব? কিংবা এমন নভোযান কি বানানো সম্ভব, যা দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করা যাবে আলোর চেয়ে বেশি গতিতে? অন্য আরেকজনের মন কি পড়া যাবে? অদৃশ্য হওয়া যাবে চোখের পলকে? কোনো বস্তু কি নাড়ানো সম্ভব হবে স্রেফ মনের শক্তি দিয়ে? মহাকাশের সুদূরে আমাদের দেহকে দ্রুতবেগে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে কখনো?
ছেলেবেলায় এসব প্রশ্ন সব সময় তীব্র শিহরণ জাগাত আমার মনে। বড় হয়ে ওঠার সময়গুলোতে অনেক পদার্থবিদের মতো আমিও টাইম ট্রাভেলের সম্ভাবনা, রে-গান, বলক্ষেত্র, প্যারালাল ইউনিভার্স বা সমান্তরাল মহাবিশ্বের মতো বিষয়ে জাদুমুগ্ধ হয়ে থাকতাম। আমার কল্পনাজগতে প্রকাণ্ড এক মাঠ হিসেবে কাজ করেছে ম্যাজিক, ফ্যান্টাসি আর বিজ্ঞান কল্পকাহিনি। এসবের সংস্পর্শে এসে সূচনা হয়েছিল অসম্ভব বিষয়গুলোর সঙ্গে আমার আজীবন ভালোবাসার বন্ধন।
টেলিভিশনে পুনঃপ্রচারিত ফ্ল্যাশ গর্ডন সিরিজ দেখার কথা আমার এখনো বেশ মনে আছে। প্রতি শনিবার আমার চোখজোড়া টিভি সেটের পর্দায় আঠার মতো লেগে থাকত। ফ্ল্যাশ, ড. জারকভ ও ডেল আরদেনের দুঃসাহসী সব অ্যাডভেঞ্চার আর তাদের রকেটশিপ, অদৃশ্য ঢাল, রে-গানের মতো চোখধাঁধানো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও আকাশছোঁয়া শহরগুলোই ছিল এর পেছনের কারণ। কোনো সপ্তাহে আমি এ সিরিজ বাদ দিইনি। এই টিভি প্রোগ্রাম আমার ভাবনায় সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ খুলে দিয়েছিল। কোনো একদিন সুদূর এলিয়েন গ্রহে রকেটে চেপে যাওয়া যাবে, তারপর সেখানকার অদ্ভুত ভূখণ্ডে অনুসন্ধান চালানোর কথা ভাবতাম আমি। এসব ভেবে ভেবে বেশ রোমাঞ্চিত হতাম তখন। ওই প্রোগ্রামে দেখানো দারুণ সব উদ্ভাবনের এক অমোঘ টানে সারা বেলা ঘুরপাক খেতাম আমি। এভাবেই একসময় জেনে গেলাম, আমার নিজের ভাগ্যও কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের প্রতিশ্রুত এই বিস্ময়ের সঙ্গে বাঁধা পড়ে গেছে।
পরে দেখলাম, এ পথের যাত্রী শুধু আমি একা নই, অনেক সফল বিজ্ঞানীও একসময় বিজ্ঞান কল্পকাহিনির মাধ্যমে বিজ্ঞানে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। জুল ভার্নের লেখার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন নামকরা জ্যোতির্বিদ এডুইন হাবল। জুল ভার্নের লেখা পড়ার কারণেই হাবল আইন পেশা ছেড়ে দেন। অথচ এ পেশায় তাঁর সফল হওয়ার বেশ সম্ভাবনা ছিল। তারপর বিজ্ঞানে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করেন বাবার আদেশ অমান্য করে। পরিণামে বিশ শতকের সেরা জ্যোতির্বিদ হতে পেরেছিলেন তিনি। এডগার রাইজ বারোজের জন কার্টার অব মার্স উপন্যাস পড়ার পর বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও বেস্টসেলার লেখক কার্ল সাগানের কল্পনাজগৎ রঙিন হয়ে উঠেছিল উপন্যাসের নায়ক জন কার্টারের মতো তিনিও মঙ্গলের বালুকণায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন।
আলবার্ট আইনস্টাইন যখন মারা যান, তখন আমি ছোট শিশু। মানুষজন তাঁর জীবন, মৃত্যু নিয়ে চাপাগলায় আলাপ-আলোচনা করছিল—সেসব আমার এখনো বেশ মনে আছে। পরদিন খবরের কাগজে দেখি, তাঁর ডেস্কের ছবি ছাপা হয়েছে। সেখানে তাঁর অতিগুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকাজের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপি পড়ে ছিল। সেদিন নিজেকেই প্রশ্ন করেছি আমি, কী এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল সেটা যে আমাদের কালের সেরা এক বিজ্ঞানী হয়েও তিনি তা শেষ করে যেতে পারেননি? সেদিনের ওই লেখাতে দাবি করা হলো, আইনস্টাইন এক অসম্ভব স্বপ্ন দেখতেন। সেটি এমন কঠিনতর সমস্যা ছিল, যা কোনো জীবিত মানুষের পক্ষেও সমাধান করা সম্ভব নয়। ওই পাণ্ডুলিপিটি ঠিক কী বিষয়ে ছিল, তা খুঁজে বের করতে অনেক বছর লেগে গিয়েছিল আমার। পরে জানতে পারি, সেটি ছিল একটি পূর্ণাঙ্গ, একীভূত ‘থিওরি অব এভরিথিং’ বা যাকে বলে সার্বিক তত্ত্ব। স্রেফ এই স্বপ্নের পেছনে জীবনের শেষ তিনটি দশক ব্যয় করেন আইনস্টাইন। তাঁর এই স্বপ্ন পরবর্তী সময়ে আমার নিজের কল্পনাজগতের দিকে মনোযোগ দিতেও সহায়তা করে। এরপর থেকে ছোটখাটো যেকোনো উপায়েই হোক না কেন, আইনস্টাইনের এ গবেষণা সম্পূর্ণ করার বা পদার্থবিজ্ঞানের সব সূত্র একটি একক তত্ত্বে একীভূত করার উদ্যোগের অংশ হতে চাইতাম আমি।
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আমি বুঝতে পারি, পর্দায় ফ্ল্যাশ গর্ডন নায়ক। আবার সব সময় মেয়েদের সান্নিধ্য সে। কিন্তু তা হলেও একমাত্র বিজ্ঞানীদের নেপথ্যে কাজের কারণেই আসলে এসব টিভি সিরিজ কার্যকর হয়ে ওঠে। ড. জারকভ ছাড়া থাকত না কোনো রকেটশিপ, মনগো গ্রহে কোনো অভিযান চালানোও যেত না, এমনকি রক্ষা করা যেত না পৃথিবীকেও। মোদ্দা কথা, বিজ্ঞান ছাড়া কোনো বিজ্ঞান কল্পকাহিনি বা বীরোচিত ঘটনার অস্তিত্বই থাকত না।
আমি বুঝতে পারি, বিজ্ঞান দিয়ে চিন্তা করে দেখলে এসব কল্পকাহিনি এককথায় অসম্ভব। শুধু কল্পনার পাখায় ভর করে চলে এগুলো। বড় হয়ে ওঠা মানে এ ধরনের ফ্যান্টাসির জগৎ থেকে বেরিয়ে আসা। অনেকেই আমাকে বলত, বাস্তব জীবনে সবাইকে এসব অসম্ভব কল্পনা বাদ দিয়ে নিরেট বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়।
তবে একসময় সিদ্ধান্তে পৌঁছালাম, অসম্ভব বিষয়গুলোতে আমার মুগ্ধতা যদি অটুট রাখতে চাই, তাহলে সেটি করে যেতে হবে পদার্থবিজ্ঞানের রাজ্যের ভেতরে থেকে। উচ্চতর পদার্থবিজ্ঞানে শক্ত ভিত ছাড়া ভবিষ্যৎ-মুখী যেকোনো কাল্পনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে আমাকে সব সময়ই সন্দেহ করতে হবে। কারণ, তখনই কেবল বোঝা যাবে, প্রযুক্তিগুলো বাস্তবে আদৌ সম্ভব, নাকি অসম্ভব। বুঝতে পারলাম, উচ্চতর গণিতে মনোযোগ দিতে হবে আর সেই সঙ্গে ভালো করে শিখতে হবে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান। কাজেই এরপর থেকে সেগুলোই করে যেতে থাকি আমি।
হাইস্কুলে বিজ্ঞান মেলার প্রজেক্টের জন্য আমার মায়ের গ্যারেজে একটা অ্যাটম স্ম্যাশার বা পরমাণু চূর্ণকারক যন্ত্র বানাই আমি। সে জন্য ওয়েস্টিংহাউস কোম্পানিতে গিয়ে ৪০০ পাউন্ড ট্রান্সফরমার স্টিলের জঞ্জাল জড়ো করি। বড়দিনের ছুটির পুরো সময়টা হাইস্কুলের ফুটবল মাঠে ২২ মাইল তামার তার প্যাচাই সেবার। এভাবে ২৩ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের বেটাট্রন পার্টিকেল অ্যাকসিলারেটর বানিয়েছিলাম। যন্ত্রটি চালাতে ৬ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ খরচ হতো (যা আমাদের পুরো বাড়ির বিদ্যুৎ খরচের সমান)। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের চেয়েও ২০ হাজার গুণ বেশি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করতে পারত আমার যন্ত্রটি। আমার লক্ষ্য ছিল, এমন শক্তিশালী গামারশ্মির ঝলক তৈরি করা, যা দিয়ে অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তু তৈরি করা যায়।
এই প্রজেক্টের কল্যাণে সেবার আমি জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় যেতে পেরেছিলাম। এরপর একসময় হার্ভার্ডে স্কলারশিপ পেয়ে পূরণ হয় আমার স্বপ্নটাও। সেখানে একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হয়ে আর আমার রোল মডেল আলবার্ট আইনস্টাইনের পদাঙ্ক অনুসরণ করি। এভাবে অবশেষে আমার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি।
এখন বিজ্ঞান কল্পকাহিনির লেখক ও চিত্রনাট্যকারদের কাছ থেকে আমি প্রচুর ই-মেইল পাই। তাঁদের লেখা গল্পগুলোকে আরও ক্ষুরধার করতে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর সীমাবদ্ধতা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমার সহায়তা পেতে চান তাঁরা।
‘অসম্ভব’ হলো আপেক্ষিক
পদার্থবিদ হিসেবে আমি শিখেছি, ‘অসম্ভব’ হলো একটা আপেক্ষিক শব্দ। মনে আছে, বড় হয়ে ওঠার সময়, আমার এক শিক্ষিকা তাঁর পেছনের দেয়ালে ঝোলানো পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে হেঁটে যেতে যেতে দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকার উপকূলরেখার দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। এরপর তিনি বলেন, এই যে দুই মহাদেশের উপকূলরেখা পরস্পরের সঙ্গে মিলে যায়, এটা কি জিগস পাজলের মতো নিছক কাকতালীয় নয়? তিনি বললেন, কিছু কিছু বিজ্ঞানী মনে করেন, একসময় সব কটি মিলে হয়তো একসঙ্গে অনেক বড় একটা মহাদেশ ছিল। কিন্তু বিষয়টি হাস্যকর। কোনো শক্তিই এ রকম বিশাল দুই মহাদেশকে আলাদা করতে পারবে না। সবশেষে বললেন, সে রকম কোনো কিছু ঘটার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব।
সে বছর কিছুদিন পর আমরা ডাইনোসর নিয়ে পড়ি। আমাদের শিক্ষক বললেন, ডাইনোসর কয়েক লাখ বছর ধরে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে। তারপর একদিন হুট করে এখান থেকে গায়েব হয়ে গেল তারা। বিষয়টি কি অদ্ভুত নয়? কেউই জানে না, তারা এ রকম হুট করে সবাই কেন মারা গেল। কিছু ভূতত্ত্ববিদের ধারণা, মহাকাশ থেকে হয়তো একটা উল্কা এসে দলবলসহ তাদের মেরে ফেলেছিল। কিন্তু সেটা তো অসম্ভব, ওটা কেবল বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতেই ঘটা সম্ভব।
এখন আমরা জানি, প্লেট টেকটোনিকের মাধ্যমে মহাদেশগুলো ক্রমেই পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আর ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে প্রায় ৬ মাইল লম্বা, বিশাল আকারের এক উল্কা আছড়ে পড়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল ডাইনোসরসহ আরও অনেক প্রাণীকে। আমার নিজের স্বল্প জীবনকালে একদা অসম্ভব মনে হওয়া অনেক কিছুকে বারবার বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। কাজেই আমরা একদিন নিজেদের হয়তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় টেলিপোর্ট করতে পারব, কিংবা আমাদের বহু আলোকবর্ষ দূরের কোনো নক্ষত্রে নিয়ে যেতে সক্ষম কোনো স্পেসশিপও বানাতে পারব—সেসব কল্পনা করা কি অসম্ভব?
সাধারণত এ রকম কাণ্ডকারখানাকে বর্তমানের পদার্থবিদেরা অসম্ভব মনে করেন। সেগুলো কি বাস্তবে সম্ভব হতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে? নাকি কয়েক হাজার বছরের মধ্যে প্রযুক্তি যখন আরও উন্নত হবে, তখন সম্ভব হবে সেগুলো? নাকি আরও কয়েক লাখ বছর লেগে যাবে এসব সত্যি হতে? অন্যভাবে বলা যায়, আমরা যদি কোনোভাবে আমাদের চেয়ে দশ লাখ বছর বেশি উন্নত কোনো সভ্যতার মুখোমুখি হই, তাহলে কি তাদের দৈনন্দিন প্রযুক্তিগুলো আমাদের কাছে ‘ম্যাজিক’ বলে মনে হবে? আসলে এটিই এ বইটির মূল আলোচ্য বিষয়। আজকে অসম্ভব হওয়ার কারণে কি সেটা ভবিষ্যতে কয়েক শতাব্দী বা কয়েক লাখ বছরেও অসম্ভবই থেকে যাবে?
গত শতাব্দীতে বিজ্ঞানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। বিশেষ করে ওই শতকে আবিষ্কৃত হয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর সাধারণ আপেক্ষিকতা। কাজেই এ ধরনের চমকপ্রদ কোনো প্রযুক্তি আদৌ যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে তা কখন ঘটবে, তার মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। স্ট্রিং থিওরির মতো আরও উন্নত কিছু তত্ত্ব আসার সঙ্গে সঙ্গে টাইম ট্রাভেল ও সমান্তরাল মহাবিশ্বের মতো বিজ্ঞান কল্পকাহিনির পাতায় বন্দী থাকা ধারণাগুলো নিয়ে পদার্থবিদেরাও এখন একটু নড়চড়ে বসতে শুরু করেছেন। ১৫০ বছর আগের কথা চিন্তা করুন। এখনকার চলমান অনেক প্ৰযুক্তিগত উন্নয়নকে সেকালে স্রেফ আজগুবি বা অসম্ভব বলে ঘোষণা করতেন বিজ্ঞানীরা। অথচ সেগুলোই এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জুল ভার্ন প্যারিস ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি শিরোনামে এক উপন্যাস লেখেন ১৮৬৩ সালে। বাক্সের ভেতর দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ ছিল সেটি। প্রায় এক শতাব্দীর বেশি সময় উপন্যাসটির কথা সবাই বেমালুম ভুলে যায়। হঠাৎ সেটি আবিষ্কার করে বসেন জুল ভার্নের প্রপৌত্র। তারপর ১৯৯৪ সালে প্রথমবারের মতো সেটি প্রকাশ করেন তিনি। প্যারিস শহর ১৯৬০ সালে দেখতে কেমন হতে পারে উপন্যাসটিতে অনুমান করেছেন জুল ভার্ন। তাঁর এ উপন্যাসজুড়ে প্রযুক্তির ছড়াছড়ি। অথচ উনিশ শতকে একদম অসম্ভব বলে মনে করা হতো সেগুলোকে। এসব প্রযুক্তির মধ্যে আছে ফ্যাক্স মেশিন, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যোগাযোগের নেটওয়ার্ক, কাচের তৈরি বহুতল ভবন, গ্যাসচালিত অটোমোবাইল আর উচ্চগতির এলিভেটেড ট্রেন।
জুল ভার্ন যে বিস্ময়করভাবে এমন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, বিজ্ঞানজগতে মগ্ন থাকতেন তিনি। তা ছাড়া সেকালের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে নিত্য ওঠবস ছিল তাঁর। বিজ্ঞানের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে একজন বিদগ্ধ সমঝদার হওয়ার কারণে তিনি এ রকম অবাক করা সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন।
দুর্ভাগ্য, উনিশ শতকের অন্যতম সেরা কজন বিজ্ঞানীর অবস্থান ছিল এর ঠিক বিপরীতে। কোনো কোনো প্রযুক্তিকে বাস্তবে বানানো একেবারে অসম্ভব বলেও ঘোষণা দিয়ে বসেন তাঁরা। ভিক্টোরিয়ান যুগের সম্ভবত সবচেয়ে নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন লর্ড কেলভিন (তাঁকে ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে আইজাক নিউটনের সমাধির পাশে সমাহিত করা হয়)। অথচ তিনি একবার ঘোষণা দিলেন, বাতাসের চেয়ে ভারী কোনো যন্ত্র (যেমন উড়োজাহাজ) ) বানানো অসম্ভব। শুধু তা-ই নয়, তাঁর ধারণা ছিল, এক্স-রে হলো স্রেফ ধাপ্পাবাজি, আর রেডিওর কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এদিকে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আবিষ্কর্তা আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পারমাণবিক বোমা তৈরির সম্ভাবনাকে অবাস্তব কল্পনা বলে একদম নাকচ করে দেন। উনিশ শতকের রসায়নবিদেরা পরশপাথরের (কাল্পনিক এমন এক পদার্থ, যা সিসাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে পারে) অনুসন্ধানের ধারণাকে বৈজ্ঞানিকভাবে অচল বলে রায় দেন। উনিশ শতকের রসায়নের ভিত্তি ছিল সিসার মতো পদার্থের মৌলিক নিত্যতা। কিন্তু বর্তমানের অ্যাটম স্ম্যাশার ব্যবহার করে আমরা তাত্ত্বিকভাবে সিসার পরমাণুকে সোনায় রূপান্তর করতে পারি। একবার ভেবে দেখুন, আজকের যুগের টেলিভিশন, কম্পিউটার আর ইন্টারনেট গত বিশ শতকে কতটা বিস্ময়কর বলে মনে হতো।
কিছুদিন আগেও কৃষ্ণগহ্বরকে বিজ্ঞান কল্পকাহিনি বলে ভাবা হতো। ১৯৩৯ সালে আইনস্টাইন এক গবেষণাপত্রে লেখেন, কৃষ্ণগহ্বর কখনোই গঠিত হতে পারবে না। অথচ আজকের যুগে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ ও চন্দ্র এক্স-রে টেলিস্কোপ মহাকাশে কয়েক হাজার কৃষ্ণগহ্বর উদ্ঘাটন করেছে। [ইভেন্ট হরাইজন নামের একটি বিশেষ ধরনের টেলিস্কোপে এম৮৭ ছায়াপথে অবস্থিত ৫০০ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন দূরের একটি কৃষ্ণগহ্বরের ছবি সম্প্রতি তোলা সম্ভব হয়েছে।—অনুবাদক]
এসব প্রযুক্তি অসম্ভব মনে হওয়ার পেছনের কারণ হলো, উনিশ ও বিশ শতকের শুরুর দিকে তাঁদের পদার্থবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞান জানা ছিল না। আসলে সেকালে বিজ্ঞানের অনেক কিছুই অজানা ছিল, বিশেষ করে পারমাণবিক পর্যায়ে। সুতরাং সেকালে এ ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যে অসম্ভব মনে হবে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।
অসম্ভব নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
মজার ব্যাপার হলো, অসম্ভব ব্যাপার নিয়ে গুরুতর পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করলে বিজ্ঞানের আরও উন্নত ও পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত দিগন্ত উন্মোচিত হয়। যেমন, কয়েক শতক ধরে পারপিচুয়াল মোশন মেশিন বা অবিরাম গতির যন্ত্রের পেছনে হতাশাজনক আর বৃথা অন্বেষা চালানো হয়েছে। এর কারণে পদার্থবিদেরা একসময় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন যে এ ধরনের যন্ত্র বানানো অসম্ভব। পাশাপাশি শক্তি সংরক্ষণ নীতি ও তাপগতিবিদ্যার তিনটি সূত্রকে মৌলিক নীতি হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে তাদের। কিন্তু অবিরাম গতির যন্ত্র বানানোর ব্যর্থ অনুসন্ধান তাপগতিবিদ্যার সম্পূর্ণ নতুন কোনো ক্ষেত্র খুলে দিতে পারে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, যন্ত্রযুগ ও আধুনিক শিল্পসমাজের ভিত্তির অনেকটাই তাপগতিবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল।
উনিশ শতকের শেষে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন, পৃথিবীর বয়স কয়েক বিলিয়ন বছর হওয়া অসম্ভব। লর্ড কেলভিন মোটাদাগে ঘোষণা করলেন, গলন্ত কোনো পৃথিবী ২০ থেকে ৪০ মিলিয়ন বছরের মধ্যেই ঠান্ডা হয়ে যেতে পারবে। অন্যদিকে তাঁর বিপক্ষের ভূতত্ত্ববিদ আর ডারউইনবাদী জীববিজ্ঞানীরা দাবি করে বসলেন, পৃথিবী সম্ভবত কয়েক বিলিয়ন বছর পুরোনো। নিউক্লিয়ার বল আবিষ্কার করে এই অসম্ভবটাই শেষ পর্যন্ত সম্ভব বলে প্রমাণ করেন মাদাম কুরি আর অন্য বিজ্ঞানীরা। তাঁরা দেখালেন পৃথিবীর কেন্দ্র কীভাবে তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ে উত্তপ্ত হয় এবং কয়েক বিলিয়ন বছর গলন্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে।
বিপদের সময় আমরা সব অসম্ভবকে উপেক্ষা করি। ১৯২০-এর দশক থেকে ১৯৩০-এর দশকে আধুনিক রকেটবিদ্যার জনক রবার্ট গডার্ড সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। সেকালে অনেকের ধারণা ছিল, রকেট কখনোই মহাকাশে যেতে পারবে না। আসলে তারা ছিল তাঁর প্রধান সমালোচক। তারা ব্যঙ্গ করে তাঁর গবেষণাকে বলত ‘গডার্ডের গাধামি’। ১৯২১ সালে নিউইয়র্ক টাইমস-এর সম্পাদক ড. গডার্ডের বিরুদ্ধে লেখেন : ‘প্রফেসর গডার্ড ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার ভেতর সম্পর্কটাই জানেন না। এমনকি বিক্রিয়া ঠেকাতে ভ্যাকুয়ামের চেয়েও যে ভালো কিছুর দরকার, তা-ও জানেন না। হাইস্কুলে যে তাঁর সাধারণ জ্ঞানের অভাব ছিল, সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।’ রকেট চালানো অসম্ভব, কারণ মহাকাশে তাকে ঠেলার মতো কোনো বাতাস নেই বলে ওই সম্পাদক বেশ তর্জন-গর্জন করেন সেবার। দুর্ভাগ্যক্রমে, একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান গডার্ডের এই ‘অসম্ভব’ রকেটের মর্ম সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ছিলেন অ্যাডলফ হিটলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি তাদের তৈরি অতি উন্নত ভি-২ রকেট অবিরাম বৃষ্টির মতো ঝরিয়ে লন্ডন শহরের বুকে আঘাত হানে। তাতে সেখানে অগণিত মৃত্যু আর ধ্বংস ডেকে এনে ইংল্যান্ডকে প্রায় পদানত করে ফেলে জার্মানি
অসম্ভব নিয়ে এ রকম আলোচনা বিশ্ব ইতিহাসও হয়তো বদলে দিতে পারে। ১৯৩০-এর দশকে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো, পারমাণবিক বোমা বানানো ‘অসম্ভব’। এমনকি খোদ আইনস্টাইনও বিশ্বাস করতেন সেই কথা। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ E=mc2 অনুযায়ী পদার্থবিদেরা তখন জানতেন, পরমাণুর নিউক্লিয়াসে বিপুল শক্তি মজুত আছে। কিন্তু তারপরও পরমাণুর কোনো নিউক্লিয়াস থেকে শক্তি বের করে আনা খুবই অর্থহীন কাজ বলে ভাবা হতো। তবে এইচ জি ওয়েলসের উপন্যাস দ্য ওয়ার্ল্ড সেট ফ্রি পড়ার কথা স্মরণ করেছেন পরমাণু পদার্থবিদ লিও জিলার্ড। উপন্যাসটিতে পারমাণবিক বোমা বানানোর ভবিষ্যদ্বাণী করেন ওয়েলস। বইতে তিনি উল্লেখ করেন, পদার্থবিদেরা পারমাণবিক বোমার রহস্য উদ্ঘাটন করবেন ১৯৩৩ সালের মধ্যেই। ভাগ্যক্রমে ১৯৩২ সালে হঠাৎ বইটি হাতে এসে পড়ে জিলার্ডের। দুই দশক আগে এই উপন্যাসে ওয়েলসের করা ভবিষ্যদ্বাণীর তাড়না থেকেই চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে একটি পরমাণুর ওপর শক্তি কেন্দ্রীভূত করার আইডিয়াটি হঠাৎ তাঁর মাথায় আসে। এই চেইন রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে একটি ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস ভেঙে তার শক্তিকে অনেক গুণ বেশি শক্তিতে পরিণত করা যায়। একে একে বেশ কিছু ধারাবাহিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন জিলার্ড। তারপর আইনস্টাইন আর প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করেন তিনি। এসব ঘটনাই ম্যানহাটান প্রজেক্টের দিকে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রকে। আর এই প্রজেক্টেই বানানো হয় প্রথম পারমাণবিক বোমা।
এভাবে আমরা বারবার দেখতে পাব, অসম্ভব নিয়ে গবেষণার কারণে পুরোপুরি নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। পাশাপাশি পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের চৌহদ্দির দিকে ঠেলে দেয় এবং বিজ্ঞানীরা যাকে ‘অসম্ভব’ বলে মনে করেন, তাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করে। স্যার উইলিয়াম অসলার একবার বলেছিলেন, ‘এক যুগের দর্শন পরের যুগের উদ্ভট বিষয়ে পরিণত হয়। আর গতকালের বোকামি পরিণত হয় আগামীকালের বিচক্ষণতায়।’
পদার্থবিদ টি এইচ হোয়াটের বিখ্যাত বাণীটিতে একমত অনেকে। তিনি দ্য ওয়ানস অ্যান্ড ফিউচার কিং-এ লেখেন, “নিষিদ্ধ নয় এমন যেকোনো কিছুই বাধ্যতামূলক’–পদার্থবিজ্ঞানে আমরা সব সময়ই এ রকম প্রমাণ খুঁজে পাই। নতুন কোনো ঘটনায় পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্র স্পষ্ট বিরুদ্ধাচরণ না করা পর্যন্ত, আমরা তার অস্তিত্ব টের পাই না। (নতুন অতিপারমাণবিক কণা খোঁজার সময় এটা বারবার ঘটতে দেখা গেছে। কোনটা নিষিদ্ধ, তার সীমানা অনুসন্ধান করতে গিয়ে পদার্থবিদেরা প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবে পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কার করে বসেন।) কাজেই টি এইচ হোয়াটের কথাটিতে একটু ঘুরিয়েও হয়তো বলা যায়, ‘অসম্ভব নয় এমন যেকোনো কিছুই বাধ্যতামূলক!’
যেমন বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্ববিদ স্টিফেন হকিং প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন, টাইম ট্রাভেল অসম্ভব। সে জন্য পদার্থবিজ্ঞানের নতুন একটি সূত্র খুঁজে বের করেন তিনি, যা টাইম ট্রাভেলকে নিষিদ্ধ করে। একে তিনি বলেন ক্রনোলজি প্রটেকশন কনজেকচার বা কালপঞ্জি সুরক্ষা অনুমান। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক বছরের কঠোর পরিশ্রমেও নীতিটি প্রমাণ করা যায়নি। আসলে বিপরীত দিকে পদার্থবিদেরা এখন প্রমাণ করেছেন যে টাইম ট্রাভেল ঠেকিয়ে দেওয়া সূত্র আমাদের বর্তমান যুগের গণিতের সীমানার বাইরে। এখন টাইম মেশিনের অস্তিত্ব ঠেকিয়ে দেওয়ার মতো পদার্থবিজ্ঞানের কোনো সূত্র না থাকার কারণে পদার্থবিদেরা এই সম্ভাবনাকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন।
এই বইয়ের উদ্দেশ্য হলো যেসব প্রযুক্তিকে এখন ‘অসম্ভব’ বলে ভাবা হচ্ছে, কিন্তু যা কয়েক দশক থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে—সেগুলো নিয়ে আলোচনা।
ইতিমধ্যে একটি ‘অসম্ভব’ প্রযুক্তি এখন সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। সেটি হলো টেলিপোর্টেশন (অন্তত পরমাণু পর্যায়ে এটি করা সম্ভব হয়েছে)। অথচ কয়েক বছর আগেও পদার্থবিদেরা বলতেন, কোনো বস্তুকে এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে পাঠানো বা বিমিং করা হলে তা কোয়ান্টাম ফিজিকসের সূত্র অমান্য করে। পদার্থবিদদের সমালোচনায় একসময় খুবই যন্ত্রণার ভেতর ছিলেন স্টার ট্রেকের টেলিভিশন সিরিজের লেখকেরা। সে কারণে তাদের টেলিপোর্টেশনকে ব্যাখ্যা করতে ‘হাইজেনবার্গের ক্ষতিপূরণ’ যোগ করেছেন তাঁরা। সাম্প্রতিক যুগান্তকারী এক ঘটনার কারণে পদার্থবিদেরা এখন পরমাণুকে একটি ঘরের এ প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পাঠাতে পারেন। আবার ফোটন পাঠাতে পারেন দানিয়ুব নদীর তলদেশ দিয়েও।
ভবিষ্যতের অনুমান
ভবিষ্যদ্বাণী করা সব সময়ই বিপজ্জনক। বিশেষ করে যে ভবিষ্যদ্বাণীটি পূরণ হতে ভবিষ্যতে কয়েক শতাব্দী থেকে কয়েক হাজার বছর লেগে যেতে পারে, তাতে বিপদ আরও বেশি। পদার্থবিদ নীলস বোর প্রায়ই একটা কথা বলতেন, “ভবিষ্যদ্বাণী করা খুবই কঠিন। বিশেষ করে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।’ কিন্তু জুল ভার্নের সময়কাল ও বর্তমানের মধ্যে এক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সূত্রগুলো বোঝা সম্ভব হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, প্রোটনের অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে শুরু করে তার তুলনায় ১০৪৩ গুণ বড় প্রসারণশীল মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রগুলো বর্তমানে জানেন পদার্থবিদেরা ফলে মোটাদাগে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির চেহারা কেমন হবে, সে সম্পর্কে পদার্থবিদেরা এখন যৌক্তিক আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে পারেন। আবার কোন কোন প্রযুক্তির অসম্ভাবনা সন্দেহজনক আর কোনগুলো সত্যি সত্যিই অসম্ভব, তার মধ্যে পার্থক্য টানতে পারেন তাঁরা।
সে কারণে যেসব প্রযুক্তি ‘অসম্ভব’, সেগুলোকে এই বইয়ে তিনটি ভাগে ভাগ করেছি আমি।
এগুলোর মধ্যে প্রথমটিকে আমি বলব প্রথম শ্রেণির অসম্ভাব্যতা। এই প্রযুক্তিগুলো বর্তমানে অসম্ভব, কিন্তু এরা পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্ৰ অমান্য করে না। কাজেই সেগুলো এই শতাব্দীতেই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতে পারে কিংবা হয়তো রূপান্তরিতভাবে সম্ভব হতে পারে পরের কোনো শতাব্দীতে। এ শ্রেণির মধ্যে আছে টেলিপোর্টেশন, অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিপদার্থ ইঞ্জিন, নির্দিষ্ট ধরনের টেলিপ্যাথি, সাইকোকানেসিস আর অদৃশ্য হওয়া।
দ্বিতীয় ধরনটিকে বলব দ্বিতীয় শ্রেণির অসম্ভাব্যতা। এসব প্রযুক্তি ভৌত বিশ্বে আমাদের উপলব্ধির দিক থেকে খুবই কাছাকাছি রয়েছে। এগুলো যদি কখনো আদৌ সম্ভব হয়, তাহলে তার জন্য সহস্রাব্দ থেকে কয়েক মিলিয়ন বছরও লেগে যেতে পারে। এদের মধ্যে রয়েছে টাইম মেশিন, হাইপারস্পেস ট্রাভেলের সম্ভাবনা আর ওয়ার্মহোলের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ।
সর্বশেষ ধরনটিকে আমি বলব তৃতীয় শ্রেণির অসম্ভাব্যতা। এসব প্রযুক্তি আমাদের বর্তমানে জানা পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলো লঙ্ঘন করে। অবাক ব্যাপার হলো, এ রকম প্রযুক্তির সংখ্যা একেবারে হাতে গোনা। এগুলো যদি কখনো সম্ভবপর হয়, তাহলে সেগুলো আমাদের উপলব্ধির মৌলিক ধারণা পাল্টে দেবে।
আমার ধারণা, এই শ্রেণিবিভাগটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বিজ্ঞান কল্পকাহিনিতে দেখানো বেশ কিছু প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা এমনভাবে নাকচ করে দেন, যেন সেগুলো কখনোই সম্ভব নয়। আসলে এর মাধ্যমে তাঁরা বোঝাতে চান, আমাদের মতো আদিম সভ্যতার পক্ষে এগুলো অসম্ভব। যেমন এলিয়েন দেখাকে সাধারণত অসম্ভব ঘটনা বলে মনে করা হয়। কারণ, নক্ষত্রগুলোর একটি থেকে আরেকটির মাঝখানের দূরত্ব অনেক বেশি। সে কারণে আন্তনাক্ষত্রিক ভ্রমণ আমাদের জন্য আক্ষরিক অর্থেই অসম্ভব। কিন্তু তবু আমাদের চেয়ে কয়েক শতাব্দী থেকে কয়েক হাজার কিংবা কয়েক লাখ বছর এগিয়ে থাকা অন্য কোনো সভ্যতার জন্য হয়তো তা সম্ভবও হতে পারে। কাজেই এ ধরনের ‘অসম্ভাব্যতা’র শ্রেণিকরণ করা জরুরি। আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যেসব প্রযুক্তি অসম্ভব, সেগুলো অন্য কোনো ধরনের সভ্যতার জন্য অসম্ভব না-ও হতে পারে। আমাদের থেকে হাজার বা লাখ বছর সামনে অগ্রসর কোনো সভ্যতায় কোনটি সম্ভব আর কোনটি অসম্ভব, সে সম্পর্কে বিবৃতি গণনায় ধরতে হবে।
কার্ল সাগান একবার লিখেছিলেন, ‘কোনো সভ্যতার জন্য এক মিলিয়ন বছর বয়সের অর্থ কী? আমাদের কাছে রেডিও টেলিস্কোপ ও স্পেসশিপ আছে মাত্র কয়েক দশক হলো; আমাদের প্রযুক্তিগত সভ্যতার বয়স মাত্র কয়েক শ বছর। কাজেই দশ লাখ বছরের পুরোনো উন্নত কোনো সভ্যতা আমাদের থেকে ততটাই এগিয়ে থাকবে, যতটা কোনো বুশ বেবি বা ম্যাকাও বানরের চেয়ে আমরা এগিয়ে আছি।’
আমার নিজের গবেষণায় পেশাগতভাবে আইনস্টাইনের স্বপ্নের ‘থিওরি অব এভরিথিং’ সম্পূর্ণ করার দিকে মনোযোগ দিয়েছি আমি। চূড়ান্ত তত্ত্ব নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করতে গিয়ে বেশ আনন্দ খুঁজে পাই। এটিই হয়তো এখনকার বিজ্ঞানের সবচেয়ে কঠিন কতিপয় ‘অসম্ভব’ প্রশ্নের চূড়ান্ত উত্তর দিতে পারবে। প্রশ্নগুলো যেমন টাইম ট্রাভেল সম্ভব কি না, কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে কী আছে কিংবা মহাবিস্ফোরণের আগে কী ঘটেছিল। আমি এখনো অসম্ভাব্যতার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের ভালোবাসা নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখি। কখনো যদি এ অসম্ভবগুলোর কিছু কিছু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ঢুকে যেতে পারে, তাহলে যারপরনাই বিস্মিত হব।
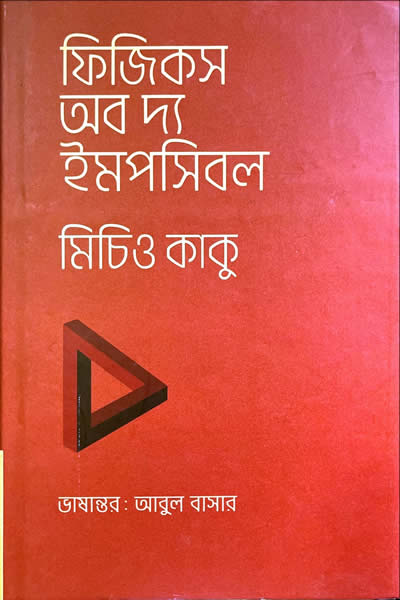
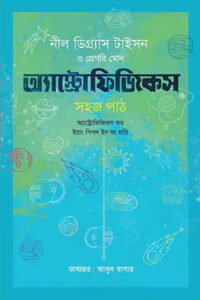
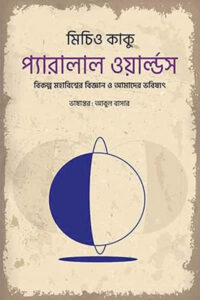

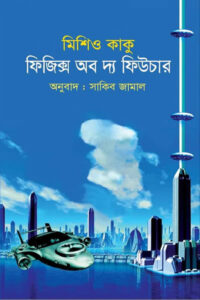

Leave a Reply