পুরাণ ও অন্যান্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য
পুরাণ ও অন্যান্য – সুকুমারী ভট্টাচার্য
প্রথম প্রকাশ–অক্টোবর, ২০১২।
উৎসর্গ – ড. দীপক ভট্টাচার্য ড. রণজিৎ পাল প্রীতিভাজনেষু
.
প্রকাশকের নিবেদন
ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য ধ্রুপদী ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালের অন্যতম অগ্রগণ্য বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর বয়োভার ও ভগ্নস্বাস্থ্য উপেক্ষা করে নিয়মিত মিলেমিশে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে এসেছেন। আমাদের অনুরোধে তিনি মিলেমিশে পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তিনি মিলেমিশে সংস্থার শিরোভূষণ, তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।
বিশ্বভারতীর সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগের সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. নীরদবরণ মণ্ডল স্বতঃশ্রদ্ধচিত্তে ড. সুকুমারী ভট্টাচার্যের এই রচনাসংকলন ‘পুরাণ ও অন্যান্য’ গ্রন্থটির একটি মহার্ঘ ভূমিকা লিখে দিয়েছেন, যা গ্রন্থটির সমীক্ষণ-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। ড. মণ্ডলকে আমাদের কৃতজ্ঞ অভিবাদন।
মিলেমিশে সংস্থা ও পত্রিকার কার্যনির্বাহী সদস্য-কর্মীবৃন্দ— স্বপ্ন ঘোষ, দীপঙ্কর দাস, বিশ্বনাথ বসু, সঞ্জীবকুমার দে, সুকান্ত দাশ, অমর দাশ ও শঙ্কর বর এই প্রকাশনা কাজে তাঁদের যথাসাধ্য শ্রম ও সতর্কতা রক্ষা করেছেন। গ্রন্থমুদ্রণে বসু-মুদ্রণের অরূপ বসু ও ধন্যবাদাহ। বন্ধুবর বাদল বসুর উৎসাহ এই গ্রন্থ প্রকাশে যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে।
সমীরকুমার গুপ্ত
.
ভূমিকা
এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে মিলেমিশে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বা প্রকাশন সংস্থাটি বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ-গবেষণায় পারঙ্গমা বিদুষী স্বনামধন্যা সুকুমারী ভট্টাচার্যের কিছু প্রবন্ধের সংকলন ও পুনঃপ্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা তাঁর নানা মননশীল প্রবন্ধের সঙ্গে অন্তত কিছুটা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয় এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাবেন—কারণ তাঁর রচিত মননশীল প্রবন্ধগুলি বিদ্যার প্রাঙ্গণে মূল্যবান সম্পদবিশেষ—যা আমাদের নানা দিক দিয়ে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে। যদিও সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদবিদ্যা তাঁর মূল অবলম্বন তবু একথা সহজেই বোঝা যায় যে বিশ্ববাঙময়ের রাজ্যে তাঁর অবাধ বিচরণ। বস্তুত এই ব্যাপক বিশ্ববোধই তাঁকে অনন্যা করে তুলেছে— গতানুগতিক সংকীর্ণতার বাঁধ ভেঙে। মনে হয়-এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। তাই তাঁর লেখনী যেমন জয়দেবের গীতগোবিন্দ আস্বাদনে উৎসুক তেমনই পৃথিবীর প্রথম মহাকাব্য গিলগামেশের অমরত্বের সন্ধানে তৎপর। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না এই বিদুষী প্রাবন্ধিকের পরিচয় নূতন করে বাঙালি পাঠকবর্গের কাছে না দিলেও চলে। এখানে তাঁর প্রথম নিবন্ধটি স্মৃতিচারণমূলক। কানাডার উইনিপেপ শহরে বিশ্বসম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে তাঁর সেই দেশের কিছু অঞ্চল ভ্রমণ ও সন্দর্শনের স্মৃতিচারণ। — আর ‘নায়াগ্রার এক ঝলক’ লেখনীর প্রসাদগুণে পাঠকের মানসপটেও আভাসিত হয়ে ওঠে। পরের প্রবন্ধটিতে বর্ণিত হয়েছে মেঘদূতের সমস্যা— তবে শুধু সমস্যাতেই তা শেষ হয়ে যায়নি— রয়েছে সুচিন্তিত সমাধান লাভের দিগদর্শন। মেঘ যে স্বরূপত জড়পদার্থ— তাই দূতরূপে তাকে পাঠাতে হলে তার উপর প্রথমে চাই ব্যক্তিত্বের সমারোপ,–মহাকবি কালিদাস তার কৈফিয়ত দিয়েছেন— ‘কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাতেনেষু’। আর্ত যক্ষের অপ্রকৃতিস্থ দৃষ্টিতে মেঘকে চেতন প্রাণী হিসাবে দেখা তাই স্বাভাবিক। “কামার্তা হি”–এই বাক্যাংশে ব্যবহৃত ‘হি’ শব্দটি তাই হেতুর দ্যোতক। যুক্তিবাদী কবি একটা হেতু প্রদর্শন না করে পারেননি। দেখা যাচ্ছে পাঠকদের চাহিদাও সেই প্রকার ছিল। আধুনিক কবি হলে হয়তো সব সময় এত কৈফিয়ত দেওয়া প্রয়োজন মনে করতেন না। মহাকবি কালিদাস এখানে সামান্যের দ্বারা বিশেষ সমর্থনরূপ সমর্থসমর্থকভাব দেখাতে বাধ্য হয়েছেন। ফলে পাঠকের জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হয়েছে এই অর্থান্তরন্যাসে। প্রসঙ্গত বলা যায়— মেঘদূত অনুসরণে রচিত অন্যান্য পরবর্তীকালের অনেক দূতকাব্যের ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন উঠতে পারে। কালিদাসের মেঘদূত হল সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ খণ্ডকাব্য বা লিরিক। শুধু সংস্কৃত সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যে-এর উল্লেখযোগ্য স্থান আছে।
যাই হোক মেঘের উপর জীবন্ত ব্যক্তিত্বের সমারোপকে বুদ্ধিগ্রাহ্য বা যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলার জন্যই বলা হয়েছে–বিরহী যক্ষ তো আর্ত-অপ্রকৃতিস্থ তাই চেতন ও অচেতনের পার্থক্যজ্ঞান হারিয়েছে। কাজেই তাঁর পক্ষে মেঘকে দূত করে পাঠাবার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। যক্ষের দৃষ্টিতে মেঘ একজন সহৃদয় দূত–আবার বিলাসী নায়কও বটে। অতএব মেঘের উপযুক্ত নায়িকা বা প্রেয়সীও আছে। পথের নদীরাই মেঘের যোগ্য নায়িকা হতে পারে। অতএব মেঘের উপর নায়কভাব সমারোপের সঙ্গে সঙ্গে নদীগুলির উপর নায়িকার ভাবও আরোপিত হল। তাই যক্ষ মেঘকে বলেছেন—যথা—
বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসৰ্পন্ত্যাঃ লিতসুভগংদর্শিতাবৰ্ত্তনাভেঃ।
নির্বিন্ধ্যায়ঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমোহি
প্রিয়ে।।
অর্থাৎ–পথেই আছে নির্বিন্ধ্যা নদী। তরঙ্গের ক্ষোভে মুখরিত বিহঙ্গের শ্রেণি যেন তাঁর–সেই নদীরূপা চঞ্চলা নায়িকার) মেখলা। (বিহগশ্রেণির কলরব যেন মেখলার ঝংকার)। লিত সুভগ গতিতে চলে যাওয়ার ফলে দেখা যায় আবর্তনাভি। হে মেঘ, তুমি কাছাকাছি এসে এই নদীর রসের অভ্যন্তরে নামো। কেননা— নারীর প্রথম প্রেমনিবেদন হয় প্রিয়তমের প্রতি হাবভাবের মাধ্যমে। (কিন্তু কথায় নয়)। দেখা যাচ্ছে–নিছক নারীত্বের সমারোপই নয়, নদীকে একটি সবিশেষ হাবভাবময়ী নায়িকারূপে উপস্থাপিত করাই কবির অভিপ্রায়। নির্বিন্ধ্যার হাবেভাবেও তাই ফুটে উঠেছে প্রথম প্রেমনিবেদনের আকুতি, কিংবা এটা বোধহয় আর্ত অপ্রকৃতিস্থ যক্ষের কল্পনা।
আবার ক্ষীণজলধারার একবেণি ধারণ করে মলিন জীর্ণপর্ণে পাণ্ডুচ্ছায়া কৃশাঙ্গী বিরহিনী নদীকেও মেঘের রাস্তায় দেখা গেছে।
অনুরূপভাবে গম্ভীরা নদীও যেন এক প্রকৃতিগম্ভীরা নায়িকা। তার স্বচ্ছ সলিল যেন প্রসন্নচিত্ত — অনাবিল। প্রকৃতিতে গম্ভীরা হলেও দৃষ্টিপাতে চটুলতা ঠিক বোঝা যায়। চঞ্চল শফরী। মৎস্যের উদ্বর্তনই হচ্ছে তার সেই চপল দৃষ্টিক্ষেপ।
এইভাবে দেখা যাচ্ছে অচেতন জড়পদার্থ নদীর উপরে চেতন ব্যক্তিত্বের আরোপ ঘটেছে মেঘের সাথে সাথেই। কারণ বিরহী যক্ষ আর্ত অপ্রকৃতিস্থ। তাই তো মেঘদূত প্রসঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যক্ষের কাছে এই আশঙ্কা ব্যক্ত করার অবকাশ পেয়েছেন— ‘তোমার তো চেতন অচেতনে পার্থক্যজ্ঞান নাই, কি জানি, যদি সত্য ও কল্পনার মধ্যেও প্রভেদ হারাইয়া থাক।’
২.
জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ কাব্যটি নিয়ে সাধারণত দু-ধরনের বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমত জয়দেব কোথাকার লোক তিনি কি বাংলার না উড়িষ্যার? বীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি গ্রামে এই কবির স্মৃতির উদ্দেশে প্রতিবছর মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং এখানকার অধিবাসীদের বিশ্বাস— তিনি এই কেন্দ্রবিন্দুতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অপরপক্ষে উড়িষ্যার অনেক বিদ্বানেরা দাবি করেন— জয়দেব উড়িষ্যার লোক। হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন প্রমুখ। বীরভূমের দাবিই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরে গীতগোবিন্দের গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে। এবং কথিত আছে যে জগন্নাথদেব এতেই সবচেয়ে বেশি প্রীত হন। ভক্তমাল গ্রন্থে জয়দেবচরিত্র বর্ণিত হয়েছে। জয়দেব যে জগন্নাথের মন্দিরের কাছাকাছি থাকতেন সে কথাও বলা হয়েছে। উড়িষ্যা ও মিথিলার কোনো কোনো বিদ্বান জয়দেবকে নিজ নিজ প্রদেশের বলে দাবি করেছেন। তবে এ বিষয়ে প্রখ্যাত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত হল বীরভূম জেলার অজয় নদীর তীরস্থ কেন্দুবি বা কেঁদুলির দাবিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি জয়দেব মেলার বহুশতবর্ষব্যাপী ধারাবাহিক প্রচলনের ঐতিহ্যও উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে— হরিনামামৃত ব্যাকরণের একটি টীকার পাণ্ডুলিপির অন্তভাগে (সন ১১৫৩ অর্থাৎ খ্রি. ১৭৪৬তে লেখা) গোপীচরণ দাস বিদ্যাভূষণ নিশ্চিতভাবেই উল্লেখ করেছেন যে জয়দেব কেন্দুবি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন (বর্তমানে কেঁদুলি নামে পরিচিত)। কেন্দুবিল্বই গীতগোবিন্দকারের নিজ গ্রাম ছিল। এই তথ্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ড. হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। (সাহিত্য আকাদেমি, দিল্লি ১৯৮২-তে প্রকাশিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত জয়দেব নামক পুস্তকের ৮ পৃ.দ্র.)।
সেন রাজত্বকালে বটু দাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১১২৭ শকে (বা ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে) সদুক্তিকর্ণামৃত নামে একটি সংস্কৃত কবিতাসংকলন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শ্রীধর দাসের পিতা বটু দাস সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। (দ্র. সুনীতিকুমার)। শ্রীধর দাসের সংকলনে জয়দেবের রচিত বলে উল্লিখিত একত্রিশটি কবিতা স্থান পেয়েছে–যার মধ্যে পাঁচটি হল গীতগোবিন্দ থেকে নেওয়া। হয়তো শ্রীধর দাস জয়দেবের কবিখ্যাতির কথা জানতেন। জয়দেবের দুটি পদ্য সম্ভবত লক্ষ্মণ সেনের বীরত্বস্তুতি। (‘লক্ষ্মীকেলি ভুজঙ্গ জঙ্গমহরে সঙ্কল্পকল্পদ্রুম’ ইত্যাদি ও ত্বং চোলোল্লোললীলাম ইত্যাদি)। একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে বলা হয়েছে — ‘গোবর্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ। অর্থাৎ গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব উমাপতি ও কবিরাজ দোয়ী লক্ষ্মণ সেনের রাজসভার পঞ্চ রত্ন ছিলেন। গীতগোবিন্দের মধ্যেও এদের উল্লেখ দেখা যায়। যথা—
বাচঃ পল্লবয়্যুমাপতিধরঃ সন্দৰ্ভশুদ্ধিংগিরাং
জানীতে জয়দেব
এব শরণঃ শ্লাঘঘ্যা দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়বচনৈরাচাৰ্য্যগোবর্ধন—
স্পর্ধী কোহপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিক্ষ্মাপতিঃ।।
অর্থাৎ উমাপতিধর বাক্য পল্লবিত করতে পারেন, আর দুরূহ পদের দ্রুত রচনায় শরণ প্রশংসাযোগ্য, শৃঙ্গাররসের সৎ ও পরিমিত রচনায় আচার্য গোবর্ধনের সঙ্গে স্পর্ধা করার কেউ আছে বলে শোনা যায় না। আর কবিরাজ ধোয়ী শ্রুতিধররূপেই বিখ্যাত। একমাত্র জয়দেবই বাণীর সন্দর্ভশুদ্ধি জানেন— অর্থাৎ বিশুদ্ধ কাব্য রচনায় দক্ষ। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বৈষ্ণবতোষিণী টীকায় শ্রীজীব গোস্বামীও বলেছেন— শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজলক্ষ্মণসেনমন্ত্রিবরেণ উমাপতিধরেণ ইত্যাদি। গীতগোবিন্দের টীকাকার ধৃতি দাসও বলেছেন— ‘উমাপতিধরো নাম সান্ধিবিগ্রহিকঃ।’
এই সমস্ত নানা তথ্যের ভিত্তিতে জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ও বাঙালি বলে মনে করেন বাংলার অনেক বিদ্বানেরা। কিন্তু উড়িষ্যার বিদ্বানদের অনেকেই পূর্বোক্ত শ্লোকটির প্রামাণ্য স্বীকার করেন না।
গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে যে দ্বিতীয় বিতর্ক বা মতভেদের সম্মুখীন হতে হয়–তা হল এই কাব্যটি কি উৎকর্ষের দিক দিয়ে খুব ভালো বলা যায়? এটা কি সার্থক কবিতা বা কাব্য হয়ে উঠেছে? এই সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য বা মতভেদ আছে। সেইটাই এই অবকাশে আলোচনা করা যেতে পারে।
শ্রীগীতগোবিন্দ রচনার অল্পকালের মধ্যেই ভারতের নানা প্রদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয়। টীকাকারদের সাক্ষ্য থেকে তাই মনে হয়। এই জনপ্রিয়তার কারণ কী?
আবার পুরোনো আমল থেকেই গীতগোবিন্দের বিরুদ্ধ সমালোচনাও হয়ে আসছে। আরাধ্য দেবতা বিষয়ে রতি বর্ণনার বাহুল্য অনুচিত বা অনৌচিত্যদোষদুষ্ট। অনেকটা এইরূপ মনোভাব নিয়ে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর রসগঙ্গাধরে বলেছেন— ‘জয়দেবাদিভিস্তু গীতগোবিন্দাদি প্রবন্ধেষু সকল-সহৃদয়-সম্মতোহয়ং সময়ো মদোন্মত্ত-মতঙ্গজৈরিব ভিন্নঃ’। অর্থাৎ জয়দেব প্রমুখ। এই সহৃদয়-সম্মত নিয়মটি মদমত্ত হস্তীর মতোই ভেঙে ফেলেছেন। কারণ মানুষের মতো করে উত্তমদেবতাদের সম্ভোগরতির সমস্ত অনুভাব পরিষ্কার করে বর্ণনা করা অনুচিত। (স্ফুটীকৃত সকলানুভাববর্ণনম অনুচিতম)। (যেমন মাতাপিতার প্রতিবর্ণনা রসনিষ্পত্তির কারণ হয় না)। এখানে পণ্ডিতরাজের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্ব আছে। তিনি বলতে চাইছেন যে নায়কনায়িকা যদি আরাধ্য দেবতা হয় তা হলে তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রতিবর্ণনা অনুচিত। আর গীতগোবিন্দের নায়ক নায়িকা তো দেবতাই। স্বয়ং দশাবতারী শ্ৰীকৃষ্ণ এর নায়ক। এতে মনে হয়–জগন্নাথের অভিপ্রায় হল— নায়ক নায়িকা মানুষ হলে (বা আরাধ্য না হলে) উক্ত প্রকার বর্ণনায় আপত্তি থাকত না। মাতাপিতার দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে আরাধ্য বা সম্মাননীয় মানুষ হলেও উক্ত প্রকার বর্ণনা অনুচিত। কারণ আরাধ্যতার প্রতীতিটি রসানুভবে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (যেমন পিতামাতার ক্ষেত্রে)। যাই হোক— এ ছাড়া অন্য সাধারণ ক্ষেত্রে মানুষ নায়ক নায়িকার উক্ত প্রকার বর্ণনায় দোষ নাই— এটাই এখানে মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু অশ্লীলতাদোষের লক্ষণও অলংকারশাস্ত্রে আছে। বিস্তারিত বিশ্লেষণে না গিয়ে এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে জয়দেবের আগে বহু সংস্কৃত কাব্যে বা মহাকাব্যে নরনারীর দেহধর্মের অকুণ্ঠ বর্ণনা আছে। মনে হয়— তদানীন্তন সাহিত্যরুচি ও প্রেমসম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি এর একটা কারণ। যাইহোক— জগন্নাথের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বিচারেও জয়দেব অভিযুক্ত হয়েছেন।
আধুনিককালে যাঁরা জয়দেবের অত্যন্ত প্রতিকূল সমালোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন— ‘জয়দেব অধিকাংশ কবিদিগের অপেক্ষা কাব্যের বিষয় নির্বাচনে নিজের নিকৃষ্টরুচির পরিচয় দিয়াছেন।’ ‘গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথাই নাই— কেবল আদিরসের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই—শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার’। ’জয়দেবের ভাষার প্রধান দোষ Rhythm অর্থাৎ ছন্দের। তাল লয়ের অভাব। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দ সকল একটি প্রায় সম্পূর্ণ অন্য আর একটির ন্যায়।’ অর্থাৎ তাঁর মতে কী শব্দের দিক থেকে কী অর্থের দিক থেকে গীতগোবিন্দ কালিদাসকাব্যের মতো উৎকৃষ্ট হয় নাই। তবে প্রমথ চৌধুরী স্বীকার করেছেন— ‘তিনি শৃঙ্গার রসেরই কবি। কিন্তু যে রসের হউন না কবি তো বটে’। অর্থাৎ শৃঙ্গার রস পরিবেশনে তাঁর নৈপুণ্য স্বীকার্য। তাঁর মতে গীতগোবিন্দের জনপ্রিয়তার কারণ অসংস্কৃতজ্ঞ শ্রোতৃবর্গের বৈষ্ণবভাবে ভাবিত হৃদয় ও কাব্যের শ্রুতিমাধুর্য।
অবশ্য প্রমথ চৌধুরী এ কথাও স্বীকার করেছেন যে তিনি যতদূর বুঝেছেন তাতে গীতগোবিন্দে আধ্যাত্মিকতার কোনো পরিচয় নেই। তাই তিনি বলেন— ‘যদি যথার্থই একটি সুগভীর আধ্যাত্মিক ভাব কাব্যখানির প্রাণস্বরূপ হয় তাহা হইলে আমি উপস্থিত প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা একান্ত অর্থশূন্য।’
কবিবর বুদ্ধদেব বসুও তাঁর অনূদিত মেঘদূতের ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে গীতগোবিন্দের এই পঙক্তিটি প্রকৃত কবিতা হয়ে উঠেছে (যুক্তিবৈমুখ্যের জন্য)। যথা— ‘ত্বমসি মম ভূষণং তৃমসি মম জীবনম ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম।’ (অন্যান্য অংশে তেমন কবিত্ব নেই— এটাই অভিপ্রায়)।
আবার জয়দেবের খুব অনুকূল সমালোচনা করেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন এবং সুশীলকুমার দে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সুশীলকুমার দে বলেন— ‘কেবল শিল্প হিসাবে জয়দেবের কৃতিত্ব এত অসাধারণ যে অনেক সময় তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যকে তাঁহার কবিপ্রতিভার সর্বস্ব বলিয়া ধরা কিছু অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজ কবি কীটস বলিয়াছেন—Poetry must surprise by its fine excess. গীতগোবিন্দে এ কথা খুব খাটে। কবিকল্পনার প্রাচুর্য তো আছেই, কিন্তু fine এই শব্দটির দ্বারা শিল্পীর যে সংযম ও নৈপুণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও গীতগোবিন্দের লিপি কুশলতায় বর্তমান’। তিনি আরো বলেছেন যে— ‘আদি রসের মত মানবহৃদয়ের একটি নিগূঢ়, মধুর ও শক্তিশালী বৃত্তিকে ধর্মসাধনার অঙ্গীভূত করিয়া, অপরূপ দেবলীলাকে সুপরিচিত মানবলীলার যে নির্দিষ্টরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে, তাহা কেবল কৃষ্ণলীলার মাধুর্য পিপাসু ভক্তের আদরের সামগ্রী নয়, কাব্যরসপিপাসু সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী।’
অনুরূপ ভাবে হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্নও বলেছেন— ‘আমাদের মনে হয় জয়দেব কামের আবরণে প্রেমের কথাই বলিয়াছেন।’ শ্রীগীতগোবিন্দ যতবার পাঠ করিয়াছি, জয়দেবের নিত্য নূতন রসচাতুর্যে, ভাবমাধুর্যে ও অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার স্বরাজ্যে আমি দিশাহারা হইয়াছি’ ইত্যাদি।
বোঝা যাচ্ছে যে গীতগোবিন্দের রসাস্বাদনী পর্যালোচনায় মতভেদ রয়েছে। বর্তমান সংকলনে সুকুমারী ভট্টাচার্যের সুলিখিত জয়দেব বিষয়ক প্রবন্ধটিতে নিপুণ বিশ্লেষণে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে প্রথমোক্ত প্রমথ চৌধুরী বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের মতের কিছুটা মিল আছে। তিনিও কবিতা হিসাবে গীতগোবিন্দের ব্যর্থতার স্থানটি দেখিয়েছেন।
মনে হয় জয়দেবের সবচেয়ে ভালো পর্যালোচনা করেছেন জয়দেব নিজেই। তিনি বলেছেন–‘যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ, যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম। মধুর-কোমলকান্ত- পদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম।’ অর্থাৎ যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, যদি বিলাস কলায় কৌতূহল থাকে — তা হলে শোনো জয়দেবের এই মধুর কোমলকান্ত পদাবলীরূপ বাণী। বোঝা গেল এই কাব্যের দুটি দিক আছে— একটি হরিস্মরণের ধর্মীয় সাধনার দিক, আর একটি শৃঙ্গার বিলাসকলার শিল্পনৈপুণ্যের দিক। আর এটা কিন্তু মূলত পদাবলী। (যা পরে বৈষ্ণব পদাবলীতে রূপ পরিগ্রহ করেছে— বস্তুত এখনও কীর্তনের গানে নিজস্ব আঙ্গিকে দু একটি জয়দেবের পদ বা পঙক্তি গাওয়া হয়। আর এই পদগুলি হল কোমল ও কান্ত। আর এর মূল ভাব হল মধুর। মধুর কাকে বলে?’ধ্বন্যালোক’ (২৭)-এ আছে ‘শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ।’ পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ‘মধুর’ শব্দটি একটি পরিভাষায় পরিণত হয়ে গেছে। ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের পার্থক্য স্মরণীয়— এটা অবশ্য পরবর্তীকালের চিন্তার ফল। শৃণু তদা— এইভাবে শুনতে আহ্বান করায় বোঝা যায় কানেরও তুপ্তি ঘটাতে পারে। অর্থাৎ শুনতেও মধুর। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও জয়দেবের বিশেষত্ব আছে। গীতগোবিন্দের মূল বিষয়— মানভঞ্জন। অর্থাৎ বিষয়টিও মধুর। এটির বিশেষত্ব আছে—কারণ কৃষ্ণলীলার অন্যান্য আকর গ্রন্থ যেমন বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এমনকী শ্রীমদ্ভাগবতেও মানভঞ্জন নেই। সেদিক দিয়ে গ্রন্থটি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। বলপ্রয়োগ করে প্রকৃত প্রেম লাভ করা যায় না— এমনকী ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হলেও নয়। তাঁকেও বলতে হয়— দেহি পদপল্লবমুদারম। অনেক দ্বিধার পর জয়দেব এ কথা বুঝেছিলেন ও লিখেছিলেন। তাঁর সেই দ্বিধা নিয়ে নানা কিংবদন্তির সৃষ্টি হয়েছে।
যাইহোক— গীতগোবিন্দের নির্মাণ শৈলী বিচার করলে বলা যায় যে এটি কয়েকটি সর্গে বিভক্ত। এবং অন্যান্য লক্ষণ মিলিয়ে একে সর্গবদ্ধ মহাকাব্য বলা যায়। কিন্তু তা হলে প্রশ্ন ওঠে এর মধ্যে এত গান কেন? কিরাতাৰ্জুনীয় প্রভৃতি মহাকাব্যে তো এমন গান নেই। এইখানে মনে রাখতে হবে যে প্রতিভাধর স্রষ্টা এমন অভিনব সৃষ্টিও করতে পারেন যা আমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণায় লব্ধ নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা যায় না। কবিরা হলেন স্রষ্টা প্রজাপতির মতো নিরঙ্কুশ—যদিও আলংকারিকেরা অনেক সময় কঠোর অনুশাসনে বাঁধার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। গীতগোবিন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তাই ইতস্তত করতে হয়। অভিনব সৃষ্টির এটাই বৈশিষ্ট্য।
গীতগোবিন্দের কথা শেষ করার আগে এর আরএকটা পরিচয় উপেক্ষণীয় নয়। তা হচ্ছে বিষয়বস্তুর গুণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা এটিকে ধর্মগ্রন্থের স্থান দেন। তাঁদের প্রেমভক্তির গভীর তত্ব তাঁরা এর মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। শ্রীচৈতন্যের পাঠ্যতালিকায় এটি সমাদৃত গ্রন্থ। গীতগোবিন্দের শ্লোক নিয়ে রায় রামানন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনা করে তৃপ্তি লাভ করেন।
এখানে মনে হয়— কৃষ্ণলীলাগীতির কোনো প্রাকৃত ধারার সঙ্গে জয়দেবের পরিচিতি ছিল। কেননা প্রাকৃত ও অপভ্রংশে মাত্রাচ্ছন্দ (বা জাতি) ও অন্ত্যমিলের প্রচলন উপলব্ধ। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবিরা মাত্রাচ্ছন্দ বা জাতির চর্চা করতেন— গোবর্ধনের আর্যাসপ্তশতী তার উদাহরণ। জয়দেব দশাবতারের ধারণাটিও সম্ভবত লোকবিশ্বাস বা অন্য কোনো ঐতিহ্য থেকে নিয়েছিলেন। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে অবতারদের সংখ্যা দশ নয়।
৩.
রাত্রি ও অথর্ববেদের প্রার্থনা— এই প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের মন্ত্র অবলম্বনে রচিত। অত্যন্ত প্রাচীনকালেই ভারতীয়দের কবিত্বের আশ্চর্য উন্মেষ ঘটেছিল। ছন্দে, শব্দচয়নে, চিত্রকল্পে ও ভাববাদ্দীপকতায় বেদের অনেক মন্ত্রই তার উদাহরণ। প্রাচীন কবিতাকে যাঁরা আদিমজনোচিত বলে উপেক্ষা করেন, তাঁদের এগুলি পড়া প্রয়োজন। নীচে মূল রাত্রিসূক্তটি পাঠকদের উপহার দেওয়া হল। ঋগ্বেদ (১০/১২৭/১-৮)।
রাত্রী ব্যখ্যায়তী পুরুত্ৰা
দেব্যক্ষভিঃ। বিশ্বা অধি শিয়োহধিত।। ১
ওবপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ।। ২
নিরু স্বসারমস্কৃতোষসংদেব্যায়তী। অপেদু হাসতে তমঃ।। ৩
সা নো অদ্য যস্যা বয়ং নিতে যামনুবিক্ষণহি। বৃক্ষে ন বসতিং বয়ঃ।। ৪
নি গ্রামাসো অবিক্ষত নি পদ্বন্তো নি পক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ।। ৫
যাবয়া বৃক্যংবৃকং যবয় স্তেনমূৰ্ম্যে। অথানঃ সুতা ভব।। ৬
উপ মা পেপিশত্তমঃ কৃষ্ণং ব্যক্তমস্থিত। উষ ঋণেব যাতয়।। ৭
উপ তে গা ই বাকরংবৃণী দুহিতাৰ্দিবঃ। রাত্রি স্তোমং ন জিষে।। ৮
এর অর্থ, ভাব ও তাৎপর্য প্রবন্ধকার খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। নিবিড় উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে সূক্তকারের অভিপ্রেত ভাব।
অথর্ববেদের প্রার্থনা প্রবন্ধে বৈদিক প্রার্থনা মন্ত্রের এক অনাবিষ্কৃত দিক উন্মোচিত হয়েছে। মন্ত্রটিতে কোনো স্কুল কাম্য বস্তুর উল্লেখ নাই। শুধু একটি শুভ ইচ্ছা দ্যোতিত হয়েছে। সেই সঙ্গে একটি আস্থা যে শুভ ইচ্ছা থাকলে আমাদের পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তোলা যেতে পারে— অপ্রেম, হিংসা ও পীড়ন থেকে মুক্ত করে। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর মধ্যে মন্ত্রটি যেন পরম শান্তির শুভেচ্ছা।
৪.
ষষ্ঠী ও প্রেতজগৎ নামে প্রবন্ধ দুটি লৌকিক দেবী ও লোক বিশ্বাস নিয়ে গবেষণারত ব্যক্তিদেরও কাজে লাগতে পারে বলে মনে হয়। এ সমস্ত লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি নিয়ে বিভিন্ন দেশের লোকসংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনাও করেন অনেকে। নৃতত্ববিদেরাও এই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করেন। দেবীভাগবত একটি উপপুরাণ— এটি খুব প্রাচীন বলা যায় না। স্কন্দ পুরাণও অনেকের মতে তা-ই। স্কন্দপুরাণ আকারে প্রকারে বিশাল। আদি মধ্যযুগ বা কিছু উত্তরকালের ধর্মকর্ম ও অন্যান্য ধারণার আলেখ্য এই সব উপপুরাণে বিধৃত। স্কন্দ পুরাণ কি দাক্ষিণাত্যের রচনা। কেননা— ওখানে স্কন্দ কার্তিকের সুব্রহ্মণ্য নামে পূজা হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলে (স্মরণীয়-কামাখ্যা) শক্তিপূজার একটি বিশেষ বিকশিত রূপ লক্ষ করা যায়। দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে দেবীদের মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। অনেক সময় আঞ্চলিক লোকবিশ্বাসে উদ্ভূত কোনো দেবী অজ্ঞতাবশত বা ভক্তির আতিশয্যবশত পরমাশক্তির অংশরূপে বা অভিন্নরূপে পরিগণিত হয়ে গেছে। ষষ্ঠীও তো লৌকিকদেবী, সন্তানলাভ ও আঁতুড়ঘরে শিশু রক্ষার প্রয়োজনে উদ্ভূত, ক্রমে ক্রমে পুরাণাখ্যানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছেন পুরাণকারদের আগ্রহে ও বিশ্বাসে। স্কন্দের ভাষা ষষ্ঠীর গল্পে দেখা যায়— ষষ্ঠী দেবী নিজের পূজার প্রচারের জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং সেটা শর্তসাপেক্ষে। মনে পড়ে যায়—এ যেন মঙ্গলকাব্যের মনসা। বিভিন্ন ধরনের মেয়েলি ব্রতপার্বণ, প্রচলিত ব্রতকথা— এগুলিও লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। আবার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী, মনসা–এরা সবাই একই প্রকৃতির অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতিখণ্ড স্মরণ করা যায়। এই পুরাণে শ্রীমতী রাধাও পরমা প্রকৃতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রয়োজনে ষষ্ঠী অপরিহার্য হলেও দুর্গা বা কালীর মতো এর প্রাধান্য নেই। তবে লৌকিকদেবী রূপে এর গুরুত্ব আছে।
প্রেত জগৎ-এ জগতে–প্রবন্ধটিও লেখনীগুণে উপভোগ্য। ’প্রেতে বিচিকিৎসা’ (দ্র. কঠোপনিষৎ) বৈদিক যুগ বা তার আগে থেকে একবিংশ শতক পর্যন্ত চলে আসছে। ঝাড় ফুক, মন্ত্র, তুকতাক, ভর আসা এসব কাণ্ড এখনও দেখা যায়। অনুসন্ধান করলে অনেক বিচিত্র তথ্য উঠে আসবে। এসবের পক্ষে অথর্ববেদ একটি আকরগ্রন্থ। শুধু প্রেত নয়— ডাকিনী, শাঁখচুন্নি ইত্যাদিরাও লোকবিশ্বাসে সমভাবে বিদ্যমান। শোনা যায়— শাঁখচুন্নিরা পুকুর বা দিঘির জলের ভিতরে বাস করে। খারাপ দৃষ্টি প্রতিরোধ করার জন্যও লোকবিশ্বাসে নানা ব্যবস্থা আছে।
তুলনামূলক ভাষাতত্ব পুরাণতত্বের মতো লোককথার তুলনামূলক পাঠগ্রহণও অনেক অজানা তথ্যের সন্ধান দিতে পারে। বিশেষত অনেক সময় লোকসাহিত্য ছড়া প্রভৃতি অনেক প্রাচীনকাল থেকে চলে আসে। তাই ইতিহাসের অনেক অজানা তথ্যও অজ্ঞাতসারে চলে আসে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতেই ভূতপ্রেত প্রভৃতি সংস্কার-উদ্ভূত ধারণা প্রচলিত।
৫.
গিলগামেশ মহাকাব্যটি সুমেরীয় সভ্যতার অবদান বলা যায় তবে এই মহাকাব্যের যে সর্বাপেক্ষা সুসম্পূর্ণ রূপটি সম্রাট আশুরবানিপালের বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগার থেকে উদ্ধার করা গেছে সেটি আক্কাদীয় ভাষায় কিউনিফর্ম লিপিতে লিখিত। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। (জনৈক বিদ্বান জানাচ্ছেন—The most complete version of the story in the Akkadian language was discovered in the library of king Ashurbanipal (r. 668-627 BC at Nineveh.) পাঠকের স্মরণার্থে বলা যায়— ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজা হামুরাবির আইনলেখ বা Code ও সুমেরীয় ভাষায় লিখিত নয় কিন্তু আক্কাদীয় ও আমোরাইট ভাষায় রচিত (The code is not written in Sumerian, but in the Semitic language of the Akkadians and Amorites. হামুরাবির কাল প্রায় ২১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। (Vide-An outline History of the World by H.A. Davies. p-50.)।
যাই হোক— ঐতিহাসিক এ.কে.এম. শাওনাওয়াজ জানাচ্ছেন যে এশিয়া মহাদেশে প্রাচীনতম সভ্যতাটির বিকাশ হয় মেসোপটেমিয়ায়— এই গ্রীক শব্দটির অর্থ দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি। ভৌগোলিক বিশেষত্বের কারণে জীবন যাত্রার সুবিধা থাকায় এখানে ৫০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নবোপলীয় গ্রাম সংস্কৃতির বিন্যাস ঘটেছিল— অঞ্চলটির নামানুসারে একে ইউবেইদ সংস্কৃতি বলা হয়। এই সংস্কৃতির (স্থানটির) দক্ষিণে আরেকটি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সেটি ওয়ারকা। (Warka) নামক অঞ্চলে ইয়াননা Eanna মন্দির আবিষ্কারের পরে বোঝা যায়। এই ওয়ারকা সংস্কৃতিকে সুমেরীয় ভাষায় ইউরুক (Uruk) ও সেমিটিক ভাষায় ইরেচ (Erech) বলা হয়। এটি হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতার আদি সাক্ষরতার যুগ। ৪০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের শেষদিকে মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল এবং এইভাবে নগররাষ্ট্র উর, ইউরুক, লাগাশ, উম্মা প্রভৃতির উন্মেষ ঘটে। এখানে ইউরুক নগরটি খুব প্রাসঙ্গিক। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দেই ক্রমবিকাশের সূত্র ধরে আদি সাক্ষরতার যুগের অবসান ঘটলে মেসোপটেমিয়রা উন্নততর সভ্যতায় পদার্পণ করে। নদীর জলকে কৃষির প্রয়োজনে ব্যবহার করতে শেখে। খাল খনন, লাঙল কুঠার প্রভৃতির ব্যবহার করতে শেখে। কৃষি ও পশুপালনে (ভেড়া ও ছাগল) দক্ষ হয়। প্রধান ফসল যব। নগরও তৈরি হয়।
প্রতিটি নগরকেন্দ্র ছিল দুর্গবেষ্টিত আর দুর্গের দেওয়াল রোদে শুকানো ইটের দ্বারা তৈরি হত। ইউরুক নগরে ছ মাইল দীর্ঘ দুর্গ ঘেরা একটি অঞ্চল ছিল। কিংবদন্তি অনুসারে বীর রাজা গিলগামেশই সেটি তৈরি করেন। নগরে তোরণ ছিল আর সেনাবাহিনী সেখানে পাহারায় নিযুক্ত থাকত। রথ ও ফসলের গাড়ি চলার জন্য বড়ো বড়ো রাস্তাও করা হত। ধর্মবিশ্বাস বশত পাহাড় সদৃশ, সিঁড়ির ধাপ কেটে তৈরি, মন্দিরকে বলা হত জিগুরাত (Ziggurat)। গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে উরুক বা ইউরুক ছিল গিলগামেশের রাজধানী। জনৈক বিদ্বান বলেছেন— ‘In the third millennium BC the city (Uruk) was surrounded by a wall c.6 mi (10km) long, later said to have been constructed by the legendary Gilgamesh, leader of a rebellion against kish.’ তিনি উরুকে প্রায় ছ মাইল দীর্ঘ একটি প্রাচীর তৈরি করিয়েছিলেন এবং kish এর Agga-এর বিরোধিতা করেছিলেন। এই প্রকার কিংবদন্তি আছে। কিন্তু এর মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য নিহিত তা বলা শক্ত। গল্পটিতে বলা হয়েছে— ‘এই শহর তাঁর নিজের রাজধানী। সেখানে ফিরে তিনি উর্সানাবিকে বললেন প্রাচীরের ওপরে উঠে শহরটার সমৃদ্ধি ভালো করে দেখতে।’ এখানেও প্রাচীরের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। (বর্তমান সংকলনে দেখুন।
ঐতিহাসিক শাওনাওয়াজ গিলগামেশ মহাকাব্যকে সুমেরীয় সাহিত্যকীর্তি হিসেবেই উল্লেখ করেছেন। (পৃ. ৮৫)। তাঁর মতে এই পুরাকথা নির্ভর সাহিত্যের কাহিনিগুলো প্রাচীন রাজাদের সাথে দেবতাদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠত এবং তা সুমেরীয় ধর্মের অনুষঙ্গী ছিল। এর মধ্যে বিখ্যাত ছিল জলপ্লাবনের কাহিনি। যেটি পরবর্তীকালে হিব্রু ভাষায় বাইবেলে ওল্ড টেস্টামেন্টে স্থান পেয়েছে। গিলগামেশ মহাকাব্যেও এই জলপ্লাবনের কথাপ্রসঙ্গটি আছে। জলপ্লাবনের এই কাহিনি সম্পর্কে Marian Edwardes ও Lewis Spence বলেছেন— (p.66) Flood-. There are two Babylonian accounts extant, one from Berosus and the other in the Gilgamesh epic… In the epic the flood is said to be sent by the gods on account of the sinfulness of the people of Suruppak. Ea warns Utnapishtim (or Sit-napishtim) and directs him to build a ship. নোয়াকে যেমন জলপ্লাবনে রক্ষা পাবার জন্য একটি নৌকা তৈরি করতে বলা হয়েছিল— এখানেও দেখা যাচ্ছে এয়া (Ea) উতনাপিশতিমকে সেইরূপ নৌকা তৈরি করতে বলছেন। ঝড়, বজ্রপাত ও জলপ্লাবনের এক ভয়ংকর বর্ণনা রয়েছে। উতনাপিশতিম অবশ্য রক্ষা পেলেন নৌকার মধ্যে থেকে এবং তাঁর পরিবার ও অন্যান্য যাদের তিনি নৌকার মধ্যে নিয়েছিলেন তাঁরাও রক্ষা পেলেন। সাতদিন ধরে সেই বন্যার দুর্যোগ বজায় রইল। পরে উতনাপিশতিম তিনটি পাখি পাঠালেন—শেষেরটি ফিরে এল না। উতনাপিশতিম ও তাঁর স্ত্রীকে দেবত্ব প্রদান করা হল। এবং তাঁদের সপরিবারে বহুদূরে নদীমুখে এক জায়গায় পাঠানো হল।
বর্তমান সংকলনের গল্পটিতেও দেখা যাচ্ছে দেবতার কৃপাধন্য দূরের মানুষ উতনাপিশতিমের কাছেই গিলগামেশ অমৃতত্ব লাভের উপায় খুঁজতে চলেছেন। কারণ তাঁর যে বাসনা অমরত্বলাভ করা তা এইখানে সম্ভব হবে, উতনাপিশতিম তাঁকে সেই অমোঘ নির্দেশ দেবেন, যে পথে তিনি অমৃতত্ব লাভ করবেন।’ জলপ্লাবনেও দেবতার নির্দেশ পালনে রক্ষাপ্রাপ্ত দিব্যক্ষমতাপ্রাপ্ত উতনাপিশতিমের উপর গভীর আস্থা ব্যক্ত হয়েছে। কেননা তিনি অমরত্বলাভের উপায় বলে দিতে পারেন। তাই গিলগামেশ দিনের পর দিন, সুদীর্ঘকাল ধরে বিপুল অকূল নদীর ওপরে নৌকা বেয়ে চলেছিলেন উর্সানাবির সঙ্গে উতনাপিশতিমের উদ্দেশে। এ যেন মৃত স্বামীকে বাঁচাবার জন্য কলার ভেলায় নদীপথে সতী বেহুলার যাত্রা দেবী মনসার উদ্দেশে। সঙ্গে স্বামীর মৃতদেহ। তবে বেহুলা ছিলেন একাকিনী, শুধু স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে।
এখন আক্কাদীয় ভাষা ও কিউনিফর্ম লিপি সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। H.A Davies 1699- The earliest people to found cities in Mesopotamia were the Sumerians, a mysterious race, neither Aryan nor Semite, probably dark white in complexsion. They used a kind of writing which they scratched with a reed pen upon soft clay, which became very hard when exposed to sunlight. Their first writing was picture writing; then at a very early date, it became phonetic. Sumerian writing finally possessed over three hundred and fifty signs; each sign representing a syllable. It was never alphabetic… Owing to the curious wedge-shaped character of this writing it is called cuneiform (Latin cuneus = a wedge). (page 47) Capital PTT67 বা পার্চমেন্টের ব্যবহার (লেখার ক্ষেত্রে) জানত না। Their books and memoranda, even their letters, were pot-sherds. (H.G. wells). Olet po has talo olist লিখতেন— cuneus অর্থাৎ কীলকের আকারের লিপি। কীলকাকার লিপি। Cuneiform অর্থাৎ wedge-shaped বা কীলকাকার লিপি। সুমেরীয়গণ কাদামাটির স্লেটে খাগের কলম (Reed pen) দিয়ে কৌণিকরেখা ফুটিয়ে তুলে লিখতেন। এই লিপির প্রধান গুণ হচ্ছে এটি কাদামাটির জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। তবে কাদামাটি ছাড়া অন্য কিছু উপকরণেও সুকৌশলে কিউনিফর্ম লিপি খোদিত করা হয়েছে। যেমন পাথরে স্তম্ভশিলা অথবা ওজনদণ্ডের উপর। পুরাতন সুমের বা ব্যাবিলন ছাড়াও এলামাইট, হিট্টাইট, হুরিয়ান ফিনিশিয়া ইত্যাদি অঞ্চলেও এই লিপির ব্যবহার চালু হয়। আক্কাদীয়রা আগেই সুমেরীয়দের কাছ থেকে এই কিউনিফর্ম লিখন প্রণালী গ্রহণ করে। তাই আক্কাদীয় ভাষাও কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা হয়েছে।
2750 BC তে সুমেরীয় রাজত্ব শেষ হয়। সুমেরিয়া তখন দখল করে সেমিটিক ভাষাভাষী আক্কাদীয়রা। এদের ভাষা সেমিটিক, অর্থাৎ এ ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ভাষাটি মেসোপটেমিয়ায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দেও ব্যবহৃত হত। সুমেরীয়দিকে পরাজিত করার পর আক্কাদীয়রা সুমেরীয়দের ভাষার স্থানে নিজেদের ভাষাকে প্রাধান্য দেয়। এই আক্কাদীয় ভাষার নমুনা বিভিন্ন শিলালেখ, সিল ও কাদামাটির ফলকে পাওয়া যায় কিউনিফর্ম লিপিতে— যা আক্কাদীয়রা সুমেরীয়দের কাছ থেকে শিখেছিল। 2000BC থেকেই আক্কাদীয় ভাষাটি দুটি উপভাষায় বিভক্ত হয়ে যায়—অ্যাসিরীয় ও ব্যাবিলনীয়। এই ব্যাবিলনীয় আক্কাদীয় উপভাষাটিই কালক্রমে প্রাধান্য লাভ করে এবং প্রায় Lingua Franca-তে পরিণত হয়। মনে হয় এই কারণে কেউ কেউ Akkadian Language কে Assyro-Babylonian ভাষা বলেছেন। — পরে আক্কাদীয় ভাষার প্রভাব কমতে থাকে। এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধেই অ্যারামাইক ভাষাই এই আক্কাদীয় ভাষার স্থানটি গ্রহণ করে। (এখানে স্মরণ করা যায় যে এই অ্যারামাইক ভাষাটিই হচ্ছে বিশ্বখ্যাত যিশুখ্রিস্টের মাতৃভাষা বা কথ্য ভাষা। তখন প্যালেস্টাইনে অ্যারামাইক ভাষা হিব্রুরও স্থলাভিষিক্ত হয়ে উঠেছিল।)
যাই হোক, মনে হয়, স্থায়িতৃবৃদ্ধির জন্যই কিউনিফর্ম লিপি প্রস্তরফলকেও খোদাই করা হত। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক কাদামাটির ফলক বা clay tablet এর কথাই বেশি বলেছেন। (দ্র. বিশ্বসভ্যতা-এ.কে.এম শাহনাওয়াজ— সুমেরের বিখ্যাত শহর নিপ্পুরে খনন কার্যের ফলে একটি পুরানো মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পঞ্চাশ হাজার মাটির চাকতি পাওয়া গেছে ইত্যাদি)।
প্রায় ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ সুসভ্য অরামীয়গণ ফিনিসীয়দের কাছে বর্ণমালা গ্রহণ করেছিল। এদের প্রধান নগর দামাস্কাস। এরা মিশরীয়দের মতোই লিখনের উপকরণ ব্যবহার করতে শিখেছিল। They used papyrus, the reed-stylus, and ink like the Egyptians. অ্যাসিরীয় রাজত্বের সময় দুরকম লিখন পদ্ধতিই চলত! Assyrian tablets have been found with marginal notes in Aramaic, and it was a common thing in the Assyrian Empire to find Aramean and Assyrian clerks in Government offices; the former keeping their records by writing with pen and ink on a roll of papyrus, the latter by writing cuneiform characters on tablets of clay (vide An outline History of the World H.A. Davies. p. 55)
গিলগামেশ ছিলেন বীর যোদ্ধা শিকারি। কোনো কোনো বিদ্বান তাঁকে বাইবেলের আদিপুস্তকের (Gen. 10:8-9) নিমরোদের সঙ্গে অভিন্নরূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। (দ্র. A Dictionary of non-classical Mythology p. 76)। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের আদিপুস্তকের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে— (১০:৮) নিম্রোদ কুশের পুত্র; তিনি পৃথিবীতে পরাক্রমী হইতে লাগিলেন। তিনি সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ হইলেন। তজ্জন্য লোকে বলে, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে পরাক্রান্ত ব্যাধ নিম্রোদের তুল্য।’ অর্থাৎ বীর হিসাবে এঁর খ্যাতি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। এ সমস্তই অবশ্য গবেষণার বিষয়।
মনে হয় গিলগামেশ মহাকাব্যের আখ্যানভাগ লোকমুখেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং পরবর্তীকালকে প্রভাবিত করেছিল। শাহনাওয়াজ বলেন— ‘খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অব্দে হিব্রাইট ও ক্যাসাইটদের দ্বারা ব্যাবিলনের পতন ঘটলে এ সমস্ত সভ্যতা কিউনিফর্ম লিপি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে; তারা গিলগামেশের মহাকাব্য দ্বারা প্রভাবিত হয়।’ ‘হিব্রু ধর্মের বন্যার কাহিনী মেসোপটেমীয় কিংবদন্তী থেকেই এসেছে’ (পৃ. ৯৮)।
বর্তমান সংকলনে উপস্থাপিত গিলগামেশের আখ্যানভাগে যে দেবী ইশতারের কথা আছে— সেমিটিক জনগণের কাছে তিনি নানা নামে পরিচিত হলেও ব্যাবিলনীয় ও অ্যাসিরীয়দের কাছে ইশতার নামেই বিখ্যাত। তাঁকে স্বর্গের রানিও বলা হয়েছে। এই দেবী দুটি বিভিন্ন রূপে পরিচিত। —মাতৃদেবী ও প্রেমের দেবী। প্রেমের দেবীরূপে ইনি গ্রীকদের আফ্রোদিতে এবং রোমানদের ভেনাসের সঙ্গে তুলনীয়। এর প্রাচীনতম মন্দিরটি উরুকেই পাওয়া যায়। প্রেমের দেবীরূপে কামনার উন্মাদনা এর বৈশিষ্ট্য। আখ্যানভাগেও তা প্রকাশিত।
বর্তমান প্রবন্ধ সংকলনে ‘গিলগামেশ— অমরত্বের সন্ধান’ প্রবন্ধে লেখিকা অত্যন্ত মনোজ্ঞভাবে গিলগামেশের আখ্যানভাগ পরিবেশন করেছেন সংক্ষিপ্তরূপে এবং তৎসংক্রান্ত কিছু কথা জানিয়েছেন বাঙালি পাঠকদের জন্য। বাংলা ভাষায় গিলগামেশের কথা খুব বেশি আলোচিত হয়নি। যতদূর মনে পড়ে মাননীয় পরমেশ চৌধুরীর একটি বই আছে। এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও তাঁর ‘প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য’-এ কিছু আলোচনা করেছেন। তাই এ সম্বন্ধে আরও আলোচনার প্রয়োজন। বর্তমান প্রবন্ধটি সেই চাহিদা কিছুটা পূরণ করতে পারে। গিলগামেশের মুখ্য ভাবটি চিরন্তনতায় প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অমরত্বলাভের ইচ্ছা। বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথও তো চিরন্তন ইচ্ছাকে কবিতায় রূপ দিয়ে বলেছেন— ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।’ যোগশাস্ত্রেও আছে— এই অভিনিবেশ আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্বভূতে নিহিত।’ শব্দান্তরে একে বলা হয় মরণত্রাস। গিলগামেশ বহু যুদ্ধে জয়ী প্রচণ্ড বীর যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু তিনিও একদিন বুঝলেন যে তাঁর বন্ধু এনকিডুর মতো তাঁকেও একদিন এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে— তাঁর প্রচণ্ড বিক্রমও তাঁকে বাঁচাতে পারবে না। এই নির্মম অথচ সমস্ত মানুষের কাছে চিরন্তন সত্যের প্রকাশ গিলগামেশকে সাহিত্যের ধ্রুবপদে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
বলা বাহুল্য গিলগামেশ মহাকাব্যের ঘটনাক্রম বহু শাখাপ্রশাখায় প্রলম্বিত। এর মধ্যে তদানীন্তন সংস্কৃতির আরও নানা কথা স্থান পেয়েছে—যা সুদীর্ঘ আলোচনার বিষয়। যেমন কেউ কেউ বলেন— The epic ends with the return of the spirit of Enkidu, who gives a dismal_report on the underworld. ব্যাবিলনীয় পুরাকথার এই পাতালরাজ্যকে বলা হয় অরলু (Aralu).
মানুষের অমৃতত্বলাভের ইচ্ছা আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে ও শাস্ত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। তবে নানা ধারণার বৈচিত্র্যও আছে। গিলগামেশের মতো একটি সুপ্রাচীন ও বিদেশি মহাকাব্য— যা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনাযোগ্য— তা অবলম্বন করে জটিল ঘটনাক্রমকে অত্যন্ত সহজ সরল মনোজ্ঞ ভাষায় অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে, এবং মহাকাব্যের মূল তাৎপর্যগত ভাবটি বজায় রেখে বাঙালি পাঠকদের জন্য উপস্থাপিত করা—মনে হয়— শ্রদ্ধেয়া সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।
৬.
দেবতার প্রতারণা— প্রবন্ধে তুলনামূলক পুরাণকথাতত্ব (comparative mythology) বিশ্লেষণের সাহায্যে হারিয়ে-যাওয়া ঐতিহাসিক সত্যের পুনরাবিষ্কারের প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বলি ও বামনের কাহিনি পুরাণে সুপ্রসিদ্ধ (বিশেষত বামন পুরাণে)। বিষ্ণুর বিক্রমনের উল্লেখ যর্জুবেদেও আছে এবং এটি আর্য অভিক্রমণ সূচিত করে— এ কথা বলেছেন স্বর্গত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তুলনামূলক ভাষাতত্বের মতো তুলনামূলক পুরাণকথাতত্ব থেকেও ইতিহাসের অনেক অস্পষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা যেতে পারে এবং অবশ্যই সেক্ষেত্রে নিজের গণ্ডিবদ্ধ সংকীর্ণ বিষয় ছাড়িয়ে অন্যান্য সংস্কৃতিরও পরিজ্ঞান প্রয়োজন। লেখাটিতে সেই কৃতিত্বের স্বাক্ষর আছে — তাই এটির উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য। সৌধ নির্মাণ কার্যে ময়দানবের দক্ষতা আমাদের মনে করায় যে হয়তো অনার্য দানবেরাই এই সমস্ত নির্মাণ কর্মে বেশি নিপুণ ছিল। যাঁরা মনে করেন সিন্ধু সভ্যতার নগর সৌধপরিকল্পনা অনার্যদের অবদান, আর্যদের নয়, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি তাদের সপক্ষেই যাবে।
দেবতাদের ছলনা প্রবন্ধে নানা দেবতার চরিত্র ও চরিতাবলী কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়েছে। পুরাণাদিতে চিত্রিত দেবতারা যেন রিপুতাড়িত রক্তমাংসের মানুষের মতোই। মাঝে মাঝে মনে হয় তার চেয়েও খারাপ— যেমন ব্রহ্মা নিজের কন্যার প্রতি আসক্ত হন। বস্তুত পুরাণে কামতত্ব সম্পর্কে কিছু কিছু কথাবার্তা আছে যা ফ্রয়েডের তত্বকে মনে পড়িয়ে দেয়। যাই হোক শুধু হিন্দুদের দেবতারাই এমন ছিলেন তা বলা যায় না। গ্রীকদের দেবতারাও একটি বিচার্য বিষয় হতে পারে।
।তবে গীতা সম্পর্কে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বহু মনীষীই এ নিয়ে বড়ো বড়ো দার্শনিক গ্রন্থ লিখেছেন। সেগুলির যুক্তি সমূহও বিচারের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।
প্রবন্ধটিতে একটি প্রণিধানযোগ্য তথ্য হল দেবীরা কেউ তেমনভাবে ছলনা করেননি পুরাণে ও মহাকাব্যে। তবে বিশ্বরূপ প্রদর্শন যদি জাদুবিদ্যা তথা ছলনা হয় তবে দেবী ভাগবতে দেবী তা করেছেন। দেবীগীতায় বিশ্বরূপপ্রদর্শন আছে। (হিমালয়কে ও দেববৃন্দকে দেবী বিরাট রূপ দেখান)।
৭.
মায়াতির লক্ষণ সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডের ৬৪তম অধ্যায়ে কিছু কথা বলা আছে। (পঞ্চানন তর্করত্নের সম্পাদিত সংস্করণে)। যথা— মায়াতীনাঞ্চনির্ণীতং শ্ৰয়তাং মুনিসত্তম। বক্ষ্যাম্যথর্ববেদোক্তং ফলহানি ব্যতিক্রমে। ১০০ পিতৃমাতৃবিহীনঞ্চ যুবকং ব্যাধিহীনকম। বিবাহিতং দীক্ষিতঞ্চ পরদারবিহীনকম।। ১০১ অজরাকং বিশুদ্ধঞ্চ সহ্দ্রং মূলকং বরম। তদ্বন্ধুভ্যো ধনং দত্বা ক্রীতং মূল্যাতিরেকতঃ।। স্নাপয়িত্বা চ তং ধর্মী সম্পূজ্য বস্ত্ৰচন্দনৈঃ। মাল্যৈ ধূপৈশ্চ সিন্দুরৈর্দধিগোরোচনাদিভিঃ। তঞ্চবর্ষং ভ্রাময়িত্বা চরদ্বারেণ যত্নতঃ। বর্ষান্তে চ সমুৎসাৰ্য্য দুর্গায়ৈ তং নিবেদয়েৎ।। অর্থাৎ ‘হে মুনিবর! অথর্ববেদে নরবলি যেরূপ কথিত আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ফলহানি হয়। পিতৃমাতৃহীন, যুবা, নীরোগ, বিবাহিত, দীক্ষিত, পরস্ত্রীপরাঙমুখ, অজারজাত, বিশুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, আত্মীয়দিকে ধন দিয়া অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত, সৎশূদ্রকে ধার্মিক ব্যক্তি স্নান করাইয়া বস্ত্র, চন্দন মাল্য ধূপ সিন্দুর দধি গোরোচনা প্রভৃতি দ্রব্যের দ্বারা পূজা করিয়া স্বচার (চক্র) দ্বারা সংবৎসর তাহাকে ভ্রমণ করাইয়া, বর্ষান্তে উৎসর্গ করিয়া, দেবী দুর্গাকে নিবেদন করিবে। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে ওই নরকে বলি দিবে।’
এখানে এ কথাও বলা হয়েছে যে দেবী দুর্গা নরবলিদানে সহস্রবৎসর— দাতার প্রতি প্রসন্না। থাকেন। ’মায়াতিং মহিষং ছাগং দদ্যান্মেষাদিকং শুভম।’ ‘সহস্ৰবৰ্ষং সুপ্রীতা দুর্গা মায়াতিদানতঃ।’ দেখা যাচ্ছে মায়াতি, মহিষ ও ছাগ বলি দেওয়ার বিধি রয়েছে। তবে মায়াতি বলি দিলে সহস্র বর্ষ প্রসন্ন থাকেন দেবী। অপর পক্ষে মহিষ বলিদানে একশতবৎসর ও ছাগ বলিদানে দশবর্ষ প্রসন্না থাকেন। দেবীর প্রসন্নতার কালব্যাপ্তির বিচারে নরবলির গুরুত্ব বেশি তা বোঝা যাচ্ছে। ধর্মের নামে এই সব অমানবিক প্রথা চলত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য। অজ্ঞ জনসাধারণ এইসব মেনে নিত কারণ প্রকৃত ধর্ম সম্বন্ধে অনেকেরই কোনো ধারণা থাকত না। ধর্ম বলতে যখন কিছু যুক্তিহীন আচার অনুষ্ঠান বোঝানো হয় তখন এই সব নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত হয়—আর পরলোকে বা ইহলোকে অলৌকিক ভাবে কিছু প্রাপ্তির প্রলোভনও থাকত এর পিছনে। পুরাণে এবং কিছু কিছু তন্ত্রে (দ্র. যোগিনীহৃদয়) এ ধরনের প্রথার ইঙ্গিত আছে। পুরাণের মধ্যে নানা সামাজিক রীতিনীতির ও অবক্ষয়ের চিত্র ভালোভাবেই ধরা পড়েছে— যার আরও অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান অপেক্ষিত।
বর্তমান সংকলনে প্রবন্ধকারের নিপুণ বিশ্লেষণে তদানীন্তন সমাজের এই অমানবিক দিকটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
৮.
রবীন্দ্রনাথের নারীর ভাগ্যজয় ও বেদের যুগে স্ত্রীশিক্ষা— এই প্রবন্ধ দুটি পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর পরতন্ত্র অবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। —’ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি’— এই শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠ ধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন যে নারী আপন ভাগ্য জয়। করার অধিকার পায়নি। কিন্তু বিধাতার পক্ষে সেই অধিকার নারীকে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বিধাতা কেন? বিধাতা কি নারীকে সেই অধিকার দিতে এগিয়ে আসবেন? এই প্রশ্ন তুলেছেন প্রবন্ধকার। রবীন্দ্রসাহিত্যের চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের কথা চিন্তা করলে বোঝা যায় চিত্রাঙ্গদার উক্তিতে প্রকাশিত হয়েছে নারীর অন্তরের কথা। অন্তত রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ভেবেছেন। বোঝা যায়–নারী দেবীও নয়, আবার দাসীও নয়। সে ঊর্ধ্বেও উঠতে চায় না, আবার পিছনেও পড়ে থাকতে চায় না। সে হতে চায় পুরুষের পার্শ্ববর্তিনী— যদি পুরুষ তাকে সেই স্থান দিতে চায়। কিন্তু এখানে আবার ‘যদি’ কেন? নারীকে তো নিজে থেকেই সেই স্থান— সেই অধিকার জয় করে নিতে হবে। অন্যের উপর নির্ভর করে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করা যায় না। কারণ তখন সেটা আর স্বাতন্ত্র থাকে না— অন্য নির্ভরতা হয়ে যায়। কাজেই বিধাতার প্রসাদে বা পুরুষের দয়ায় নয় কিন্তু নিজের চেষ্টাতে নিজের সাধনায় নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এটাই সিদ্ধান্ত। কিন্তু সাহিত্যে সাধারণত নারীকে ভোগ্যবস্তুরূপে চিত্রিত করা হয় কিংবা রসশাস্ত্র অনুসারে বলা যায় শৃঙ্গাররসের আলম্বন বিভাবরূপে কিন্তু সেই রসসৃষ্টির আড়ালে নারীর ভোগ্য-হয়ে-ওঠা চেহারাটাই প্রাধান্য পায়। বিশ্বকবি মনীষী রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় তা চাননি। তাঁর সাহিত্যে বা গল্পে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে নিজের চেষ্টায় নারীর আপন ভাগ্য জয় করার অনেক কাহিনি আছে। কিন্তু তার জন্য রবীন্দ্রনাথকে তো কল্পনার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বাস্তবে সেই নারীরা। কোথায়? হয়তো খুব কম বলেই চট করে চোখে পড়ে না।
মানবলোকে অর্ধেক পৃথিবী হওয়া সত্বেও নারী তার প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি পুরুষপ্রধান সমাজে। বেদের যুগে স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গেও সেই কথাটাই বলা যায়। সেই যুগেও স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোনো ঢালাও ব্যবস্থা বা ব্যাপক পরিকর ছিল না। তবু দু-একজন মহিলা ব্যতিক্রম ছিলেন। তাঁরা নিজের চেষ্টায় আপন ভাগ্য জয় করেছিলেন। যদিও বলা হয়েছে ‘ভক্তৃণ্ডশ্রষণং স্ত্রীণামগ্নিহোত্রনিষেবনম।’ অর্থাৎ স্বামীর সেবা করাটাই হল মেয়েদের পক্ষে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। তবু ইতিহাসে দেখা যায় অনেক মহিলা বিদুষী হয়ে উঠেছিলেন— তা হয়তো পুরুষেরই সহযোগিতায়। তা ছাড়া হয়তো নানা কারণে সব নারীরা গাৰ্হস্থজীবনে প্রবেশের সুযোগ পেতেন। না। কারণ আজ পর্যন্ত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিবাহের বিজ্ঞাপনে শারীরিক সৌন্দর্যই প্রধান বিবেচ্য হয়ে ওঠে। অতএব রূপহীনা বা শারীরিক ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় যাদের বিয়ে হত না— পুরুষের করুণায় হয়তো বিদ্যাচর্চা তাদের একটা বড়ো অবলম্বন ছিল। এটাই লেখিকার অনুমান। গোধা, সার্পরাজ্ঞী, রাত্রি প্রভৃতি নাম হয়তো তাঁদের চেহারাগত বিশেষত্বেরই সূচক।
আজকাল সাহিত্য পর্যালোচনার রাজ্যে— হয়তো প্রয়োজনের তাগিদে নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনা অভিধায় একটি অভিনব ধারা যুক্ত হচ্ছে বা প্রাধান্যলাভ করেছে। বেশ কিছু সাহিত্য বিশ্লেষণমূলক ইংরাজি গ্রন্থে এটি স্পষ্ট লক্ষ করা গেছে। যাঁরা এই ধারায় আগ্রহী আলোচ্য প্রবন্ধদুটি তাঁদের বিশেষ করে উপযোগী হবে— একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে এটাই আশা করা যায়।
৯.
সমার্থক যুগ্মশব্দ প্রবন্ধটি নাম থেকেই বোঝা যায়— শব্দতত্ব বা ভাষাতত্বের অন্তর্গত। ভাষার বিশ্লেষণ করেও অনেক ক্ষেত্রে অতীত কালের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের নানা দিক উপলব্ধি করা যায়। যেমন ভাষাতাত্বিকেরা বলেন পূজা শব্দটি তামিল থেকে এসেছে সংস্কৃতে। পাণিনির সূত্রে এর ব্যবহারও আছে। (সুঃ পূজায়াম—১/৪/৯৪)। একই অর্থে দুটি ভাষার দুটি শব্দ একসঙ্গে প্রয়োগ করার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে দুটি পৃথক ভাষাভাষীর পরস্পরের বোধগম্য হওয়া। দুজন পৃথক ভাষাভাষী এইভাবে একে অন্যের প্রযুক্ত শব্দটির অর্থ বুঝতে পারে। একাধিক ভিন্নভাষাভাষীদের সম্মেলন-সমৃদ্ধ অঞ্চলেও এই প্রকার বাস্তব প্রয়োজন অনুভূত হতে পারে। ফলে ওই যুগ্মশব্দের পরিচিন্তনে বোঝা যায় সেই যোগাযোগের ইতিহাসটা। ভারতবর্ষে নানা সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে। তার স্বরূপ বুঝতে গেলে ভাষাতত্বের এইসব দিকগুলি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। নানা সংস্কৃতির সঙ্গে নানা ভাষার একত্র ব্যবহারও প্রয়োজনানুসারে ঘটে গেছে। শব্দগুলি যেন জীবাশ্মের মতো কালপ্রবাহে হারিয়ে যাওয়া তথ্যের প্রমাণবাহী। আলোচ্য প্রবন্ধের একটি আকর্ষণীয় দিক হল— ইতিহাস সমর্থিত যুগানুক্রমিক আলোচনা। প্রথমে— আর্য প্রাগার্য (যেমন-বনজঙ্গল)। তারপর মধ্যযুগের মুসলমানি আমল বা তার প্রভাবে তৈরি যুগ্ম শব্দ (যেমন বিয়েশাদি)। এরপর আধুনিক যুগের ইংরেজ আমল। অর্থাৎ একই অর্থে ইংরাজি ও ভারতীয় শব্দ দুটির একত্র প্রয়োগ (যেমন— ডাক্তারবদ্যি)। এইভাবে শব্দবিশ্লেষণের মাধ্যমে অনেক অজানা ইতিহাসও অনুমান করা যায়।
১০.
বুদ্ধের জীবন থেকে প্রবন্ধে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানব গৌতমবুদ্ধের জীবনালেখ্য মনোজ্ঞ ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে। তৎকাল প্রচলিত ধর্মের অনেক ক্রিয়াকাণ্ড, পশুবধ ও অন্যান্য চিন্তাধারা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তার মধ্যে শুভ কিছু দেখতে পাননি। দেখা যাচ্ছে আমাদের ধর্ম সংস্কারের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই খ্রিস্টপূর্বাব্দেই। এমনকী পালি নিকায়ে দেখা যায় জন্মানুসারে বর্ণবিভেদের সারবত্তাও তিনি খুঁজে পাননি— যে চিন্তাধারার প্রভাব কিছুটা ধরা আছে পরবর্তীকালে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ ‘শার্দুলকর্ণাবদান’-এ। (যার কিছু আখ্যানাংশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা রচিত হয়েছে)। অশ্ব ঘোষের বুদ্ধচরিত অনুসরণ করলে বলা যায়— আড়ার কালামের তথা সাংখ্য ও উপনিষদের আত্মবাদের মধ্যেও তিনি আত্মমোহ ও স্বার্থকেন্দ্রিকতার বীজ উপলব্ধি করেছেন। কাজেই ‘আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া’ ঘুরে মরতে তিনি রাজি ছিলেন না। অহংসর্বস্বতা ত্যাগ করে পরার্থে জীবন ব্যয় করেছিলেন। তিনি শিষ্যদের এ কথাও বলেছিলেন যে তাঁর কথা যেন যুক্তি দিয়ে পরীক্ষা করে তবেই গ্রহণ করা হয়। তিনি ছিলেন এমনই বাস্তব যুক্তিবাদী। দার্শনিক কূটতর্ক তিনি এড়িয়ে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন— সে সব প্রশ্নের সর্বাদিসম্মত সমাধান দুষ্কর। তার চেয়ে বাস্তব জগতে দুঃখ দূর করার প্রচেষ্টাই মানবসমাজের পক্ষে বেশি কল্যাণবহ। পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণভাবে বাসযোগ্য করে তুলতে হলে চাই—মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষাবুদ্ধির অনুশীলন। আর সেই লক্ষ্যে প্রকৃত জ্ঞান হল চতুরার্যসত্যের উপলব্ধি। বৌদ্ধ সাধনার এটাই সোপান। তার জন্য অনুসরণ করতে হয় অষ্টাঙ্গিক মার্গ। মানুষের শ্রেয়েলাভের জন্য কঠোর তপশ্চর্যা বা আত্মপীড়ন —দৈহিক নিপীড়ন প্রয়োজন নয়— যা অনেক ধর্মসাধকেরা করে থাকেন—আবার পশুর মতো শুধু ইন্দ্রিয়ের তাগিদে যথেচ্ছ কামসুখে ভেসে যাওয়া কোনোটাই প্রকৃত জীবনের সঠিক পথ নয়। কিন্তু এর মধ্যবর্তী পন্থাই গ্রহণীয়। এই মধ্যম পন্থাকে পালির ভাষায় বলা হয় মজঝিমা পটিপদা। বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে বুদ্ধ এই সত্য পঞ্চবঙ্গীয় ভিক্ষুদের বুঝিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায় বলা যায়—
‘দ্বেমে, ভিকখবে, অন্তা পব্বজিতেন ন সেবিতা। কতমে দ্বে? যো চায়ং কামেসু কামসুখল্লিকানুযোগো হীনো গম্মো পোথুজ্জনিকো অরিয়ো অনতথসংহিতো, যো চায়ং অত্তকিলমথানুযোগো দুখো অনরিয়ো অনতথসংহিতো। এতে খো, ভিকখবে, উতভা অন্তে অনুপগম্ম মজঝিমা পটিপদা তথাগতেন অভিসমবুদ্ধা চকখুকরণী ঞাণকরণী উপসমায় অভিঞঞায় সম্বোধায় নিব্বানায় সংবত্ততি।’
অর্থাৎ হেভিক্ষুগণ— এই দুটি অন্ত প্রব্রজিতের পক্ষে গ্রহণীয় নয়। কোন দুটি অন্ত? এই যে কাম্যসমূহের মধ্যে কাম সুখের আসক্তি (যা অত্যন্ত) হীন, গ্রাম্য, ইতরজনোচিত অনার্য এবং অনর্থসংযুক্ত। (আর দ্বিতীয়টি) আর এই যে আত্মপীড়নে আসক্তি (যেটাও কিন্তু দুঃখকর অনার্য এবং অনর্থসংযুক্ত। হে ভিক্ষুগণ, এই দুটি অন্ত পরিহার করে তথাগতের অভিসম্বুদ্ধ মধ্যম পন্থা— যা চক্ষুদায়িনী জ্ঞানদায়িনী উপশম অভিজ্ঞা সম্বোধ ও নির্বাণের জন্য বিদ্যমান।
প্রসঙ্গত বলা যায় বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ, বিশ্ববিশ্রুত, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা বুদ্ধের প্রতি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ছিলেন।
১১.
মূলত মহাভারত অবলম্বনে চারটি প্রবন্ধ রয়েছে। (১) দ্রৌপদী (২) শান্তিপর্ব (৩) মানুষ বাঁচে কেন? এবং (৪) কুন্তী গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র। অর্জুনকেই দ্রৌপদী সবচেয়ে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলেন এবং কামনা করেছিলেন একাধিপত্য। এদিকে পরিস্থিতির প্রভাবে তাঁকে নীরবে পঞ্চস্বামীকে সমভাবে মেনে নিতে হয়েছিল। তবে সেটা বাইরের সাংসারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। পঞ্চস্বামীকেই নিবিড় সাহচর্যের অধিকার দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ অর্জুনই ছিলেন তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত প্রেমের অধীশ্বর। তাঁর অন্তরের এই বেদনাময় দিকটি কিন্তু তিনি কখনো কাউকে বুঝতে দেননি। ফলে তাঁর অন্তরের দুঃখের ভার তাঁকে সারাজীবন একাই বইতে হয়েছে। — ভার লাঘব করার কোনো সঙ্গী পাননি। পেলেও অপরিহার্য সত্য মেনে নিতেই হত। মানুষ চায় একপ্রকার আর ঘটনা ঘটে আর এক প্রকার। দ্রৌপদীর অন্তরের এই যন্ত্রণাদিগ্ধ দিকটি আমরা বুঝতে পারি মহাপ্রস্থানের পথে যখন যুধিষ্ঠির এই গোপন কথাটি প্রকাশ করে দিলেন। এই বিষম ভালোবাসার পাপেই দ্রৌপদীকে ভূপতিত হতে হল। লেখিকার নিপুণ বিশ্লেষণে তা পরিস্ফুট হয়েছে। পরিস্থিতির শিকার দ্রৌপদীর ভালোবাসা কি পাপ?
পৃথিবীর বৃহত্তম মহাকাব্য মহাভারতের চরিত্রগুলি বিচিত্র ঘটনাসংঘাতে উজ্জ্বল ও জটিল। প্রতিটিই যেন স্বমহিমায় অনন্য অতুলনীয়। ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব এই মহাকাব্যটি সব দিক থেকেই বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। এমনকী এটি সমগ্রভাবে কোনো একটি বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয়নি। এতে এর গৌরব বেড়ে গেছে বলাই বাহুল্য। যেন বিশাল ভারতবর্ষের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি। এর মধ্যে নানা দর্শন, নানা জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরিচয় দেদীপ্যমান। মানুষ বাঁচে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পাওয়া যায় মহাভারতে। ধৃতরাষ্ট্রের কাছে প্রাজ্ঞ বিদুরের বলা এই গল্পটি আসলে দার্শনিক তাৎপর্যে পরিপূর্ণ। মনে পড়ে যায় বৈদিক ঋষিও তো মধু প্রার্থনা করেছেন ‘মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্ত নঃ পিতা।’ বিশ্বকবিও বলেছেন তাঁর গানে— আমি কিসের মধু খুঁজে বেড়াই ভ্রমরগুঞ্জনে।’ তবুও আশ্চর্য কী? অর্থাৎ দিন দিন এত প্রাণী শেষ হয়ে যাচ্ছে তবুও কী আশ্চর্য? মহাভারতে ধর্মরাজ বকের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির সেই কথাই বলেছিলেন—
অহনহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম।
শেষাঃ স্থিরভৃমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম।।
প্রতিদিন কত প্রাণী যমের সদনে চলে যাচ্ছে। তবু যারা বাকি থাকে তারা চায় চিরস্থায়িত্ব (ভাবে যে আমরা চিরস্থায়ী) এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী আছে? জীবনের প্রতি মানুষের মমতা এমনই।
এইভাবে মহাভারত অবলম্বনে অপর প্রবন্ধ— কুন্তী গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র–। তিনটি চরিত্রই নানা দিক দিয়ে আলোচ্য।
বহুগুণান্বিতা হয়েও কুন্তীর কিছু পাপ কাজ করা ছিল— যার প্রতিফল তিনি পেলেন অন্তিমলগ্নে। কুন্তী জতুগৃহে পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার অসৎ পরিকল্পনাটি জানতেন। তাই কৌশলে এক নিষাদী ও তাঁর পাঁচ পুত্রকে রাত্রে থাকতে দিতে রাজি হয়েছিলেন। যাতে তাদের মৃতদেহ দেখে কুন্তী সহ পঞ্চপাণ্ডব মারা গেছেন বলে ধারণা হয়। এইরকম পরিকল্পনা তো নর হত্যারই সমতুল্য পাপজনক— সেটা যে কারণেই হোক না কেন। কুন্তীর জীবনে আরো বিষাদের কারণ ছিল। কুমারী অবস্থায় তিনি সূর্যের প্রভাবে পুত্র কর্ণকে লাভ করেও সামাজিক অপবাদের ভয়ে একটি ছোটো ভেলায় তাকে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেই কর্ণ পালক পিতামাতার (অধিরথ ও রাধা) কাছে বড় হয়ে বীর যোদ্ধায় পরিণত হল। সব কিছু জেনে কুন্তী যখন একদিন নিরালায় দেখা করে কর্ণকে পাণ্ডবপক্ষে আনতে চাইলেন— কর্ণ রাজি হলেন না। কুন্তী প্রত্যাখ্যাত হলেন। মহাভারতের বিচিত্র ঘটনাবিন্যাসে চরিত্রগুলিও বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে দোলায়িত, তাই এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও কর্ণকুন্তীর বৃত্তান্তটি কাব্যরূপ দিয়েছেন। এইরকম আর একটি বিচিত্র পরিস্থিতির নিরুপায় শিকার হলেন গান্ধারী। তিনি জানেন যে তাঁর স্বামী ও পুত্রেরা অন্যায়পথে চলেছে তিনি সেটা বুঝতে পেরেও তেমন কিছু করতে পারছেন না। এই সঙ্গে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহান্ধ ন্যায়বর্জিত হৃদয়ের অন্ধকারময় পক্ষপাত দুষ্ট দিকটা। গান্ধারী কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে নিষ্পাপ।
শান্তিপর্বকে মহাভারতের মহাফল বলা হয়। শান্তিপর্ব মহাফলম। এই পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নোত্তরে নানা বিষয়ে তত্ব কথার সার সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মতত্ব, দর্শনতত্ব প্রভৃতি নানা কথাই স্থান পেয়েছে। ঘটনা বর্ণনার চেয়ে তত্ব পর্যালোচনাতেই এখানে আগ্রহ বেশি। প্রবন্ধকারের মতে এখানে আচার সর্বস্ব ধর্মের একটি জটিল রূপই পরিস্ফুট হয়েছে যা বৈদিক ধর্মের বেশ কিছু বিবর্তিত রূপ। কালের প্রবাহে বৈদিক-ধর্মও ঠিক অবিকলভাবে পুরানো রূপে প্রতিষ্ঠিত রইল না। তা আরও অভিনব খুঁটিনাটি আচার-বিচারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এক ‘বহুশাখ সমাজতরু’ পল্লবিত হতে শুরু করল। পুরোনো কিছু হয়তো বাদও গেল— আর অভিনব সংযোজনও থেমে নেই। এইভাবেই হিন্দু সমাজ (ধর্মীয়) বর্তমান রূপে এসে পৌঁছেছে। শান্তিপর্বের মধ্যে থেকে সেই বিবর্তন পর্বটি শ্রদ্ধেয়া লেখিকার নিপুণ বিশ্লেষণে ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ধীরে ধীরে নিয়তিবাদের বিকাশও লক্ষ করেছেন তিনি। তবে সবচেয়ে দামি কথা হল ভীষ্ম। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন। ভারতবর্ষে এত দেবতার ভিড় সত্বেও আশ্চর্য কণ্ঠে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষিত হল। যে উপাদেয় সত্য পরবর্তীকালেও কবি চণ্ডীদাসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’
এই সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি সাধারণ পাঠক এবং বিশেষ গবেষক সকলেরই বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তার খোরাক জোগাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এখানে উপস্থাপিত নানা বক্তব্য বিষয়গুলি যদি জিজ্ঞাসু পাঠকদের তৃপ্ত করে তা হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।
ড. নীরদবরণ মণ্ডল, কাব্যতর্কতীর্থ
অধ্যাপক, সংস্কৃত পালি প্রাকৃত বিভাগ,
বিশ্বভারতী
১৬ জুন ২০১২
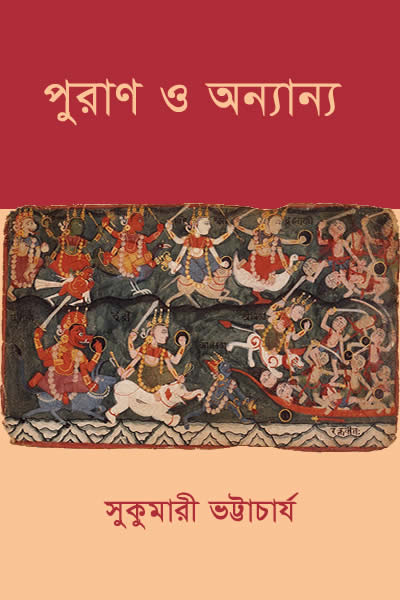
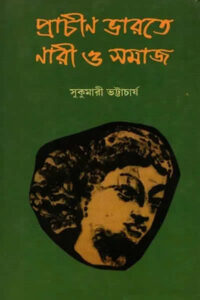


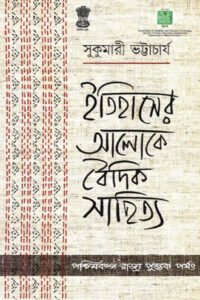

Leave a Reply