নিয়তিবাদের স্বরূপ – সুকুমারী ভট্টাচার্য
নিয়তিবাদের স্বরূপ – সুকুমারী ভট্টাচার্য
ঋণস্বীকার
স্পলডিং ফান্ড অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ লাইব্রেরিতে কাজ করবার জন্য দু’বার অনুদান দিয়ে আমার উপাদান সংগ্রহে প্রচুর সাহায্য করেছিল। প্যারিসে ‘মেজঁ দ সিয়ঁন্স দ ল’ ম’ একাধিকবার সুযোগ দিয়েছে লাইব্রেরিগুলি ব্যবহার করতে। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বি এম বড়ুয়া সিনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ পেয়ে তিন বছর এশিয়াটিক সোসাইটিতে কাজ করতে পেরেও বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করতে পেরেছি। এ বিষয়ে প্রথমে মূল গ্রন্থটি ইংরেজিতে লিখি। তার উপর ভিত্তি করে বর্তমান রচনা
প্রয়াত পণ্ডিত অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মোতিলাল নানা আলোচনা ও অন্যান্য ভাবে নানা কাজটি সমাধা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন; তাঁকে শেষ ধন্যবাদটুকুও জানাবার সুযোগ পেলাম না। বিশেষ ঋণ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছে, যিনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে কখনওই আপত্তি করেননি, এবং তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বিস্তর বই ধার দিয়েছেন পড়তে। তাঁর কাছে আমার অপরিশোধ্য ঋণ রইল। ড. তপোধীর ভট্টচার্য নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে এসেছিলেন পাণ্ডুলিপির ত্রুটিগুলি দেখে দিতে, তাঁর কাছে ঋণ স্বীকারে আনন্দ রইল, কারণ একদা তিনি আমার গবেষণার ছাত্র ছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ দে তাঁর অনেক সময় ও উৎসাহ ব্যয় করেন আমার অপরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি গুছিয়ে দিতে, তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।
শ্রীমতি তনিকা ও শ্রীমান সুমিত সরকার, আমার কন্যা ও জামাতা, উৎসাহ দিয়েছেন এবং দৌহিত্র শ্রীমান আদিত্য তার উপস্থিতি দিয়ে প্রেরণা জুগিয়েছে। বান্ধবী শ্রীমতি বাণী ভট্টাচার্য বারে বারে ভরসা দিয়ে আমাকে বিশেষ ভাবে ঋণী করেছেন। অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচি দুটি তথ্যের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমার দেবর অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য ওই দুটি তথ্য উৎস-সমেত উদ্ধার করে আমার বিশেষ উপকার করেন; দু’জনের কাছেই আমার কৃতজ্ঞতা রইল। এ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনাগুলো ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশকালে এর রূপ অনেকটাই পরিবর্তিত, পরিমার্জিত হল।
ভূমিকা
ক্লস্টারমাইয়ার তাঁর প্রবন্ধ ‘একোলজিক্যাল ডিমেনশন্স অব অ্যানশেন্ট ইন্ডিয়ান থট’-এ বলেন, বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা কায়ক্লেশে নির্বাহিত হত: টিকে থাকাই অনিশ্চিত ছিল এবং দুর্ভিক্ষ, রোগ, শত্রু ও শ্বাপদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। যে শক্তিসূত্রে দেবলোক মনুষ্যলোকের সঙ্গে যুক্ত, প্রত্যেক আপতিক দুর্ঘটনা যেন সেই সূত্র ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জন্যেই ঘটেছে এমন মনে করা হত। (জশ সম্পাদিত, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫১) ভারতবর্ষের প্রথম রচিত প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য অর্থাৎ সংহিতা ও ব্রাহ্মণগুলিতে নিয়তির কোনও চিহ্নই নেই। অর্ধ সহস্রাব্দ পরে যতটা বিপদসংকুল ছিল তার চেয়ে বেশিগুণ বিপদসংকুল ছিল তখনকার, অর্থাৎ বৈদিক যুগের জীবনের পরিবেশ; কিন্তু এই সাহিত্যের মূল সুরটি ছিল: দেবতারা স্বর্গ থেকে মানবজীবন নিয়ন্ত্রণ করেন এবং প্রয়োজনের মানুষ সর্বদাই যজ্ঞে স্তোত্রপাঠ করে, সুস্বাদু হব্য ও পানীয় দিয়ে তাঁদের তুষ্টিবিধান করতে পারত। সাধারণ ভাবে দেবতারা মানুষের শুভার্থী এবং যতদিন সম্ভব এই পৃথিবীতেই থেকে সুদীর্ঘ জীবনযাপন করাই মানুষের পক্ষে বাঞ্ছনীয়; প্রকৃতি সুদৃশ্য, সদয় এবং জীবন আনন্দময়। ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই কৃষিতে প্রাচুর্য দেখা দিলে, পশুপালের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে, আর্যরা আসার সঙ্গে যা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল সেই নৌবাণিজ্য এবং তার দ্বারা গ্রিস ও রোমের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে, সম্পদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটল।
গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে, ‘(অত্রাঞ্জিখেরার) পুরো বসতিপুঞ্জে দেখা যায় ‘চিত্রিত ধূসর’ পাত্রের সংস্কৃতি। সেখানে লোহা ব্যবহারের কৌশল গোড়া থেকেই ছিল। লোহার খনি থেকে ধাতু উৎখনন বেশ অনেক পরিমাণেই হত, যাতে প্রচুর লোহার যন্ত্রপাতি তৈরি করার সুবিধা ছিল। অতএব উষ্ণমণ্ডলের উদ্ভিদ অরণ্য উৎপাটন করে, তারা জমিকে প্রসারিত করে কৃষির কাজে লাগাতে পেরেছিল এবং ধান, বাজরা, যব ও রবিশস্যের সঙ্গে গমেরও চাষ করত। বহির্বাণিজ্যেও তারা লিপ্ত ছিল, না হলে অত পরিমাণে ধাতু ও সস্তা মণির পুঁতি সংগ্রহ করতে পারত না। এই সব সিদ্ধান্ত থেকে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, এই সময়টিতে বেদের শেষের পর্যায়ের সংস্কৃতিই প্রতিফলিত।’ (ঘোষ সম্পাদিত, অ্যান এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইন্ডিয়ান আর্কেওলজি, পৃ. ২৬) এই প্রাচুর্য সমাজে শ্রেণিবিভেদকে দৃঢ়তর করে এবং আরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ অন্য বৃহত্তর শ্রমজীবী অংশের তুলনায় কত বেশি প্রাচুর্য ও ভোগ্য উপকরণ পেত।
এর একটা ফল হল, গোষ্ঠী ও কৌম-গত জীবন ভেঙে গেল, একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবার (কুল) সমাজের নিম্নতম একক হিসেবে দেখা দিল। আর্যরা যখন প্রাগার্যদের পরাস্ত করে আর্যাবর্তের উত্তর পশ্চিম ভাগ থেকে দূরে সরিয়ে দিল, তখন পরাজিত জনগোষ্ঠীর অনেককেই দাস ও ক্রীতদাস হিসেবে আর্য সমাজের বেশি শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ করল। এদের শ্রমের বিনিময়ে আর্য সমাজের উপরতলায় একটি অবসরভোগী উদ্বৃত্তভোগী শ্রেণি তৈরি হল। সমাজ চারটি বর্ণে বিভক্ত ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এখন এক অবসরভোগী ও উদ্বৃত্ত-সম্পদভোগী শ্রেণির উদ্ভবে নতুন একটি বিভেদ— শ্রেণিবিন্যাস— দেখা দিল। এই অবসরভোগী শ্রেণি বেঁচে থাকার জন্য কায়িক শ্রমপ্রয়োগে উৎপাদনের কাজ থেকে ছুটি পেয়ে মন দিল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চায় আত্মনিয়োগ করায়। তাদের নিচের মানুষেরা রইল কায়িক পরিশ্রমের দায়িত্ব নিয়ে। অবসরভোগী শ্রেণি শ্রমজীবীদের তুলনায় নিতান্তই মুষ্টিমেয়। কিন্তু শ্রমজীবীদের এরাই নিয়ন্ত্রণ করত। তাদেরকে বোঝানো হল, দৈহিক শ্রমের তুলনায় মানসিক শ্রমের মূল্য ও মর্যাদা বেশি।
এরই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক এক তত্ত্ব হল, সমাজে কী ভাবে মন্দের অনুপ্রবেশ ঘটল। দীঘ-নিকায়ের সুত্ততে (২৬, ২৭ নং) প্রথমে বলে যে, আদিতে সমাজ শান্তি ও সংহতিপূর্ণ ছিল, লোভ, কৃষি, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, বাণিজ্য, চৌর্য, মিথ্যা এবং অন্যান্য অপরাধের মধ্যে দিয়ে সমাজে পাপ প্রবেশ করল। কল্পনা করতে অসুবিধে হয় না, এই অংশের তথ্য ভারতীয় সমাজে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতকের চিত্রের সঙ্গে মেলে, অথবা তার সামান্য কিছু পরবর্তী কালের সঙ্গে— হয়তো বা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের; তখন ব্যাপক ভাবে কৃষিকর্ম চলছে, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যও চলছিল এবং অল্পসংখ্যক লোকের হাতে ধন সঞ্চিত হচ্ছিল ও সমাজের অধিকাংশের জীবন-মান খুবই নিচু ছিল।
ধনীদের গৃহে ক্রীতদাস ও দাসেরা শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত হলে পর, পরিবারের নারীরা উৎপাদন ব্যবস্থার বেশি পরিশ্রমের কাজ থেকে অব্যাহতি পেলেন, কৃষিক্ষেত্রের কাজ থেকেও। তা ছাড়া আর্যরা এ দেশে আসবার অল্প পর থেকেই আর্য-প্রাগার্য মিশ্র বিবাহ চলিত হল। আর্য পুরুষ প্রাগার্য নারীকে বিবাহ করা শুরু হওয়ার পর থেকেই নারীর উপনয়ন বন্ধ হয়ে গেল, পাছে অদীক্ষিত অনার্যের বৈদিক জ্ঞানে অধিকার জন্মায়। ফলে শিক্ষা থেকে নারী বঞ্চিত হল। সুতরাং লিঙ্গভিত্তিক আর একটি ভেদ সমাজে দেখা দিল; বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদের সঙ্গে যুক্ত হল লিঙ্গভেদ। শিক্ষার অধিকার রইল অবস্থাপন্ন তিনটি বর্ণের বিত্তবান পুরুষের; এই সময়েই পৌরোহিত্যে পুরুষের, বিশেষত, শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণের একাধিপত্য কায়েম হল।
এ যুগের সমস্ত রচনাই আস্য অর্থাৎ মুখেমুখেই রচিত এবং প্রজন্ম-পরম্পরায় হস্তান্তরিত। এগুলি সঞ্চিত ছিল সমাজের শীর্ষভাগের মানুষের মধ্যে। পুরোহিতরা সামাজিক আইন এবং যজ্ঞবিধি দুই-ই প্রণয়ন করতেন। সম্ভবত সিন্ধুসভ্যতার কাছ থেকে লিপিজ্ঞান আহরণ করবার পর সমস্তই লিপিবদ্ধ হয়েছিল।
খুব সম্ভব প্রাগার্যদের মধ্যেই কোনও কোনও সন্ন্যাসী সম্প্রদায় ছিল। হয় ভ্রাম্যমাণ, নয় তো আশ্রমবাসী। এঁরা হয়তো বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতেন না; আশ্রমধর্মের শেষ দুটি, বানপ্রস্থ ও যতি, সম্ভবত এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়গুলির সঙ্গে সমাজের আপোসের ফলে সমাজব্যবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ে। যজ্ঞকারী মূল ব্রাহ্মণ্য সমাজের সঙ্গে ওই সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একটা ঘাত-প্রতিঘাত হয়েছিল। মানুষ নিরুপায় ভাবে বিত্তবৈষম্যে দ্বিখণ্ডিত সমাজ এবং তারই অনুপাতে ক্ষমতাবণ্টন লক্ষ্য করেছিল। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠদের জীবনমান নিরতিশয় সংকুচিত ও দীন ছিল। পুরোহিত ও শাস্ত্রকারদের কাছে এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা অপেক্ষিত ছিল। এই পুরোহিত শাস্ত্রকাররা ধর্মের ভাষায় জীবনের অভাব, ক্ষতি ও অবিচার ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হলেন; এগুলি বেদের শেষ পর্যায়ে ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছিল ব্যাখ্যায়। গীর্ৎস-এর কথায় ‘ধর্ম একটি রূপক-সংস্থা যার ক্রিয়া হল মানুষের মধ্যে, (১) শক্তিশালী এবং ব্যাপক ও স্থায়ী মেজাজ ও প্রেরণা সৃষ্টি করা, (২) সত্তা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মের ধারণাগুলির সংজ্ঞানিরূপণ করা এবং (৩) এই ধারণাগুলিকে এমন বাস্তবতার গরিমায় মণ্ডিত করা, যাতে ওই মেজাজ ও প্রেরণা বিশিষ্ট ভাবেই বাস্তবধর্মী বলে প্রতিভাত।’ (গীস, ১৯৭৩, পৃ. ৯০) ব্রাহ্মণ সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে এবং উপনিষদে আমরা প্রথমে কিন্তু জন্মান্তরের কথা পাই না বরং পৌনঃপুনিক মৃত্যুর কথাই শুনি, ধীরে ধীরে এটি প্রত্যক্ষ একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে জন্মান্তরবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই। ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন বলছে, ‘যখন সমস্ত সমাজসংগঠন এবং এমনকী সমগ্ৰ মহাবিশ্ব অপ্রকৃত বলে প্রতীত হয়, যেমন হয়েছিল (ইয়োরোপের) মধ্যযুগের শেষপ্রান্তে, (তখন) দেবতার ‘ভর’ থেকে, উম্মাদনা থেকে, যুগক্ষয়ে প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিঃসৃত হতে পারে; সমবেত প্রতিবাদ মৌলিক এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে… অনুমাননির্ভর চিন্তা রাজসভার পরিবেশ ও পুরোহিত মহলেই প্রথম দেখা দেবে, কারণ এটি নির্ভর করে বহু পুরুষের সংহত প্রচেষ্টা ও বিশেষ প্রশিক্ষণের ওপরে, যার দায় আদিম সমাজে একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় পুরোহিতমণ্ডলীই নিতে পারত।’ (পৃ. ৩৭৮)
ধর্মীয় নেতা ও শাস্ত্রকাররা যখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রাধান্য পেল, তখন থেকেই তারা হতদরিদ্র জনসাধারণের আত্মিক প্রয়োজন অনুযায়ী ধর্ম ব্যাখ্যা করতে শুরু করল; বিত্তবান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তখন চাই জনসাধারণের সম্ভাব্য প্রতিবাদ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার আশ্বাস এবং পুরোহিতদের নিজেদের জন্য চাই ধন ও ক্ষমতা। সাধারণ লোক কেন পুরোহিতদের শিক্ষা মেনে নেবে? গীস অন্যত্র বলছেন, ‘ধর্মকে দেখতে হবে সাধারণ জ্ঞানের অ-পর্যাপ্ততা অথবা অনুভূত অপর্যাপ্ততার পরিপ্রেক্ষিতে, জীবন অভিমুখে একটি সামগ্রিক মনোভাবের বিকাশরূপে এবং সাধারণ জ্ঞানের ওপরে গঠনাত্মক একটি প্রভাব হিসেবেও দেখতে হবে; যে ভাবে প্রশ্নাতীতকে প্রশ্ন করে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে আমাদের বোধ নির্মাণ করে।’ (গীস, ১৯৬৮, পৃ. ৯৫) এই ভাবে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে ব্যাখ্যা করে ধর্ম তাকে আরও বেশি বোধগম্য করে তোলে বলেই মানুষ শাস্ত্রকারদের কথা শোনে।
ইহুদি জাতেও এই ব্যাপারই ঘটেছিল। প্রথম নগরায়ণে যে সব নগরের পত্তন হয় সেগুলিতে অনেক সুসংহত নির্দিষ্ট একটি পুরোহিত সম্প্রদায় (রাম্বাই) ছিল। ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন বলছে, ‘যেখানেই সম্ভব হয়েছিল, এই ‘রাম্বাই’-রা সমাজের ওপরে তাদের কর্তৃত্ব প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলেছিল। পরে এর অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে ইহুদি রাজসভাগুলিও ‘রাম্বাই’দের কর্তৃত্বাধীনে চলে এসেছিল।’ (১৪শ খণ্ড পৃ. ২৫৯ )
সন্ট হাইমার ও কুল্কে সম্পাদিত বইতে পাচ্ছি, ‘এখানে গ্রামে পুরোহিতের ভূমিকা ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ দেবতা ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করা ততটা প্রাধান্য পায়নি। নগরভিত্তিক মুখ্য ধর্মধারার কঠিন শৃঙ্খলার চেয়ে জাদুর কাছাকাছি ছিল এরা, এবং (জাদু) লোকধর্মের একটি ‘অপরিহার্য’ উপাদান। এতে দেব বা দেবীর অব্যবহিত সান্নিধ্য আছে… তা বিগ্রহাশ্রিতঃ হতে পারে, বিমূর্তও হতে পারে। দেবতা এখানে, এখনই আছেন।’ (১৯৮৯, পৃ. ৪) এই মধ্যস্থের ভূমিকাটিই নগরের পুরোহিতদের তাৎপর্য বৃদ্ধি করেছিল, যাতে (পুরোহিততন্ত্রের) পর্যায়বিভাগ ও ভূমিকা বহুগণিত হয়েছিল, নগরের চারিপাশে গ্রামগুলিও পুরোহিতদের ক্রমবর্ধমান মহিমায় প্রভাবিত হচ্ছিল, এবং সে-মহিমা আত্মসাৎ করে গ্রামগুলিও নগরের অনুসরণ করছিল।
সাধারণ মানুষ যদি তাদের কর্ম ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সরাসরি কোনও যোগসূত্র দেখতে পেত, তা হলে এই মধ্যবর্তী শ্রেণির কোনও অবকাশই থাকত না। কিন্তু জীবনে দেখা গেল ব্যাখ্যার অতীত কর্ম ও অভিজ্ঞতা, যেগুলির কোনও সামঞ্জস্যই নেই, কাজেই ব্যাখ্যার জন্যে একটা আধ্যাত্মিক জমি তৈরি হল। গীর্ৎস বলছেন, ‘হতবুদ্ধিতা, দুঃখভোগ এবং নিষ্পত্তির অতীত নৈতিক স্বতোবিরোধ— এগুলি যথেষ্ট তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী হল। জীবন বোধগম্য হয় এবং ‘বুদ্ধিপূর্বক চলে এর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারি’— এ বোধকে মৌলিক ভাবে প্রত্যাহ্বান জানায়— এ এমন প্রত্যাহ্বান, যা যে কোনও ধৰ্ম, যত ‘আদিম’ই হোক না কেন, যদি টিকে থাকতে চায় তা হলে তাকে কোনও ভাবে তার মোকাবিলা করতেই হবে।’ (১৯৭৩, পৃ. ১০০)
সাধারণ মানুষের একটি শ্রেণির কাছে আত্মসমর্পণ করার এটিই প্রথম ধাপ, যে শ্রেণি সমাজের জ্ঞানগুরুর ভূমিকা গ্রহণ করে। এ কথা সত্য নয় যে, যা কিছু মানুষের সামনে উপস্থাপিত করা হত তা-ই তারা গ্রহণ করত; তাদের কিছু কিছু প্রশ্ন ও প্রতিবাদের চিহ্ন শাস্ত্রের মধ্যেই রয়ে গেছে। মরণোত্তর জীবন সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতা একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছে: ‘লোকে বলে মানুষের এই জগৎ থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ নয়, কে জানে এ (আত্মা) অন্য কোনও জগতে থাকে কিনা।’ (৬:১:১:১) কঠ উপনিষদেও পরলোক সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছে: মৃত্যুর পরে কিছু থাকে কি না নিয়ে মানুষের এই যে সংশয়— কেউ বলে (পরলোক বা আত্মা) আছে, অনেকে বলে নেই। (১:১:২০) মরণোত্তর অস্তিত্ব যা অধিকাংশ ধর্মের সূচনা-বিন্দু, তা-ই সংশয়িত হল। এই সংশয় নিয়ে শত শত গূঢ় বা প্রকাশ্য উক্তি আছে— এ সংশয় খাঁটি, কারণ এর মধ্যে জীবনের সম্বন্ধে বিশ্বাস নিহিত। এবং এ সংশয় থেকে শুধু যে কিছু বস্তুবাদী দর্শন প্রস্থানের উদ্ভব হয়েছে তা-ই নয়, পুরোহিত শাস্ত্রকারদের প্রণীত কিছু কিছু বিশ্বাসের মূল উপজীব্যকেও প্রত্যাহ্বান জানানো হয়েছে। পরে আমরা দেখব নিয়তিবাদকেও এই সংশয়ই প্রত্যাহ্বন জানিয়েছে।
ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন বলছে, ‘যে রহস্য মানুষের জীবনকে ঘিরে আছে তা কখনওই পুরোপুরি উন্মোচিত হবে না। ফিরে ফিরেই তা দেখা দেবে— কখনও কখনও সেগুলি (ঐ বিশ্বাসগুলি) নৈরাশ্যবাদকে প্রকাশ করে, এমন কী এক ধরনের স্বাভাবিক সংশয়বাদকেও। মূল প্রশ্নটি হল, পরলোক, দেবতাদের বিশ্ব ও নিজের মরণোত্তর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্য করে কিছু বলা সম্ভব কিনা।’ (৯ম খণ্ড, পৃ. ৪০৪ )
এই সংশয়বাদ এবং পুরোহিত ও শাস্ত্রকারদের রচিত শাস্ত্র মিলে একটা বিরোধ ও আততি সৃষ্টি করে, যার থেকে ভারতবর্ষে নির্মিত হল ব্রাহ্মণ্যধর্ম, যাতে সংশয় ও বিশ্বাস দুই-ই আছে, আছে নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদ। কিংবা অন্য ভাষায় বলতে গেলে, জীবনমুখীনতা ও জীবনবিমুখতা। মানুষের কর্মের ভিত্তিতে আছে এই সৃষ্টিধর্মী আততি, নিয়তি ও পুরুষকার, যে পুরুষকার গুরুতর প্রত্যাহ্বান জানায় নিয়তিবাদকে।
প্রাগরায়ণ স্তরেও পুরোহিত সম্প্রদায় ও সামাজিক-নৈতিক বিধানদাতারা অনেক সুবিধা ভোগ করতেন। মামফোর্ড বলছেন, ‘…নগর ভ্রুণ আকারে গ্রামের মধ্যেই ছিল। বাসগৃহ, মন্দির, জলাধার, সাধারণের পথ, বাজার… সবই প্রথমে গ্রামেই রূপায়িত হয়…প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইন ও ন্যায়বিচারের শুরু হয় গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠদের সভায়। আস্য সংস্কৃতিতে শুধু বয়োবৃদ্ধরাই যথেষ্ট সময় পেতেন যা কিছু জ্ঞাতব্য বা আত্মস্থ করার।’ (১৯৬১, পৃ. ১৯) বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে থেকেই আসত আইন প্রণেতারা। গভীরতর অভিজ্ঞতার জন্যে সে সব সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে মনে করা হত যে, তাঁদের প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক গভীরতা, জ্ঞান, পূর্বদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি আছে; তাই তাঁদের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছিল রাষ্ট্র ও সমাজকে মসৃণ ভাবে চালানোর দায়িত্ব।
এই বয়োবৃদ্ধরা (সংস্কৃত ‘সনৎ’ শব্দ, যার অর্থ প্রাচীন, দীর্ঘজীবী। তুলনীয়, ল্যাটিন ‘সেনাটুস’ বৃদ্ধসভা), পরে শুধুই উচ্চ তিন বর্ণের থেকে নির্বাচিত হত। এঁদের দায়িত্ব ছিল (১) দৈনন্দিন জীবনে এবং সংকটের সময়ে নির্দেশ দেওয়া এবং (২) জীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য এবং স্বরূপ কী, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের বিধানগুলি ব্যাখ্যা করা; অর্থাৎ এমন একটা ধর্মদর্শনের ছক নির্মাণ করা যাতে তাঁদের বিধানগুলির সমর্থন মেলে এবং লোকে তা নির্বিবাদে গ্রহণ করে। মোটের উপরে এ কাজ তাঁরা সার্থক ভাবেই করতে পেরেছিলেন।
সামন্তবাদের সংজ্ঞা নিয়ে মতবিরোধ আছে, বিশেষত ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে। যদি মনে করে নিই যে, আর্যরা আসবার পরে, বিশেষত মৌর্যযুগ থেকে, একটি প্রাথমিক বা আদিমরূপে এটি দেখা দিয়েছিল, বিশেষত আৰ্য-প্রাগার্য সংমিশ্রণের পরে, তবুও এ সামন্তবাদের চরিত্র ভিন্ন, এবং এতে বর্ণবিভাগের একটি ভূমিকা ছিল। ব্রাহ্মণরা সামাজিক-ধর্মীয় বিধানের হর্তাকর্তা হিসেবে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। সামন্ততন্ত্রের যুগে অধিকাংশ ব্রাহ্মণের জীবিকা পৌরোহিত্যের ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠান করায় ততটা নির্বাহিত হত না যতটা হত রাষ্ট্রব্যবস্থার রাজসভায়, ভূস্বামীদের দরবারে কোনও বৃত্তি অবলম্বনের দ্বারা।
গ্রেট সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়া বলে, ‘মনে করা হয় প্রাচীনতম শ্রেণিবিভক্ত সমাজ ছিল সিন্ধু উপত্যকায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এবং কিছু অধিককাল গুজরাতে টিকে ছিল। বৈদিক আর্যদের সমাজে (সম্পত্তির) ব্যক্তিগত স্বত্বাধিকার ছিল পশুপালে, জঙ্গম সম্পত্তিতে, ক্রীতদাসে এবং গৃহস্থের অধীন জমিতে। গোষ্ঠীতন্ত্রের মধ্যে একটা অভিজাত সম্প্রদায় ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠল, গোষ্ঠীর অন্যদের ওপরে তাদের ক্ষমতা বিস্তার করে। (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৫০) ব্রাহ্মণরা যে রাজসভায় এবং সমাজে বাড়তি সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করত, তাতে তারা এমন একটি গরিমায় মণ্ডিত হত যা বিধাতার অভিপ্রায় মানুষের কাছে সমর্থনযোগ্য করে তোলার দাবি করত। উপনিষদের তথ্য প্রমাণে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ক্ষত্রিয়দের মধ্যেই প্রথম জন্মান্তরবাদ উত্থিত হয় (সম্ভবত সমাজের অন্যদের চেয়ে বেশি করে তারাই যুদ্ধে অকালমৃত্যুর সম্মুখীন হত, তাই সম্ভবত তারাই বেশি উৎসুক ছিল মরণের পরে কী আছে তা জানতে)। কিন্তু খুব প্রথম দিকেই ব্রাহ্মণরা ওই তত্ত্বটি আত্মসাৎ করে এবং এ নিয়ে চর্চা করে, ব্যাখ্যা করে, অলংকৃত ও বিস্তারিত করে এবং প্রায় দুই শতকের মধ্যেই কর্মবাদকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর দ্বারা এতে সংলগ্ন হয় কিছু বিশিষ্ট গুণ ও চরিত্র, যা পরবর্তী কালে নিয়তিবাদের অভ্যুত্থানের পথ সুগম করে দেয়। সে কথা পরে। জন্মান্তরবাদ যে কৃষিজীবী সমাজের সৃষ্টি, এ ধারণায় সত্য থাকতে পারে: বীজ মাটিতে পড়ে কিছুকাল পরে শস্যরূপে দেখা দেয়— এর থেকে ধারণা হতেই পারে যে, মৃত্যুই জীবনের শেষ কথা বা চূড়ান্ত অবসান নয়। বীজ-শস্যে যে পুনর্জন্ম, তার ধারণা সহজেই সংক্রমিত হতে পারে মানসিক স্তরে, তার থেকে পুনর্জন্মের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় এবং মানুষ সহজেই তা গ্রহণ করে। মৃত্যুকে আত্যন্তিক অবসান বলে গ্রহণ করা কঠিন। মানুষের বোধে সত্তা ওতপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট, কাজেই মানুষের মন শূন্যতার ফাঁক মেনে নিতে পারে না। তা ছাড়াও, সিন্ধু সভ্যতার কৃষিজীবী মানুষের মধ্যে পুনর্জন্মের তত্ত্বটি বিদ্যমান থেকে থাকতেও পারে; আর্যরা তাদের কাছে কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে এ তত্ত্বও ধীরে ধীরে গ্রহণ করে থাকতে পারে। স্বভাবত এ তত্ত্ব মানুষের আত্যন্তিক নাস্তিক্যের সম্ভাবনার দুঃসহ যন্ত্রণায় পরম সান্ত্বনা দিয়েছিল, এবং জীবনকে বাড়তি একটা রহস্যে মণ্ডিত করেছিল। শুধু যখন কর্মবাদ এসে জুড়ল জন্মান্তরবাদের সঙ্গে, কতকটা আকস্মিক ভাবেই, হয়তো তখনই একটা জটিল তত্ত্বজাল রচিত হল বহুতর রহস্যময় অনুষঙ্গ ও উপাদান নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদ্য হল, জন্মান্তর বা কর্মবাদ তত্ত্ব। প্রথম দিকের উপনিষদগুলি জন্মান্তরের তত্ত্বের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, যার দ্বারা নতুন একটা মাত্রা জুড়ল এই বিশ্বাসে যে মৃত্যুর পরেও জীবন দেহ থেকে দেহান্তরে অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। পরের যুগে জন্মান্তরবাদের সঙ্গে যুক্ত হল কর্মবাদ। এতে শুধু যে জন্মের পরম্পরা উপস্থাপিত হল তাই নয়, সুখ-দুঃখ ও জীবনের ঘটনাগুলিও এর সঙ্গে যুক্ত হল। একটা স্তরে এটি আরও তৃপ্তিদায়ক তত্ত্ব, কেননা এতে মানুষের অহমিকার গৌরব কীর্তিত হয়েছে, মানুষই নিজের ভাগ্যবিধাতা, এই মত প্রচার করেছে; যদিও মানুষের জীবন স্পষ্টত দৃশ্যমান, কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সরাসরি কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। ভারতী-র মতে, ‘অনৈতিহাসিক, কালাতীত অনন্তকাল-স্থায়ী সত্তা, যা কোটি কোটি জন্মান্তর পরম্পরার মধ্যে (দিয়ে চলে) তা নৈতিক ভাবে অপেক্ষাকৃত ভূমধ্যসাগরীয় ধর্মগুলির নিয়তিবাদনিষ্ঠ ধর্মগুলির চেয়ে কম তৃপ্তিদায়ক। বাড়তি আড়ম্বর বাদ দিলে এতে বাকি থাকে এই তত্ত্বটি যে, ভগবান কিছু লোককে নির্বাচন করেন এবং বাকিদের পরিত্যাগ করেন… ভারতীয় বিকল্পটি মানুষের দুঃখ এবং নৈতিক নির্বাচনের কর্তৃত্ব দিব্যশক্তির বদলে ব্যক্তিতে আরোপ করে অনেক বেশি রুচিকর ভাবে ব্যাখ্যা করে।’ (১৯৭৮, পৃ. ৪২)
কিন্তু জন্মান্তরবাদের সঙ্গে কর্মবাদ যুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নানা দার্শনিক ও নৈতিক সমস্যা দেখা দিল। তাই প্রথম ভারতীয় নিয়তিবাদী মস্করী গোসাল বলেন, ‘প্রয়াস, প্রযত্ন, শ্রম বা কর্মশক্তি বা মানুষের ক্ষমতা বলে কিছুই নেই; সব কিছু অপরিবর্তনীয়রূপে পূর্ব হতেই স্থিরীকৃত।’ (উবাসগদসাও, ১:৯৭:১১৫) শুধু আজীবিকবাদ নয়, চার্বাক ও তাঁর শিষ্যরাও কিছু পুরোহিতদের উক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন; বালাস্লেভ-এর লেখায় পাচ্ছি, ‘..এটাও লক্ষণীয় যে, চার্বাকপন্থী বস্তুবাদীরা কার্যকারণের যে ভিত্তি, হেতু ও ফলের মধ্যে আবশ্যিক যে সম্পর্ক, তার সম্বন্ধে তাৎপর্যপূর্ণ আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁরা দেখান যে, কার্য ও কারণের মধ্যে বস্তুর তত্ত্বগত বা যুক্তিগত কোনও সম্বন্ধই নেই। এ শুধু চিন্তার একটা অভ্যাস মাত্র ও কল্পনাসিদ্ধ একটা ব্যাপার।’ (১৯৮৩, পৃ. ২০) কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় চিন্তাবিদদের মতে কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে সম্পর্কটি দৃঢ় ও স্থির, কাজেই নিয়তিকে বর্জন করা যায়। মাধবন দেখাচ্ছেন, ‘কর্মবাদের সঙ্গে নিয়তিবাদ অভিন্ন মনে করা ভুল। কর্ম বাইরের কোনও ভাগ্য নয় যা মানুষকে তার সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে, এ কোনও অন্ধ যান্ত্রিক কাঠামো নয় যার থেকে কোনও উদ্ধার নেই।’ (১ম খণ্ড, ১৯৫৪, পৃ. ১৭২) কিন্তু নিয়তি যদি নির্ভরযোগ্য কোনও অনুমান না হয়, তা হলে কর্ম, কর্মফল ও জন্মান্তর সম্বন্ধে পূর্বতন প্রতিজ্ঞাও তো অনিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু, কার্ল পটার যেমন বলেন, ‘কর্ম একটি অনুমানেই পর্যবসিত থাকবে, কোনও যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞানের পদ্ধতিতে একে প্রমাণ করা যাবে না। কর্ম শেষ যে সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করে, সে দিকেই সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়: বৈষম্যের এবং মন্দের সমস্যা; মানুষে মানুষে এত বেশি পার্থক্য কেন, তাদের আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক বৈষম্য তাদের আচরণের ফল। সমাজে তারা যে স্থান অধিকার করে তা তাদের অতীত কর্মের ফল।’ (১৯৬৩, পৃ. ২১৯) কিন্তু একই কর্ম সব সময়ে একই ফল উৎপাদন করে না। সেই জন্যেই একটি অজ্ঞাত বস্তুর অনুমান করা হয়েছিল, তা হল নিয়তি। কেস ও ড্যানিয়েল-এর মতে, নিয়তির নির্ধারক ভূমিকায় … ‘প্রত্যেক কর্মই পৃথক ভাবে নথিভুক্ত হয়। এবং প্রত্যেকটিরই প্রতিক্রিয়া থাকে (পুরস্কার বা শাস্তি) পৃথক ভাবে, কর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। শুভকর্ম অশুভকর্মকে নাশ করে না যদিও শুভকর্মের সংখ্যা অধিক হলে ললাট-লেখনে সুখভোগের মাত্রাও বেশি হয়। ললাটলিপির ভূমিকা, এই মতে হল, কোন কর্মে (কর্তা) সক্রিয় হবে, অর্থাৎ কোন কর্মটি ফলধারণ করে জীবনের কোন বিশেষ সময়, তা-ই নির্ধারণ করা। কোনও কোনওটি বহু জন্ম পরে ফলপ্রসূ হয়।’ (১৯৮৩, পৃ. ৩৯-৪০)
বুদ্ধ বলেছিলেন, ‘স্বেচ্ছাকৃত ও সঞ্চিত কর্ম ফলভোগ করার পূর্বে কখনও মুছে যায় না এবং এগুলি এ জন্মে বা পরবর্তী কোনও জন্মে ফল ধারণ করতে পারে। স্বেচ্ছাকৃত ও সঞ্চিত কর্ম থেকে উপজাত অশুভের কোনও শেষ নেই।’ (অঙ্গুত্তর নিকায় ১৯৫:৬:১-২:১৩) কাজেই সঞ্চিত কর্ম ক্ষয় করবার জন্যে পুনর্জন্ম অপরিহার্য হয়ে উঠল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে জন্মান্তর-কর্মবাদের পুরো আকল্পটি সমাজে সর্বত্র সঞ্চরণ করছিল। আজীবিকরা যা পরিহার করল তা জন্মান্তর নয়, জন্মান্তরের হেতু যে কর্ম সেই তত্ত্বটি। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য, সব ধর্ম কর্মের মুখ্য কারণ অর্থাৎ জন্মান্তরের হেতুভুত কর্মবাদকে স্বীকার করে। তথাপি কর্মের অবশেষ এবং কর্ম ও ফলের মধ্যে অসামঞ্জস্যের সমস্যা রয়েই গেল। এর থেকেই এল নিয়তিবাদ। আনোসাকি বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তর সম্বন্ধে লিখছেন, ‘তত্ত্বগত ভাবে বৌদ্ধধর্ম আত্মার অস্তিত্ব বা জন্মান্তর কোনওটিই স্বীকার করে না। কিন্তু জোর দেয় সংসার বা পুনর্জন্মের ধারার ওপরে।… সর্বত্রই এটি মিশে গেছে সর্বজীবাত্মবাদের সঙ্গে, মানুষের আত্মাই হোক বা অন্য জীবজাতিরই হোক।… সাধারণ লোকের চিত্তে এতে এক ধরনের নিয়তিবাদকে স্থান দিল এই বিশ্বাস যে, প্রত্যেক ঘটনাই পূর্বকৃত কোনও কর্মের ফল।’ (হেস্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৬৭৫) জি ডটেন কেল্টিক ধর্মের বিষয়ে লিখতে গিয়ে লিখেছেন যে, দুটি অংশে প্রাচীন কেল্টদের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। সীজার বলেন যে, আত্মার বিনাশ হয় না কিন্তু মৃত্যুর পরে (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য দেহে সংক্রামিত হয়।’ (ডে বেল্লো গল্পিকো ৬:৪) সীজারের উক্তি সম্পূর্ণ করে ডিওডোরাস স্পষ্ট করেই বলেন, গালাটিয়াতে পিথাগোরাসের এই তত্ত্ব প্রচলিত যে, মানুষের আত্মা অমর এবং নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পরে আবার দ্বিতীয় একটি দেহে সঞ্চারিত হয়। (৫:২৮) লুকান বলেন, ‘একই নিঃশ্বাস পরলোকে তার প্রত্যঙ্গগুলিতে চালিত করে।’ (ফার্সালিয়া ১:৪৪৯:৪৫৬) এস্পেডক্লেস-এর বিখ্যাত দাবি মনে পড়ে, ‘এর আগে আমি এক তরুণ ছিলাম, এক কুমারী, একটি গুল্ম ও সমুদ্রে একটি বোবা মাছ।’ অর্ফিক ও গ্রস্টিক পিথাগোরীয়, ডায়ানেীয়ান ও এলেউসিনিয়ানদের এবং অন্য কিছু বিশ্বাস প্রস্থানের রচনায় পণ্ডিতরা গূঢ় এবং বিভিন্ন ধরনের জন্মান্তরবাদের উল্লেখ পান। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতকের মধ্যে সারা ভূমধ্যসাগরীয় জগতে ও মিশরে জন্মান্তরবাদ বাতাসে ঘুরে বেড়াত। ভারতবর্ষে এ বিশ্বাস বহু সহস্রাব্দ ধরেই জীবিত, প্রথম নগরায়ণে উদিত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের তিন-চার শতক জনমানসে অন্তর্গঢ় থেকে আবার উপনিষদের যুগে স্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।
কিন্তু আর্যাবর্তে এটি ঘটবার পূর্বে ভারতবর্ষে গ্রিক, পহ্লব, শক, কুষাণ আক্রমণ ঘটে। আক্রমণকারীরা তাদের নিজেদের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও আচরণ সঙ্গে এনেছিল। ষোড়শ মহাজনপদের উদয় হয় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, এগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়, এবং এর পরে দুই শতাব্দীর মধ্যেই মৌর্য সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরে। প্রথমে শকরা ও পরে কুষাণরা রাজ্য স্থাপন করে, কুষাণরা প্রকৃতপক্ষে একটি বিশাল ভূখণ্ডের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করে যা ভারতবর্ষের বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। একটা লেখায় দেখছি, শতপথ ব্রাহ্মণ রচনা ও প্রথম পর্যায়ের বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের মধ্যে মগধ ও সমীপবর্তী অঞ্চলে বিস্তৃত জনসমাবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটে। এই সব অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য অনুপ্রবেশ ও বিস্তার অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে এবং ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃত্তি নিয়ে এবং দার্শনিক চিন্তা নিয়েও প্রচুর প্রভেদের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক বৌদ্ধধর্মেই ভক্তদের সামাজিক অবস্থানে ক্রমাগত ও অব্যাহত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।’ (নারায়ণ, সম্পাদিত, ১৯৮০, পৃ. ৬৮)
কুষাণ সাম্রাজ্যের সময়ে আর্যাবর্তে বহুপ্রকার চিন্তা, বিশ্বাস, ধারণা ও আচরণের সংমিশ্রণ ঘটেছিল এবং অসন্তোষ, সংশয় ও অনুসন্ধিৎসার একটা পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয়েছিল। যজ্ঞ তখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বটে কিন্তু পূজার প্রচলন ক্রমেই বাড়ছিল। ধর্মীয় ও দার্শনিক জগতের সীমা কখনও প্রসারিত হচ্ছিল, কখনও সংকুচিত হচ্ছিল। নিয়ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রভাব আত্মসাৎ করে সংমিশ্র একটি সংগঠন নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে দুটি মাত্র ধ্রুব তত্ত্ব ছিল— জন্মান্তর ও কর্মবাদ, কিন্তু এ দুটিও কোনও কোনও প্রস্থানে তৃতীয় একটি তত্ত্বের সঙ্গে সংযোজিত হচ্ছিল, তা হল, নিয়তি; আবার কোনও কোনও প্রস্থানে নিয়তি বর্জিতও হচ্ছিল। যদি নিয়তিবাদের একটি ছক আঁকা যায় তা হলে শীর্ষে থাকা আজীবিকদের বিশুদ্ধ নিয়তিবাদ, যেখানে নিয়তি আপন দুর্বোধ্য পথেই চলাফেরা করে; এখানে নিয়তিবাদ কর্ম থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একেবারে তলদেশে থাকবে, বৌদ্ধধর্ম, সেমিটিক ধর্মগুলির মত যা নিয়তিকে স্বীকার করে না, কিন্তু সেমিটিক ধর্মগুলি থেকে যার পার্থক্য লক্ষ্য করি এক বা একাধিক দেবতাকে স্বীকার করায়। এই দুই প্রত্যন্তসীমার মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এর দেবমণ্ডলী পরিবর্তনশীল, যেখানে প্রায়ই পুরাতন দেবতারা লুপ্ত হয়ে যান এবং নুতন দেবতারা মুখ্য ভূমিকা নেন। কিন্তু কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, এবং তারই সঙ্গে নিয়তি। এই নিয়তি, আমরা দেখব, কর্মনির্ভরও বটে এবং কর্মনিরপেক্ষও বটে।
সামাজিক ভাবে নগরের পত্তনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ নিয়তিবাদ। ভারতবর্ষে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের কাছাকাছি প্রথম নগরায়ণের সূত্রপাত হয়েছিল। সে সময়কার কোনও দলিল আমাদের নেই, কিন্তু অন্যান্য দেশের থেকে তা মৌলিক ভাবে ভিন্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই। বর্তমানে যতটা নজির পাওয়া যায় শস্য, কৃষি, লাঙল, কুমোরের চাক, পালতোলা নৌকো, হাতে বোনা তাঁত, তামা গলানোর পদ্ধতি, ধাতুবিদ্যা, অপ্রায়োগিক গণিত, অভ্রান্ত জ্যোতিবির্দার সমীক্ষণ, ঋতুপঞ্জি, লিপির ব্যবহার ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যান্য আদানপ্রদানের বিধি— এ সবই প্রায় একই সময়ে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের উদ্ভাবন, দু-এক শতক আগে পরে হতে পারে।
নগরের সঙ্গে বহু প্রতিষ্ঠানের একটি জটিল সংগঠন সৃষ্ট হয়। শুধু যাজকশ্রেণি নয়, কিন্তু একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণি দেখা দিল— লিপিকার, বৈদ্য, জাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা। …এদের সঙ্গেই প্রাসাদের কর্মচারীরা, যাঁরা নগরে বাস করেন এবং দেবতাদের কাছে যাঁরা অঙ্গীকারবদ্ধ।’ (মামফোর্ড ১৯৬১, পৃ. ৩৩, ৩৮; সেখানে জর্জ কঁতন্যুর একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করেছেন এক বার যখন নগর একটি গ্রামপুঞ্জের স্নায়ুকেন্দ্রের ভূমিকা গ্রহণ করল, তখন পুরোহিত ও বুদ্ধিজীবীরা প্রাথমিক উৎপাদনের দায় থেকে মুক্ত হয়ে জনসাধারণের আদর্শনির্ধারক হয়ে উঠলেন। যেহেতু যত আদিম ভাবেই হোক না কেন, রাষ্ট্র চালনার জন্য আইন তৈরি হল, তখন পূর্বকৃত পাপ দেখা দিল অপরিশোধিত ঋণের চেহারায় যা শোধ করতেই হবে, হয় এ জন্মে, না হলে পরবর্তী কোনও জন্মে, যেমন পিতার ঋণ পুত্র বা পরবর্তী প্রজন্ম শোধ করে। ঠিক সেই রকমই যেহেতু শাস্তি ও পুরস্কার বিচারকের সিদ্ধান্তেই হয়, পাপ ও পুণ্যও তেমনই সুখ দুঃখ অর্জন করে, যা এ জন্মে বা পরজন্মে ভোগ করতে হয়। স্বর্গ ও নরক রচিত হয়েছে ধনীর সম্ভোগের ও রাজা জমিদারের হাতে দরিদ্র বা ঋণীর নিপীড়নের কল্পচিত্ররূপে।
কুষাণ যুগ থেকে, কিংবা হয়তো তার দুয়েক শতক পূর্ব থেকেই, একটি সম্পূর্ণ নূতন ধর্মবিধি প্রবর্তিত হয়েছিল— এর সঙ্গে ছিল বিগ্রহ, মন্দির, ভিন্ন ধরনের নৈবেদ্য, তীৰ্থ, ব্রত, মানত, ইত্যাদি। দেবতারা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত ভাবেই তাঁদের বৈদিক ভূমিকা অর্থাৎ পার্থিব সুখ— দীর্ঘ জীবন, পশু, সন্তান, পত্নী, বিজয়, লুণ্ঠন, স্বাস্থ্য এবং সুখসমৃদ্ধিময় ইহজীবন— দান করার সঙ্গে সঙ্গেই এখন স্বর্গ এবং মোক্ষও দিতে শুরু করলেন। উপাসনার লক্ষ্য ও পদ্ধতিই যে শুধু পরিবর্তিত হল তাই নয়, জীবনের লক্ষ্যেও পরিবর্তন এল: এই পৃথিবীতে দীর্ঘ সুখী জীবনের পরিবর্তে (লক্ষণীয় এটিও কিন্তু প্রার্থিত বস্তুর তালিকায় রয়ে গেল) মানুষ এখন চাইল জন্মান্তরের অবিচ্ছিন্ন ধারাটিই যাতে ছিন্ন হয়ে যায়। এর দ্বারা গৌণ ভাবে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ লোকের পক্ষেই জীবন তখন যথার্থই দুর্বহ হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক উৎপাদকরা নিষ্ঠুর দারিদ্র্যে দিন কাটাত, আর সংখ্যালঘু অবসরভোগী শ্রেণি, পুরোহিত বা বুদ্ধিজীবীরা যারা উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে, কায়িক শ্রম থেকে মুক্ত— তারা এখন কায়িক শ্রম সম্বন্ধে শ্লেষবিদ্রুপ করতে শুরু করেছে। নিজেরা পরজীবী হয়ে অন্নদাতাদের প্রতি বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করছে। কর্মবাদ ও নিয়তিবাদের প্রসারের পক্ষে এই অবস্থাটি বিশেষ অনুকূল হয়ে দেখা দেয়। লিখিত সাহিত্যের গম্ভীরতা, যা প্রথম ও দ্বিতীয় নগরায়ণের সহচারী ছিল তার প্রমাণ মেলে সুমেরের ইপুত্বেরের (খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০–২০৫০) অনুযোগে; সেখানে পড়ি, ‘এই সুমহান (গণ্ডিযুক্ত) স্থানের (মন্দিরের) লেখাগুলি পড়া হয়, (এ হল) গুপ্ত রহস্যের স্থান…(এখন) উন্মুক্ত…জাদু প্রকাশ হয়ে পড়েছে…।’ সুমেরে পরবর্তী কালে জাদুচর্চা চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে মিশে যায়। পূর্বে ভেষজ বিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ছিল। ক্রামার বলছেন, ‘আমাদের প্রাচীন চিকিৎসাবিদ্যার দলিল… জাদুমন্ত্র ও তার উচ্চারণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, যা পরবর্তী কালের কুনেইফর্ম (শলাকালেখ) চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; সে সব গ্রন্থে কোনও একটিও দেবতা বা দানবের উল্লেখ নেই। (ক্রামার, ১৯৬৩, পৃ. ৯৭) ভাবতে ইচ্ছে করে যে, ক্রামার যে প্রাচীন শাস্ত্রের কথা বলেছেন সেগুলি নগরায়ণের পূর্ববর্তী যুগের, যখন পর্যন্ত চিকিৎসাবিদ্যা জাদু, নিয়তি, প্রেততত্ত্বের আওতার বাইরে ছিল। পরে নগরায়ণের পূর্ব-বিকাশের যুগে, এর সঙ্গে শলাকালেখ সংযুক্ত হল এবং জাদুচর্চা বিশিষ্ট স্থান লাভ করল। এবং তারই সঙ্গে এল দেবতা, দানব ও নিয়তি।
জাদু বা অতিলৌকিক ঘটনা হল ‘প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয়, মানুষের সাক্ষ্যে সমর্থিত এবং বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত’। (হিউম, কনসার্নিং হিউম্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং, পৃ. ১০)। সেন্ট অগাস্টিন বলেন, ‘সৃষ্ট প্রকৃতির বাইরে যখন কোনও কিছু করা হয়, যা আমাদের অজানা, (তখন) তা-ই আমাদের পক্ষ থেকে অতিলৌকিক ঘটনা বলা হয়।’ (সূস্মা থেওলজিয়া, ১:১১০:৪:২; সিটি অব গড-এর ২১:৮ এও আছে) মনে রাখতে হবে, আদিম মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান আসত পর্যবেক্ষণ থেকে এবং প্রকৃতির একটি বৃহৎ অংশ তার জ্ঞানের পরিধির বাইরে ছিল। যখন পূর্বে অনুপলব্ধ কিছু, বা তার জ্ঞানের পরিধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না এমন কিছু ঘটত, তখন সে তাকে অতিপ্রাকৃত বলত এবং সে সম্বন্ধে বিস্ময়বিমূঢ় সম্ভ্রম বোধ করত। কালক্রমে মানুষের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের সংখ্যা ও পরিধি কমতে লাগল, ভূত প্রেত মিলিয়ে এল এবং জাদুর ব্যাখ্যা মিলল বিজ্ঞানে। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে জাদুতে বিশ্বাস ছিল ব্যাপক। আমরা প্রথম নগরায়ণের সময়কার কথা বলছি, সেখানে জাদু মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল। এ যুগে আস্য জ্ঞানের শাস্ত্র মুখেমুখে রচিত হয়ে পরবর্তী প্রজন্মেও ওই ভাবেই সঞ্চারিত হত; জাদুর দ্বারা পুরোহিতরা সাধারণ মানুষের কাছে নির্বিচারে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল।
এর ব্যতিক্রম আজকের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রীয় গুপ্ত তথ্য ফাঁস করার তুল্য অপরাধ বলে গণ্য হত। এই পুরোহিতেরা ভবিষ্যদ্বাণী করত, এ ছাড়াও দিব্য প্রবক্তার ভূমিকায় আরূঢ় হয়ে স্বপ্নের ও ‘নিমিত্ত’র ভাষ্য দিত। পশুর অস্ত্র পরীক্ষা করত, দুনির্মিত্ত নিরুপণ করত এবং শব নিয়ে চর্চা করত। তারা নিজেদের দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বলে দাবি করত, এবং এর দ্বারা সাধারণ মানুষের নিঃশর্ত বাধ্যতা ও আত্মসমর্পণ পেত জনসাধারণ যেন এক অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করে তাদের দেখত। এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজার ও রাজন্যদের অতি কাছের লোক হত, এই পার্থিক শক্তিই আধ্যাত্মিক শক্তিকে পরিবর্ধিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করত।
নিয়তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা অজ্ঞান ও অজ্ঞেয় এক শক্তিকে উপস্থাপিত করল। নিজেদের আচরণ ও জীবনের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতার মধ্যে অসামঞ্জস্যই মানুষকে পুরোহিতদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশ্বাসপ্রবণ করে তুলত। পূর্বোক্ত ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া জানাচ্ছে, ‘নাগরিক জীবন এবং এক ব্যক্তিবিশেষ ও পরিবার বিশেষের সঙ্গে অন্য ব্যক্তি ও পরিবারের ভাগ্যের গরমিল এই বিশ্বাসের জন্ম দিল যে, বিশেষ সুখ সমৃদ্ধির কারণ যেমন কোনও দেবতার ব্যক্তিগত উৎসাহ, কোনও ব্যক্তি বা পরিবার সম্বন্ধে, ঠিক তেমনই দুঃখদুদর্শার হেতু হল কোনও কারণে কোনও দেবতার কোনও ব্যক্তি বা পরিবারকে বর্জন করা। তাই সৌভাগ্যলাভের প্রতিশব্দ হল ‘কোনও দেবতাকে লাভ করা’- যেহেতু কোনও কৃতিত্বই (দেবতার) তেমন হস্তক্ষেপ অর্জন করতে পারে না। ব্যক্তিগত দেবতা ও সিদ্ধির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থেকে সমস্যার উদয় না হয়েই পারে না, কারণ অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে যে, পুণ্য সব সময়ে পুরস্কৃত হয় না; বরং পুন্যবান লোক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে অথবা অন্য রকম দুর্ভোগ ভুগতে পারে যা শুধু পাপীর ভাগ্যেই ঘটা উচিত। স্বভাবতই যে সমাধান মনে আসে তা হল পুণ্যবান নিজের অজ্ঞাতসারে নিশ্চয়ই দেবতাকে রুষ্ট করেছে— এ ব্যাখ্যা কতকদূর পর্যন্ত মানুষ মেনে নিয়েছিল; দুঃখভোগী ব্যক্তি কোন পাপ করেছে সে সম্বন্ধে আলোকসম্পাত পাওয়ার জন্যে বহু প্রার্থনাই সে করেছে, যাতে সে প্রায়শ্চিত্ত করে আত্মসংশোধন করতে পারে। কিন্তু ব্যাপক ব্যাখ্যা হিসেবে এটি মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারেনি এবং দুঃখভোগী পুণ্যবানের যে সমস্যাটি মানুষকে অস্থির করে তোলে এ ভাবেই তার উদয় হল।’ (৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৬৫) ব্যাবিলোনিয়ার ইতিহাসের এই বিবরণে নাগরিক জীবন, পুরোহিতের ভূমিকা এবং নিয়তিবাদের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবার হেস্টিংস এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন অ্যান্ড এথিক্স লিখছে, ‘নিয়তি, সম্পূর্ণ দুৰ্ত্তেয়, সমস্ত মানুষ যে শক্তির অধীনে, তা মূর্ত বা বিমূর্ত দুই-ই হতে পারে। যখনই মানুষ কোনও যুক্তিযুক্ত প্রয়োজন বা সার্বভৌম কোনও উদ্দেশ্যযুক্ত ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে না তখনই এই কল্পনার উদয় হয়, এবং এটি ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ এ দুটি অসম্পূর্ণ ভাবে হলেও উপলব্ধ হয়, যদিও চৈতন্যের পরিসরের মধ্যেই।’ (৫ম খণ্ড, ‘ফেট’)
প্রথম সামাজিক বিভাজন যেটি ধীরে ধীরে কিন্তু অনিবার্য গতিতে অন্যান্য বিভাজনের সৃষ্টি করে তা হল দেহ ও আত্মার বিভাগ; এটির চরিত্র মূলত নৈতিক ও দার্শনিক। ক্যাসপ্রে বলছেন, ‘…দ্বিতীয় একটি মানদণ্ড, পুরোহিত সম্প্রদায়ের কাছে নতিস্বীকারের মানদণ্ড, শাস্ত্রবাক্যের কাছে ধর্মবোধের নতিস্বীকারের… এখানে বিপদ হল এই যে, এটাকে এত দূর টেনে নিয়ে যাওয়া হত যে, হীন তার স্বাতন্ত্র্য হারাত এবং প্রায় এক-সত্তাবাদের (যে সম্প্রদায় যিশুর শরীর অস্বীকার করে’ তাঁকে শুধু আত্মা, একসত্তা বলে মনে করত) মত ধর্মবোধের সোপানে অবলুপ্ত হয়ে যেত উন্নততর ধর্মচারীর দ্বারা।’ (১৯৭৯, পৃ. ১১৩) সমস্ত মানুষের চেতনাতেই একটি সহজাত ধর্মবোধ, ন্যায়-অন্যায় বিচারবোধ আছে। যখন পুরোহিত ও শাস্ত্রের নির্দেশ তার ওপরে আরোপিত হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে তখন তার সহজাত বোধ আক্রান্ত ও গৌণ হয়ে যায় এবং তার জীবন আপ্তবাক্য দ্বারা যান্ত্রিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত ও আবর্তিত হতে থাকে। এইটিই বিপদ: যে শ্রেণিবিভক্ত সমাজের আধ্যাত্মিক অধিকর্তা ছিল পুরোহিতরা, সেখানে নিম্নতর ব্যক্তির সত্তা বর্ণশ্রেণিগত ভাবে উন্নততরের কাছে বিলুপ্ত করে দিত। অর্থাৎ উন্নততর বর্গ বুদ্ধিগত, নীতিগত ও অধ্যাত্মগত ভাবে নিম্নতর বর্গকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নিত। যদি ধর্মের অধিকর্তারা নিয়তিকেই অভিজ্ঞতার সমস্ত বৈষম্যের চরম ব্যাখ্যা বলে উপস্থাপিত করে থাকে তা হলে নিয়তিবাদ একটি ধর্মতত্ত্ব বলে স্বীকৃত হবেই। শূদ্র, দাস, ম্লেচ্ছ, শবর, নিষাদ, পুলিন্দ, পুল্কস, শ্বপাক এরা সকলেই বহুদিন ধরে সমাজের নিচের তলায় ছিল। এদেরই সঙ্গে যুক্ত হল যাদের পেশা ‘নিচু’, যাদের বিত্ত সামান্য এবং যারা বহু চেষ্টাতেও কোনও ক্রমে বুঝতে পারেনি তাদের কর্ম এবং তাদের সামাজিক অবস্থানের কী সম্পর্ক। পাছে তাদের এই বৈষম্যের উপলব্ধি তাদের বিদ্রোহের প্রেরণা দেয়, তাই একটি আপাত সুবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব নির্মাণ করা হল। এটি নির্মিত হল, তিনটি স্তরে। প্রথম জন্মান্তর; এ জীবনই অস্তিত্বের শেষ কথা নয়, কাজেই মানুষের আশা করবার মতো ভবিষ্যৎ আছে। দ্বিতীয় সংযোজন হল কর্মবাদ: ‘যেমন বীজ বীনবে তেমন ফসল কাটবে’, ‘মানুষ নিজেই তার নিজের ভাগ্যবিধাতা’। আপাত ভাবে এটি আরও আশাব্যঞ্জক একটি সংবাদ যে মানুষই তার ভাবী জীবনগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। শাস্ত্র মানুষকে বলে, ‘এ জীবন তোমার নিজেরই কৃতকর্মের ফল। শূদ্র, দাস, চণ্ডাল হয়ে জন্মেছ? তাতে দুঃখের কী আছে? উচ্চ ত্রিবর্ণের সেবা কর কায়মনোবাক্যে, বিনা প্রশ্নপ্রতিবাদে, তা হলে অবশ্যই আগামী জন্মে তুমি যেমন কামনা কর তেমন ভাবেই জীবনযাপন করবে।’ জনসাধারণ এই টোপটি গিলেছিল, কারণ, এর বিকল্প কোনও সান্ত্বনা তাদের সামনে ছিল না। তৃতীয় স্তরে দেখা দিল নিয়তি। স্পষ্ট বৈষম্যের দু’ রকম ব্যাখ্যা পাওয়া গেল: নিজের কৃত কর্ম, এবং ভাগ্য তার জন্যে যা মেপে রেখেছে। এই অজ্ঞেয় তত্ত্বটিকে কর্মবাদের অন্তর্ভুক্ত করা হল, কিন্তু নিশ্চয়তাকে আরও নিশ্চিত করতে বলা হল, নিজের অগোচরে পূর্বজন্ম থেকে মানুষের বহু পাপকর্ম সঞ্চিত হয়ে থাকে, যা অপরিশোধিত ঋণের মতো কোনও না কোনও সময়ে শোধ করতেই হবে, এ জন্মে না হলে পরজন্মে। কিংবা অজ্ঞাত কোনও পুণ্যকর্মের সঞ্চয় সহসা অপ্রত্যাশিত সুখের আকারে দেখা দিতে পারে, সে হবে তার অদৃষ্ট পুণ্যের পুরস্কার। এ দুটি মিলে দুটি তত্ত্ব শেখায়, (১) জীবনে যত দুঃখই আসুক না কেন তাকে পুরনো ঋণ শোধ করার মনোভাব নিয়ে স্বীকার করে নেওয়া এবং (২) যারা মন্দ কর্ম করেও সুখে থাকে তাদের সম্বন্ধে কোনও রকম মাৎসর্যের মনোভাব পোষণ না করা, কারণ তারা তাদের পূর্বজন্মকৃত পুণ্যের ফল পাচ্ছে মাত্র, যার ফলে তারা প্রভূত ঐশ্বর্য ও বিপুল সম্ভোগের অধিকারী হতে পেরেছে। অনুক্ত শিক্ষাটি হল ‘নিজের ভাগ্যের উন্নতিবিধান কর ‘ঠিক’ লোকদের সর্বতো ভাবে সেবা করে; এবং যেহেতু কোনও কিছুই চরম নয়, তুমিও এক দিন অজ্ঞাত পূর্বকর্মের ফলে ওই রকম ভোগ করতে পারবে।’ সুখভোগের মৃগতৃষ্ণিকাকে সামনে উপস্থাপিত করে ধনী উচ্চত্রিবর্ণ তাদের ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ নিম্নবর্গের নিস্প্রতিবাদ ঐকান্তিক সেবাটা পেয়ে যাচ্ছে সমাজের সকল দুঃখী দরিদ্রের কাছ থেকে।
মানুষের দৃষ্টিতে নিরপরাধকে অকারণ পীড়া দেয় নিয়তি। শ্রমজীবী জনসাধারণ, যারা মাত্র প্রাণধারণের উপকরণটুকু পেত এবং কখনওই বহু প্রয়োজনীয় বস্তু পেত না, এবং পাওয়ার স্বপ্ন দেখার সাহসও ছিল না, তাদের ভাগ্যই হল মুখ বুঁজে আধ-পেটা খেয়ে অবিশ্রান্ত খেটে চলা এবং তাদের চেয়ে শ্রেণিবর্ণধর্মগত ভাবে যারা শ্রেষ্ঠ তারা এদের শ্রমের ফল ভোগ করে সুখে থাকবে সে কথা নির্বিচারে মেনে নেওয়া। একটি আক্কাদীয় কথাতে এই ব্যাপারটার একটা আদিকল্প পাই ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন-এ ‘…আদিতে খাদ্য উৎপাদনের জন্য দেবতাদের নিজেদেরই পরিশ্রম করতে হত, প্ৰয়োজনীয় সেচের খাল খুঁড়তে হত। শেষ পর্যন্ত তারা বিদ্রোহ করল, এবং (দেবী) ‘ত্রয়া’ এর সমাধান বের করল: কঠিন পরিশ্রমের জন্য মানুষ সৃষ্টি করল। এই উদ্দেশ্যে একটি দেবতাকে হত্যা করে তার রক্ত মিশ্রিত কাদা দিয়ে মানুষ নির্মিত হল। দেবী মহাজননী তাকে জন্ম দিলেন এবং চারদিকে উৎসব হতে লাগল।… ‘নিনমাহ’ যে (জননী) নম্মাকে প্রসবের সময়ে সাহায্য করেছিল, সে মদ্যপান করে দম্ভ প্রকাশ করল যে সে-ই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে, কে ভাল ও কে মন্দ হবে সেটা নিরূপণ করে’। (৯ম খণ্ড, পৃ. ৪৫৬) এই কাহিনিটি রচিত প্রথম নগরায়ণের সময়ে, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের উদয়ের সময়ে। এতে নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষ এবং কায়িক শ্রমের প্রতি সমাজের ওপরতলায় তাচ্ছিল্য ধরা পড়েছে। এখানে মানুষের সৃষ্টি বলতে বুঝতে হবে শ্রমিকের সৃষ্টি, যার শ্রমফল ভোগ করবে সমাজের ওপরতলার অবসরভোগী দেবতার মনুষ্য-বিকল্প, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বিত্তবান মানুষ। এই শোষণের ফলে ওই সুখী শ্রেণির সর্বাঙ্গীণ আরাম ও সমৃদ্ধ বাড়ে। কাজেই দেবতা মানুষের সম্পর্কের আদিকল্প হল প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক, কায়িক শ্রমের জন্যেই দেবতারা মানুষকে নিচুতলার শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করল। শুধু তা-ই নয় দেবী নিনমাহ দম্ভভরে বলে যে, মানুষের সুখদুঃখের ও ভাগ্যের চাবিকাঠিটি শুধু তারই কাছে আছে। এখানে ‘ভাগ্য’ দেবীরূপে দেবমণ্ডলীতে স্থান পেয়েছে।
নগরায়ণের সঙ্গে নিয়তিকে যুক্ত করতে আমাদের এই আগ্রহ কেন? কারণ ঐতিহাসিক সাক্ষ্যে এ দুইয়ের যুগপৎ উদ্ভভ ঘটেছিল। ম্যাকমিলান এনসাইক্লোপিডিয়া লিখছে, ‘যে সব সভ্যতা প্রাথমিক শস্য উৎপাদনের স্তরের পূর্বে ছিল সেগুলিতে ধর্মগত ভাগে কেন্দ্রস্থানীয় নিয়তিবাদের কোনও চিহ্ন নেই। এবং মৃগয়াজীবী কোনও সভ্যতাতেই নিয়তিকে ধর্মীয় ভাবে কোনও তাৎপর্যপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়নি।’ (‘ফেট’ শীর্ষক আলোচনায়) কাজেই নিয়তিবাদ নগরায়ণের পরে পরেই আসে। নগর কিছু পরিমাণ শারীরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অধিবাসীদের জন্যে, কিন্তু এখন আমরা জানি যে, এর মূল সংজ্ঞা অনুসারেই নগরবাসীদের তিন-চতুর্থাংশই প্রাথমিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে প্রাথমিক উৎপাদক চাষির ওপরই নির্ভরশীল ছিল। এই চাষিরা অধিকাংশই নগরের বাইরে কৃষিভূমি-সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করত। নগরের মধ্যে শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও ছিল জাতিবর্ণ বিভাগ, যা ক্রমেই তীক্ষ্ণতর, কঠিনতর ও অনমনীয় হয়ে উঠেছিল। তার পরে কখনও খরা, বন্যা, অজম্মা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে, অভুক্ত শ্রমিক সাধারণের বিদ্রোহের প্রকাশ ও অবাধ্যতার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠত। সে সব বিদ্রোহের ইতিহাস পরবর্তী কালে পৌঁছায়নি, শুধু কিছু অতিকথায় উপকথায় তাদের ছায়া রয়ে গেছে।
আমরা দেখেছি প্রাচীন পৃথিবীতে প্রথম নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে বীজাকারে নিয়তিবাদের অতিকথার সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে এটি স্পষ্ট কোনও স্বাক্ষর রেখে যায়নি। কারণ প্রথমত, সিন্ধুসভ্যতা থেকে লিখিত সাহিত্য খুব বেশি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, যা পাওয়া গেছে তার থেকে তৎকালীন চিন্তার উপাদান খুব কমই পাওয়া যায় এবং তাদের বস্তুগত জীবনের কিছু তথ্য-সাক্ষ্য আছে তাতে। সীলমোহর, ধাতুপত্র, সিলিন্ডার, এগুলি প্রাথমিক ভাবে উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথাই বলে; সিন্ধু-সভ্যতার মনোজগতের চিহ্ন তাতে কমই আছে। হয়তো সঞ্চারণের দ্বারা এর কিছু কিছু উপাদান পরে সংমিশ্র ব্রাহ্ম্যণ সংস্কৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গেছে।
ঘোষ লিখছেন, ‘পরবর্তী কালের নগরগুলিতে, তার ‘দ্বিতীয় নগরায়ণে’, ভারতবর্ষকে সহস্রাব্দেরও বেশি প্রতীক্ষা করতে হয়েছিল— খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত; এই সময়ে যুগপৎ তার ঐতিহাসিক যুগেরও সূচনা হয়।… খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক যা আর্যাবর্তের পক্ষে একটি যুগান্তরের সূচনা করে… (সেই সময়) জনপদগুলির প্রতিষ্ঠাই বেদের শেষাংশের নতুন সমাজের একটি ফল যেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা উভয়েরই ভূমিকা ছিল, হয়তো অর্থনৈতিক দিকটা পশ্চাৎপটে ছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার প্রধান সহায়ক রূপে।’ (১৯৭২, পৃ. ২, ১৩, ২২) এই যুগে ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নগরায়ণে দেখা দিল লিপি, নানা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মতের সম্প্রসারণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঞ্চয়, গোষ্ঠীগত সমাজের অবক্ষয় এবং এরই ফলে একটি নতুন ধরনের সামাজিক নৈতিক, আধ্যাত্মিক অস্থিরতা এবং একটা নিরাপত্তার অভাববোধ। এ সবের দ্বারাই নতুন চিন্তা, বিশ্বাস, বিশ্বাসকেন্দ্রিক সম্প্রদায় ও আনুষ্ঠানিক আচরণের জমি প্রস্তুত হল। এ যুগে যা বীজাকরে ছিল বেশ কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল তার পূর্ণ বিকাশের জন্যে। কিন্তু সারা আর্যাবর্তে এ সময়ে যে আধ্যাত্মিক আলোড়ন চলেছিল তার ফলে তৎকালীন যাজ্ঞিক ধর্ম সম্বন্ধে মোহমুক্ত মানুষের মধ্যে থেকে বহু সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হল। প্রথম নগরায়ণের যুগ থেকেই সন্ন্যাসিত্ব কোনও না কোনও রূপে সম্ভবত একটি অন্তঃসঞ্চারী উত্তরাধিকার হিসেবে ছিল। যখন যজ্ঞনির্ভর ধর্মে লোকে আস্থা হারাল, তখন দু-এক শতাব্দীর মধ্যেই বিকল্প উপাসনা পদ্ধতি তার নিজস্ব শাস্ত্র ও অনুষ্ঠানসমেত আত্মপ্রকাশ করল। সন্ন্যাসধর্মের যে ঐতিহ্য নগরের বাইরে প্রচলিত ছিল— অরণ্যে আশ্রমে, ভ্রাম্যমাণ যতিসম্প্রদায়ে— তা যজ্ঞক্রিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া; এর সঙ্গে অরণ্যস্থ সম্প্রদায়ের একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আশ্রমধর্মের শেষ দুটি আশ্রম বানপ্রস্থ ও যতি— ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার স্বীকৃত ও গৃহীত হয়, কারণ আরণ্য ধর্মজীবন বহু গৃহীকে সমাজের বাইরে এনেছিল, এ ব্যবস্থায় সেটার আর প্রয়োজন রইল না।
এ কে নারায়ণ বলছেন, শ্রমণ ঐতিহ্য নগরের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত; নগরগুলি নতুন শিল্পায়নের অগ্রগতির ফলে গড়ে ওঠে, কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্বৃত্ত এবং তার ফলস্বরূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃদ্ধি ঘটে। এই নগরায়ণ বস্তুগত সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে; (আবার) সমৃদ্ধির নিয়মে চাহিদা ও জোগানের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দেখা দেয় সংঘর্ষ, জীবনের আততি থেকে জাগে দুঃখ বেদনা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অভাব। যে সব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ সম্পদ সংরক্ষণের জন্য মানুষের স্বাভাবিক উদ্বেগ হচ্ছিল, যা বিলাসীর বর্বর ভোগসুখের ও ক্রীড়ার জন্যে বিনষ্ট হচ্ছিল, নগরের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে তা ধ্বংস হচ্ছিল। দ্বিতীয় নগরায়ণের যুগে নগরের পরিকল্পনা, স্থাপত্যের আদিমতম কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় বৌদ্ধ ও জৈন উৎসে, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে নয়।’ (হরদয়ালের দ্য বোধিসত্ত্ব ডকট্রিন ইন বুটিস্ট স্যাংস্ক্রিট লিটারেচার-এর ভূমিকা, পৃ. ২৬–২৮) পশুযাগে গোধনের খেয়ালি অপচয় এমন এক সময়ে হচ্ছিল, যখন লোহার লাঙলের ফলার বহুল প্রয়োগের সঙ্গে পশুধন সংরক্ষিত হলে অধিকতর ধন উৎপাদনের সহায়ক হত। কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্য অরণ্যানী দগ্ধ করার ক্ষেত্রে এবং পরাজিত অনার্য জনসমূহের একটি বৃহৎ অংশকে ক্রীতদাসে পরিণত করাতে বাধা পাওয়ার ফলে এই সময়ে ধর্মে, দর্শনে ও সমাজ চিন্তায় একটি দিক-পরিবর্তনের সূচনা হয়, দেখা দেয় নূতন মূল্যবোধ ও সমাজচেতনা। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক ও খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের মধ্যে বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। গ্রান্ট-এর মতে ‘সংমিশ্রণের পদ্ধতিটি নিশ্চয়ই খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যেই শুরু হয়ে যায়, সেই সময়, যখন পারসিক সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ঘটে, এবং তখন থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটি স্তর পার হয়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি এসে দেখি বৃহৎ পরিসরের মধ্যে চিন্তার আনাগোনা দীর্ঘদিন চলে আসছে এবং প্রায়ই এমনই অলক্ষিত ভাবে যে, কোথাও কোথাও ‘কিছু আত্মসাৎ করার’ চেতনাটি পর্যন্ত নেই।’ (১৯৬১, পৃ. ৩৪)
গর্ডন চাইল্ড তাঁর ‘দ্য আর্বান রেভোলুশন’ প্রবন্ধে (পৃ. ৩–১৭) প্রথম নগরায়ণের একটি বিবরণ দিয়েছেন যাতে আছে ‘নগরগুলির আকৃতি, ঘন জনবসতি, শ্রমিকদের যানবাহন, বণিক, কর্মচারী ও পুরোহিতদের কথা। নগরের কেন্দ্রে থাকত একটি রাজপ্রাসাদ এবং / বা মন্দির, যেখানে এসে পৌঁছত প্ৰাথমিক উৎপাদকের যৎসামান্য উদ্বৃত্ত। একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ ছিল বৃহৎ সৌধনির্মাণ, যা সমাজের উদ্বৃত্তের প্রতীক হয়ে উঠত।’ অনুৎপাদক (শিল্পকর্মে ব্যাপৃত কর্মী ও কখনও কৃষিজীবীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ বাদে) জনতা বেঁচে থাকত মন্দির বা রাজকীয় শস্যভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত অন্নে। পুরোহিত, সেনানী এবং সমাজমুখ্যরা সমগ্র উদ্বৃত্তের একটি বৃহৎ অংশ ভোগ করত, এবং একত্রে মিলে এরাই ছিল শাসকশ্রেণি। এই শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে দলিল রক্ষণের পদ্ধতি ও অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উপযোগী অন্যান্য বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছিল— যেমন গণিত, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ। সমাজের এই নূতন প্রয়োজনের তাগিদেই লেখন-পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল মিশরে, মেসোপটেমিয়ায়। চাইল্ডের মতে নগরের শিল্প শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের জোগান আসত নগর থেকেই। সেখানে ছিল ‘অনেক বেশি সংহতি, অনেক জটিল শ্রমবিভাজন, বেশি মাত্রায় ধর্মনিরপেক্ষ বিশেষ চর্চার অবকাশ, মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিকাশ, অনেক কম সুনির্দিষ্ট পারিবারিক সম্পর্ক ও অপেক্ষাকৃত শিথিল সামাজিক পরিবেশ, নির্ব্যক্তিক নিয়ন্ত্রণ, প্রতিষ্ঠানগুলির উপরই ছিল তার নির্ভরতা।’
এ সব লক্ষণের অধিকাংশই ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নগরায়ণে পুনর্বার দেখা দেয়, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে। এ পদ্ধতি একবার শুরু হয়ে যাওয়ার পর অব্যাহত গতিতে চলল খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত এবং তত দিনে এটি একটি নির্দিষ্ট আকৃতি লাভ করেছে। আরও বিশেষ ভােেব বললে, কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মধ্যে এ ব্যাপারে একটি যুগান্তর ঘটে, বিশেষত, মহাভারতে ভার্গব সংযোজনের কালে। এই বিশেষ অংশটি সাম্প্রদায়িক পুরোহিতদের রচনা, যারা জন্মান্তর ও কর্মবাদকে একটি পরিণত ও স্থায়ী রূপ দান করতে চেয়ে নিয়তিবাদকে এর সঙ্গে সংযুক্ত করে। জন্মান্তর ও কর্মবাদ দিয়ে যার ব্যাখ্যা হয় না তা-ই বিধৃত হল নিয়তিবাদে এবং জন্মান্তর ও কর্মবাদের সঙ্গে মিলে নিয়তিবাদ এমন একটি ছক নির্মাণ করল যা আজও অব্যাহত আছে।
দেখা দিল পরলোকতত্ত্ব, স্বর্গ, নরক, মোক্ষ ও পরিত্রাণতত্ত্ব, তীর্থ, ব্রত, মানত, মন্দির, ধ্যানজপ-ভক্তিসহ পরিত্রাতা ইষ্টদেবতার বিগ্রহপূজা; এগুলি পূর্বতন সমষ্টিগত যজ্ঞ বা পূজার উপাসনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। দানদক্ষিণা, পুণ্যার্জনের উপায়রূপে, ওঝার ভূত ঝাড়া, দেবতার ভর, ধরনা, ভবিষ্যদ্বাণী, দৈববাণী, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের দ্বারা মৃতদের আত্মিক উন্নতির প্রয়াস, প্রায়শ্চিত্ত, শাপ ও বর, দিব্যশক্তি ও সাধারণ লোকের মধ্যে মধ্যস্থতার উপায় হিসেবে পুরোহিতকুলের গণ্য হওয়া, পুণ্য বিনিময় এই সবই দেখা দিল একে একে। মোটের ওপর সেই চার শতকের মধ্যে, যে সময়ে ভার্গব সংযোজন সৃষ্ট হয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন সংজ্ঞা ও একটি জটিল রূপ পরিগ্রহ করে যা পরে পুরাণগুলিতে বিস্তার লাভ করে। এবং এ সবের মধ্যে নিয়তিবাদ এমন একটি অমোঘ শক্তি অর্জন করল যা গত দেড় হাজার বছর ধরে অক্ষুণ্ণ আছে।
সংজ্ঞা থেকেই নিয়তি দুৰ্জ্জেয়; কিন্তু মানুষ তো বুদ্ধিমান জীব, তাই সে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে চলেছে ওই রহস্যের জালটি ভেদ করবার জন্য। এর অভিমুখে তার প্রযত্ন দু’ ধরনের: প্রথম, আসন্ন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও পূর্বাভাস বা প্রাগবোধ লাভ করা এবং দ্বিতীয়ত, ভাগ্যের গতির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া— প্রায়শ্চিত্ত, প্রসাদন ও বৈকল্পিক প্রচেষ্টার দ্বারা। নিয়তি যদি অপ্রতিরোধ্য হয় এবং তত্ত্বগত ভাবে সে তা-ই বটে— তা হলে তাকে ব্যাহত বা প্রতিহত করার জন্যে মানুষের সব চেষ্টাই বালুকাসৌধ নির্মণের মতো নিষ্ফল। তবু যারা ভাগ্যহত তারা এ সব থেকে সান্ত্বনা পায় ভাগ্য ফেরাবার জন্যে যা হোক কিছু করছে এই ভরসায়, এবং পুরোহিতশ্রেণি নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা পায় সাধারণ মানুষের কাছে।
কিন্তু মানুষের অন্তঃস্থিত শৌর্য নিয়তির রায় মানতে প্রস্তুত ছিল না। এবং ওই সব শাস্ত্রই আলোচনা ও কাহিনির মাধ্যমে প্রতিকূল দৈবের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের সাক্ষ্য দেয়। মানুষ সদম্ভে ঘোষণা করে যে, শুধু স্বাধীন ভাবে ইচ্ছা করাই নয়, সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার শক্তিও সে রাখে এবং এ ভাবে দৈবকে প্রতিহত করতে পারে। শাস্ত্র ও পুরোহিত একযোগে চেষ্টা করেছে মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিক গর্বকে চূর্ণ করতে, এবং এ চেষ্টায় তারা প্রায় সফলও হয়েছে: মুক্তদৃষ্টি নিয়ে মানুষ এ সব তত্ত্বের অন্তর্বিরোধ এখনও নিরূপণ করতে পারেনি; আর যদি পেরেও থাকে, কখনও যথেষ্ট সাহস সংগ্রহ করতে পারেনি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাস্ত্র পুরোহিতের যুগ্ম চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিস্পর্ধা প্রকাশ করতে। আবার এ-ও সত্য যে, যদিও প্রকৃতি ও মানুষ সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্বে যাকে নিয়তি বলা হত তার অনেকটাই এখন ভিন্ন ভাবে প্রতীত হয় এবং মানুষের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, তবুও এমন বহু অদৃষ্ট এবং অদৃশ্য আপতিক দুর্ঘটনাও আছে, যার ওপরে মানুষের সত্যিই কোনও কর্তৃত্ব নেই। প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, যুদ্ধ এবং সাধারণ দৈনন্দিন বিপৎপাত চিরদিনই বেশির ভাগ মানুষের কর্তৃত্বের বাইরে থেকে যাবে। কাজেই একটা অঞ্চল থেকেই যাবে যেখানে অদৃশ্য ভাবে অলক্ষিত বিপদ গুঁড়ি মেরে আসবে এবং হঠাৎ মানুষকে কাবু করে ফেলবে। কিন্তু যদি লক্ষ্য করি, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় সহস্রাব্দে মানুষ যাকে নিয়তি বলত, তার কতখানি আজ মানুষের জ্ঞান ও শক্তির আয়ত্তের ভেতরে এসে গেছে, তা হলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রতি প্রজন্মে মানুষের সমবেত চেষ্টা কত তথাকথিত দুরারোগ্য রোগকে পরাজিত ও নির্বাসিত করেছে, ব্যক্তির ইচ্ছা ও প্রয়াস মানুষের জীবনের কত অঞ্চলে যে অসাধ্য সাধন করেছে তার ইয়ত্তা নেই। এখন মুখ্যত যা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি রূপে মানবসমাজের কাছে প্রতিভাত, তা হল সারা পৃথিবীর ওপরতলার শাসনকর্তারা নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে ও সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে পরাজিত করবার জন্যে বিজ্ঞানের নবতম, যুগান্তকারী উদ্ভাবনগুলিকে জেনেশুনে সুপরিকল্পিত ভাবে সাধারণ মানুষের ধ্বংসের জন্যে ব্যবহার করছে। এক দিকে তা যেমন ভোগ্যপণ্যে দৃষ্টিকটু অথচ সর্বাত্মক আসক্তি জন্মাচ্ছে, তেমনই অস্ত্রনির্মাণে, রোগজীবাণু সৃষ্টিতে, স্বাস্থ্যহানিকর পরিকল্পনায়, পরিবেশদূষণে, পরিকল্পিত মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার প্রবর্তনায় পৃথিবীর সম্পদ বিনিয়োগ করছে, যাতে ওপরতলার মুষ্টিমেয়রা সব দেশে ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারে ও সংখ্যাগরিষ্ঠরা অসহায় ভাবে মরে। এ পর্যায়ে সংগ্রামটা রাজনীতিতে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। অথচ এই রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতিতেই তো লক্ষ্য করি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের একাগ্র ও সংহত প্রচেষ্টা হিটলারের মতো আপাত-অজেয় মূর্তিমান দুর্দৈবের মতো মন্ত্রশক্তিকে পরাহত করেছে। ধূমকেতুর মতো বহু মন্দ শক্তি রাষ্ট্রগগনে বার বার উদিত হয়ে বহু ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমবেত শুভ চেষ্টার কাছে হার মেনেছে।
সত্যিই যে বস্তুটির অভাবে অমঙ্গল কিছুকাল আধিপত্য করতে পারে তা হল সমবেত মঙ্গলচেষ্টা এবং মানবসমাজ থেকে দুর্দশাকে সম্পূর্ণ নির্বাসন দেওয়ার দৃঢ়, সক্রিয় সংকল্প। বহু কায়েমি স্বার্থ এ পথে বাধা হয়ে রয়েছে; তবু মানুষ কখনও আশা করতে বিরত হবে না যে, সমবেত উদ্যমে সে কোনও দিন নিয়তিবাদকে অজেয় ভয়াবহ শক্তির স্থান থেকে হটিয়ে দিতে পারবে। তত্ত্ব হিসেবে নিয়তিবাদের মূল প্রোথিত আছে ওই কায়েমি স্বার্থেরই মধ্যে, সমাজশাসকদের, পুরোহিত ও শাস্ত্রকারদের মধ্যে, যাদের ধমক ও প্রতারণা অজ্ঞান মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো করে রাখে এবং এই সংগ্রামে তারা জেতে। মানুষের দুর্বলতর ভীরু সংস্কারাচ্ছন্নকে লালন করে, এ সব সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন যুগে এবং ক্রমেই বহুগণিত হতে থাকে। অতএব জ্ঞান যদি কোথাও শক্তি হয়ে থাকে, তবে তা এখানেই; শুভ ইচ্ছাই সে জ্ঞানের ফল, সুসংহত শুভ ইচ্ছাই অপরাজেয় শক্তি।
মানুষ জীবনে এক বারই মাত্র বাঁচে এবং পূর্বজন্মের কোনও সঞ্চিত কর্মফলের বোঝা তার পিঠে চেপে নেই; তার জীবনের গতিপ্রকৃতি মূলত নির্ধারণ করে সে নিজে আর তার সামাজিক পরিবেশ এবং এই একটি মাত্র জন্মেই কোনও অজেয় শক্তি তার ভাগ্য নিরূপণ করে না। তার ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত, এবং এটি তার একটি অনপনেয় অধিকার, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। এক বার এই অবস্থান গ্রহণ করলে মানুষ তার স্বাধীনতার ও সর্বাঙ্গীণ সুখবিধানের সপক্ষে দাঁড়াবে, যার মধ্যে নিহিত আছে মানবিক সীমার বোধ, কিন্তু যা তাকে নিয়তির আতঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মানুষের এই গর্ব প্রকাশের অধিকার রয়েছে যে, ইচ্ছা করা এবং সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার শক্তি ও স্বাধীনতাও তার আছে। তথাকথিত নিয়তির ওপরে তার সামান্যতম জয়ও সমগ্ৰ মানবজাতির আত্মিক সংগ্রামকে মহিমান্বিত করবে।
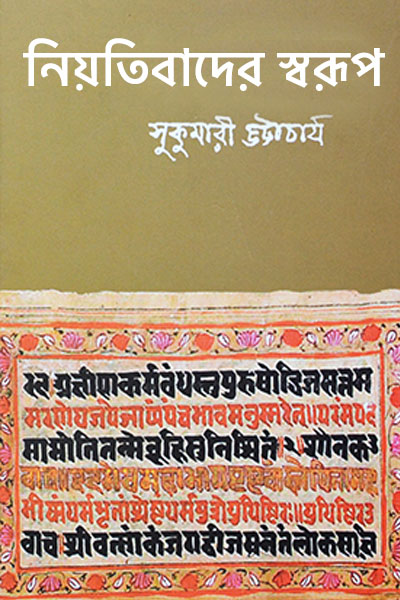


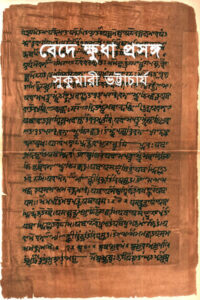
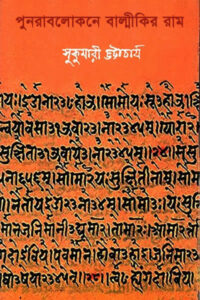

Leave a Reply