নিকষিত হেম (অনুগল্প গ্রন্থ)
১. গুড ইভেনিং আঙ্কেল
আমার এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র ভাই একদিন আমাকে অনুরোধ করে বলেছিল — বিকাল এবং সন্ধ্যা রাত্রিতে তুমি তো ফ্রী-ই থাকো, তোমার যদি কোনো অসুবিধা না থাকে, হাতিরপুলে আমার এক আত্মীয়ের একটি বাচ্চা মেয়েকে বাসায় যেয়ে তুমি কী একটু পড়াতে পারবে? মেয়েটি ক্লাস ওয়ানে পড়ে। এ জন্য তুমি ভালো সম্মানীও পাবে।
একটি বাচ্চা মেয়েকে পড়াতে হবে। শুনে খুব ভালো লাগল……. আমারও তো একলা সময় গুলো ভালো কাটতে পারে। আমি তার প্রস্তাবে বিনা বাক্য ব্যয়ে রাজি হয়ে যাই।
একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার সেই সিনিয়র ভাইটির সাথে হল থেকে হেঁটে হেঁটে চলে যাই হাতিরপুলের সেই বাড়িতে। মেয়েটির বাবা মা বললেন কিছু অদ্ভুত কথা — তাদের মেয়েটির সাথে রোজ সন্ধ্যাবেলা অন্ততঃ এক দেড়ঘন্টা এসে গল্প করতে হবে । গল্পের ছলে একটু পড়িয়ে দিলে হবে। মেয়েটির নাম সঞ্চিতা।
সঞ্চিতা খুব একলা মেয়ে। বাবা মা দুজনে চাকরি করেন। অফিস থেকে ফিরে সঞ্চিতার অজস্র প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন না দুজনেই। ক্লান্ত লাগে। যেমন, হাতি কালো কেন ? আল্লাহকে দেখতে পাই না কেন? সুমীর মা অত খেতে পারে কি করে? আমার একটি ছোট্ট ভাই নেই কেন? এ একেবারেই যেন রবি ঠাকুরের কাবুলিওয়ালার মিনির ডুপ্লিকেট ।
সঞ্চিতা বলছিল, তুমি কাল থেকে আসবে তো আঙ্কেল?
সঞ্চিতার মা বলে উঠলেন — তুমি নয় সঞ্চিতা, আপনি বলো ওনাকে। সম্মান করে কথা বলতে হয়।
সঞ্চিতা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে……..
আমি সঞ্চিতাকে একটু কাছে ডেকে পাশে বসাই। ওকে বলি — ঠিক আছে, তুমি যা কিছু আমাকে ডেকো এবং বোলো।
এরপর প্রায়ই সন্ধ্যাবেলায় আমি সঞ্চিতাকে পড়াতে যাই, কিংবা ওর সাথে গল্প করতে যাই। সঞ্চিতা রূপকথা শুনতে খুব পছন্দ করত। রোজই কিছু না কিছু আবদার থাকে সঞ্চিতার। ‘আঙ্কেল তুমি সেই মুনিয়া পাখির গল্পটা আরেকবার বলো।’
আমি সঞ্চিতাকে মুনিয়া পাখির গল্প শোনাই —
‘একবার সৃষ্টিকর্তা ঠিক করলেন , সব পাখিদের মনের মতো রং করে দেবেন গায়ে। যে যেমন চাইবে সেরকম রং করা হবে। আবদার মতন, কাককে কালো, বককে সাদা, টিয়াকে সবুজ, ময়ূরকে নীল …. এরকম করে দিচ্ছিলেন। মুনিয়া বারবার ওড়াউড়ি করে দেখছিল আর কত বাকি ? তার লাইন শেষের দিকে। মুনিয়া পাখি ছিল সঞ্চিতার মতো চঞ্চল । ছটফট করতে করতে আবার উড়ে গেল আকাশে । ভাবল একটু ঘুরে আবার আসবে। তারপর ….. তারপর যখন এল তখন দেখল আর কোনই রং নেই। সব পাখিরাই রং পেয়ে গেছে। অল্প একটু রংয়ের ছিটে চারিদিকে পড়ে ছিল। সৃষ্টিকর্তা তাই পাখির পেটের দিকে আর পালকের দিকে একটু একটু দিয়ে দিলেন। তাতেও মুনিয়া খুশি। দেখে সে বেশ সুন্দর লাগছে।’
আমি যেন ওকে বেশি করে সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্প শোনাই এ জন্য সে আমাকে প্রায়ই খুশি করত। ক্যাডবেরী চকলেট আমি যে খুব পছন্দ করতাম। এই কথাও জেনে গিয়েছিল সঞ্চিতা। সঞ্চিতা ওর নিজের চকলেট গুলো আমাকে চুপিচুপি খেতে দিত। তাছাড়া, বাগান থেকে ফুল, ঝাউপাতা ছিঁড়ে রাখত আমার জন্য। আমার হাতের মুঠোর ভিতরে ফুল গুঁজে দিয়ে বলত — ‘গুড ইভিনিং আঙ্কেল।’
দিনে দিনে আমি আর সঞ্চিতা কেমন যেন সন্ধ্যাবেলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যাই। কী এক অদ্ভূত টানে হেঁটে হেঁটে প্রতি সন্ধ্যায় চলে যেতাম। ছোট ভাই-বোনহীন এই শহরে সঞ্চিতাকে খুব আপন করে নেই। আমি সঞ্চিতার ভিতরেও আমার প্রতি একটি নিগুঢ় টান দেখতে পাই। এমন করেই চলে গেল দুই বছর। সঞ্চিতা এখন তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রী।
গরমের ছুটিতে সেইবার বাড়িতে চলে আসি। দুই মাস ক্লাস হবে না। বাড়িতে এসে কেমন খালি খালি লাগছিল। মনে হচ্ছিল কী যেন একটি রূপার ছোট্ট পুতুল ঢাকায় ফেলে রেখে এসেছি। সেই পুতুলটি মুনিয়া পাখির মতো। ফুল বাগানের ডালে বিষণ্ন হয়ে হয়ত সে বসে আছে।
ইতোমধ্যে আমার গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে যায়। আমি ঢাকা চলে আসি। এসেই সন্ধ্যাবেলায় হল থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সঞ্চিতাদের বাসায় চলে যাই। বাসায় ঢুকতেই দাড়োয়ান বলে ওঠে — ‘সঞ্চিতা’রা আর এখানে থাকে না। ওর বাবা মা দু’জনেরই বদলি হয়ে গেছে। ওরা এখন চট্টগ্রামে থাকে।’
মনটা খুবই বিষণ্ন হলো। হাত পা চলছিল না। তবুও আলোছায়ার পথ ধরে হলে চলে আসি।
কয়েকদিন ঠিকমতো ক্লাশে যেতে পারিনি। বালিশে মুখ গুঁজে চুপচাপ শুয়ে থাকতাম। একটা বাৎসল্য প্রেম এত কষ্ট দেয়, এ বেদনা জীবনে প্রথম বুঝতে পারলাম। মানুষকে ভুলে থাকা যায়, মানুষের মায়া মমতাকে ভুলে থাকা যায় না।
তারপর চলে গেছে তেত্রিশ বছর।
জীবনের মোড়ে মোড়ে কতো কিছু হলো। কতো মানুষ এল। বিয়ে করলাম। আমাদের ঘরেও সঞ্চিতার মতো মেয়ে এল। কিন্তু কবেকার সেই ছোট্ট একটি বালিকা অন্তরের এক কোণে ঠাঁই করে নিয়েছিল। তাকে ভুলতে পারলাম না। ওকে প্রায়শ মনে পড়ত। যে নিতান্তই ক্ষণকালের জন্য ছিল। সেই বহু বিস্মৃত নিষ্পাপ মুখখানি মনে পড়ে বিচলিত হয়ে উঠতাম। না জানি কোথায় সে এখন কতো বড়ো হয়ে আছে! অতটুকুন মেয়ে কী আমাকে মনে রেখেছে?
একদিন অনেকটা আলস্যে শুয়ে শুয়ে ফেসবুকে নিউজফিড স্ক্রল করে করে দেখছিলাম। হঠাৎ কোনো এক সঞ্চিতার একটি স্টাটাস চোখে পড়ল –
‘ আমি তখন তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের বাসা ছিল ঢাকার হাতিরপুলে। কবি জসীম উদ্দিন হল থেকে একটি ছেলে এসে আমাকে পড়াত। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তাকে আমি আঙ্কেল ডাকতাম। নাম রঞ্জন রহমান। কেউ কী তাঁর কোনো খোঁজ দিতে পারেন?’
কেমন যেন বিচলিত হয়ে উঠল মন।
কবেকার সেই স্নেহের ফল্গুধারা আজও দুচোখ বেয়ে ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল।
২. ২৪ নং দক্ষিণ গাঁও
বর্ষার সন্ধ্যা রাত্রি। একটি মেয়ে বাস থেকে স্ট্যান্ডে নামে। স্ট্যান্ডে কোথাও একটি রিক্সা নেই। মূসুলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাগ থেকে সে ছাতা বের করে। এত বৃষ্টি যে ছাতা মানছিল না। পরনের শাড়ি ভিজে একসারা হয়ে যাচ্ছিল। পথে পথচারী তেমন কেউ নেই। একটি কাভার্ড ভ্যান গায়ে পানি ছিটিয়ে দ্রুত চলে যায়। সে হেঁটে হেঁটে সামনের মহল্লায় গলি মুখে প্রবেশ করে। এই গলিতে এর আগে কখনো সে আসেনি। লাইটপোস্ট গুলোতে কোনো বাতি নেই। একটি নেরি কুকুর ভুগভুগ করে পাশে দিয়ে চলে যায়।
মেয়েটি খুঁজছে চব্বিশ নং বাড়ি। ২৪ নং দক্ষিণ গাঁও। অদূরে একটি বাড়ির সামনে চালার নীচে একজন ঠেলা গাড়িওয়ালা জড়োসরো হয়ে বসে আছে। এগিয়ে গিয়ে তার কাছে থেকে সে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় কোনটি চব্বিশ নং বাড়ি।
মেয়েটি একটি টিনশেড পুরোনো শ্যাওলা পড়া বাড়ির সামন চলে আসে। বাড়িটির বাহিরের দিকে দরজা। আলাদা কোনো গেট নেই। তখনও বৃষ্টি হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল ঘন ঘন। সে বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের ভিতরে তখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে কেউ একজন এই গানটি গাইছিল —
‘এসো এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে।
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এসে আমার ঘরে।’
মেয়েটি দরজায় কড়া নাড়ে কয়েকবার। ভিতরে থেকে বিষাদের সুরে ভেসে আসা গানটি হঠাৎ থেমে যায়। একজন উম্মূল উদ্বাস্তু যুবক দরজা খুলে দেয়। বাইরে চমকিত বিদ্যুতের আলোয় যুবকটি দেখতে পায় মেয়েটির মুখ। সে বিস্ময়ে বলে ওঠে — ‘নেলী, এত রাতে তুমি? এই দূর্যোগের রাতে তুমি একা আমার ঘরে?’
নেলী বৃষ্টি ভেজা শীতল কপাল যুবকটির বুকে ঠেকিয়ে বলে — ‘ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে আমি তোমার ঘরে চলে এলাম।’
যুবকটি যক্ষা রোগে আক্রান্ত। ওর নাম মোহাম্মদ আনিস। ভালো গান গাইত তারুণ্যের সময়। গান গাইতে গাইতে গানের শিক্ষক হয়ে যায় সে। আনিস নেলীকে গান শেখাত।
হারমোনিয়ামের রিডে ছুঁয়ে থাকা জীবনে কখন যে এই চালচুলোহীন সঙ্গীত শিক্ষককে নেলী ভালোবেসে ফেলেছিল বুঝতে পারেনি। তারপর কত রোদেলা পাখি উড়ে আসল, কত সমুষ্ণু বাতাস বয়ে গেল! সন্ধ্যার মেঘের ছায়াও পড়ল বুড়িগঙ্গার জলে। কিন্তু দুইজন আর দুজনের কাছাকাছি থাকতে পারেনি। আনিসকে অবাঞ্চিত করে দেয় নেলীর পরিবার।
এক হেমন্তের শেষ বিকেলে আনিস তার শেষ সুরটি তুলে দিয়েছিল নেলীর কণ্ঠে এই গানটি দিয়ে —
‘এসো এসো আমার ঘরে এসো
আমার ঘরে
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে
স্বপন দুয়ার খুলে এসো…..’
আর সেই দিনের সেই নিস্তব্ধ বিকালের নীরবতাকে স্বাক্ষী রেখে নেলী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল — ‘আমি একদিন তোমার ঘরে চলে আসব।’
তারপর চলে গেছে আরও কয়েক বছর। মরণ ব্যাধি যক্ষা এসে বাসা বাঁধে আনিসের শরীরে। এর জন্য দায়ী সে নিজেই। অনিয়ম আর অত্যাচার করেছে নিজের শরীরের প্রতি। আনিস নেলীকে বলছিল — ‘ তুমি এই অনিষ্ট জীবনের ভার নিতে পারবে না। আমার এখন সায়াহ্ন কাল। তুমি ফিরে যাও।’
আনিস কাশছিল বেশি করে। কাশতে কাশতে হাঁপিয়ে উঠছিল বারবার। এত ক্লান্তি এত দুর্দশা জীবনে। নেলী এবারও তার বুকে মাথা রেখে বলে — ‘না, যাব না। ছিন্ন করে সব চলে এসেছি। আমি তোমার ঘরেই থাকব। আমি আমার সকল যত্ন দিয়ে তোমাকে ভাল করে তুলব।’
নেলী আরও বলছিল, ভোর হওয়ার আগেই আমাদের এখান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে হবে। বাড়ি থেকে লোক অথবা পুলিশ চলে আসতে পারে। রাত পোহালেই আমাকে বিয়ে দিয়ে দেবে অন্যত্র।
কিছুই ছিল না ঐ যুবকের ঘরে। যা আছে তা সব ফেলে রেখে দুজন হাত ধরে সেই রাতে বেরিয়ে পড়ে।
মহল্লার লোকজন ভোরবেলা দেখতে পায়, ২৪ নং দক্ষিণ গাঁও এর পুরনো টিনসেড বাড়িটির দরজা খোলা। রুগ্ন যুবকটি ঘরে নেই। কোথাও চলে গেছে। তার এলমেল বিছানার পাশে মৃত সঞ্জিবনীর একটি খালি বতল, সিগারেটের খালি প্যাকেট, স্লীপিং পিলের ছেঁড়া খোসা ও একটি পুরনো হারমোনিয়াম পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।
ওরা হয়ত চলে গেছে দূরে কোথাও। যেখানে গেছে সেখানেও চরম অনিশ্চয়তায় ভরা জীবন ওদের । হোক না তা সে জীবন ! প্রিয় মানুষ পাশে থাকলে ঐ পথ চলাতে, ঐ জীবন যাপনেও জন্মান্তরের সুখ আছে।
৩. শোনাও প্রাণে প্রাণে
সেদিন ছিল শ্রাবণ বর্ষার ভোর। প্রতিদিনের মত সেদিনের ভোরেও পাখি ডেকেছিল। পুকুরের চালায় কুর্চি ফুল গুলো ফুটে উঠেছিল। বাড়ির কৃষি কর্মীরা প্রাত্যহিক কাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হঠাৎ সারা গ্রামে শোরগোল উঠেছে — ‘কুসুমপুর হাটে মিলিটারি এসেছে। তারা জেলে পাড়াতে আগুন দিয়েছে। বাড়ি ঘর সব পুড়ে ছারখার করছে। মানুষ মারছে।’
সবাই বলছে — ‘পালাও, পালাও। মিলিটারিরা গুলি করে মেরে ফেলবে।’ কেউ বলছে — ‘ যুবকরা তোমরা কেউ বাড়িতে থেক না। তোমরা বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাও।’
আমি যুবক ছিলাম না। আমি ছিলাম কিশোর। মা বললেন, তুমি বাড়িতে থেক না। তুমি দূরে কোথাও চলে যাও।’
আমিও অনেকটা ভয়ে গাঁয়ের কিছু লোকের সাথে নৌকায় করে দূরের আর একটি গ্রামের দিকে চলে যাই। যেখানে মিলিটারিদের যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।
আমাদের ছোট নৌকাখানি চলছিল দূরের আর একটি গাঁয়ের দিকে। চারদিকে জলের থৈথৈ প্রান্তর। জলে ভাসা আমন ধানের ভিতর দিয়ে, আখ ক্ষেত মারিয়ে, পাট ক্ষেতের আড়াল দিয়ে স্রোতের টানে নৌকাটি বেশ বেগ পেয়েছিল। সবাই জোরে জোরে লগি আর বৈঠা চালাচ্ছিল।
আমরা নৌকার উপর থেকেই দেখতে পাই মাঝি পাড়ার উপর থেকে কুন্ডলী পাকিয়ে ধাউ ধাউ করে আগুন জ্বলছে। থেকে থেকে রাইফেলের গুলির শব্দও শুনতে পাচ্ছিলাম।
একটু পর দূর থেকে দেখি, আমাদের বাড়ির দিক থেকেও আগুনের কুন্ডলী উঠছে। আমরা নিরাপদ দূরত্বে নৌকার উপরই অবস্থান করতে থাকি। দুপুর পর্যন্ত সেখানেই থাকি। পরে খবর পাওয়া যায় — মিলিটারিরা তান্ডব শেষে সিরাজগঞ্জ শহরে ফিরে
চলে গেছে।
আস্তে আস্তে ফিরে আসতে থাকে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়া গ্রামের মানুষ গুলো। ফিরে আসি আমিও। সবাই দেখতে পায় অনেক বাড়ি ঘর তখনও ধাউ ধাউ করে জ্বলছে। যে যেভাবে পারছে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ততোক্ষণে জ্বলে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে গেছে ঘরের টিন, কাঠ, আসবাবপত্র ও পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে গোলাঘরের ধান, চাল অন্যান্য ফসল। বাতাসে তখনও পোড়া ধান চাউলের গন্ধ ভাসছিল। মানুষের আহাজারিতে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠেছিল।
এখন যে ঘটনাটি বলব সে ঘটনাটি গ্রামের অনেকেই জানেনা। দু’একজন জানলেও মানবিক কারণে তা এখনও গোপন করে রেখেছে। আমার চাচাতো ভাই ছিলেন একজন এলএমএফ ডাক্তার। তাঁর বাড়ীটিও পাকসেনারা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। ঘটনাটি সেদিন জানি নাই। পরে শুনেছি। আসুন, ঘটনাটি ডাক্তার সাহেবের মুখ থেকেই শুনি:
‘বাইরের একটি অতিথী ঘর পাকসেনারা অক্ষত রেখেছিল। রাতে সেই ঘরেই আমি শুয়ে আছি। চারদিকে পোড়া সব জিনিষের গন্ধ। চোখে ঘুম আসছিল না। রাত তখন এগারোটা হবে। দরজায় আস্তে করে কড়া নারার শব্দ শুনতে পাই। আমি উঠে দরজা খুলে দেই। দেখি দড়জার সামনে আমারই গাঁয়ের এক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। সে
বলে — ‘আমার মেয়েটার অবস্থা খুব সংকটাপূর্ণ। তোমাকে একটু যেতে হবে।’
আমি আমার ডাক্তারি ব্যাগটা হাতে নিয়ে তার বাড়িতে চলে যাই। দেখি মেয়েটি অর্ধচৈতন্য অবস্থায় বিছানায় শুয়ে আছে। কাঁথা রক্তে ভিজে গেছে। আমি বললাম– ‘কখন থেকে এ অবস্থা ?’
লোকটি বলল — ‘দুপুর থেকেই। পাকসেনারা চলে যাবার পর থেকেই। প্রথমে রক্ত কম ঝরছিল, কিন্তু ক্রমেই রক্তপাত বাড়তে থাকে। ভেবেছিলাম, ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু হয় নাই। লজ্জায় এত সময় তোমাকে ডাকিনি।’
মেয়েটির বয়স কতই হবে, তের চৌদ্দ বছর হবে। আমি ঐ লোকের স্ত্রীকে বললাম —‘লন্ঠনের আলো একটু তুলে ধর। ওর কাপড়টি সরাতে হবে।’
আমার কথা শুনে অর্ধচেতন মেয়েটা নিজেই তার পায়জামার ফিতা খুলে ফেলে। সে অনেকটা অবচেতন হয়েই আমাকে ওর ক্ষত জায়গাগুলো দেখাতে থাকে। মেয়েটি এত বেশি ধর্ষিত হয়েছে যে, আমি দেখে নিজেই শিউরে উঠি।
আমি সারারাত জেগে থেকে আমার সকল প্রচেষ্টা দিয়ে ওকে অনেকটা ভাল করে তুলি। সকালবেলায় ঘরের জানালাটা খুলে দিতে বলি। সূর্যের আলো মেয়েটির গায়ে এসে লাগে। ততোক্ষণে ওর রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গেছে।’
এই ঘটনাটি বলে কেমন যেন ভারি করে দিলাম সবার মনটিকে। আসুন রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা’ র কন্ঠে একটি মঙ্গলের গান শুনি —
‘সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে,
শোনো শোনো পিতা
কহো কানে কানে, শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গলবারতা ………..।’
৪. মেহেরজান
অপ্রেমে দূরে রেখেছিলাম তাকে। প্রেমেই তাকে কাছে নিয়ে আসে। এত কাছে যে — ওর মায়াভরা চোখের মায়া একদিন আমি না দেখতে পেলে আমার মন খারাপ হয়ে যেত। আমার সমস্ত চৈতণ্যে, অবচৈতণ্যে তার ভালোবাসা জড়িয়ে থাকত যে!
মেহেরজানকে প্রথম দেখে বিমুুগ্ধ হয়েছিলাম বুড়িগঙ্গার পাড়ে। তখন সেখানে এত অট্রালিকা ছিল না। ওয়াইজ ঘাট থেকে হেঁটে হেঁটে আরো একটু পশ্চিমে, নদীর তীরে একটা ভাঙ্গা ইটের ঢিঁপির উপর দু’জন একদিন বসেছিলাম। সূর্য তখন অস্তমিত। নদীতে ভেসে থাকা আকাশ থেকে ঝরে পড়া লাল আভার ঝিলিক মেহেরজানের মুখে এসে পড়েছিল। ওকে দেখে প্রথম বিমুগ্ধ হওয়া সেখানেই।
সেদিন ঝুনু আপা ক্লাশে আসেনি। তাই ক্লাশ আর হলো না। তবলচি কিছুক্ষণ একাকী তবলায় তাল দিল। কিন্তু সে তালে নাচ আর কারও করা হলো না। তারপর মর্নিং শো’তে স্টার সিনেমা হলে যেয়ে আমি আর মেহেরজান ঢুকে পড়ি। সুভাষ দত্তের ‘বসুন্ধরা’। সিনেমা কি দেখব? আমরা যেখানে বসেছিলাম, তার আশে পাশে ওয়াইজ ঘাটের এক গাদা Out of Bond এর মেয়েরা বসেছিল। উদ্ভট সাঁজ, আর রংবেরঙের পোষাক পরিহিতা ঐ সব বনিতারা অকারণে হাসি আর শীষ দিচ্ছিল। বিরতির সময় আমরা বের হয়ে চলে আসি।
আর একদিন আহসান মঞ্জিলে গিয়েছিলাম। প্রকোষ্ঠ্যের পর প্রকোষ্ঠ্য ঘুরছিলাম। একটি রুম আছে নবাবদের পানশালা হবে হয়ত। দেয়ালে টানানো একজন অর্ধনগ্ন নর্তকীর তৈলচিত্র দেখতে পাই। আমি মেহেরজানকে বলি — তুমিও তো নাচ শিখছ। নবাবরা থাকলে এই রকমই নর্তকী হতে পারতে।
মেহেরজান: তুমি কি ঐ মেয়ের চোখ দেখে কিছু বুঝতে পারছ ?
আমি: যে মাদকতা আমি দেখছি ওর চোখে মুখে, সেখানে কেবল আনন্দই দেখতে পাচ্ছি।
মেহেরজান: তুমি দেখেছ কেবল ওর আনন্দময়ী দুটি চোখ। আমি দেখেছি ওর চোখের পিছনে — যেখানে অনেক বেদনার অশ্রু জমে আছে। যা দেখাও যায় না, ঝরেও পড়ে না।
আমি দেখলাম, মেহেরজানের চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে। হঠাৎ মনে হলো ঐ রুমের মধ্যে ঘুঙ্গুরের শব্দ হচ্ছে। তবলচি বাজাচ্ছে তবলা। শরাব খা্চ্ছি আমি।মেহেরজান নাচছে নুপুর পায়ে। আমি তো মেহেরজানের চোখে কোনো দুঃখ দেখছি না, দেখছি আনন্দ। শরাব পান করছি। প্রিয়া আজ মেহেরজান।
হঠাৎ মনে হলো, পাশের প্রকোষ্ঠ্য থেকে কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। মনে হলো কোনো একজন নর্তকী আথবা যৌনদাসী কাঁদছে। যখন ঘোর কাটে তখন দেখতে পেলাম — আমি মেহেরজানের চুলে মুখ লাগিয়ে চুলের সুবাস নিচ্ছি। মেহেরজান আমার বুকে জড়িয়ে আছে। সে এক বিমুগ্ধ আবেশ!
তারপর অনেক কথা।
কতো ভালোবাসা হলো দুজনের। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সেই প্রেম কালস্রোতের উল্টো দিকে ভাসিয়ে দিল। প্রেমেই একদিন মেহেরজানকে কাছে টেনে এনেছিল, আবার প্রেমেই তাকে দূরে রেখে দিলাম। যার চোখের মায়া দিয়ে আমাকে একদিন না দেখলে সারাদিন মন খারাপ লাগত, তাকেই নয়নের আড়াল করে রাখলাম। মেহেরজানকে আমার সমস্ত চৈতণ্যে, সমস্ত অবচৈতণ্যে ভুলে যেতে থাকি।
কেন ভুলে যেতে থাকি — সে দীর্ঘশ্বাশের কথা আরেক দিন বলব।
৫. নূরী
শেষ পর্যন্ত একজন বালিকাকে আমার বিবাহ করতে হলো। কোনও এক শীতের সন্ধ্যায় তাকে লাল বেনারসি শাড়ি পরানো হলো। মুখে আলপনা আঁকা হলো। হাতে চুড়ি পরানো হলো। মেহেদি লাগিয়ে দেয়া হলো দুই হাতে। খুব একটা উৎসব হলো না। সানাইও বাজেনি। ইচ্ছা ছিল দুই ঘোড়ার গাড়িতে করে বউ তুলে আনব, তাও হলো না। ফুলহীন, সাজসজ্জাহীন একটি সাদা গাড়িতে করে সেদিন নববধূকে ঘরে তুলে এনেছিলাম।
এ যেন পুতুলখেলার সংসার শুরু হলো। বাজারে যেয়ে হাঁড়ি পাতিল কিনলাম। বালতি কিনলাম। শীল পাটা কিনলাম। মাদুর, ফুলদানী সব কিনতে হলো। এ এক অত্যশ্চর্য জীবনের শুরু। যা জীবনে কোনও দিন চোখে দেখি নাই। শুনি নাই। বুঝি নাই। এখন আর সকাল বেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙ্গার অপেক্ষা করতে হয় না। এলার্ম দিয়ে রাখতে হয় না ঘড়িতে। এত সুুন্দর জীবন আছে জীবনে, আগে বুঝি নাই।
ওর নাম আয়শা নূর। বলেছিলাম তুমি এষা না নুরী। ও বলেছিল আমি নুরী।
নূরী চঞ্চল হয় সকাল বেলা। রোদ্রের উত্তাপে হয় দহন।
সাওয়ারের নীচে জল ঢালে সারা দুপুর,
সন্ধ্যায় আকুল হয় রবি ঠাকুরের গানে,
মনে পড়ে তার দূর গায়ের কথা
স্টেশনে রেল গাড়ির সেই হুইসেলের শব্দ, মনে পড়ে সেই ঝিকঝিক আওয়াজ।
নুরী ওর বাবার সাথে একদিন বাড়ি চলে যায়। সেখানে ওর ছোটো বোনকে পায় খেলার সাথী করে। দু’জন হেঁটে হেঁটে চলে যায় রেল লাইনের ধারে। দূর থেকে হুঁইসেল বাজিয়ে ট্রেন এসে থামে প্লাটফরমে। হৈহুল্লর করে যাত্রিরা নেমে আসে কামরা থেকে।
আমি বুঝতে পারি আমার প্রথম শূন্যতা। আলনায় কাপড় হয়ে থাকে এলমেল। আবার পাখির ডাকের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ঘুম ভাঙ্গার। জীবনের এতটা বছর একা লাগেনি। কবিতা লেখার ভাবনা চলে যায় সমান্তরাল রেল লাইনের সেই দূরের প্রান্তে। নিঃসীম শূন্যতা পড়ে থাকে সেখানে। একদিন ঘুম আসে সন্ধ্যাবেলা, আরেকদিন সারা রাতেও আসে না।
আর একদিন রাতের বেলা ল্যাম্পের আলো জ্বেলে চিঠি লিখতে বসি —
‘নূরী, তুমি চলিয়া যাইবার পর হইতে আমার খাওয়ার অরুচি হইয়াছে। প্রত্যহ অফিসে যাইতে লেট হইতেছে। ঘুমও ঠিকমতো হইতেছে না। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, স্বপ্নে তোমাকে কাছে পাইতে। কিন্তু একদিনও তোমাকে স্বপ্নে পাই নাই। যাহা হোক, পত্র পাঠ তুমি চলিয়া আসিও। ইতি—
উত্তরে নুরী লিখল —
‘প্রিয়তম, তোমার চিঠি পেলাম। আমি এখানে খুব ভালো আছি। আমরা প্রতিদিন রেল লাইনের ধারে বেড়াতে যাই। কাল কাজিপুরা নানী বাড়ি বেডাতে যাব। উল্লাপাড়া ছোটো ফুপুর বাড়িতেও যাব। বেশি খিদা লাগলে তুমি আজিজের হোটেলে যেয়ে খেয়ে নিও। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শুনিও। তবেই ঘুম আসবে।
ইতি- নুরী।
নুড়িতে থাকে মুক্তা, পাথরে ভারী
হয়ে থাকে বুক
যমুনার জলে রুপালি মাছের ঝাঁক ঘুরে বেড়ায়
হেমন্তের রাত্রিতে চাঁদ নেমে আসে দুই পাড়ে-
তার চোখ আমাকে বিষণ্ণ করে,
কোথায় পড়ে আছেবকুল ফুলের মালাখানি।
আমি প্রতিদিন চেয়ে থাকিঅন্ধকারে–
বালিকা চলে আসছে
রেল লাইনের স্লিপারে হেঁটে হেঁটে।.
আমি নিজেই ওকে দেখতে চলে যাই একদিন। রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনটি থামল জামতৈল স্টেশনে। তখন সন্ধ্যা হয়েছে। মুগ্ধতার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম বুকের তল থেকে। রক্তের স্পন্দন বাড়ছিল তাকে দেখবার আনন্দে। বাড়ি পৌঁছে শুনি — ছোটো ফুফুর বাড়িতে নুরী বেড়াতে গেছে। আজকেই ওর ফেরার কথা ছিল। কিন্তু আসেনি।
দূর ভ্রমণে শরীরে ক্লান্তি ছিল। মন খারাপের চোখে নাকি ঘুম বেশি আসে। অবসাদ আর মনবেদনা নিয়ে একসময় ঘুমিয়ে যাই। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গে — তখন চোখ মেলে দেখি পাশে নুরী শুয়ে আছে। ঘুমের ঘোরে ওর একটি হাত আমার বাহুতে জড়িয়ে ধরে আছে।
তারপর পাখি সব কলরব করে ডেকে উঠল
ভোরের আলো জ্ব্বলে উঠল
স্টেশন থেকে ছেড়ে যায় রাতের ক্লান্ত ট্রেন —
তখন গান কবিতা হয়, কবিতা হয়ে যায় গান।
৬. কুসুম
একটি রিসার্স প্রজেক্টে কাজ করতে কুসুম ঢাকা এসেছিল । সাময়িক চাকুরী। ও আমার সহকর্মী ছিল।গত সপ্তাহে কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে। তাই চাকুরী আর নেই। আজ সে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। কমলাপুর স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জানালার পাশে বসে থাকা কুসুমের বিষণ্ণ চোখ আমার দিকে চেয়ে আছে । ট্রেনের চাকার খট্ খট্ কর্কশ আওয়াজ দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে সামনের সমান্তরাল পথের দিকে। কুসুমের
চোখ আর দেখা গেল না। এই শহর ছেড়ে কুসুম চলে গেল।
কতক্ষণ প্লাটফরমে একাকী হাঁটছিলাম। কেমন যেন উদাস লাগছিল। পাশে অদূরে একটি চা’র দোকানে গিয়ে বসি। এক কাপ লাল চা খাই। তারপর সিগারেট ধরাই। পাশে কেউ ছিল না। ধূয়াগুলো মিলিয়ে দিচ্ছিলাম শুন্য প্লাটফরমের দিকে।
স্টেশন থেকে পথে নেমে পড়ি। প্রখর রোদ্রে হেঁটে হেঁটেই মুগদাপাড়ায় মেসে চলে আসি। মনটা ভাল লাগছিল না। বিছানায় সোজা শুয়ে পড়ি। টেবিলের উপর রাখা ডাইরীটার উপর চোখ যায়। একবার প্রজেক্টের কাজে নেত্রকোনা’র বারোহাট্রা গিয়েছিলাম। কংস নদীর পাড়ে এক নিরিবিলিতে আমার ডায়েরীটা নিয়ে কুসুম লিখেছিল —-
”তুমি আমাকে পূর্ণ করো। আমাকে পূর্ণ করবেনা অন্য কেউ। আমাকে তুমি স্বপ্ন দেখাও। যে স্বপ্ন ভাঙ্গতে পারবেনা কেউ। আমি বসে থাকি তোমার পথের দিকে।তোমার সাথে পথ চলব। সে পথ চলা বন্ধ করতে পারবেনা কেউ। আজকের এই কংস নদীর জলকে সামনে রেখে বলছি —- ‘আমি তোমাকে ভালবাসি।’এই ভালোবাসাও কেড়ে নিতে পারবেনা কেউ।”
একদিন দুইদিন যায়। সময় কাটতে চায় না। সব চেনা পথগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে। দুটো টিউশনী করি।বিকেল হলে একাকী স্টেশনের প্লাটফরমে ঘুরে বেড়াই।কখনও অসময়ে ঘুমিয়ে থাকি। কখনও সারারাত জেগে থাকি। মাঝে মাঝে ভাবি, কুসুম আমার কি না হতে পারত। ওকে কেন যেতে দিলাম। রেখে দিতাম আমার উদ্বাস্ত জীবনের কাছে।
একটি কোম্পানীতে পণ্য মার্কেটিংএর চাকুরী পাই। প্রথম দিনেই সহকর্মী মালতী নামে একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়। যেন কুসুম। সেই চোখ, সেই চুল, সেই স্মিত হাসি। সেই ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠা। সেই পুরানো প্রেম ফিরে পাওয়া। কুসুমকে নিয়ে যে পথগুলো দিয়ে হেঁটেছিলাম, সে পথ দিয়েই মালতীকে নিয়ে হাঁটি। পার্কে যে বেঞ্চে কুসুমকে নিয়ে বসে থেকেছি সেই বেঞ্চেই মালতীকে নিয়ে বসে থাকি। মালতীর ভালোবাসাগুলোও কুসুমের মতোই। সেই একই শরীরের গন্ধ, আলিঙ্গনের উষ্ণতা একই, চুম্বনের মাধূর্যও একই।’
এক অগ্রহায়ণে মালতী আর আমার বিয়ের সানাই বেজে ওঠে। আমার পরনে শেরওয়ানী, মাথায় কারুকার্য খচিত টুপি, ওদিকে মালতীর পরনে লাল বেনারশী শাড়ি। সিঁথিতে টিকলী বাঁধা। গালে কপালে আবির মাখা সাঁজ। যখন আমার পাশে মালতীকে বসানো হল, তখন একবার তাকালাম মালতীর দিকে। দেখি এ যেন সেই কুসুম। সেই মায়াবী চোখ, সেই আনত ললাট। চারদিকে কতো আনন্দ, কতো হৈহুল্লুর, কতো গান বাজছিল । সব গান ছাপিয়ে এই গানটি বিষাদের সুরে ভেসে
এল –
”প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।
চারি দিকে হাসিরাশি, তবু প্রাণ কেন কাঁদে রে।”
৭. কণিকা
তখন কলেজে পড়ি। ঢাকা থেকে একবার ট্রেনে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে যাচ্ছিলাম। আমি বসেছিলাম সামনের মুখো সিটে জানালার পাশে। ট্রেনের ভিতর থেকে শ্রীপুর, রাজেন্দ্রপুর, ধীরাশ্রম, নুরেরচালা জায়গাগুলো দেখতে দেখতে যেতে ভালই লাগছিল আমার । বিশেষ করে ঘন শালবন যখন পার হচ্ছিলাম, তখন মনটা কেমন যেন প্রেমময় হয়ে উঠেছিল। গভীর অরণ্য দেখে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, মানুষ বিয়ে করে হানিমুনের জন্য কক্সবাজার যায়। আমি আর কক্সবাজার যাব না। আমি আসব নতুন বউ নিয়ে এই শালবনে।
ট্রেনটি ময়মনসিংহ জংশনে এসে পৌঁছলে দেখি — কম্পার্টমেন্ট অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, ময়মনসিংহের এই মানুষগুলোর জন্য কমলাপুরে সিট পেতে কতোই না অসুবিধা হয়েছিল। এখন দেখছি সব খালি। আবার দেখি, এই খালি সিটগুলোতে মুহূর্তেই লোক উঠে ভরে গেল, অনেকটা সেই কমলাপুর স্টেশনের ভীড়ের মতই। আসলে ময়মনসিংহের মানুষ ট্রেন জার্নি করা ছাড়া কিছু বুঝত না।
এই ময়মনসিংহ থেকে একটি পরিবার ওঠে আমার কম্পার্টমেন্টে। ঠিক আমার সামনের সিটে তারা আসন নেয়। তারা ছিল স্বামী স্ত্রী সাথে ষোল সতের বছরের একটি মেয়ে ও পাঁচ ছয় বছরের একটি ছেলে। মেয়েটি যখন সিটে এসে বসে তখন আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি কিন্তু সে আমার দিকে তাকাচ্ছিল না। আমি আমার দৃষ্টি বেশ কিছুক্ষণ মেয়েটির চোখের দিকে রাখি। ভাবি, মেয়েটি অন্তত একটিবার সরাসরি আমাকে তাকিয়ে দেখুক। কিন্তু নাহ্, মেয়েটি আমার দিকে একবারও তাকাল না। আমি অনেকটা মন খারাপ করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম।
ট্রেন চলছিল ঝিকঝিক করে । আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম, গ্রামের পর গ্রাম, খাল, নদী,বিল, সাঁকো, মানুষ, বক, পাখি, জেলে, নৌকা আরও কত দৃশ্য। এসব দেখতে খুব ভাল লাগছিল আমার। আমি আর ঐ মেয়ের দিকে একটিবারও তাকালাম না। ওর প্রতি একটু রাগ হয়েছিলাম, মনে মনে বলছিলাম — ‘ মেয়ে! তুমি একটিবার আমাকে তাকিয়ে দেখলেনা। তুমি বুঝতে পারলেনা, আমার এই চোখে তোমাকে দেখে কী যে ভাল লেগেছিল। তুমি জানলেনা, বৃক্ষের ছায়ায় ছায়ায়, মেঘে মেঘে, রোদ্রে পুড়ে পুড়ে আমার এই চোখ তোমাকেই দেখছে বারবার।’
আমার অন্তর চোখ দেখতে পাচ্ছিল, মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ক্ষণে ক্ষণেই । ওর ছোট ভাই যখন জানালার ধারে যেয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল, তখন সে ওর ভাইকে ডেকে বলেছে — ‘বাইরে কি দেখছ? আসো এখানে। আমার কাছে থাক। দেখ আমাকে। ‘ আমার কাছে মনে হয়েছিল, এ যেন পরোক্ষ ভাবে আমাকেই আমন্ত্রণ করছে। বসতে বলছে তার পাশে। তাকিয়ে দেখতে বলছে তাকে। তারপরেও আমার ভিতরে কি এক অবাস্তব জেদ হয়েছিল যে, মেয়েটিকে আমি আর তাকিয়ে দেখলামই না।
জামালপুর জংশনে ঐ মেয়ে এবং ওর পরিবারের লোকজন নেমে চলে যায়। আমি ওদের নেমে যাওয়াটুকুও তাকিয়ে দেখলাম না। ওদের আলাপচারিতায় জানতে পেরেছিলাম, মেয়েটির নাম কণিকা। ময়মনসিংহ মমিমুন্নেসা গার্লস কলেজে ইন্টারমিডিয়েট দ্বিতীয় বর্ষে পড়ে। যাই হোক, আমার ট্রেনটি জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের দিকে ঝিকঝিক করে চলতে থাকে। আমি এবারও বাইরে তাকিয়ে দেখছিলাম — গ্রাম, খাল, নদী,বিল, সাঁকো, মানুষ, বক, পাখি, জেলে, নৌকা আরও কত দৃশ্য। কেন জানি এসব দেখতে আমার ভাল লাগছিল না। সবকিছুই কেমন যেন বিষাদের মনে হচ্ছিল।
বিকেলের রোদ্র ছায়ায়, আর মেঘের নীচে নীচে, আমার এই চোখ কণিকার সৌন্দর্যমাখা মায়াবী মুখটিকেই খুঁজে দেখছিল বারবার।
৮. ক্ষণিকা
একদিন এক শান্ত শীতল বিকেলে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে দুজন হাঁটছিলাম। পাহাড়ের গায়ে ছিল হাজার রকমের লতাগুল্ম। মনে মনে খুঁজছিলাম কী যেন একটি ফুল। উপরে তাকিয়ে দেখি পলাশও ফুটে আছে। দেখলাম লজ্জায় নুয়ে পড়েছে অপরাজিতা। আমার পাশে থাকা মেয়েটিও কী যেন খুঁজছিল আমার মতোই, কোনো ফুল বা পত্র পল্লব। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করি, কী খুঁজছ তুমি? মেয়েটি বলেছিল — ‘আমি যে তোমাকে কিছু দিতে চাই। তাই খুঁজছি এই পাহাড়ের বন-ঝাড়ে।’
আমরা দুজনই পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলাম। হঠাৎ মনে হলো আমি কী অমিত রায়? এ জন্মে আমি তো অমিত রায় নই। আমি নামযশহীন এক লেখক। আর পাশের মেয়েটি লাবণ্যও নয়, সে অন্য কেউ।
অথচ লাবণ্যের মতোই সেইদিনের সেই বিকেলের মেয়েটি বলেছিল — “তুমি গোপন হবে আর আমি তোমায় প্রকাশ করব। এ তো আমাদের জন্মজন্মান্তরের খেলা। কিন্ত তোমার তো কেটির মতো আছে অন্য কেউ। আমি কেন তোমার হবো এই ক্ষণিকের তরে ক্ষণিকা হয়ে?”
কেমন মায়াময় হলো চন্দ্রিনাথের পাহাড়। আমি আবৃত্তি করছিলাম —-
“পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত।”
সেই মেয়ে সেদিন চোখ নামিয়েছিল বনলতা সেনের মতো। আমরা নিতে পারিনি বন্ধনহীন পথ চলার শপথ। সেদিনের সেই অস্তপ্রায় সূর্যের শেষ রশ্মি এসে রক্তিম আবীর মাখিয়ে দিল আমাদের দুজনের সর্বাঙ্গে। মৃদু হাওয়ায় তখন চারদিকে ঝরে পড়ছে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল। না, লাল পলাশ নয়। রডোডেনড্রন।
৯. শেষ বিকেলের কথা
রাতে খাবারের পর কেমন যেন আলস্য লাগছিল। শুয়ে ছিলাম বালিশে মুখ গুজে। ভালো লাগছিল না। উঠে তাই ছাদে চলে আসি। ছাদের এককোণে আমি দাঁড়িয়ে আছি। আজ আকাশে চাঁদ নেই। ছড়ানো ছিটানো আছে কয়েকটি তারা। আমার পরনে টি-সার্ট এবং ট্রাউজার্স।একটা সিগারেট ধরাই। সিগারেট টানছিলাম আর ভাবছিলাম আজকের শেষ বিকেলের কথা। সিগারেটের ধূয়ার টানে মনটা চলে গেল — বিকালে পার্কের সেই বিবর্ণ সময়ের কাছে ।
দুটো প্রজাপতি একটাই গোলাপের উপর বসে আছে।পাশে আরও গোলাপ আছে, আরো অনেক ফুল আছে।সেখানে কোনো প্রজাপতি নেই। একটি ফুল থেকেই দু্টো প্রজাপতি সুবাস নিচ্ছে। ওরা মধুরাক্ষী কিনা জানিনা। এই অপূর্ব মোহনীয় দৃশ্যটি দেখছিলাম আমি আর পাঁপড়ি।
পাঁপড়ি আমার সহপাঠী। আমাদের ক্লাশ আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজকে পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল।ক্যাম্পাসকে বিদায় জানিয়ে এসেছি। কাল থেকে কেউই আমরা ক্যাম্পাসে থাকব না। সেমিনার কক্ষে কতো ছাত্র বসে থাকবে, আমরা সেখানে থাকব না। ক্যান্টিনে আর চা’র কাপে ঝর উঠবে না। লাইব্রেরী বারান্দায় বসে আর কোনো আড্ডাও হবে না।
আমার আর পাঁপড়ির এইসব নিয়ে এমনিতেই মন খারাপ ছিল। তারপরেও আজকের এই শেষ বিকালটা কাটানোর জন্য পার্কে চলে আসি। এসেই প্রজাপতিদের ঐ মোহনীয় দৃশ্যটি দেখতে পাই। এলোমেলো ভাবে হাঁটছিলাম দু’জন। এক সময় লেকের পাড়ে ঘাসের উপর যেয়ে বসি। পাঁপড়ি কালকেই চলে যাবে দেশের বাড়ি। ওর বিয়ের দিন তারিখও ঠিক হয়ে আছে। অপেক্ষা ছিল শুধু পরীক্ষা শেষ হবার। পাঁপড়ি বলছিল — তুমি যাবে না আমার বিয়েতে ?
আমি : তুমি বললে অবশ্যই যাব।
পাঁপড়ি মায়াবী চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলছিল — তুমি অবশ্যই যাবে।
আমি: যাবো। কিন্তু কোনো কারণে যদি না যেতে পারি?
আমি আমার ঝুলানো কাপড়ের ব্যাগ থেকে রবীন্দ্রনাথের ‘গীতবিতান’ বইটি বের করি। পৃষ্ঠা উল্টাতে গিয়ে এই গানটি চোখে পড়ে-
‘অনেক কথা বলেছিলেম কবে তোমার কানে কানে
কত নিশীথ-অন্ধকারে, কত গোপন গানে গানে
সে কি তোমার মনে আছে তাই শুধাতে এলেম কাছে–
রাতের বুকের মাঝে মাঝে তারা মিলিয়ে আছে সকল খানে।’
গীতবিতানের প্রথম পাতায় লিখি — ‘ তোমার শুভ দিনে আমার এই শুভাশিস ‘। নীচে আমার নাম ও তারিখ লিখি। তারপর বইটি পাঁপড়ির হাতে দিয়ে বলি — সেদিন যদি কোনো কারণে তোমার বিয়েতে না যেতে পারি, তোমার জন্য আমার এই গীতবিতান।’
বইটি আমার হাত থেকে নিতেই দেখি পাঁপড়ির মুখ।মহুয়া গাছের ফাঁক দিয়ে বিকেলের রোদ এসে ওর মুখে পড়েছে। লেকের নিস্তব্ধ জলের মতো চোখ বিনম্র হয়ে আছে। উদ্ভান্ত বাতাসে কড়ই গাছ থেকে তখন মরা পাতা ঝরঝর করে ঝরে পডছে। কি কথা যেন বলতে চেয়েছিল পাঁপড়ি কিন্তু আর বলতে পারেনি। দেখলাম —পাঁপড়ি কাঁদছে।
১০. বৃষ্টিমঙ্গল
আমি তখন বাগবাটী স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্র। আষাঢ় মাস শুরু হয়েছে। কিন্তু নদী নালায় তখনও বন্যার পানি ঢোকে নাই। সেদিন স্কুলে ক্লাস শেষে বাড়ি ফিরব কিন্তু হঠাৎ আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দেয় এবং বৃষ্টি নামা শুরু হয়। সবাই বৃষ্টি থেমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি আর তা করলাম না। বইগুলো প্লাস্টিকের কাগজে পেঁচিয়ে নেই। ধূলির রাস্তা একটু বৃষ্টি হলেই কাঁদা হয়ে যেতো। কাঁদায় স্যান্ডেল পরে হাঁটা যেত না। আমি একহাতে বই আরেক হাতে স্যান্ডেল নিয়ে আড়াই মাইল পথ কাঁদায় হেঁটে এবং বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়ি ফিরি। মা প্রথমেই তার শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মাথা মুছে দেয়। কিন্তু মাথা মুছে্ দিলে কি হবে, রাতে ঠিকই ভীষণ জ্বর এসে গিয়েছিল।
একবার বাবার সাথে শহর থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলাম। শৈলাভিটা খেয়াঘাট পার হওয়ার পর থেকেই মুশলধারে বৃষ্টি শরু হয়ে যায়। পথ চলতে যেয়ে বাবা তার হাতের ছাতা আমার দিকে ঝুঁকে রাখে। আমি যেন ভিজে না যাই। কিন্তু আমি বার বার ছাতার বাইরে এসে বৃষ্টিতে ভিজতে থাকি। সেদিন সারা রাস্তা বাবার ছাতার নীচে এমনি লুকোচুরি খেলে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।
তখখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমি। কবি জসিম উদ্দীন হলে থাকি। সেদিন সারাদিন বৈশাখের তপ্ত গরম ছিল। রাতে সামান্য গুরি গুরি বৃষ্টি হচ্ছিল। ঠিক ঐ রকম নয়, দু’এক ফোঁটা ফোঁটা। একটু শীতল হওয়ার জন্য সে রাতে সারারাত আমি আর আমার এক বন্ধু হলের ছাদে শুয়ে থেকেছিলাম।
ঢাকার দক্ষিণখানের বাড়িতে তখন আমি একা থাকি। বর্ষার দিনে সন্ধ্যার পর অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন প্রায়ই বৃষ্টির জন্য প্রা্র্থনা করতাম। এয়ারপোর্ট বাস স্ট্যান্ডে নামার পর যেদিন বৃষ্টি পেতাম, সেদিন আমার মনের স্ফূর্তি বেড়ে যেত। আমি সারা পথ একাকী ভিজতে ভিজতে ঘরে চলে যেতাম। একা থাকার কারনে কেউ দেখতে পেত না আমার শরীরের ভেজা কাপড়।
সবে মাত্র বিয়ে করেছি তখন। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা দুজন শেরেবাংলা নগর মামার বাসা থেকে রিক্সায় করে মিরপুরে আমার বোনের বাসায় ফিরছিলাম। আবহাওয়া অফিসের কাছে যেতে না যেতেই মেঘ শুরু গম্ভীর করে বিদ্যুৎ চমকাতে থাকে। আকাশ ভেঙ্গে বূষ্টি শুরু হয়ে যায়। বউ রিক্সার হুট উঠিয়ে দিতে চায়। আমি বাঁধা দেই। আমরা দুইজন কাক ভেজার মতো ভিজে চুপসেে যাই। সেদিন মিরপুর পর্যন্ত সারা রাস্তা ভিজে ভিজে চলে এসেছিলাম। আমার বালিকা বধূ প্রথম সেদিন বুঝতে পেরেছিল- একটা পাগল তার কপালে জুটেছে।
ফুয়েন্টসোলিং ভূটানের একটি ছোট্ট শহর। একে একটি বাজারও বলা যেতে পারে। ভারতের জলপাইগুড়ির জয়গাঁও সীমা্ন্ত লাগোয়া এই শহরটি অবস্থিত। ভারত থেকে সড়কপথে ভূটানে যাবার অন্যতম এটি একটি প্রবেশ দূয়ার । এই ফুয়েন্টসোলিং এ যাওয়ার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি থেকে আমি আর আমার স্ত্রী ট্যাক্সিতে জয়গাঁঁও যাচ্ছিলাম। আমরা যখন ডুয়ার্স অতিক্রম করি তখন থেকেই মুশুলধারে বূষ্টি শুরূ হয়ে যায়। জলপাইগুরির চা বাগানের ভিতর দিয়ে আঁকাবাঁকা টিলা পথে আমাদের ট্যাক্সি জয়গাঁওয়ের দিকে চলতে থাকে। গাড়ির উইন্ড গ্লাস বৃষ্টির জলে ঘোলা হয়ে আসছিল। চা বাগাানের ভিতর দিয়ে বৃষ্টিমুখর সেই দিনের পথচলা স্বর্গীয় মনে হয়েছিল । কি যে ভালো লেগেছিলো সেই ক্ষণ। মনে হয়েছিল এই পথ যেন কোনোদিন শেষ না হয়। কিন্তু-
‘গীতিময় সেইদিন চিরদিন বুঝি আর হলো না
মরমে রাঙ্গা পাখি উড়ে সে গেলো নাকি
সে কথা জানা হলো না…..
চোখের ভাষাতে আজকে না হয়
মনের কথা বলো না।’
১১. মায়া মরিচীকা
হঠাৎই আচ্ছন্ন হয়ে থাকি। ঘুম আর জাগরণের মাঝামাঝি কোনো প্রতিতী যেন। স্বপ্ন আর কল্পনার পার্থক্য অনেক সময় বূঝতে পারি না। শত বছর আগের পুরোনো ধূলি মাখা কোনো পথ। এক গায়েন কবি পায়ে ধূলি উড়িয়ে হেঁটে এসেছিল কুসুমপুর।
ইছামতির তীরে ছোনপাতা ঘরে তার বাস। পিছনে ঘন বাঁশ ঝাড়। উঠোনেই একটি বাবলা গাছ। গাছ ভরা ছোট ছোট হলুদ ফুল। বাবলা তলায় বসে থাকত কবি, অনেকটা সিদ্ধার্থের মতো। কার কথা মনে করে তাকিয়ে থাকে বিষন্ন চোখে ইছামতির জলের দিকে। মনের দুঃখ কী ঝরে পড়ে যায়? মৃত্যুর পরে মানুষের কী হয়? এসব সে ভাবে। তারপর চোখ মেলে তাকায়। চারিপাশে সব কিছু কেমন কোমল সবুজ হয়ে আছে। আকাশটা কেমন নীল। মেঘগুলো ধীরে ধীরে কোথায় ভেসে যাচ্ছে যেন। সে চোখ বুজে থাকে। কখনো চোখ খুলে এই মাঠ, এই জলফড়িং, এই মেঘ, এই আকাশ সে দেখে।
ঠিক তখনই দূর থেকে হেঁটে আসে একটি মেয়ে। সেও আসে শতাব্দী পুরানো ধূলি পথের পথ ধরে। সব কবিদের জীবনেই হয়ত এমন স্বপ্ন দেখানিয়া রমণীর আগমন ঘটে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম হলো না। সেই মুখরিত রমণীর খিল খিল হাসির শব্দে সে চমকে ওঠে।
বাবলা গাছে হঠাৎ আচমকা বাতাস লেগে হলুদ ফুল সব ঝরে পড়তে থাকে। সেই নির্জন দুপুরে বাবলা গাছের তলায় কী কথা হয়েছিল তাদের? কী প্রেম ছিল? ঐ মেয়েটার নামই বা কী ছিল? যাকে ইছামতির জলে ভাসতে দেখেছিল জেলে মাঝি মল্লাররা।
উত্তর পুরুষেরা এবং অগনিত ভক্ত পাঠককুল কবির অনেক লেখা পড়িয়াছে কিন্তু সেই মেয়ের নাম তাহারা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে নাই।
১২. বিপুল তরঙ্গ রে
কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে তখন ভর্তি হয়েছি। শেষ কৈশোরের উন্মাতাল সময়কাল কেবল শুরু। সারা শরীর মনে কেমন যেন ‘বিপুল তরঙ্গ রে ‘। কলেজের নবীন ররণ অনুষ্ঠানে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে দ্বৈত কন্ঠে একটি গান গেয়েছিল। তাদের নাম আজ আর মনে নেই। একরকম অখ্যাত ছিল তারা। সেই অনুষ্ঠানের গান শুনে গ্রাম থেকে আসা এক অর্বাচীণ তরুণের মন কেমন যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো ঝলমলিয়ে উঠেছিল। কী এক আবেগ দিয়ে, কী এক প্রেমাশ্রিত কন্ঠে গেয়েছিল তারা সেই গান। আমি তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম গানটি । গানটি হয়ত অনেকের কাছে সাধারণ মনে হবে। কিন্ত আমার কাছে ঐসময়ে ঐ বয়সে অসাধারণ মনে হয়েছিল। বিশেষ করে তাদের গায়কী ভঙ্গি। যখন তারা একে অপরে মুখপানে চেয়ে গেয়েছিল :
‘তুমি সাত সাগরের ওপার হতে আমায় দেখেছ
আর মন ভ্রমরের কাজল পাখায় ছবি এঁকেছ
আমি ময়ুর পংখি নাও ভিড়িয়ে তোমায় দেখেছি
আর প্রবাল দ্বীপের পান্না ভেবে চেয়ে থেকেছি…’
আমার জীবনের একধরনের অব্যক্ত ভাবনা তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। ক্লাশে কয়েকটি মেয়ে ছিল আমাদের। কখনও কখনও ওদের সাথে খুব কথা বলতে ইচ্ছা করত। কখনও আবার ভয়ে আর লজ্জায় বেঞ্চের একপাশে চুপচাপ বসে থাকতাম। ক্লাশ শেষ হলে প্রায়ই একাকী ধানমন্ডি লেকের পাড় ধরে হেঁটে হেঁটে চলে যেয়ে বসতাম কোনও কৃষ্ণচূড়া ছায়াতলে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের ম্লান রোদ এসে মুখে পরত। তখন একটা অদ্ভুত মনখারাপের ভাব কোত্থেকে যেন চলে আসত আমার মুখের উপরে। একসময় লেকের সেই নির্জন রাস্তায় ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসতাম কলাবাগানের কালাচাঁদ রেস্টুরেন্টে। তখন আট আনা দিয়ে সিঙাড়া পাওয়া যেত। খিদে পেটে আমি দুটো সিঙারা খেয়ে নিতাম।
সেই তরঙ্গায়িত যৌবন সময়ে কাউকে যে ভাল লাগেনি তা নয়। অনেককেই খুব ভাল লেগেছিল। মনে হত মেয়ে তুমি আমার বন্ধু হও। তখন কার সাথে যে সম্পর্ক হয়েছিল, আর কাকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখতাম। আর কত যে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে। তার ইয়াত্তা নেই। সেই সব ভাঙ্গা গড়ার সময়কাল কখন যে শেষ হয়ে গেছে তাও জানতে পারিনি। শেষবারের মতো কলেজ ইউনিভার্সিটির গেট ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময়, একের পর এক সম্পর্ক গড়া আর ভাঙার মুহূর্তের মর্মর কথা আর কতজনেরই মুখচ্ছবি যে মনে ভেসে উঠেছিল, সেইসব মুখগুলো মনের কোণে অস্পষ্ট জলছবি হয়ে আছে।
জীবনের এ প্রান্তে এসে মনে হয়, জীবনের কোনও গানই স্বপ্ন দেখাতে পারেনি। সব ভাললাগাগুলো হয়ে গেছে বিগত জীবনের বিষাদসিন্ধু। সব রোমান্টিক ভাবনাগুলো হয়ে গেছে প্রেমের বৃন্দগান। চির মনখারাপের একান্ত এলেজি।
এখন সেই গান আর নেই। নেই যৌবনকাল। নেই বিপুল তরঙ্গ রে। তবুও —
‘তরঙ্গ মিলায়ে যায় তরঙ্গ উঠে,
কুসুম ঝরিয়া পড়ে কুসুম ফুটে।…
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥’
১৩. সে আসেনি
মেয়েটি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বাংলা একাডেমির গোল পুকুরপাড়ে। ফাল্গুনের সেই বিকেলে বইমেলায় আগত দর্শনার্থীদের কোলাহলে মুখর ছিল প্রাঙ্গণ। কেউ একজন মেয়েটিকে বলেছিল — ‘এসো তুমি আজ,আমিও আসব। দেখা হবে এই পুকুর পাড়ে।’ মেয়েটি ভেবেছিল ফাগুন সন্ধ্যা নামবে তাদের চোখের দিকে চেয়ে থেকে। ফুসকাওয়ালার দোকান থেকে পানি ফুসকা খাবে। তারপর দুজনে মিলে খুঁজতে বের হবে শামসুর রাহমানের ‘প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে’ কবিতার বইটি কিনতে। কিন্তু সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল ছেলেটি আর এলো না।
মেয়েটি ভাবছিল মানুষ এমন হয় কেন? কথা দিয়ে কথা রাখে না। তার সাথে এই ছলটুকু না করলে কী হতো না তার? সত্যিকারের ভালোবাসা কখনও এমন মিথ্যা করে কথা বলে না। চারপাশে কত ছেলেমেয়ে এখানে ঘুরছে। আমতলায় বসেছে যেন গল্প আর আড্ডার আসর। কেউ কেউ খাবার দোকানে বসে খাবার খাচ্ছে। গরম কফি কাপে দিচ্ছে চুমুুক।
মেয়েটি পরে এসেছিল আজ নীল রঙের শাড়ি। কানে পরেছিল জয়পুরী ইমিটেশনের দুল। হাতের নোখে মেখেছিল শাড়ির রঙে মিলিয়ে নেইল পালিশ। হাতের কাঁচের চুড়িগুলো তখনও রিনঝিন করছিল। সন্ধ্যার ফাগুন বাতাসে উড়ছিল মাথার চুল। মেয়েটি ভাবছিল, চোখের কাজল তার ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। খোঁপায় বাঁধা বেলীফুলগুলো কখন একটি একটি করে ঝরে পড়েছে। তার এই সাজগোজ নিরর্থক হয়ে গেল। শরীরের ভিতরে বয়ে যাওয়া ঘ্রাণগুলো প্রাঙ্গণের ধূলি বাতাসে মিলিয়ে গেল।
মেয়েটি বাড়িতে ফিরে যায়। রাতে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পড়তে বসে। অনাহুতভাবে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকে। মা এসে একবার জিজ্ঞেসা করে —
‘তোমার কী আজ মন খারাপ?’
মেয়েটি মাথা নেড়ে বলে — ‘না।’
রাতে সে আর কিছু খেলো না। শুয়ে পড়ে বিছানায়। ওর চোখে ঘুম আসে না। অন্ধকারে চেয়ে দেখে একটি আবছা মুখকে। যে বলেছিল আজ আসবে, কিন্তু সে আসেনি।
১৪. পিঞ্জিরা
হুইল চেয়ারের হাতল ঘুরিয়ে বৃদ্ধ নাজির আলি নিজেই আস্তে করে এগিয়ে যায় ঘরের এককোণে রাখা পুরনো লোহার পিঞ্জিরাটির কাছে। প্রায় ষাট বছরের পুরনো এই পিঞ্জিরাটি এতবছরে জং ধরে ক্ষয়ে গেছে। নাজির আলি তার অশিত হাত দিয়ে পিঞ্জিরাটি ধরে । যেন পরম মমতায় বার বার স্পর্শ করে দেখছিল পিঞ্জিরাটির দরজা, শিকল এবং শিকগুলি।
তখন সে একুশ বাইশ বছরের টগবগে যুবক। ঘরে নববিবাহিতা পরমাসুন্দরী বালিকা বধূ। একদিন রাতে গল্পের ছলে তার স্ত্রী আবদার করল — তাকে একটি ময়না পাখি কিনে এনে দিতে হবে। নাজির আলি পরেরদিনই বাজার থেকে একটি ময়না পাখি কিনে এনে দেয়। তার স্ত্রী পাখিটিকে পেয়ে যারপরনাই আদর যত্ন করতে থাকে। তিনদিন পর তার স্ত্রী এসে বললো, পিঞ্জিরা থেকে কখন পাখিটি উড়ে চলে গেছে, জানিনা। ‘
তার বালিকা বধূ আবারও বায়না ধরল, ময়না পাখি কিনে দিতে হবে। নাজির আলি আবারও তার স্ত্রীর জন্য ময়না পাখি কিনে এনে দেয়। এবারও তিন দিন পর তার স্ত্রী এসে বললো, কালরাতে কখন পিঞ্জিরা থেকে পাখিটি উড়ে চলে গেছে, জানিনা। এই বলে সে অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকে।
স্ত্রীর এইরকম কান্না দেখে নাজির আলি আবারও বাজার থেকে একটি ময়না পাখি কিনে এনে দেয়। এবার তার স্ত্রী ময়না পাখিটিকে সারাক্ষণ কাছে কাছে রাখল। রাতে ঘুমাবার সময়ও সে পাখিটিকে খাটের পাশে এক কোণে রেখে দেয়। যেন উড়ে চলে না যায়।
একদিন গভীর রাতে তার স্ত্রী দেখতে পায়, তার স্বামী চুপি চুপি পিঞ্জিরাটির দরজা খুলে ময়না পাখিটিকে ছেড়ে দিচ্ছে। এটা দেখে সে তার স্বামীকে বলে — ‘ তুমিই তাহলে পাখিগুলোকে ছেড়ে দিতে? ‘ নাজির আলি তার অবুঝ বালিকা বধূকে বুকে টেনে নিয়ে পরম আদর করে বলতে থাকে — ‘ পাখিকে খাঁচায় আটকে রাখতে নেই। ওরা খোলা আকাশে উড়তে চায়। এই যে ঘর! এই ঘরে তোমাকে যদি সারাক্ষণ আটকে রাখি, তোমাকে যদি বাইরে বের হতে না দেই, তোমার কেমন লাগবে? নিশ্চয়ই তোমার দম বন্ধ হয়ে আসবে। ‘
ঈশ্বর তখন কী ভেবে রেখেছিল নাজির আলি তা জানতে পারেনি। সে বেশি দিন তার স্ত্রীকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখতে পারে নাই। অকালেই এই ঘর ছেড়ে, এই সংসার ছেড়ে সে না ফেরার দেশে উড়ে চলে যায়।
এরপর ষাট বছর চলে গেছে। এই ঘরের ভিতরেই জীবনের বেশির ভাগ বছর নাজির আলি একাকী কাটিয়েছে। বিছানায় শুয়ে থেকে আর হুইল চেয়ারে বসে দিনগুলি যেন তার শেষ হয়না। হতভাগা নাজির আলি তাই মুক্তি খূঁজে এই ঘর থেকে বের হবার। ইচ্ছা হয় তাঁর এই পিঞ্জিরা থেকে বের হয়ে দূরে কোথাও উড়ে চলে যেতে।
১৫. ম্যাপল পাতা ঝরে পড়ে
আমার বয়স তখন ছয় কী সাত হবে । আমার বড় বোনের সবে মাত্র বিবাহ হয়েছে। এক বর্ষার দিনে বুবু প্রথম তার শ্বশুরবাড়িতে যায়। যাওয়ার সময় আমাকেও সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়িতে। বাড়ির ঘাট থেকে নৌকায় করে প্রথমে আমরা সিরাজগঞ্জের বয়রা ঘাটে যাই। সেখান থেকে স্টীমারে করে যমুনা পার হয়ে জগন্নাথগজ্ঞ ঘাটে যেয়ে নামি। তারপর আবার নৌকা করে পিংনার চিতলিয়া নামে একটি গ্রামে চলে গিয়েছিলাম। ঐখানেই ছিল বুবুর শ্বশুরবাড়ি।
এত বছর আগের কথা যে, আমি এখন সব বিস্মৃত প্রায়। আমার বয়স কতই ছিল? অনেক কিছুই পুরো মনে নেই। আমার মনে আছে বুবু তখন নিতান্তই চৌদ্দ পনের বছরের একজন বালিকা ছিল। আমাদের বোনদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সুন্দরী ছিল। বুবু পড়েছিল টিয়া রঙের একটি জর্জেট শাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে বুবু বাড়ির উঠোনে ছোট ছোট পা ফেলে হেঁটে এ ঘর থেকে ওঘরে যেত। ইন্দারা পারে যেয়ে বালতি দিয়ে জল তুলত। সকাল বেলা কবুতরদের ধান গম ছিটিয়ে খাবার খেতে দিত। বুবুকে নিয়ে আমার এই টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলি এখনও মনে আছে।
এর আট দশ দিন পরে বাবা আমাদের আনতে যায়। ফেরার পথে আবার নৌকা করে প্রথম জগন্নাথগজ্ঞ ঘাট আসি। সেখান থেকে আমরা স্টীমারে করে প্রমত্তা যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে সিরাজগঞ্জে বয়রা ঘাটে চলে আসি । বয়রা ঘাটে ছোট একটি পানসী নৌকা ভাড়া করেন বাবা। আমরা সেই পানসী নৌকা করে বাড়ির দিকে রওনা হই।
তখন শ্রাবণ মাসে বর্ষার পানিতে মাঠ ঘাট বিল নদী টইটুম্বর থাকত। আমার মনে আছে, সেদিন দক্ষিণা প্রবল বাতাস ছিল। মাঝি টানিয়েছিল নৌকায় বাদাম। শোঁ শোঁ করে আমাদের নৌকাটি কখনও আমন ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে, কখনও বিলে ভেসে ওঠা শাপলার ফুলের মধ্যে দিয়ে, কখনও ইছামতী নদী দিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসতে থাকে। নৌকা যখন বাড়ির ঘাটের কাছাকাছি চলে আসে, তখন আমাদের গ্রামেরই কেউ একজন হাসিমুখে বাবাকে বলেছিল — ” তালুকদারের ব্যাটা, গজ্ঞে থেকে মিষ্টি এনেছেন নাকি? বাড়িতে যান, আমাদেরকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে।” আমি নৌকায় বসে, তখন ঐ লোকের এই কথার অর্থ বুঝি নাই। বাড়িতে এসে দেখি, মা’র কোলের কাছে বিছানায় ছোট্ট একটি শিশু শুয়ে আছে। যে আমাদের পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ।
কয়দিন আমাদের বাড়িতে উৎসবের আনন্দ হলো। বুবু এসেছে শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার উপরে নতুন এক অতিথি। সবার এত আনন্দ যে! কে কার আনন্দ দেখে! আশেপাশে দূর গায়ে থেকে আত্মীয় স্বজনেরা নৌকায় করে বুবু ও নতুন বাবুকে দেখতে আসতে থাকে। যেন ‘আনন্দলোকে মঙ্গল আলোকে বিরাজ।’ যেন চারিদিকে হাসি রাশি প্রাণ।
ঠিক আটদিনের দিন একদিন সন্ধ্যা থেকে আমাদের সেই ফুটফুটে বাবুটি চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। অন্য কোনো অসুখ নয়, শুধুই চিৎকার করে কান্না তার। এ কান্না কিছুতেই থামানো যাচ্ছিল না। মা তার বুকের দুধ খাওয়াবার চেষ্টা করে, দুধও মুখে নেয় না। শুধুই চিৎকার করে কাঁদতে থাকে । আমার চাচাতো ভাই একজন এল.এম.এফ ডাক্তার ছিলেন, তিনি তার সমস্ত প্রচেষ্টা চালালেন কান্না থামাবার। আমরা ভাই বোনেরা অসহায়ের মতো সেই রাতে ওর কাছেই বসে ছিলাম।
বাবুকে বুবু তার কোলের ভিতরে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল। ঠিক প্রত্যুষে তার কোলের ভিতরেই বাবুর কান্না চিরতরে থেমে যায়। কাছ থেকে কোনো মৃত্যু দেখা আমার সেই প্রথম ছিল। আমার কিছুতেই মনে হলো না শিশুটি মরে গেল। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলাম তার বন্ধ চোখের দিকে। কী সুন্দর! চিৎকারহীন। পৃথিবীর সব রূপ আর সৌন্দর্য নিয়ে সে ঘুমিয়ে আছে। কিন্ত এই বিশ্বজগতেরে কোনো কিছুই শিশুটি দেখে যেতে পারল না। সবাই কাঁদছিল তখন। বুবুও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল ওকে বুকে চেপে ধরে ।
আজ ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখ। ২০১৫ সালে এইদিনে কানাডার মন্ট্রিলের একটি হাসপাতালে আমার সেই বুবু ইন্তেকাল করেন। সে এখন ঘুমিয়ে আছেন মন্ট্রিলের নিঝুম একটি কবরস্থানের মাটির নীচে। প্রতি বসন্ত দিনে হয়ত তার কবরের উপর শুকনো ম্যাপল পাতা ঝরে পড়ে। শীতে সাদা বরফে ঢেকে থাকে হয়ত কবরের মাটি। আপনজনদের এই রকম ঘুমুতে থাকতে দেখলে আমার দুই চোখে কেমন যেন ঘুম নেমে আসে। কিছুই ভাল লাগেনা।
নিজেকে খুব দুঃখী মনে হলে ছুটে যাই কবিগুরুর কাছে। লিখেছিলেন তিনি —-
‘অনন্ত জনম মাঝে গেছে সে অনন্ত কাজে ,
সে আর সে নাই ।
আর পরিচিত মুখে তোমাদের দুখে সুখে
আসিবে না ফিরে ।
তবে তার কথা থাক্ ,যে গেছে সে চলে যাক
বিস্মৃতির তীরে । ‘
১৬. আমার বসন্ত দিনে
পৃথিবীতে সেই সৌভাগ্যবান যিনি কোন বালিকার প্রথম ভালোবাসা পেয়েছে কিংবা তার প্রথম ভালোলাগার মানুষ।
গল্পটা এমন।
এক আলস্য ফাগুন দুপুরে একটি চিঠি এলো। বিকেলের রোদ্র ছায়া তখনও চোখে মুখে লেগে আছে। তরুণ মন তখনো তৈরি হয়নি কোন স্বপ্নের ঘোরে। পাখি সব করে রব করে রাত্রি পোহায়। প্রতি দিনের জীবন ধারা স্বপ্নেও নেই, যাযাবরেও নেই। জীবনের কোন্ গোপন অলিন্দে কখন কাকে দেখেছিলাম, কখন কাকে ভালোলেগেছিল তা সবই মনে নেই।
অনেক সময়ই তো ভালোলাগে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা। নদীর কূল ধরে হাঁটতে হাঁটতে মাঝি মল্লারদের গান শুনতে ভালোলাগে। ভালোলাগে সন্ধ্যায় ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির। এই সুন্দর পৃথিবীতে এতো সব চমৎকার জিনিস রয়েছে যে, সেসব ভালোলাগার জিনিসকে দেখে শেষ করা যায় না। মনেও রাখা যায় না অনেক কিছু।
কি লেখা ছিল সে চিঠিতে :
‘প্রিয় সুহৃদতম,
আমি যেদিন প্রথম দেখেছিলাম তোমাকে সদরঘাটের প্লাটফর্মে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। দেখছিলে বুড়িগঙ্গার জল। হাতে তোমার সিগারেট জ্বলছিল। সেদিন সন্ধ্যায় ছিল নদীতে ঝিরিঝিরি হাওয়া। বাতাসে উড়ছিল তোমার মাথার চুল। আমি তোমাকে অনেক কাছ থেকে দেখেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার দিকে একবারও ফিরে তাকালে না। এই যে তুমি আমায় একটিবার দেখলে না। এই অহংকারটি ভালো লাগলো আমার। এর আগে ভালো লেগেছিল তোমার কবিতা এবং তোমার আবৃত্তি। এসব তুমি কিছুই জানতে না। আম্মু আর ভাইয়া ছিল আমার সাথে। আমি ভাইয়াকে বলে তোমার একটা অটোগ্রাফ নিয়েছিলাম সেদিন । মনে আছে তোমার? অটোগ্রাফ নেওয়ার ছলে তোমার ঠিকানাও চেয়ে নিয়েছিলাম। বলেছিলাম — অকেশনে গ্রিটিং পাঠাবো।
তুমি চলে গেলে চাঁদপুরে। আমরা চলে এসেছিলাম বরগুনায়। তারপর মাঝে চলে গেল একটি বছর। তোমাকে আর কোনও গ্রিটিংস পাঠানো হয়নি। কিন্তু তুমি যে আমার প্রথম ভালোলাগা ছিলে সেটি তুমি জানলে না। জানলে না তাই ভালোও বাসলে না। গত এক বছরে তোমাকে নিয়ে আমি স্বপ্ন দেখলাম। নিভৃতে বসে বসে তোমাকে ভেবেছি কত প্রহর। এক অজানা আলোয় তুমি আমার জীবনকে আলোকিত করলে। এই চিঠিখানা পড়ে তুমি নির্বাক হয়ে বসে থাকবে হয়তো কিছুক্ষণ। একমাত্র আমিই জানি, তোমাকে আমার কতটা ভালোলাগে। আজ আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, তার সবটাই তো তোমারই দান। কতজন ভালোবাসতে চাইলো, কত বসন্ত পাখি এসে গান শোনাতে চাইলো। কিন্তু তুমিই আমার বসন্ত দিনের গান হয়ে রইলে। বৈশাখী ঝড়ের রাতেও রত্ন কুড়িয়েছি আমি । সব ঝড়ের রাতে কুড়ানো রত্ন জমিয়ে রেখেছি তোমায় দেবো বলে। কবে আবার দেখা হবে আমাদের? প্লাটফর্মে দাঁড়ানো বুড়িগঙ্গার তীরে দেখা তোমার মুখখানি আজো আমার বেঁচে থাকার নিঃশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ে। ইতি — সাহানা।’
চিঠিখানি পড়ে সেদিনের সেই বিকেলে দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছিল আমারও। চিঠির এ পাতায় ও পাতায় এবং খামের উপর কোথাও সাহানার ঠিকানা খুঁজে পেলাম না। ভেবেছিলাম, পরে হয়তো আবার চিঠি লিখবে, কিন্তু লেখেনি আর।
তারপর আমার জীবন থেকে কতো বসন্ত চলে গিয়েছে। কতজনই তো আমার বসন্ত দিনে বসন্তের গান শোনাতে চেয়েছিল। কিন্তু সাহানা নামের সেই মেয়েটি আমার কোন বসন্ত দিনেই তার কোন বসন্ত গান শোনাতে আর আসেনি।
১৭. তারে খুঁজে বেড়াই
এই গোলকে ঘুরতে ঘুরতে কতোজনের সাথেই তো দেখা হয়ে যায়। পথ চলতে চলতে পথের উপরে কিংবা কফি হাউসে গরম চা চুমক দিতে দিতে। তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় কবি জসিম উদদীন হলে। আমার রুমমেটের কাছে তিন দিনের অতিথি হয়ে সে এসেছিল। চিত্রালীতে প্রকাশিত ‘সেই চোখ’ কবিতাটি পড়ে সে আমার ভক্ত হয়ে যায়। অদ্ভূূত এক বন্ধু বৎসল চুম্বক শক্তি ছিল তার। তাইতো তিনদিনেই সে আমার প্রাণের ভিতর ঠাঁই করে নিয়েছিল।
তারপর অনেক বছর দেখা নেই। ভুলেই গিয়েছিলাম সেই স্বল্প সময়ের বন্ধুটিকে। এক সন্ধ্যায় ফার্মগেট বাস স্ট্যান্ডে আমি দাঁড়িয়ে আছি। পাবলিক বাসে আসব এয়ারপোর্টে। হঠাৎ আলো আঁধারিতে সেই বন্ধুটি আমার কাছে এগিয়ে আসে। যার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিলো জসিম উদ্দীন হলে। সেও যাবে এয়ারপোর্ট বাস স্ট্যান্ডে। পরে জানলাম আমার এলাকা দক্ষিনখানে একটি মেসে সে ভাড়া থাকে।
সে সময় আমার কর্মহীন জীবন চলছিল। নতূন বিয়ে করেছি। হঠাৎ সেই বেকারত্ব জীবনে এই বন্ধুটি আমার সকাল বিকালের সাথী হয়ে যায়। প্রায় তিন মাস ঢাকা শহরের কতো পথে পথে একসাথে ঘুরেছি তার কোনো শেষ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, লাইব্রেরী চত্বর, পাবলিক লাইব্রেরী, যাদুঘর প্রাঙ্গন, ধানমন্ডি লেকের পার, পুরানো ঢাকায়,পথের উপর টং চা’র দোকান, কতো জায়গায় যে দু’জন ঘুরে বেড়িয়েছি, আর সময় কাটিয়েছি।
একবার সদরঘাটের প্লাটফরমের রেলিং এ দাঁড়িয়ে দু’জন বুড়িগঙ্গার জল দেখছিলাম, কতো লঞ্চ এসে ভিড়ছে প্লাটফরমে। কতো মানুষ জীবিকার জন্য আসছে ঢাকা শহরে। মনটা কেমন উদাস লাগছিল। জীবনের প্রতি হতাশার কথা বলছিলাম ওকে। সে তখন আমার ঘাারের উপর হাত রেখে বলেছিলো- Never give up easily in life, success is right around the corner.
ওর এক কাজিন ছিল একটি বেসরকারী ব্যাংকের পরিচালক। নিজে ভালো কিছু করত না। তরপরেও তার কাজিনকে বলে ব্যাংকে ভালো একটি চাকুরী আমাকে পাইয়ে দেয়। এরপর থেকে আমি চাকুরীতে ব্যস্ত হয়ে যাই। আগের মতো তার সাথে আড্ডা বা ঘোরাঘুরি করা সম্ভব হতো না। এর কিছুদিন পর দক্ষিনখানের মেস ছেড়ে কলাবাগানের একটি মেসে সে চলে আসে।
এরপর মাঝে মাঝেই সুযোগ সময় পেলে কলাবাগানের মেসে যেয়ে ওর সাথে আমি দেখা করতাম। একবার প্রায় ছয় মাস, ওর সাথে আমার দেখা করা হয় নাই। পরে যখন যাই, যেয়ে দেখি কলাবাগানের ঐ মেস ছেড়ে সে অন্যত্র চলে গেছে। মেসমেটরাও বলতে পারেনি সে কোথায় গিয়েছে।
এই পৃথিবীর পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে কতোজনের সাথেই তো মানুষের দেখা হয়। যে পথগুলো দিয়ে আমি ঘুরেছি, সে পথের উপর দিয়ে আকাশ ছিল, কিন্ত সে পথে তার দেখা পাই নাই। কত শূন্য প্রান্তরের মধ্য দিয়ে একাকী দৌড়ে দৌড়ে হেঁটেছি কিন্তু কোথাও আমার সে বন্ধুটি ছিল না। এখন ফেসবুক,গুগল, টুয়েটারেও সার্চ দিয়ে দেখেছি, সেখানেও তার খোঁজ পাওয়া যায় নাই।
মানুষ ঘুরতে ঘুরতে নাকি চাঁদ হয়ে যায়, যেখানেই থাক, পৃথিবীর যে কোনো কোণকে নাকি সে আলোকিত করে রাখে। আমিও আমার সেই বন্ধুটির আলোর দ্যূতি গায়ে মাখি। আমার জীবনের এক ক্রান্তিকালে যে উপকার সে করেছিল, তার ঋণ আমি শোধ করতে পারি নাই। সেই ঋণ শোধ করার জন্য আমি এখনো এই ঢাকা শহরের পথে পথে তাকে খুঁজে বেড়াই।
ওর ঠিকানা আমার পুরোপুরি জানা নেই। গ্রামের নামও মনে নেই। শুধু পোস্ট অফিস ও থানার নামটি মনে আছে। মোঃ শফিকুল ইসলাম, পোঃ ভিটঘর, থানা- নবীনগর, জেলা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া। কেউ একটু খুঁজে দেখবেন কি ?
১৮. এক রাজকুমারীর গল্প
রাজকুমারীর প্রথম ভালোলাগা আমাকেই লেগেছিল। আমিই ছিলাম তার প্রথম ভালোবাসার মানুষ। সে ছিল তখন বালিকা থেকে তরুণী পর্যায়ের একটি মেয়ে। ভালোবাসা কী বুঝত না ঠিকমতো। স্বপ্ন দেখত না অন্য কাউকে। বুঝত না সংসার গড়তে হয় কিভাবে? তারপরও আমি তাকে প্রেম দিয়েছিলাম। যা কোনো বিষয় সম্পত্তির মতো করে দেইনি। দিয়েছিলাম অপার্থিব আলোর মতো করে। মন থেকে মননে তা ছড়িয়ে গিয়েছিল ।
রাজকুমারীকে আমার পাওয়া হলো না। বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র । স্বামীর ঘরে যেয়ে সে প্রেমের আলো ছড়ালো। যেন ত্রিভূবন আলোকিত হয়ে গেল, আমারই দেওয়া প্রেম রশ্মিতে। সংসার বাঁধল রাজকুমারী। সন্তান, ধন দৌলত সব পেল সে।
তারপর কত বছর চলে গেছে। কত বসন্ত হয়েছে পলাশ শিমুলে রঙ্গিন। কত পূর্ণিমা আলো ছড়িয়েছে কত অন্ধকার রাত্রিতে। দিনগুলি কেটেছে আমার কেবলই প্রেমহীন একাকীত্বে। নিজ হাতে কখনও জ্বালাতে মন চায়নি ঘরে সন্ধ্যা বাতি। ভাবতাম, এমনি এক আঁধার রাত্রিতে আলো জ্বেলে রাজকুমারী হয়ত ফিরে আসবে একদিন। কিন্তু আসেনি।
অনেক বছর হলো রাজকুমারীর দেখা নেই। সে জানেও না আমি কেমন আছি। আজ তার ফেসবুকের ওয়ালে একটি লেখা দেখতে পেলাম। গল্পের মতো করে লিখেছে সে। মনে হলো যেন তারই কথা। এখানে অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি।
” তুমি আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছিলে সেই ভালোবাসা দিয়েই ভালোবাসলাম আমার স্বামীকে। কী ভাবে প্রিয়তর করতে হয় তা তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে। আমি ঠিক সেইভাবেই তাকে প্রিয়তর করলাম। তুমি একদিন বলেছিলে, প্রেম কোনো বিষয় সম্পত্তি নয়, যে কাউকে বস্তুর মতো করে দান করা যাবে। কিন্তু তোমার দেওয়া সেই প্রেম বস্তুর মতো করেই আমি আমার স্বামীকে দান করে যাচ্ছি । “
১৯. সাদা পৃষ্ঠার শূন্যতা
আবারও পুরনো টিনের বাক্স ঘেঁটে পাই একটি লাইন টানা বাংলা খাতা। খাতার প্রথম পাঁচছয় পাতা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া। ছিঁড়ে ফেলা পাতাগুলো পরের পাতায় দিনলিপির মতো কিছু লেখা আছে। লেখাগুলো অস্পষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু পড়া যায় —
২৬ শে জুন, ১৯৮৫ ইং
এম এম ওয়ার্ড, বেড নং ১৮
হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল। ঢাকা।
আজ আমাকে কেউ দেখতে আসেনি। মিতা খালা, তাজুল, প্রেমনাথ, দীপক কেউ না। শহরে হরতাল ছিল। তাই কী হয়েছে? তুমি তো মগবাজারেই থাকো। কতদূর আর? হেঁটে হেঁটে তো আসতে পারতে!
বিকালে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলাম একাকী। আমগাছের ডাল হেলে আছে ব্যালকনির দিকে। নির্জন পাতাগুলো খুব সবুজ ছিল আজ। তুমি আসলে তোমাকে নিয়ে দাঁড়াতাম ঠিক এখানেই।
ডাঃ কানিজ মাওলা ডিচচার্জ অর্ডার করে গেছেন। কাল সকালে হাসপাতাল ছেড়ে বোনের বাসায় চলে যাব। সকালবেলা তুমি আসতে পারবে না জানি। তাই দেখা হবে না।
ফ্ল্যাশব্যাক:
জীবনের রঙিন আলোরেখা গুলো কত উজ্জ্বল এখনও! এই খাতাটি নাজনীন একদিন হাসপাতাল বেডে আমাকে দিয়ে বলেছিল –‘ যখন তোমার মন খারাপ লাগবে, কিংবা মন ভাল লাগবে, তখন এই খাতার পাতায় কিছু লিখে রেখ আমার জন্য। আমি প্রতিদিন তোমাকে দেখতে এসে একটি করে পাতা ছিঁড়ে নিয়ে যাব।’
খাতার পরের পাতা গুলো উল্টিয়ে দেখলাম। কোথাও কিছু লেখা নেই। আছে সেখানে দীর্ঘশ্বাস আর সাদা পৃষ্ঠার শূন্যতা।
২০. কঙ্কনা উপাখ্যান
সেই অনেক দিন, অনেক কাল, বহু বহু বছর আগের এক শ্রাবণ রাত্রির কথা। ঝিলিক ঝিলিক জ্যোৎস্না ঝরছিল সেই রাতে। অনুপম আলো আর জোনাক জ্বলা আঁধারে পথ চলতে চলতে প্রাচীন এক বটবৃক্ষ তলে দাঁড়িয়েছিলাম। ঘর ছেড়ে ঘরহীন হয়েছিলাম, আকাশ আর মাটি ছিল সহচর।
কী আনন্দময় নিশী কাব্য। চারদিকে তাকিয়ে যখন দেখেছিলাম, পৃথিবী ছিল জনমানবহীন। রাত দেখছিল আমাদের রোমাঞ্চিত হৃদয়ে। মিটি মিটি চোখ তুলে তাকিয়েছিল লুব্ধক কালকুট, বিপাশা, ললিতা, চন্দ্রাবলী আরও কতজন, আরও কত তারা। বিনম্র হাওয়ায় দুলছিল অশ্বত্থ পল্লব।
আজ তোমাকে খুব করে পুরনো নামে ডাকতে ইচ্ছা করছে। পুরনো সেই তুমি। প্রথম তোমাকে কী নামে ডেকেছিলাম মনে আছে? কঙ্কনা। কী কারুকার্য তোমার রূপ ছিল! আমি প্রাচীন চর্যাকার আর বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিকারদের লেখা ঘেঁটে ঘেঁটে তোমার রূপ মিলিয়েছিলাম।
তুমি তন্বী, তপ্তকাঞ্চনবণা কিন্তু চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়না ছিলে। নিবিড় কালো চোখ দুটি শান্ত অপ্রলভ, সর্বাঙ্গের উচ্ছলিত যৌবন যেন চোখ দুটিতে এসে স্থির নিস্তরঙ্গ হয়ে যেত। তোমার অন্তঃসলিলা যৌবন যেন ফল্গুধারায় বয়ে চলত।
এই কথা কী সুধায়েছিলাম তোমাকে সেই রাতে?
‘এস এস বধু এস, আধ আঁচরে বস,
আজি নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।
আমার অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধেনে মিলাইল বিধি।’
সেই শ্রাবণ রাত্রি গেছে। তারপর কত রাত্রি চলে গেছে। যে গেছে—তার সবই গেছে, কুল গেছে—মান গেছে,রূপ গেছে, লাবণ্য গেছে। কত নতুন পুরাতন হলো। কত নামে কতজনকে ডাকলাম। কিন্তু ঘুরে ফিরে কঙ্কনাই যে শ্রেয়া হয়ে থাকল। সকল রাত্রির আঁধারে দূরবর্তী একটি নক্ষত্র হয়ে আজও সে জ্বলে আছে।
২১. পিছনের পৃষ্ঠা
পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম পিছনের দিকে।
১৬ জুলাই, ১৯৮২ ইং
কিছু গান আছে আমার হয়ে কানে বাজে। ‘এই মণিহার আমায় নাহি সাজে।’ কেন জানি না, এই গানটি আমার নিজের গান হয়ে গেছে। নিজে খেয়াল না করে যে সুর গুনগুন করি।
দুপুর ছিল সেই সময়। শ্রাবণ দিনে বৃষ্টি না হলে মানায় না। কিন্তু, সেদিন ছিল কাঠ পোড়া রোদ। চানখাঁর পুল বাস স্ট্যান্ড থেকে জয়দেবপুরের কাঠবডি বাসে করে সোজা লতিফ গেট যেয়ে নামি — আমি এবং ফারিয়া মির্জা।
বর্ষার ফুল লাগিয়েছিলাম ঘরের চারপাশে। কয়েকটি ফুলেই যেন মালঞ্চ ঘেরা ঘর যেন আমার। নতুন ফুল এসেছিল। এত সুন্দর সাজের ফুল ফুটে থাকে, একলা দেখি, একলা অনুভব করি। এই ফুল দেখবার সাধ হয়েছিল ফারিয়া মির্জার।
ফারিয়া আমার বন্ধু। ওর স্বামী কৃষি বৈজ্ঞানিক। দেরাদুনে একটি কৃষি কর্মশালায় যোগ দিতে চলে গিয়েছিল। ফারিয়া বলেছিল, ‘কেমন যেন একলা লাগে আমার। তোমার ফুল দেখতে যাব। এবং দেখব তোমার মালঞ্চ ঘেরা বাড়ি।’
লতিফ গেট থেকে কাঁচা রাস্তার পথ। তবুও রিক্সায় উঠি। রিক্সা এ দোল ও দোল করে চলে আসে। পথ ছিল সামান্য। মাথার উপর বর্ষার রোদ। ফারিয়া বলছিল–
‘ভাল লাগছে এই পথ।’
রাতে বৃষ্টি হয়ে যাওয়া মাটিতে রোদ্দুর পড়ে গন্ধ ভেসে আসছিল।
মালঞ্চ ঘেরা বাড়িতে সেদিন অনেক ফুল ফুটেছিল। গন্ধরাজ পাপড়ি মেলেছিল ভুজঙ্গের মত। বেলী আর রক্ত জবা রঞ্জিত করেছিল তার চারপাশ।
এই সৌন্দর্য ছিল স্বর্গীয়, যে দেখে সেই জানে, যে গন্ধ নেয় সেই বোঝে এর তীব্র সুবাস। যে কন্ঠে পরে সেই জানে, এই মণিহার কেমন?
ফারিয়া সেদিন একটি গান গেয়ে শোনায়েছিল আমাকে। ঠিক ঐ গানটি, এই মণিহার আমায় নাহি সাজে। যখন ও গাইছিল গান, তখন অলিন্দে বসে দেখেছিলাম — প্রখর রোদ্দুরে মালঞ্চের সব ফুলের পাপড়ি নির্যাসিত হয়ে ঝরে পড়ছে।
পৃষ্ঠাগূলো আর উল্টালাম না। বন্ধ করে রাখি। জীবনের অনেক সৌন্দর্যে অমঙ্গল লুকিয়ে থাকে।
২২. টিনের বাক্সে সোনা-রৌপ্য
পুরোনো টিনের বাক্স থেকে আজ একটি চিঠি পেলাম। খাগড়াছড়ি থেকে চিঠিটি লিখেছিল চিনু চাকমা। চিনু আমার কলম বন্ধু ছিল। খাগড়াছড়ি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ত। চিঠিটির মাঝের কিছু অংশ আমি এখানে উল্লেখ করলাম। চিঠির তারিখঃ ২১/১২/ ১৯৮০ ইং, গোলাবাড়ী, খাগড়াছড়ি।
বন্ধু আমার,
…………………. ………
………….. ……. ……..
পাহাড় দিনে দিনে আরও বেশি অস্থির হয়ে উঠছে। ঘরে থেকে বেশি বের হতে পারি না। পোস্ট মাস্টার কাকা খবর দিয়েছে, তোমার দুই তিনটি চিঠি নাকি এসে রয়েছে। ভাবছি কাল আনতে যাব। এবং সাথে এই চিঠিটা পোস্ট করে আসব।
ঠিকমতো কলেজেও যেতে পারছি না। পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত দিতে পারব কিনা, ঈশ্বর জানেন। আমাদের পরিবারের উপর চাপ আসছে দুই দিক থেকেই। হয়ত বেশি দিন আর এখানে থাকা সম্ভব হবে না। চলে যেতে হবে আরও দূর পাহাড়ে, গভীর অরণ্যে। নতুবা পার্শ্বের দেশে ত্রিপুরায়।
তোমাকে হয়ত আর চিঠি লেখা সম্ভব হবে না। তোমার চিঠিও আমি পাব না। খুব খারাপ লাগবে। যে অরণ্যেই থাকিনা কেন, যত দূরে যত দূর দেশেই যাই না কেন, তোমার কথা খুব মনে পড়বে।
এ জীবনে মনে হয় তোমার সাথে দেখা হবে না। কী এক পোড়ামুখী হয়ে জন্মেছিলাম, কিছুই পাওয়া হলো না।
………. ……….. ……
……. …… …….. …….
ভালো থেকো তুমি।
জন্ম থেকে জন্মান্তর ধরে তোমাকে আমি মনে রাখব।
ইতি — চিনু ।
এরপর চিনুর কাছে থেকে মনে হয় তিন চারটি পত্র পেয়েছিলাম। তারপর আর পাই নাই। সম্ভবত ওরা পলাতক জীবনে চলে গিয়েছিল।
১৯৮৩ সনে নভেম্বরে একদিন দুপুরে অফিসে বসে আছি। তারিখটা সম্ভবত বারো তারিখ হবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকাটি হাতে নিয়ে পড়তে যেয়ে একটি খবরের উপর চোখ পড়ে। …’পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর প্রতিপক্ষের গুলিতে শান্তি বাহিনী প্রধান মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা সহ আরও সাতজন সহযোগী নিহত হয়েছে।’ ….. ভিতরে খবরে জানতে পারি, তাদের ভিতর অপর্ণা চরণ চাকমাও রয়েছেন। এই অপর্ণা চরণ চাকমা হচ্ছেন চিনুর পিতা।
কয়েকদিন পর একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে পত্রিকা পড়ছিলাম। দেখি, টেবিলের উপর রাঙামাটি থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকাটি রয়েছে। ঐ পত্রিকায় একটি জায়গায় অপর্ণা চরণ চাকমার উপর এই কথাগুলো লেখা আছে —-
‘…..গ্রাম পঞ্চায়েত বিভাগের সহকারী পরিচালক
অপর্ণা চরণ চাকমার ’র মরদেহখানি সকলের সামনে খুলে ধরলেন। … তাঁকে দেখার সাথে সাথে তাঁর শোক সন্তপ্ত পত্নী, দুই ছেলে ও এক কন্যা আকাশ বিদীর্ণ করা ক্রন্দনে আর্তনাদ করে উঠলো। … এই মর্মভেদী দৃশ্য থেকে উপস্থিত লোকজন তাদেরকে বোঝাবার ভাষা হারিয়ে তারাও কান্নায় ভেঙে পড়ে। ……..’
এরপর চিনু চাকমার আর কোনো খবর পাইনি। চিনু লিখেছিল — ‘ তোমাকে আমি জন্ম জন্মান্তর ধরে মনে রাখব।’ চিনু আমাকে মনে রেখেছে কিনা জানি না। আমি চিনুকে এখনও মনে রেখেছি। হয়ত জীবনের বাকি সময়টাতেও মনে রাখব।
২৩. এই মায়ালোকে
সবিতা মালবী বাংলাদেশের যমুনা পাড়ের মেয়ে।
কিন্তু সে এখন এ পাড়ে নেই। যৌবন প্রস্ফুটিত সময়ে সে ভালবেসেছিল এক তরুণকে। তারই ঘরে সে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু কনকাঞ্জলীর সময় হলো ক্রান্তিকাল। হঠাৎ সানাইয়ের সুর থেমে যায়। অমাঙ্গলিক এক ঝড়ে অঞ্জলীর সব ফুল মাটিতে পড়ে যায়। হলো না তার আর ধান দূর্বার মঙ্গলচরণ পেরিয়ে কারোর ঘরে যাওয়া।
তারপর কত দিন হয়েছে গত। সবিতা এখন বিগত যৌবনা। অনেক মঠ, মন্দির,আশ্রম ঘুরে এখন সে ক্লান্ত। একদিন সূর্যক্লান্ত এক বিকেলে দেরাদুনের হিমালয়ের পাদদেশে মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে তার সাথে দেখা হয় এক পর্যটকের। সেও বাংলাদেশের এক যুবক। পার্বত্য সোপান পেরুতে পেরুতে কথা হয়েছিল সেই যুবকের সাথে। পার্বত্য শিখরে যে পাথর খণ্ডে বসে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করত, সেই পাথরে বসে সবিতাকে যুবক বলেছিল — ‘তুমি কী আমার সাথে তোমার সেই যমুনার তীরে কুসুমপুর ফিরে যাবে ?’
রুক্ষ বসন্তের মায়াবতীর পার্বত্য গাত্রে সারি সারি পাইন গাছ থেকে শুকনো পাতা দুঃখের মর্মর বেদনার মতো ঝরে পড়ছিল তখন। অরণ্যের আলোছায়াময় পথগুলো নির্জন অন্ধকারের মতো আঁধারে ঢেকে আসছিল। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে নীলনীলনীল আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ঢেকে যায়। এত পাখির কলরব যেখানে সারা মায়াবতীতে। আচমকা সব পাখির কলরব যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
শত বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দের সেই ধ্যান মগ্নের ক্ষণ যেন মূর্তিমান হলো সেই পার্বত্য শিখরে। কোথাও কারও স্পর্শ নেই। কারও শরীরের ছায়া পড়ল না কারও উপরে। বিবেকানন্দের সেই পাষাণ খন্ডে বসে সবিতা সেই যুবককে বলেছিল —
‘এই খেলাঘর, এই ধুলোমাটির বাইরে কি রসদ নিয়ে যাব, গিয়ে কী বলতে পারব, আমি কানায় কানায় পূর্ণ? সংসারের চার দেওয়াল কী আমাকে সেই বিস্ময় এনে দিতে পারবে, যা আমি মায়াবতীর এক নির্জনবাসী যোগীর আশ্রম প্রাঙ্গনে সন্ধ্যা নামার পূর্ব মুহুর্তে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম? সেই অনুভব কি আমায় সংসার দেবে? যে অনুভব আমায় দিয়েছিল উত্তরকাশীর ক্ষীনধারা গঙ্গার বয়ে চলার আওয়াজ?
আমি যোগিনী হয়েই ভালো আছি। চলার পথে কত নতুন মানুষ, কত নতুন গল্প, কত অভিজ্ঞতা, কত ভাটিয়ারী ভোর, কত বাগেশ্রীর সুরে মেশা সন্ধ্যা, কত মালকোষী রাত … একে ছেড়ে যাই কি করে? ঐ চার দেওয়ালের খাঁচায়? এখানে এরা কি কম বড় সঙ্গী?’
যমুনার পাড়ের সেই ছায়া সুশীতল কুসুমপুরকে তুমি আমাকে মনে করে দিও না। নয়নের সমস্ত জল সব শুকিয়ে গেছে। আর কোনও জল নেই যে, তোমাদের ঐ যমুনার জলে যেয়ে ফেলতে পারব।
এই বিশ্বলোকের সারসত্য কী আমি জানি না। তবে আমার জীবনের সত্বা আমি খুঁজে পেয়েছি এই মায়ালোকে, মায়াবতীর এই অদ্বৈত আশ্রমে। সংসার লোকে ফিরিবার অন্য কোনো পথ তাই আমার জানা নেই।’
২৪. চামেলী
চামেলী উজান গাঁয়ের মেয়ে। আমাদের বাড়ি ভাটিতে।দু’জনেরই বাস নদীর কূলে। সে বছর যমুনায় নৌকা বাইচ হয়েছিল। নৌকা বাইচ দেখতে চামেলী এসেছিল উজান থেকে। ওর পরনে ছিল ফ্রক। ওড়না পড়ার বয়স তখন ওর হয়নি। সে কি তুমুল নৌকা বাইচ ! আমাদের গাঁয়ের নৌকা ওদের গাঁয়ের নৌকার কাছে হেরে গিয়েছিল। এ জন্যে ও আমার দিকে চেয়ে পরিহাস করে মুচকি হেসেছিল। আমিও দিয়েছিলাম ওর গালে একটি চিমটি।
দু’জনেই একই স্কুলে পড়তাম। চামেলী যত বড় হতে থাকে, ওর সাথে কথা বলা তত কমে যেতে থাকে। এরই ফাঁকে কখন চামেলী বালিকা থেকে যৌবনবতী মেয়ে হয়ে ওঠে, আমি বুঝতেই পারি নাই। ও এখন ওড়না পড়ে, সালোয়ার কামিজ পড়ে, শাড়ি পড়ে। মাঝে মাঝে মাথায় ঘোমটাও দেয়।
ক্লাশে চামেলীর সাথে কথা বলতে পারতাম না। স্কুলে তখন নিয়ম ছিল, মেয়েরা স্যারদের পিছনে পিছনে এসে ক্লাশে ঢুকবে, আবার ক্লাশ শেষে স্যারদের পিছনে পিছনে বের হয়ে চলে যাবে। কিন্তু আমরা গোপনে গোপনে ঠিকই একে অপরকে দেখে নিতাম।
এসএসসি পরীক্ষায় আমি পাশ করি। চামেলী ফেল করে। আমি চলে আসি ঢাকায়। যেদিন ঢাকা আসব তার আগের দিন চামেলীকে একনজর দেখার জন্য নৌকা করে চলে যাই চামেলীদের গাঁয়ে। ভাটি থেকে স্রোতের উজান পথে নৌকা বেয়ে যেতে মাঝির খুব কষ্ট হচ্ছিল। তখন পড়ন্ত বিকেল। আমি যেয়ে ওদের বাড়ির আঙ্গিনায় আম গাছ তলায় দাঁড়াই। চামেলী একবার জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল । আমি দূর হতে ওকে দেখি। ওকে ইশারা দিয়ে একটি ছিন্ন কলা পাতা মাটিতে ফেলে রেখে চলে আসি। বাঁশের কাঠি দিয়ে তাতে লেখা ছিল — ‘মনে রেখো’।
ঢাকার জীবন সুন্দর ভাবে চলছে। কলেজে যাই । নিত্য নতুন বন্ধু বান্ধব। চিত্তের উৎফুল্লতাই অন্যরকম। ইতোমধ্যে এইচএসসি পাশ করি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ছুটিতে কখনও বাড়িতে গেলে চামেলীর খোঁজ খবর নিতাম না। ওর গাঁয়েও কখনও যেতাম না। অনেকটা ভূলেই যাই চামেলীর কথা।
জীবন আমার গড়ে উঠেছে যেন স্বর্ণ-মণি-কাঞ্চন খচিত হয়ে।
গ্রীস্মের ছুটিতে সেবার বাড়িতে গিয়েছিলাম। ছোনগাছা হাটে চামেলীদের গাঁয়ের আমার সহপাঠি মুকুলের সাথে দেখা হয়। কি মনে করে মুকুলকে জিজ্ঞাসা করি চামেলীর কথা।
আমি ঃ চামেলীর খবর কি ?
মুকুল বিস্মিত হয়ে বলে — তুই কিছু জানিস না ?
আমি ঃ না।
মুকুল ঃ ওতো গত বর্ষায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।
আমি ঃ নিরুদ্দেশ মানে ?
মুকুল ঃ চামেলী হয়ত যমুনার জলে ভেসে গেছে। কেউ সঠিক করে বলতে পারেনা। ওর একটা বিয়েও ঠিক হয়েছিল। বিয়ের আগের দিন রাতে ও নিঁখোজ হয়ে যায়। পুরানো এবং শুকনো একটি কলা পাতায় চামেলী লিখে রেখে গিয়েছিল — ” তুমি আমাকে মনে রাখোনি।”
আমার কন্ঠ ভারী হয়ে আসে। মুহূর্তেই মনটা বিষণ্ণ
হয়ে ওঠে। মুকুলের সাথে আর কথা বলতে পারছিলাম না। আজ থেকে প্রায় দুই বছর আগে এই কলা পাতার চিরকূটটি চামেলীর কাছে আমিই লিখে রেখে এসেছিলাম।
২৫. রিনিতা
একদিন লুডু খেলার দুপুরে প্রথম ছক্কাটা আমারই হল। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার হাতের পাঁচ আঙ্গুল।রিনিতা’র হল দুই। আমি ওকে বললাম, আহা এই দুই যদি আমার হত। দুই বিন্দু আমার খুব পছন্দ। খেলার শুরু এই লুডু খেলা থেকেই।
রিনিতা বৃষ্টি খুব পছন্দ করে। বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি হাত দিয়ে ছুঁতে চায়। হাত বাড়াতে বাড়াতে ভিজে ফেলে কামিজ।একদিন রিনিতা বাস স্টান্ডে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে ছাউনি নেই। হঠাৎ বৃষ্টি এল। কলেজে সেদিন আর যাওয়া হয়নি। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে একটি টং চা’র দোকানে দাঁড়িয়ে দু’জন চা খাই। লোকজন তীরবিদ্ধ চোখে দেখছিল রিনিতার ভেজা জামা।
আরেকদিন পার্কে রোদ্রের মধ্যে বেঞ্চে বসে আছি।হাওয়ায় উড়ছে রিনিতার চুল। রোদ্রের ঝাঁজে রিনিতার গোলাপি গাল লাল হয়ে উঠেছিল ।আরেকদিন বুড়িগঙ্গা নদীতে। এখানেও রিনিতা জলের স্পর্শ নেয়। ভেঁপু বাজিয়ে পাশ দিয়ে ছুটে চলেছিল লঞ্চ। নৌকার মাঝিও দেখছিল রিনিতার জলের সাথে খেলা।
আর একদিন সিনেমা দেখতে যাই বলাকায়। সোফিয়া লরেনের ক্যাসেন্ড্রা ক্রসিং। সিনেমায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেখেছিলাম। কিন্ত আমরা ডার্কের মধ্যেও কোনো সীমানা অতিক্রম করিনি। শুধু হাতটাই ধরা ছিল দু’জনের।
এক বিকেলে দু’জন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ঘাসের পথে হাঁটছিলাম। হেমন্ত সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছিল উদ্যানের গাছ গাছালিতে। রিনিতাকে বলি- চলো ঐ পুকুরপাড়ে য়েয়ে বসি। রিনিতা বলে- ‘না’। দেখলাম, রিনিতার মন খারাপ। সাহস করে বলেছিলাম- ‘এসো, হাত ধরো আমার। এই মনোরম সন্ধ্যাকে সুন্দর করি।’ রিনিতা আবারও বলে- ‘না’। হাঁটতে হাঁটতে উদ্যানের বাইরে চলে আসি। চলে যাবার আগে রিনিতা বলে- ‘কালকে এখানে আবার আসবে। অনেক কথা আছে।’
রাতে হোস্টেলের বিছানায় শুয়ে আছি। ঘুম আসছিল না। রিনিতা আমার সাথে কি কথা বলবে ? ভানু সিংহ চক্রবর্তীর কবিতাটি মনে পড়ছিল, বেশ পুলকিত হয়ে ওঠে মন – ‘পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,. আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী। রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল. পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,. ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে. দিগঙ্গনার নৃত্য,. হঠাৎ-আলোর ঝল্কানি লেগে. ঝলমল করে চিত্ত।’
তারপরের দিন সন্ধ্যায় রিনিতা আসেনি। তারপরেও না। তারও অনেক পরে হোস্টেলের ঠিকানায় একটি প্যাকেট আসে। খুলে দেখি একটি বই-রবীন্দ্রনাথের ‘শেষের কবিতা’। মলাটের পাতা উল্টায়ে সাদা পাতাটিতে রিনিতার হাতের লেখায় দেখতে পাই — ‘আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক, মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই, শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে, সেই ধন্য করিবে আমাকে।’ নীচে রিনিতার নামটিও লেখা নেই।
২৬. টুনি আপু
মুক্তিযুদ্ধ সময়কার কথা। এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনী সিরাজগঞ্জ শহর দখল করে নেয়। তারো কয়েকদিন আগে থেকেই শহর থেকে মানুষ গ্রামের দিকে চলে আসতে থাকে। আমাদের গ্রামের বাড়ীতে তখন তিন চারটে অপরিচিত পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলো। টুনি নামে একটি মেয়ে এসেছিলো একটি পরিবারের সাথে। কলেজে ফার্সট ইয়ারে পড়তো। আমার চেয়ে তিন/চার বছরের বড়ো হবে। আমি টুনিকে টুনি আপু বলেই ডাকতাম। খুব সুন্দরী মেয়ে ছিল। টানা টানা মায়াবী চোখ তার। লোকে বলতো: এ তো দেখি মধুবালা। গ্রামের সমস্ত মানুষ আর বউঝি’রা টুনি আপুর দিকে উৎসুক নয়নে তাকিয়ে থাকতো। সুন্দর গান করতো। ঐ সময়কার সিনেমার ভালো ভালো গান গুলো সে গাইতো। যেমন — ‘গানেরই খাতায় স্বরলিপি লিখে’ ‘মন যদি ভেঙ্গে যায় যাক’, তুমি যে আমার কবিতা’ ।
সহজ সরল বালক ছিলাম আমি। এ জন্য মনে হয় টুনি আপু আমাকে একটু বেশীই আপন করে নিয়েছিলো। এক মাস ছিলো টুনি আপু’রা। তারপর অধিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের বাড়ী থেকে আরো উত্তরদিকে দূরে অজো পাড়া গা্ঁয়ের দিকে তারা চলে যায় । যেদিন চলে যায় তার আগের দিন সন্ধ্যা রাতে বাড়ীর খোলা আঙ্গিনায় মাদুরে বসে টুনি আপু সবাইকে গান শোনায়ে গিয়েছিলো। সেদিন আকাশ ভরা তারা ছিলো। সারা গ্রামময় পূর্ণিমা ছিলো। আপু গেয়েছিলো- ‘একি সোনার আলোয় জীবন ভরিয়ে দিলে ওগো বন্ধু কাছে থেকো।’
তারপর চল্লিশ বছর চলে গেছে। এর মাঝে টুনি আপু’র সাথে আর কখনো দেখা হয় নাই।
শুধু মনে হয়, যদি আর একবার মক্তিযুদ্ধ হতো, যদি আর একবার টুনি আপু’রা আসতো আমাদের গ্রামে !
২৭. পৃথক পালঙ্ক
দ্রোণী নামটি কেমন যেন বিদঘুটে। এমন বিদঘুটে নামের একটি মেয়ের সাথে পরিচয় হয়েছিল চট্টগ্রাম টু রাঙামাটির একটি লোকাল বাসে। দুইজনেই উঠেছিলাম চট্টগ্রাম শহরের লাভ লেইন থেকে। সময়টা ছিল আশির দশক।
দূর্ভাগ্যক্রমে পাশাপাশি সিটে বসতে হলো। আমি জানালার সাইডে। সে অফ সাইডে। বাসটি যখন শহর ছেড়ে, গ্রাম ছেড়ে পাহাড় চড়ে এঁকেবেঁকে চলছে, আমি তখন মুগ্ধ চোখে কেবল পাহাড় আর অরণ্য দেখছিলাম। জীবনের প্রথম পাহাড় দর্শন। আমি কখনো তাকিয়ে থাকি পাহাড়ের গায়ে, কখনো উঁকি দিয়ে দেখি পাহাড়ের চূড়া। কখনো দেখি গিরি খাদ। দেখি পাহাড়ের পাশে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী। ছোট ছোট ছড়া ও ঝরনা। দেখি বৃক্ষরাজি, বন, পাখি, হাতি, পাহাড়ি মানুষ, বেজি ও গিরিগিটি।
পাশে যে একজন সুশ্রী তরুণী বসে আছে, তা আমি বেমালুম ভুলে যাই। আমার মুগ্ধ চোখ দেখছিল পাহাড়কে ছবির মতন। আঁকাবাঁকা পথ চলতে চলতে পাহাড়ের বাঁকগুলো দেখছিলাম রমণীর মতন। নদী, ছড়া আর ঝরনা গুলো দেখছিলাম তন্বী তরুণীর মতন। তাই পাশে বসে থাকা মেয়েটিকে লাগছিল অনাহুতের মতো। সে ছিল একা। কারো সাথে কথা নেই।
সারা রাস্তা হা করে শুধু পাহাড়ই দেখলাম। পাশে বসে থাকা মেয়েটিকে একটুও ভালো করে দেখলাম না। কথাও বললাম না। আমি একটু অন্য ধরনের ছেলে। কেউ আগে কথা না বললে কথা বলি না।
পথ ফুড়িয়ে এল। মেয়েটিকে একটু তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা হলো। দেখলামও। মুখে মুলতানি মাটির রং লাগানো যেন লোধ্ররেণু। কালো কেশ। বেণী করা চুলে ঝিনুকের মালা পেঁচিয়ে রেখেছে। চোখ দুটো তিব্বতি। সে একটি বই পড়ছে — আবুল হাসানের ‘পৃথক পালঙ্ক’। একটু বিস্মিতই হলাম। একটি উপজাতীয় মেয়ের হাতে কবিতার বই! মেয়েটির প্রতি ক্ষণিকের জন্য দূর্বল হয়ে গেলাম।
বাসটি রাঙামাটির কাছাকাছি চলে আসে। খুব ইচ্ছা হলো ওর সাথে একটু কথা বলবার। ওকে বললাম, আপনি বুঝি কবিতা পছন্দ করেন?
— করি। শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরীর কবিতা আমার খুব পছন্দ।
—- আপনার নাম কী?
—- দ্রোণী চাকমা।
বাসটি রাঙামাটি বাসস্ট্যান্ডে এসে থামে। স্টপেজে বাবার মতো কেউ একজন অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। লোকটি চলে আসে দ্রোণীর কাছে এবং ওকে নিয়ে চলে যায়। মেয়েটি যাচ্ছিল, আর ফিরে ফিরে দেখছিল আমাকে।
মনে মনে একটু আফসোসই করলাম। কতখানি পথ সে আমার পাশে ছিল। ওর সাথে কত কথাই না বলতে পারতাম। কত কিছুই জানা হতো। যে মেয়ে ‘পৃথক পালঙ্ক’ পড়ে সে হয়ত শেষের কবিতা, আরণ্যক, মাধুকরীও পড়ে। হয়ত সে আমার ভালো একজন বন্ধুও হতে পারত। আরও অনেক কিছু।
জীবনে এমন কত আক্ষেপ তৈরি হয়, কিছু তার মনে থাকে। কিছু মনে থাকে না।
২৮. চিরদিনের কিছু নেই
এ জগতে চিরদিনের বলে কিছু নেই। সবই ক্ষণকালের।
সবই মায়া। সবই মরীচিকা।
জীবনের এক একাকীত্বের সময়ে মিলা’র সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। কথা বলতে বলতে জেনে গিয়েছিলাম সেও প্রবঞ্চিতদের একজন। পৃথিবী তাকেও গ্রহণ করতে চায়নি। আমি দেখেছি, এই জীবন পারাপারের খেয়ায় একই নৌকার যাত্রী হতে হয়েছে আমাকে বারেবারে। এমনি প্রবঞ্চিত মানুষদের সাথে আমাকেও খেয়ায় পাড়ি দিতে হয়েছে।
প্রায়ই মনে হতো, কোনো একটি লোকাল ট্রেনে উঠে চলছি অজানায়। কতো স্টেশনে কতো মানুষ উঠল আর নামল। কোথাও নামা হলো না আমার। শেষ স্টেশনে যেয়ে ট্রেনটি একসময় থেমে যায়। সব মানুষ নেমে গেল। কেউ আর উঠল না। একাকী বসে আছি কামড়ায়। কেউ বলল না, তুমি নামো। পথ শেষ। সামনে আর পথ নেই।
মিলা আমার পথের সাথী হয়েছিল। সে আমার হাত ধরেছিল পরম বিশ্বাসে। আমারও মনে হয়েছিল, এই হাত ধরেনি জীবনে অন্য কোনো পুরুষের হাত? এই চোখ চেয়ে থাকেনি অন্য কারোর লোলুপ চোখের দিকে অপলক, এই মঞ্জলী ঠোঁট চুম্বন করেনি কোনো অবিশ্বাসী ঠোঁটে। বুকে আঁচর নেই অসভ্য নখের। কোনো বসন্ত বাতাসে এলোমেলো হয়ে থাকা চুল কেউ যেন পরিপাটি করে দেয়নি কোনো দিন!
বনে বনে কতো পাখি ডাকতে লাগল। নীল আকাশ ক্ষণে ক্ষণে বদলিয়ে কতো রঙের হলো। বাগানে বাগানে ফুল ফুটে উঠল। যেন মরা গাঙে জোয়ার এলো।
মিলার সাথে ছোট ছোট অভিমান হত, ঝগড়া হত, খুনসুটি হত। কতো প্রতিশ্রুতি হত দুজনের মধ্যে। বলতাম, আমার ভূবন থেকে তুমি কখনও চলে যাবে না। মিলা বলত — ‘ঐ যে তুমি বালু নদীর জল দেখছো, ঐ জলের মতো তুমি স্বচ্ছ আমার জীবনে।’ হারানো সুর সিনেমার মতো গীতা দত্ত হয়ে গান গাইত –‘ তুমি যে আমার ওগো তুমি যে আমার।’
কোথা থেকে শীতল হাওয়া আসত। মিলার চুল এসে কপালে পড়ত, ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতাম, ‘ওগো তুমি যে আমার। চিরকালের তুমি আমার। চিরদিনের তুমি আমার।’
এই পৃথিবীতে সব কিছু ক্ষণকালের। এই যে বহমান শীতল হাওয়া, এমন করে বইবে না আর কখনও। এই যে সৌর মন্ডলে এত তারা জ্বলছে, সব তারাই একসাথে কী আর জ্বলে উঠবে কখনও? সব মেঘ বৃষ্টি হয়ে ঝরে না। তুলো হয়ে উড়ে চলে যায়।
পৃথিবীর রূপ রস গন্ধের মতো মানুষের মনও বড়ই বিচিত্র। রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের মাঝেই কখন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ হয়। ঝম ঝম করে বৃষ্টি নামে। চরাচর ভেসে যায় জলে। যে মিলা শক্ত করে আমার হাত ধরে থাকত, সেই হাত কেমন যেন শিথিল হতে থাকে। দিন দিন সে দূরে সরতে থাকে। আমি এসবের কোনো মানেই বুঝতাম না। বুঝতাম না তার দ্বিধা কী ? বুঝতাম না তার প্রেম কী রূপ।
মিলা একদিন বলেছিল, আমাকে তুমি মুক্তি দাও। আমাকে তুমি আর ধরে রেখো না। মায়া কোরো না। আমাকে ঘৃণা দাও।
আমি মানুষের মুক্তির গল্প লিখি। কতো রাত্রি জেগে কতো অসীমে খুঁজি জীবনের জয়গান। কখন যে কোন্ কাহিনী নিজের জীবনের হয়ে যায়। বুঝতে পারিনা। আমি মিলাকে মুক্তি দিয়েছিলাম আমার জীবন থেকে। যখন সে এসেছিল জীবনে, তখন তার অতীত নিয়ে কোনো প্রশ্ন করিনি, আজ যখন চলে যেতে চাইছে, তখনও বলিনি — ‘কোথায় তুমি যাবে? কে তোমার ভালোবাসা।’
মনের ভিতর একটাই প্রতিতী, চিরদিনের বলতে এই জগতে কিছু নেই। হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা, ঘৃণা ও ভালোবাসা কোনোটাই না।
একদিন সব আলো নিভে দিয়ে শুয়ে আছি। হোয়াটস এ্যাপে সংকেত এলো — দেখি একটি টেক্সট —
‘ কী! খুব নিঃসঙ্গ লাগছে মনে হয়! আমি জয়িতা, তোমার একাকীত্বে আমাকে চিরদিনের সাথী করে নেবে কী?’
রিপ্লাই দিলাম–
‘ না। এই পৃথিবীতে চিরদিনের বলে কিছু নেই।
তাই — না।’
২৯. হারমনিকা
পাশের বাড়ির জানালা থেকে রোজ সকালে ভেসে আসে হারমনিকার সুর। কে বাজায় তা জানি না। যে বাজায় খুব সুন্দর বাজায়। ঘর থেকে বের হয়ে যেতে ইচ্ছা করে সুরের কাছে । ভোরে কয়েকটি দোয়েল শিস দিয়ে যায়। সারারাতের কল্লোলিনী ঢাকা শীতল শান্ত হয়। শান্তি নামে আমার ছোট ঘরেও।
যিনি হারমনিকা বাজায়, যিনি সুর তুলেন, পরে জেনেছি, সে একটি মেয়ে। ওর নাম উর্মিলা। বদরুন্নেসা কলেজের ছাত্রী।
উর্মিলা একদিন জানালা খুলে শিক ধরে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখতে পেলাম একটি সুন্দর মুখশ্রী। একটি নির্মল স্নিগ্ধ মুখ। ভোরের বাতাস ওর গা ছুঁয়ে লাগল এসে আমার গায়ে। কেমন যেন মাধুকরী গন্ধ পেলাম। কেমন যেন পরশমণির ছোঁয়া দিল প্রাণের মাঝে। আমি মুগ্ধ হলাম। গন্ধের শরীরটা খুঁজতে থাকি। কেমন উন্মনা উন্মনা হতে থাকল মন।
তার সাথে দেখা হয় একদিন ঝুমঝুম বৃষ্টির দিনে। ছাতা না নিয়ে বেরনোয় আমি ভিজতে ভিজতে কাক হয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। আর উল্টোদিক থেকে সেও বিনা ছাতায় ভিজে চুপসি হয়ে ফিরছিল। ঝড়ো হাওয়ায় মাথার চুল হয়ে গেছে তার এলমেল। চুল বেয়ে জল ঝরে পড়ছিল পিঠের উপরে।
আর একদিন বাসস্টপে ধুলো-ধুসরিত, বিধ্বস্ত, ঘর্মাক্ত শরীরে দাঁড়িয়ে আছি। দেখলাম উর্মিলাও দাঁড়িয়ে। সে কোথায় যাবে জানিনা। ওকে দেখলাম সদ্য স্নাত। মাথার চুল শুকায়নি তখনও। চুল সুন্দর পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে পিছনে খোঁপা করে বেঁধে রেখেছে। ভোরের সূর্যালোক এসে পড়েছিল ওর মুখে। যেন জগতের সকল আলো আলোকিত হয়েছে এ মুখ মন্ডলে। কী যে ভালো লাগছিল ওকে।
আমি ওর পাশের বাসার এক নতুন অতিথি। চেনেও না আমাকে। ও থাকে ঠিক পাশের রুমটায় ও পাশে। দুই রুমের দুটি জানালা। মাঝখানে প্রাচীর নেই। আবার কেউ যাওয়া আসাও করতে পারব না। মাঝে ফাঁকা, শূন্যতা। আমাকে টেনে যা নেয় ঐ মাউথ অর্গানটা। ঐ হারমনিকা। ওর সুর।
৩০. সবুজ বাতি
তার সাথে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে অনেক আগেই। কত অনন্ত মধ্যরাতে কত উতল হাওয়া বয়ে যায় দুজনের পৃথিবীতে। তা এখন দম বন্ধ হয়ে আসার মতো লাগে ।
যখন অনলাইনে কোথাও কাউকে দেখছিলাম না। দেখছি তখন টিমটিম করে সবুজ বাতি জ্বলছে তারই ঘরে।
— ‘কেমন আছো?’ ছোট্ট এই বার্তাটি চলে আসে মধ্যরাতের প্রহর ভেঙ্গে। যখন সে লিখে মায়ার আখর মিশিয়ে — ‘ তোমার যখন জ্বর আসে, কে তোমাকে মাথায় জলপট্টি দিয়ে দেয়?’
আরও কথা —
‘আমি জানি, তুমি কখনই মিথ্যা কথা বলো না। বুকে হাত রাখো। এবার বলো, কেমন আছ?
আরও লেখে সে —
মাথার চুল কী আগের মতোই এলমেল রাখ? পরিপাটি করে আমিই তো তোমাকে রাখতে বলতাম। এখন কে বলে? আমি খেতে না বললে, খাওয়ার অরুচি হতো তোমার। খেতে না কিছুই। খেতে বললে, খেতে। এখন কী তুমি না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেছ?
আমি লিখি —
এখন আর খিদে লাগে না। অসুখ বিসুখও হয় না। রোগ ব্যাধি ভয়ে পালিয়ে গেছে। ওরা সব জেনে গেছে — মুখে তুলে খেয়ে দেওয়ার মানুষটি আর নেই।
উত্তর আসে —
তোমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু, তা আর পারছি কই। সন্ধ্যা বেলায় বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। রমনা সবুজের সেই ছাতিম গাছটি এখনও আছে সেখানে। ঠিক লেকের পূর্ব কোণে। সেদিন সাদা ফুলের গন্ধে ভেসেছিল, আজও কী ভাসে? খুব যেতে ইচ্ছা করে যেয়ে দেখতে!
লিখছিলাম —
ভালোবাসা কী অযত্নে আগাছা হয়ে যায়? না মনে হয়। অনাদরে ঝোপে ঝাড়ে ঘাসফুল হয়ে ফুটে থাকে। আকাশ দেখে, বৃষ্টি ঝরে। রাত নামে। তারা দেখে। কত নিঃশব্দ নিঃশ্বাস বেগ পায়।
— যাই । কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। সেই হবে হয়ত। যে থাকে এখন আমার ঘরে।
ওদিকে ও ঘরে তখন সবুজ বাতি নিভে গেছে।

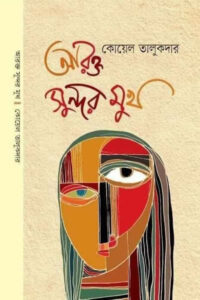



Leave a Reply