ডিসেন্ট অফ ম্যান (অখণ্ড) – চার্লস ডারউইন
ভাষান্তর – অসীম চট্টোপাধ্যায় / সঞ্জীব মণ্ডল / অসিত চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ -২০১৯
প্রকাশক – রাবেয়া খাতুন
রাবেয়া বুক্স ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
.
উৎসর্গ
পিতামহ
ইরাসমাস ডারউইন
.
প্রকাশনা প্রসঙ্গে
বাংলায় ডারইউন-চর্চা শুরু হয়েছে বহু দিন আগেই, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে। কিন্তু ডারইউনের আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থাবলি যা মানুষের চিন্তাভাবনার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে আমূল পরিবর্তনের দিকে পারিচালিত করেছিল, জাগতিক সমস্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তাভাবনার যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণের দিকদর্শন ঘটিয়েছিল, তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি। এই ঘাটতি পূরণের কথা মনে রেখেই ডারইউনের রচনাবলি বাংলা অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করি আমরা। সেই পরিকল্পনার প্রথম ফসল এই ‘ডিসেন্ট অফ ম্যান’-এর বাংলা ভাষান্তর।
‘ডিসেন্ট অফ ম্যান’-এর এই খণ্ডটি আলোচনার দিকে দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পরবর্তী খণ্ডগুলোতে ডারউইন আলোচনা করেছেন কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু এবং মানুষের জীবনে যৌন নির্বাচনের ভূমিকা প্রসঙ্গে।
বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে অনেক শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ও সহমর্মী সাথিরা নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে ও উৎসাহ জুগিয়ে আমাদের চিরন্তন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে সন্দীপন ভট্টাচার্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক প্রয়াত সন্তোষকুমার বসুর নাম উল্লেখ না করলে মানসিক পীড়া অনুভব করব।
.
চার্লস ডারউইন : জীবন ও কাজ
অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে ডাক্তার ইরাসমাস ডারউইন একটি পরিচিত নাম। চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, উদ্ভাবক, লেখক, অনুবাদক—সবের সমন্বয়ে ইরাসমাস এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ‘জুনোমিয়া’ নামে একটি বই লিখেছিলেন তিনি। বইটির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, ‘যে-সব প্রাণীর রক্ত গরম, তারা সবাই একই সূত্র থেকে এসেছে—এ কথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেয়া হবে!’
ইরাসমাসের পুত্র রবার্ট ডারউইনও নিয়েছিলেন চিকিৎসকের জীবিকা। শশয়ারের শিউসবেরি অঞ্চলের বাসিন্দা রবাট জীবনসী হিসেবে বেছে নেন সুসানা ওয়েউডকে। রবার্ট-সুসানার ছয় সন্তানের মধ্যে পঞ্চম সন্তানটি পৃথিবীর আলো দেখে ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, আমরা যাঁকে চিনি চার্লস ডারউইন নামে।
শিশু চার্লস সম্বন্ধে মোটেই আশাবাদী ছিলেন না রবার্ট, কেননা পড়াশোনায় তার মন ছিল না তেমন। ন’বছর বয়সে তাকে ভর্তি করা হয় শ্রিউসবেরি স্কুলে না, সেখানেও মন বসাতে পারেনি চার্লস। বাঁধাধরা গতের পড়াশোনা কিছুতেই ভালো লাগত না তার। সাবেককালের কিছু ভূগোল আর ইতিহাস ছাড়া অন্য কিছু পড়ানোর পাট ছিল না ওই স্কুলে। তার ভালো লাগত খোলামেলা প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। পড়াশোনা করার চেয়ে তার বেশি ঝোঁক ছিল মুদ্রা, নামাঙ্কিত মোহর, নানা ধরনের নুড়ি-পাথর সংগ্রহ করার দিকে। এছাড়াও সে ভালোবাসত রসায়নশাস্ত্র পড়তে এবং গাছপালা, লতাপাতা, পোকামাকড় আর পাখির ডিম সংগ্রহ ও চিহ্নিত করতে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে এই ঝোঁকটা সে পেয়েছিল তার বাবার বংশ থেকে আর হাতে- কলমে কাজ করার প্রেরণাটা পেয়েছিল মামার বাড়ি থেকে। এসব কাজকর্ম তার বাবা খুব অপছন্দ না করলেও, অপছন্দ করতেন স্কুলের পরীক্ষায় পাওয়া খারাপ নম্বরগুলোকে। বাবা ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না মাতৃহারা ছেলেটি পড়াশোনো ফেলে সারাদিন খেলা, মাঠ, পাহাড়, বনজঙ্গল আর শিকার নিয়ে মেতে থাকুক। রেগে গিয়ে একদিন তিনি বলেই ফেললেন, ‘তুমি দেখছি শিকার, কুকুরের পাল আর ইঁদুর ধরা নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত থাকো, পড়াশোনার দিকে ফিরেও তাকাও না। তুমি দেখছি নিজের আর বংশের নাম ডোবাবে।’ ভবিষ্যতের মহান প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছেলেবেলায় যে বেশকিছুটা আলাদাই ছিলেন, সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।
১৮২৫ সালে, ষোলো বছর বয়সে, কিছুটা বাবাকে সন্তুষ্ট করার তাগিদেই, এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞান পড়তে যান তিনি। দাদা ইরাসমাস আগেই পড়তেন সেখানে। কিন্তু ডাক্তারি পাঠ্যক্রম শেষ করার উৎসাহ ধরে রাখতে পারেননি চার্লস। পরবর্তীকালের চার্লস ডারউইনের লেখায় দেখছি : শীতকালের সকাল আটটার সময় মেটারিয়া মেডিকা সম্বন্ধে ডা. ডানকানের ভাষণ—ওহ্, সে এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা।’ এ সময়ে প্লিনিয়ান সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর, প্রাণীতত্ত্বে আগ্রহী হয়ে ওঠেন চার্লস। পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজ শুরু করেন। এই সময় তিনি সামুদ্রিক জীবদের ভ্রূণ সম্বন্ধে দুটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য আবিষ্কার করেন। এরপর ডাক্তারি পড়ার ইতি ঘটে তাঁর। বাবা তাঁকে যাজক হতে বলেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে রাজি হন চালর্স। ১৮২৮ সালের জানুয়ারিতে ভর্তি হন কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির ক্রাইস্ট কলেজে, কিছুদিন তাঁকে বসতে হয় যাজক হওয়ার ক্লাসেও।
অন্যান্য বইপত্র পড়ার অবসরে চার্লস ততদিনে পড়ে ফেলেছেন শেকসপিয়ার, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, কোজি, বায়রন, স্কট ও মিল্টনের লেখা। কবিতা টানে তাঁকে, পরবর্তীকালে জাহাজে দীর্ঘভ্রমণের সঙ্গী হয় মিল্টনের ‘প্যারাডাইস লস্ট’। কিন্তু এ-পড়াশোনাও ভালো লাগে না তাঁর। এখানেও বেরোতেন দল বেঁধে অজানা বনে-জঙ্গলে, সঙ্গে পোকামাকড় সংগ্রহ ও চিহ্নিত করার কাজও চলত।
এখানেই পরিচয় হয় উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক জন সিভেন্স হেস্লো-র সঙ্গে। হেস্লো হয়ে ওঠেন তাঁর প্রেরণাদাতা। তাঁর প্রভাবে ভূতত্ত্বের ওপর পড়াশোনা শুরু করেন চার্লস। দাদুর লেখা ‘জুনোমিয়া’ বইটি আবার ভালো করে পড়ে ফেলেন। পড়লেন লামার্কের লেখা। এই সময়েই হাতে আসে হামবোল্ড-এর ‘পার্সোনাল ন্যারেটিভ’। অনুপ্রাণিত হন চার্লস। তারপর পড়েন হারসেল-এর লেখা ‘ইনট্রোডাকশন টু দ্য স্টাডি অফ ন্যাচারাল ফিলজফি’। পরে তিনি লিখেছেন, ‘প্রকৃতিবিজ্ঞান পঠনে এই দু’টি লেখার অবদান আমাকে তখন উৎসাহ-উদ্দীপনার তুঙ্গে তুলে দিয়েছিল।’
জানুয়ারি মাসে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন চার্লস। অধ্যাপক হেনস্লো তাঁকে ভূতত্ত্ববিদ্যা পড়তে উৎসাহ জোগান। গরমের ছুটিতে অধ্যাপক সেজউইকের সঙ্গে ভূতত্ত্ববিদ্যার উপর শিক্ষামূলক ভ্রমণে ওয়েলস-এ যান ডারউইন।
১৮৩১ সাল। বাইশ বছরের সদ্য-যুবক চার্লসের জীবন মোড় নিতে শুরু করল ভবিষ্যতের ডারউইন হওয়ার দিকে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পর হেনস্লোর সুপারিশে ‘এইচ. এম. এস. বি’ জাহাজের দীর্ঘ সমুদ্র অভিযানের শরিক হন চার্লস—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে। ‘এইচ, এম. এস. বিল্’ জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর ঠিক হয়—প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি এই ভ্রমণে যাবেন, কিন্তু কোনো মাসোহারা পাবেন না। সঙ্গে সঙ্গে এই সুযোগ গ্রহণ করেন তিনি। বিগ্ল জাহাজের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটো। এক,দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগের একটি সঠিক মানচিত্র তৈরির কাজে সাহায্য করা; দুই, যথাযথভাবে দ্রাঘিমারেখা নির্ধারণ করা। ছেলেকে ওই দীর্ঘ যাত্রায় ছেড়ে দিতে প্রথমে রাজি হতে পারেননি রবার্ট ডারউইন। অনেক টালবাহানার পর, অবশেষে রাজি হন তিনি। প্লিমাউথ বন্দর থেকে ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর তারিখে যাত্রা শুরু করে বিল্। ভবিষ্যতের পথে যাত্রা শুরু হয় চার্লস ডারউইনের 1
ডারউইনের নিজের কথায়, “বিগ্ জাহাজে সমুদ্রযাত্রা আমার জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমার জীবনদর্শনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।’
এম. এস. বি-এর যাত্রা—১৮৩১-এর ২৭ ডিসেম্বর থেকে ১৮৩৬-এর ২ অক্টোবর। ঠিক পাঁচ বছর পরে ফলমাউথ বন্দরে নোঙর করেছিল বিল। এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে সে ছুঁয়ে এনেছে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, টিয়েরা দেল ফুয়েগো, উরুগুয়ে, পাটাগোনিয়া, চিলি, আন্দিজ পর্বতাঞ্চল, গ্যালাপাগোস ও তাহিতি দ্বীপপুঞ্জ অতিক্রম করেছে প্রশান্ত মহাসাগর, স্পর্শ করেছে নিউজিল্যান্ডকে, অস্ট্রেলিয়াকে, তারপর ভারত মহাসাগরের বুক চিরে মুখ ফিরিয়েছে দেশের দিকে, আফ্রিকা মহাদেশের শেষ প্রান্ত কেপটাউনকে ছুঁয়ে, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ হয়ে ফলমাউথের ঠিকানায়।
এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে ডারউইন দেখে এসেছেন পৃথিবীর কিছু গহনতম বনাঞ্চল, সংগ্রহ করেছেন প্রচুর অদেখা-অজান। উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, মথ, প্রজাপতি, শামুক, পাথর, জীবাশ্ম, এবং সঞ্চয় করেছেন বিপুল অভিজ্ঞতা। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের চতুষ্পদ প্রাণীদের প্রচুর জীবাশ্ম আর গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের বহুবিচিত্র প্রজাতিগুলো গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁকে। বলা যায়, গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের এই প্রজাতিগুলোই ছিল ডারউইনের যাবতীয় চিন্তাভাবনার মূল উৎস।
শুরু হয় ডারউইনের লেখালেখি। প্রকাশিত হলো জার্নাল অফ রিসার্চেস, জুলজি অফ দ্য ভয়েজ অফ দ্য বিগ্ল্, দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড ডিসট্রিবিউশন অফ কোরাল রিট্স এবং জিওলজিক্যাল অবজারভেশন অন ভক্যালিক আইল্যান্ড অ্যান্ড অন সাউথ আমেরিকা। ফিরে আসার কয়েক বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছিল এগুলো। সমুদ্রযাত্রার শুরুতেই, কেপ ডি ভারতে আর্কপেলাগোতে অবস্থিত সেন্ট জ্যাগো দ্বীপে ভ্রমণের সময় তিনি দক্ষিণ আমেরিকাসহ যেসব দেশ ভ্রমণ করেছেন তাদের ভূতাত্ত্বিক গঠনপ্রণালি, বিস্তর পরিমাণ সংগৃহীত চতুষ্পদ প্রাণীদের হাড়গোড় এবং ফসিলের ওপর একটি বই লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ভ্রমণের আগে তিনি লাইয়ের-এর ‘প্রিন্সিস্ অফ জিওলজি’ বইটির প্রথম খণ্ডটি পড়েন এবং ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের মূলসূত্র ও কার্যপ্রণালি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করেন। ভ্রমণ শেষে ফিরে আসার পর তিনি ভূতত্ববিজ্ঞানের একজন হাতে-কলমে-শিক্ষা-পাওয়া তাত্ত্বিক প্রকৃতিবিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। অচিরেই এ-সব বিষয়ের অগ্রণী বিজ্ঞানীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থিত হন তিনি এবং জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সম্পাদকের পদে মনোনীত করা হয় তাঁকে। তিন বছর এই পদে ছিলেন তিনি। এই সময়ে তিনি কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন চিলির সমুদ্রতট পরিভ্রমণের সময় সংগৃহীত তথ্যাবলির সাহায্যে। তাছাড়াও প্রবালদ্বীপ গঠনের কার্যকারণ ও নিয়মনীতি সংক্রান্ত প্রথম বিজ্ঞানসম্মত কাজটিও লিপিবদ্ধ করেন এই সময়েই। ১৮৩৯ সালে তাঁর জার্নাল প্রকাশিত হয় ফিড্রয়ের ‘ভয়েজেস অফ অ্যাডভেঞ্চার অ্যান্ড বিল্’-এর সঙ্গে। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই সব জায়গা থেকে আসতে থাকে প্রশংসাবাণী। এরপর পৃথিবীতে প্রজাতিগুলো যে সৃষ্টির সময় থেকে অনড়, অপরিবর্তনীয় হয়ে থাকেনি, নানান রূপান্তরের পথ বেয়ে এগিয়েছে তারা—এ- বিশ্বাস দানা বাঁধে তাঁর চিন্তায়। প্রথমদিকে এ-চিন্তার কথা শুধু নিজের নোটবুকেই লিখেছিলেন তিনি। তখনই হাতে আসে ম্যালথাসের ‘এসে অন দ্য প্রিন্সিপ্ল্স অফ পপুলেশন’। অবিন্যস্ত চিন্তাভাবনাকে সাজিয়ে ফেলার সূত্র হাতে পান ডারউইন। জন্ম নেয় সেই সুবিখ্যাত তত্ত্ব—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বিবর্তনের তত্ত্ব। সময়টা ১৮৩৬ সালের অক্টোবর মাস। একদা বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বে গভীর-বিশ্বাসী ডারউইন পৌঁছে যান এক নতুন বিশ্বাসে। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, ম্যালথাসের রচনা পড়ার পরই তাঁর মনে হয়েছিল অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে ‘সুবিধাজনক জৈবিক রূপগুলো টিকে থাকবে আর অসুবিধাজনক রূপগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাবে। আর এ-ঘটনার ফলস্বরূপ সৃষ্টি হবে নতুন নতুন প্রজাতি।’
১৮৩৯ সালে তিরিশ বছরের যুবক ডারউইন বিয়ে করলেন তাঁর মামাতো বোন এমা ওয়েজ্উডকে। ওই বছরই প্রথম সন্তানের জন্ম দেন এমা, নাম যার উইলিয়াম ইরাসমাস ডারউইন। পরবর্তী জীবনে আরও নয়টি সন্তানের পিতা হয়েছিলেন চার্লস ডারউইন। লন্ডন শহরের ১২ নং আপার গাওয়ার স্ট্রিটের যে বাড়িতে প্রথম সংসার পেতেছিলেন চার্লস আর এমা, সেই বাড়ি, আমাদের দুর্ভাগ্য, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝোড়ো প্রহরে।
সেই লাইয়েল-এর ভূতত্ত্ববিজ্ঞান পড়বার সময় থেকেই গাছপালা, লতা, শাক-সবজি এবং জীবজন্তুদের পরিবর্তন নিয়ে তথ্য জোগাড় করতে শুরু করেছিলেন ডারউইন—মানুষের হাতে সৃষ্ট পরিবর্তন অথবা প্রকৃতিগতভাবে সৃষ্ট পরিবর্তন, দুটি বিষয়েই। তিনি লক্ষ করেন মানুষ কৃতিত্বের সঙ্গে পশু-পাখি এবং গাছপালার সবচেয়ে উন্নত প্রজাতিগুলোকে সৃষ্টি করেছে। সবচেয়ে কার্যকরী গো ও মেষজাতীয় পশুগুলোর প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছে মানুষ, বিভিন্ন গুণসম্পন্ন ওইসব পশুদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে এবং একই ঘটনা ঘটেছে ফল, শস্য ও অন্যান্য মানবোপযোগী গাছপালাগুলোর ক্ষেত্রেও। এর জন্য বিভিন্ন গুণসম্পন্ন জীবদের পিতামাতাকে আলাদাভাবে পুষ্টিপ্রধান খাদ্যের সাহায্যে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও উন্নত করে তুলতে হয়েছিল তাদের। প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর থেকে চেহারায়, রঙে এবং উপযোগিতায় এরা একেবারেই অন্যরকম।
নতুন তত্ত্ব ডারউইনের সামনে, কিন্তু তা প্রকাশ করতে তখনও দ্বিধান্বিত তিনি। আরও ভাবছেন, যাচাই করছেন, হিসেব মেলাচ্ছেন। প্রায় বিশটা বছর দ্বিধার দরিয়ায় ভেসেছেন ডারউইন। অবশেষে, ১৮৫৮ সালের এক বিশেষ ঘটনায়, দ্বিধা কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে হলো তাঁকে। সে-ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু এক প্রকৃতিবিজ্ঞানী—আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।
হামবোল্ডের ‘পার্সোনাল ন্যারেটিভ’ আর ডারউইনের “জার্নাল অফ রিসার্চেস’ পড়ে উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন তরুণ ওয়ালেস। অজানা প্রকৃতির খোঁজ নিতে পাড়ি দিয়েছিলেন ব্রাজিলে, তারপর একে একে আরও অনেক জায়গায়। সঙ্গী ছিলেন তাঁর বন্ধু প্রকৃতিবিজ্ঞানী এইচ. ডব্লিউ. বে। ডারউইনের প্রজাতি বিষয়ক চিন্তার কথা জানা ছিল না ওয়ালেসের। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ আর গভীর চিন্তাভাবনার পথ বেয়ে তিনি স্বাধীনভাবেই পৌঁছতে পেরেছিলেন প্রায় একই তত্ত্বের দুয়ারে—প্রাকৃতিক নির্বাচন মারফত বিবর্তনের তত্ত্বে। মনে রাখা দরকার, ডারউইন আর ওয়ালেসের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল থাকলেও ফারাকও কম ছিল না। ম্যালথাসের তত্ত্ব নতুন চিন্তার সূত্র জুগিয়েছিল ওয়ালেসকেও।
সালটা ১৮৫৮, ডারউইন তখন প্রকৃতিবিজ্ঞানী এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখে ডারউইনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন ওয়ালেস। (On the Tendency of Varieties to Depart Indefinitely from the Original Type) |
নাড়া খেলেন ডারউইন। তাঁর বহু শ্রমার্জিত তত্ত্বের জগতে আর-একজন পৌছে গেছে স্বাধীনভাবেই। নিজের তত্ত্ব প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন তিনি। লন্ডনের লিনিয়ান সোসাইটির সামনে পড়া হলো ওয়ালেসের প্রবন্ধ আর ডারউইনের রচনার কিছু বাছাই-করা অংশ, যা পরে ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। সোসাইটির মুখপত্রে ছাপা হলো তাঁদের দুজনের রচনা, ‘অন দ্য টেনডেন্সি অফ স্পিসিস টু ফর্ম ভ্যারাইটিস’ এবং ‘অন সিলেকশন’ নামে।
তার পরের বছর, ১৮৫৯ সালে, পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে সংযোজিত হলো এক আশ্চর্য, ইতিহাস-কাঁপানো সম্পদ। অরিজিন অফ স্পিসিস। মানবজাতির ভাবনা-জগৎ ওলোট-পালোট হয়ে গেল, গিয়ে পৌঁছল এক নতুন স্তরে, নতুন মাত্রায়। প্রজাতির বিবর্তন, তার ইতিহাস, রূপান্তর—সবকিছুর প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত হলো প্রাকৃতিক নির্বাচন 1
সৃষ্টি হলো বিপুল আলোড়ন, বিতর্ক উঠল প্রচুর। কোনো এক আদি জীব থেকেই পরবর্তীকালের সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে কি না, প্রশ্ন উঠল তা নিয়েও (সব বির্তকের সমাধান আজও হয়নি)। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠলেন সারা দেশের ধর্মগুরুরা। এই তত্ত্ব খ্রিস্টধর্ম-বিরুদ্ধ, সৃষ্টিতত্ত্বকে সে অস্বীকার করছে—এসব বলে আক্রমণ করা হলো ডারউইনের তত্ত্বকে। অক্সফোর্ডের ইউনিভার্সিটি মিউজিয়ামের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের অধিবেশন বসল ১৮৬০ সালে। সেখানে মুখোমুখি দাঁড়াল, দুই যুযুধান পক্ষ। ডারউইনের মতের পক্ষে থমাস হেনরি হাক্সলে এবং জোসেফ হুকার, বিপক্ষে অক্সফোর্ডের বিশপ ড. স্যামুয়েল ইউলবারফোর্স (যাকে পিছন থেকে মদত জুগিয়েছিলেন রিচার্ড ওয়েন।) টানা চার ঘণ্টা বিতর্কের শেষে, মাথা নিচু করে সরে যেতে হয়েছিল উইলবারফোর্সকে।
তেরো বছরের মধ্যে ছটা সংস্করণ বেরোল অরিজিন অফ স্পিসিসের। এরই মধ্যে প্রকাশিত হলো নৃতত্ত্ব এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর আরও অনেক গবেষণামূলক গ্রন্থ। ১৮৬২ সালে প্রকাশিত হলো ‘দ্য ভ্যারিয়াস কনট্রিভ্যানসেস বাই হুইচ অর্কিড আর ফার্টিলাইজড বাই ইনসেক্টস অ্যান্ড দ্য গুড এফেক্টস অফ ইন্টারক্রসিং’, ১৮৬৮ সালে ‘ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড প্ল্যান্টস আন্ডার ডোমেস্টিকেশন’, এবং ১৮৭১-এ এই বহুল-আলোচিত ‘ডিসেন্ট অফ ম্যান’। তারপর একে একে-’দ্য এক্সপ্রেশন অফ ইমোশন ইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিম্যাল’ (১৮৭২), ‘ইনসেক্টিভোরাস প্ল্যান্টস’ (১৮৭৫), ‘দ্যা এফেক্টস অফ ক্রস অ্যান্ড সেল্ফ ফার্টিলাইজেশন ইন দ্য ভেজিটেবল কিংডম’ (১৮৭৬), ‘দ্য ডিফারেন্ট ফর্মস অফ ফ্লাওয়ারস ইন প্ল্যান্টস অফ দ্য সেম স্পিসিস (১৮৭৭), ‘দ্যা পাওয়ার অফ মুভমেন্ট ইন প্ল্যান্টস’, (১৮৮০), ‘ফর্মেশন অফ ভেজিটেবল মোল্ড থু দ্য অ্যাকশন অফ ওয়ামর্স (১৮৮১)।
জীবনের শেষ বছরগুলোতে ডারউইন নিজেকে বেশি করে ব্যস্ত রেখেছিলেন বিভিন্ন উদ্ভিদ আর ছোটখাটো পোকামাকড় সংক্রান্ত অনুসন্ধানের কাজে। ১৮৭৬ সালে লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী।
শরীর ভেঙেছিল অনেক আগেই। পঙ্গুত্ব তাঁর শরীরকে গ্রাস করেছিল অনেকটাই। ইনভ্যালিড্ স্ চেয়ারে বসে চলাচল করতে হয়েছে বহু বছর। অবশেষে, ১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল, সব প্রচেষ্টা-সাফল্য যন্ত্রণার অবসান। মারা গেলেন চার্লস ডারউইন। ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি-তে, নিউটনের সমাধির খুব কাছাকাছি, সমাহিত হলেন ডারউইন। অন্তিমযাত্রায় মাথা নিচু করে হেঁটে গেলেন প্রিয় অনুরাগীরা—হাক্সলে, হুকার এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস।
ডারউইনোত্তর শতাধিক বছরে পৃথিবী অনেক পরিবর্তন, অনেক নতুন কিছু-জানার সাক্ষী। তাঁর সময়ের জীববিদ্যা আজ প্রায় শতশাখায় বিভক্ত হয়েছে, বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান ও গবেষণায় প্রচুর নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নতুন নতুন তত্ত্বের আলোয় এগিয়ে চলেছে পৃথিবী। জীববিদ্যা, জীব- রসায়নবিদ্যা, কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি, সৃষ্ট জীবনকে ইচ্ছেমতো পরিবর্তনের অধিকারী আজ মানুষ। প্রকৃতির ওপরে কিছুটা আধিপত্য সে বিস্তার করতে পেরেছে ক্লোনিং, মিউটেশন তত্ত্ব এবং নিউক্লিয়ার বায়োলজি করায়ত্ত করার দৌলতে।
১৮৫৯ সালে ‘অরিজিন অফ স্পিরিট’ প্রকাশিত হওয়ামাত্রই তা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন ফ্রিডরিশ এঙ্গেলস। পরের বছর এ-বইয়ের পাতায় মগ্ন হন কার্ল মার্কস। ১৮৬০ সালের ১৯ ডিসেম্বর এঙ্গেলসের কাছে লেখা এক চিঠিতে মার্কস লিখেছেন, ‘আমাদের ধারণার প্রাকৃতিক-ঐতিহাসিক বনিয়াদ সৃষ্টি করে দিয়েছে এই গ্রন্থটি।’ এঙ্গেলস তাঁর ‘ডায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার’ লিখতে গিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানের জগতে তিনটি ঘটনাকে চূড়ান্ত গুরুত্ব দিয়েছেন—জীবকোষ আবিষ্কার, শক্তির সংরক্ষণ ও তার রূপান্তরের নিয়ম আবিষ্কার এবং ডারউইনের আবিষ্কার। অর্থাৎ মার্কস-এঙ্গেলসের চোখে চার্লস ডারউইনের আবিষ্কার ছিল এক প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আবার তার পাশাপাশি ‘ডায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার’-এর পৃষ্ঠায় ডারউইনের কিছু সমালোচনাও করেছেন এঙ্গেলস। অস্তিত্বরক্ষা বা ঊধ্বর্তনের জন্য সংগ্রামের ওপর একপেশেভাবে অতিরিক্ত জোর দিয়েছেন ডারউইন, যা এঙ্গেলসের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক বলে মনে হয়নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন সম্বন্ধেও কিছুটা ভিন্ন মত ছিল এঙ্গেলসের। সদস্যসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে যে-প্রতিযোগিতা দেখা দেয়, তাতে সবথেকে শক্তিশালীরাই প্রধানত টিকে থাকলেও, অন্য অনেক দিকের বিচারে দুর্বলতমরাও পারে টিকে থাকতে—বলেছেন তিনি। আরও বলেছেন, অজৈব প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে শুধু সংঘাতই থাকে না, সামঞ্জস্যও থাকে; জৈব প্রকৃতির বস্তুগুলোর মধ্যে সচেতন ও অসচেতন সংগ্রামের পাশাপাশিই অবস্থান করে সচেতন ও অসচেতন সহযোগিতাও। আর তাই, এমনকী প্রকৃতির ক্ষেত্রেও, চিন্তার নিশানে শুধু ‘সংগ্রাম’ লিখে রাখাটা তাঁর মতে নেহাই একপেশে ধারণা। বিভিন্ন প্রজাতির পরিবর্তনশীলতার কারণ, পরিবেশের ভূমিকা, বিপাক- ক্রিয়ার ভূমিকা—এ সব-বিষয়েও কিছু প্রশ্ন তুলেছেন, এঙ্গেলস। প্রশ্ন তুলেছেন ম্যালথাসের তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও। তবু, সমালোচনার পাশাপাশিই, মানবদেহের শারীরস্থানবিদ্যা, তুলনামূলক শারীরস্থানবিদ্যা, ভ্রূণতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জীবাশ্মতত্ত্ব, উদ্ভিদবিদ্যা—সবকিছুর ভিত্তি হিসেবে এঙ্গেলস চিহ্নিত করেছেন প্রজাতিতত্ত্বকেই, অকৃত্রিম স্বাগত জানিয়েছেন ডারউইনের আবিষ্কারকে। বলে রাখা ভালো, ‘ডায়ালেকটিক্স্ অফ নেচার’ লেখার সময় ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ ছাড়াও এঙ্গেলস সাহায্য নিয়েছিলেন এই ‘ডিসেন্ট অফ ম্যান’ গ্রন্থেরও।
ডারউইনের ভাবনাচিন্তার কিছু কিছু অংশ আজ আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় হয়তো বা পরিত্যক্ত, না হয় সংশোধিত হয়েছে, আবার কিছু কিছু প্রশ্ন নিয়ে আজও চলছে বিতর্ক গবেষণা। ডারউইন নিজেই লিখে গেছেন, “আমি জানি, ভবিষ্যতে এ-বিষয়ে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা হবে…মানুষের উদ্ভব আর মানবজাতির ইতিহাসের ওপর এসে পড়বে আরও উজ্জ্বল আলোকরশ্মি।’ এ-কথা লিখতে পেরেছিলেন ডারউইন, কারণ সামনে এগিয়ে চলাই সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চিরন্তন সত্য। নতুন নতুন আবিষ্কার, নতুন নতুন চিন্তাই এগিয়ে নিয়ে যায় পৃথিবীকে, ইতিহাসকে, মানবজাতিকে।
তবু, সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও, এটা অনস্বীকার্য যে আধুনিক জীববিদ্যার বনিয়াদ যিনি গড়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর নাম চার্লস ডারউইন। পৃথিবীর ইতিহাসে ডারউইন এবং তাঁর বিবর্তন তত্ত্বের মৃত্যু নেই।
অসীম চট্টোপাধ্যায়।
শিবপুর হাওড়া-২
.
মুখবন্ধ
কীভাবে বইটা লেখা হলো, সে সম্বন্ধে দু-চার কথা বলে নিলে এই কাজটির প্রকৃতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। বেশ কিছু বছর যাবৎ আমি মানুষের উদ্ভব বা বিবর্তন সম্পর্কিত তথ্যসমূহ সংগ্রহ করছিলাম, এখনই সেগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করব এমন কোনো সদিচ্ছা থেকে নয়, বরং প্রকাশ করার অনিচ্ছাই ছিল তখন। কারণ আমি জানতাম এর ফলে আমার মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক শোরগোল তোলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আমার মনে হয় ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ বইটির প্রথম সংস্করণে এটা উল্লেখ করাই যথেষ্ট ছিল যে এই বইটিতে ‘মানুষের উদ্ভব ও তার বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে’ এবং তার অর্থ হলো পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাবের রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে যে-কোনো সাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষকেও অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একই তালিকাভুক্ত করতে হবে। কিন্তু সম্প্রতি এ ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দেখা দিয়েছে। যখন কাল ফৎ-এর মতো একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিদ ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে জেনেভার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশনের সভাপতি হিসেবে খানিকটা ঝুঁকি নিয়েই বলেন যে, ‘অন্তত ইউরোপে কেউ আর এখন বিশ্বাস করে না যে সমস্ত প্রজাতির জীব পৃথকভাবে সৃষ্টি হয়েছে’, তখন এটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের অন্তত একটি বড় অংশই এখন মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে একটি প্রজাতি হলো অন্য একটি প্রজাতিরই রূপান্তরিত উত্তরাধিকারী। বিশেষত নবীন এবং উদীয়মান প্রকৃতিতত্ত্ববিদদের ক্ষেত্রে এ-কথা আরও বেশি করে সত্য। অনেকের কাছে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (natural selection) মতবাদটি সমাদৃত হলেও কেউ কেউ জোর দিয়ে বলছেন, আমি নাকি এটার ওপর বড় বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফেলেছি। বিচারকর্তা হিসেবে শেষ সিদ্ধান্ত অবশ্য ভবিষ্যৎই টানবে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় ব্যক্তিরা এখনও পর্যন্ত সবরকমে বিবর্তনতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করে চলেছেন।
অধিকাংশ প্রকৃতিতত্ত্ববিদ কর্তৃক এই মতবাদটি গৃহীত হওয়ার ফলে (সব ব্যাপারের মতো এক্ষেত্রেও শেষপর্যন্ত যাঁরা বিজ্ঞানী নন তাঁরাও ব্যাপারটা মেনে নেবেন) আমি আমার সংগৃহীত তথ্যগুলো সাজিয়ে নিলাম, যাতে দেখতে পারি আমার আগেকার রচনার সাধারণ সিদ্ধান্তগুলো মানুষের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য। এটা করার দরকারও ছিল, কারণ আমি কখনো কোনো-একটি বিশেষ প্রজাতির ওপর আলাদাভাবে এই মতবাদ প্রয়োগ করে দেখিনি। আমরা যখন কোনো একটি প্রজাতির ওপর আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করি, তখন প্রকৃতির সংযুক্তি-প্রবণতা থেকে উদ্ভূত জোরালো যুক্তিগুলো এসে আমাদের চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটায়। এই সংযুক্তি-প্রবণতা জীবজগতের সমস্ত বিভাগগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে—যেমন অতীত ও বর্তমান সময়ে তাদের ভৌগোলিক বিভাজন এবং তাদের ভূতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার। আমাদের দৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে পড়া কোনো প্রজাতি—তা সে মানুষ বা অন্য প্রাণী যা-ই হোক না কেন—তাদের গঠনের সাদৃশ্য ভ্রূণের বিকাশ ও প্রাথমিক পর্যায়ের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সবকিছুই বিচার করে দেখা উচিত। তবে আমার মনে হয় এই সুপ্রচুর তথ্য এখন সুস্পষ্টভাবেই বিবর্তনবাদের ভিত্তিকে জোরদার করে তুলেছে। একই সঙ্গে বিবর্তনের সপক্ষে অন্যান্য তথ্য থেকে পাওয়া জোরালো যুক্তিগুলোও মনে রাখতে হবে।
এই বইটির মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এটা চিাির করে দেখা যে, প্রথমত, মানুষ অন্যান্য সমস্ত প্রজাতির মতো পূর্বোদ্ভূত কোনো জীব থেকে সৃষ্ট কি না; দ্বিতীয়ত, কীভাবে তার ক্রমোন্নতি ঘটেছে; এবং তৃতীয়ত, মানুষের তথাকথিত জাতিগুলোর মধ্যে পার্থক্যের তাৎপর্য কী। এই বিষয়গুলোর মধ্যেই আমার বর্তমান আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব বলে বিভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যেকার পার্থক্য প্রসঙ্গে অহেতুক কোনো গভীর বিশ্লেষণে যাব না। কারণ এ এক বিশাল কাজ এবং অনেক মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপকভাবে আলোচিতও বটে। মানুষের অস্তিত্ব যে বহু প্রাচীন, সেটা সম্প্রতি প্রথমত মঁসিয়ে বুসার দ্য পার্থের প্রচেষ্টায় এবং পরে একদল সুপণ্ডিত ব্যক্তির বিপুল পরিশ্রমের ফলে উদঘাটিত হয়েছে। মানুষের উদ্ভবকে বোঝার পক্ষে এ-সবই অপরিহার্য উপাদান। সেইজন্য এই সিদ্ধান্তকে গ্রাহ্য বলে ধরে নিয়ে পাঠকদের আমি স্যর চার্লস লাইয়েল, স্যর জন লুবক এবং অন্যদের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধগুলো পড়ে দেখতে অনুরোধ করব। মানুষের সঙ্গে বনমানুষের তফাত সম্বন্ধে সামান্য কিছু উল্লেখ করা ছাড়া আমি আর কিছু বলব না এই রচনায়, কারণ অধ্যাপক হাক্সলি (বহু গবেষক ও সমালোচক তাঁর মতামত মেনেও নিয়েছেন) নিঃসন্দেহে প্ৰমাণ করেছেন—প্রতিটি দৃশ্যমান বিষয়ে মানুষের সঙ্গে উচ্চশ্রেণির বানরদের যতটা তফাত, তার থেকে উচ্চশ্রেণির বানরদের সঙ্গে নিম্নশ্রেণির বানরদের তফাত অনেক বেশি।
মানুষ সম্পকে মৌলিক কোনো তথ্য এখানে খুব কমই আছে। কিন্তু মোটামুটি একটা খসড়া করার পর আমি যে-সিদ্ধান্ত পৌঁছেছিলাম, তা আমার বেশ মনমতো হয়েছিল এবং ভেবেছিলাম অন্যদেরও তা কৌতূহলী করে তুলবে। অনেকসময় খুব জোর দিয়ে বলা হয়—মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে কখনোই কিছু জানা যাবে না। আসলে অজ্ঞতা সবসময়েই প্রকৃত জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয়। সেইজন্য যারা জানে তারা নয়, বরং যারা কিছু জানে না বা বোঝে না তারাই খুব জোর দিয়ে বলে যে এই সমস্যাটা বা ওই সমস্যাটা কিছুতেই বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করা সম্ভবপর নয়।
প্রাচীনকালের কোনো নিম্নতর এবং বর্তমানে বিলুপ্ত কোনো জৈবিক গঠনের থেকেই যে অন্যান্য কিছু প্রজাতির সঙ্গে মানুষ উদ্ভূত হয়েছিল—এই সিদ্ধান্তটি আদৌ কোনো নতুন সিদ্ধান্ত নয়। লামার্ক বহুদিন আগেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু বিশিষ্ট প্রকৃতিবিজ্ঞানী এবং দার্শনিকও এই মত সমর্থন করেছেন। যেমন-ওয়ালেস, হাক্সলি, লাইয়েল, ফ, লুবক, বুখনার, রল্ প্রমুখ এবং বিশেষত হ্যাকেল। হ্যাকেল তাঁর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ‘জেনারেল মরফোলজি’ (১৮৬৬) ছাড়াও সম্প্রতি (১৮৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৭০-এ) প্রকাশ করেছেন ‘Naturiliche Schopfungs geschicte’ রচনাটি। এতে তিনি মানুষের বংশবৃত্তান্ত প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। আমার প্রবন্ধটি লেখা হওয়ার আগে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে আমি হয়তো কোনোদিনই আমার প্রবন্ধটি শেষ করে উঠতে পারতাম না। আমি যে- সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, তার প্রায় প্রত্যেকটিই সমর্থিত হয়েছে এই প্রকৃতিবিজ্ঞানীর রচনায়। অনেক বিষয়ে তাঁর জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশি, অনেক পূর্ণাঙ্গ। অধ্যাপক হ্যাকেল-এর রচনা থেকে কোনো তথ্য বা দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করার সময় আমি সর্বদাই সরাসরি তাঁর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। অন্যান্য বিবৃতিগুলো আমার পাণ্ডুলিপিতে যেমন ছিল তেমনই রেখেছি, শুধু অনিশ্চিত বা কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও পাদটীকায় তাঁর রচনার কথা উল্লেখ করেছি।
বহু বছরের পর্যবেক্ষণের ফলে আমার মনে হয়েছে মানুষের বিভিন্ন জাতিতে ভাগ হয়ে যাওয়ার পিছনে যৌন নির্বাচন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’-এ এই বিশ্বাসের কথাটুকু শুধু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থেকেছি আমি। মানবজাতিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার করতে বসে আমি বুঝতে পারি যে সমগ্র বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।[১] ফলস্বরূপ এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডটি, যেখানে যৌন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা প্রথম খণ্ডের তুলনায় অত্যাধিক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। মানুষ এবং নিম্নতর শ্রেণির প্রাণীদের বিভিন্ন আবেগের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছে ছিল। বহু বছর আগে স্যর চার্লস বেল-এর গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি পড়ার পরই এই বিষয়টির প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিশিষ্ট শারীরতত্ত্ববিদের মতে, মানুষের শরীরে এমন কিছু পেশি আছে যেগুলো শুধুমাত্র আবেগ প্রকাশ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। এই ধারণাটি স্পষ্টতই অন্য কোনো নিম্নতর জৈবিক গঠন থেকে মানুষের উদ্ভব সংক্রান্ত ধারণার বিরোধী। তাই এ-বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। মানুষের ভিন্ন ভিন্ন জাতির সদস্যদের আবেগ প্রকাশের মধ্যে কতটা সাদৃশ্য আছে, তা-ও দেখানোর ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের আয়তনের কথা ভেবে ওই প্রবন্ধটিকে আলাদাভাবে প্রকাশ করার জন্য রেখে দিতে হলো।
চার্লস ডারউইন
১৮৭১
—
১. এই রচনাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখনও পর্যন্ত অধ্যাপক হ্যাকেলই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি ‘অরিজিন অফ স্পিসিস’ প্রকাশিত হওয়ার আগে যৌন নির্বাচন প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন এবং বিষয়টির গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বিষয়টি নিয়ে তাঁর বিভিন্ন রচনায় চমৎকারভাবে আলোচনা করেছেন তিনি।
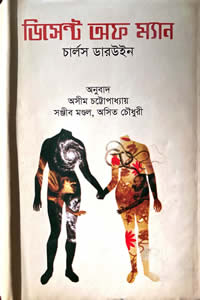
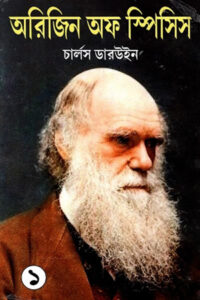
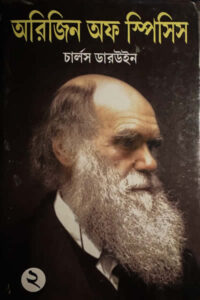

Leave a Reply