চৈতন্যদেব – নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
CHAITANNYADEB by Nrisinhaprasad Bhaduri
প্রথম প্রকাশ – সেপ্টেম্বর ২০১২
প্রচ্ছদ সুব্রত চৌধুরী
.
আমার ভগবতী জননী কুন্তলা-দেবীর প্রতি–
তাঁর শরীর-শোষী সন্তানের
প্রণামান্ত নিবেদন
.
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
অয়মারম্ভঃ
মা আমার প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত ভাবা উচিত ছিল, তা এইরকম খণ্ডিতভাবে ভাবলাম বলে অশেষ দুঃখ পাচ্ছি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি মাতৃগর্ভ থেকে হরিনাম শুনছি; হরিনাম আর ভাগবত-পাঠ শুনতে-শুনতেই আমার জাগতিক বিদ্যা-জীবন তৈরী হয়েছে। আমার পিতাঠাকুর এবং এখনও জীবিত আমার আশি-বছর-বয়সী মেজো দাদা অজিত কুমার-এর হাত ধরে এমন-এমন বিদ্বান দার্শনিক মহাপুরুষের সঙ্গ-লাভ করেছি আমি, যেটাকে অহো ভাগ্য বললে কম বলা হয়। ছোটবেলা থেকে ‘দুই ভাগবত সঙ্গে’ যেভাবে আমার সাক্ষাৎকার ঘটেছিল, তাতে চৈতন্য মহাপ্রভুর সম্বন্ধে আমার লেখার কথা ছিল আরও অনেক বিস্তৃতভাবে। তিনি আমার ঘরের ঠাকুর বলেই নয়, আমার অনন্ত ‘অবিদ্যা’র আধুনিক আলোকে চৈতন্যের। মানস প্রকাশ করার অবশ্যম্ভাবী দায় আমারই ছিল। কিন্তু এটা বুঝি, ভাল করে বুঝি আমি–এখনও তিনি আমাকে কৃপা করেননি, এখনও আমার অনন্ত অন্যাভিলাষ আছে, অনন্ত আবরণ আছে জ্ঞান এবং কর্মের, যশ-প্রতিষ্ঠার শূকরী-বিষ্ঠায় এখনও দিন্ধ আমার মনোবুদ্ধি-চিত্ত। তাই এখনও কৃপা হয়নি মহাপ্রভুর, তিনি সম্পূর্ণ স্ফুরিত হননি আমার লেখনীতে তাঁর সম্পূর্ণতা নিয়ে–সাঙ্গোপাঙ্গ-সপার্ষদে।
তবু এরই মধ্যে এইটুকু যে লিখেছিলাম–সেটা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলেও সেটা মদ্ভাবিত চৈতন্যের পূর্বাভাস-মাত্র। এই লেখা আমার প্রকাশ করার কোনও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমার এক মান্য বন্ধু–যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক দীপক। কুমার ঘোষ এমন সহৃদয়তায় এই লেখাটি একবার প্রকাশ করেছিলেন যে, আমার ‘না’ বলার উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে এমন এক বিচিত্রকর্মা পুরুষ যে, আরও হাজার। কর্মন্যাসের মধ্যে প্রকাশনার এই কন্যাস সমাপতিত হতে পারেনি, ফলে নিজে বুঝেই তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুকে আরও বহুর কাছে পৌঁছে দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন। প্রকাশের নতুন আবরণ, নতুন প্রকার এবং নতুন আকার সৃষ্টি করে ‘পত্রলেখা’-র। কর্ণধার আমার স্ফুরিত-চৈতন্যের রূপ দিয়েছে অন্যতর। তাতে অনুজ বন্ধু কৃষ্ণেন্দু চাকীর প্রচ্ছদ অলংকার হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছে আমার ছাত্রকল্প বন্ধু সীমান্ত গুহঠাকুরতা, তার প্রতি ভালবাসা রইল। আমার ছাত্রীকল্পা অধ্যাপিকা তাপসী মুখার্জী অনুলিখনে সাহায্য করেছেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল। আমার স্ত্রী, পুত্র পুত্রবধূ এবং নাতি সকলের অনুপ্রেরণা এই গ্রন্থ প্রকাশের পথে পাথেয় ছিল। যাঁদেরই নাম করলাম এখানে এবং যাদের নাম করলাম না, তাদের সবার ওপর আমার চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা করুশা বর্ষিত হোক। তিনি আমাকেও কৃপা করুন, যাতে অন্তকালের আগে তাকে আধুনিক ভাবনায় প্রকাশ করতে পারি।
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
২৫.০৮.২০১২
.
ভীতভীতঃ প্রণম্য
চৈতন্য মহাপ্রভু। ভেবেছিলাম, আরম্ভ থেকেই তাঁর কথা বলতে থাকব– বেশ একটা মঙ্গলারম্ভ হবে– বলতে থাকব তাঁর জীবন-কথা, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদদের তাঁর পরিচয় এবং অবশেষে এক যুগান্ত সৃষ্টি-করা তাঁর ধর্ম-আন্দোলনের কথা। কিন্তু সরাসরি আমি সেই চৈতন্য-জীবনে প্রবেশ করতে পারলাম না। তার একটা বড়ো কারণ তো আমার স্বভাব–আমি অবান্তর কথা না বলে আমার অন্তরের কথা বলতেই পারি না। আর আমার এই অবান্তর-প্রণয়ের ব্যাপারে আমার প্রেরণা হলেন আমার কবি। তিনিই বলেছিলেন– ‘অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা। বাজে কথাতেই মানুষ আপনাকে ধরা দেয়।’
আমি জানি, আমার কবি আমাকে উদ্দেশ্য করেই অথবা আমারই মতো শতেক অবান্তরের উদ্দেশেই একথা লিখেছেন। কিন্তু আমি এও জানি যে, দশটা অবান্তর শব্দ না শুনলে মহাকবির অন্তরটুকুও তো বোঝা যায় না। নইলে দেখুন, ওই যে শুধু একটা কথা ‘বাঁশি বাজে’। কথাটা কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য কোনওটাই নয়, একটা ভাববাচ্যের উদাহরণ বাঁশি বাজে। তা বাঁশি বাজলেই হত। কিন্তু সে এমনি বাজে না, তার জন্য আমার কবিকে উপকরণ সাজাতে হয়েছে, সৃষ্টি করতে হয়েছে বাঁশি বেজে ওঠার সেই সনাতন তথা পৌরাণিক পরিবেশ– বসন্তের বাতাস থেকে আরম্ভ করে বাঁশি শুনে লোকলজ্জা ভুলে যাবার প্রতিস্মৃতি। আর চৈতন্যলীলার শুরু কৃষ্ণদাস কবিরাজ তো শুধু রাধাভাবিত চৈতন্যের হৃদয়মূর্তি শুনিয়ে বলেছিলেন– অন্যের হৃদয়কে মন’ বলে বটে, কিন্তু আমার মনটাই বৃন্দাবন হয়ে গেছে, ফলত মনে আর বনে কোনও তফাৎ কিছু বুঝি না– অন্যের হৃদয়– মন, মোর মন বৃন্দাবন
‘মনে’ ‘বনে’ এক করি জানি।
কিন্তু আমার ব্রহ্মদর্শী কবি– আমার স্বতঃসিদ্ধ কবিও কী চৈতন্য চরিতামৃত পড়েছিলেন কখনও –তা নইলে বিশাল-হৃদয় দুই মানুষ এমন একাকার, একভাবে ভাবেন কী করে। কেমন করে তিনি লেখেন—
সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে– বনমাঝে কি মনোমাঝে।।
বসন্তরায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনি, এ সুখরজনী
কোনখানে উদিয়াছে– বনমাঝে কি মনোমাঝে।।
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা,
সখী, মিছে মরি লোকলাজে।
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে
আমি কিন্তু বাঁশীর কথা বলতে বসিনি এখানে। আমি শুধু বলেছি, ওই একটা শব্দের তাৎপর্য বোঝাতে গেলে কত অবান্তর কথা বলতে হয়। হ্যাঁ, এই কথাগুলিকে আপনি বাজে কথা বলবেন কিনা, অথবা বাজে খরচ– কিন্তু মানুষ চেনার জন্য, বিশেষত চৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এক বিরাট অভ্যুদয়কে চেনার জন্য তাঁর সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি এবং এই বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের যে মহাপ্রস্তুতি তৈরী হয়েছিল সেই সব অবান্তরের কথা না বললে চৈতন্য মহাপ্রভুকে চিনবো কী করে? হ্যাঁ, এসব কথা অবশ্যই আধুনিক ইতিহাস গবেষকের যুক্তি যে, একজন বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের জীবন এবং কর্ম জানতে গেলে তাঁর সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং মানুষ-বনিয়াদটাকেও জানতে হয়। কিন্তু আমরা বলবো–এত বড়ো যুক্তিটা আমাদের প্রাচীনেরাও খুব ভালভাবে জানতেন। অবাক হবেন না, একটু বুঝিয়ে বললে বুঝবেন, ঐতিহাসিক বিচারের ক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীনেরাও যথেষ্ট আধুনিক ছিলেন।
বলবো সেসব কথা। কিন্তু সে আমার মতো করেই বলবো। চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন আমার কাছে এক। সামাজিক গীতিকবিতার মতো। যাঁরা সে জীবন-কথা বলেছেন, তাঁরাও শতেক অবান্তর কথার মধ্যে দিয়েই কথকতা করেছেন তাঁর জীবন সন্ধান করার জন্য। বেদ-বেদান্ত-দর্শন, সমাজ, রাজনীতি– এসব তাঁরাও বলেছেন, কিন্তু সেসব কথা কখনোই ঐতিহাসিকের গবেষণা–গম্ভীর অর্থবাদে সমাকুল হয়ে ওঠেনি। অথবা সামাজিক- ঐতিহাসিকের স্মিতহাস্যহীন ‘সিগনেচারও সেটা নয়। আমাদের কথাও তেমনি হবে। আমার সুবিধেও আছে অনেক। আমার পূর্বসূরিরা আছেন, তাঁদের গবেষণা আমার কাছে সপ্ততীর্থের জল– এতদিন সেই গবেষণার তীর্থজলেই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে মহাভিষেক হয়েছে আমি সেই স্থানীয় চরণামৃত পান করে চৈতন্য কথা বলতে আরম্ভ করেছি। আর আমার ভরসা এখানে চৈতন্য-পার্ষদ রূপ গোস্বামীর একটি শ্লোক।
রূপ গোস্বামী তাঁর বিদগ্ধমাধব নাটকে বলেছিলেন– আমি যে এই নাটকখানা লিখেছি, তার মধ্যে আমার লেখা কবিতাগুলি হয়তো তেমন সুললিত নয়, কিন্তু সেই কবিতাগুলির মধ্যে আমার প্রাণারাম কৃষ্ণের গন্ধ আছে বলেই পণ্ডিতজনের আনন্দ হবে তাতে। একবার ভেবে দেখুন, বিষ্ণু-স্বরূপ শালগ্রাম শিলাকে যদি কুয়োর জলে স্নান করানো হয়, তাহলেও এমন কোনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নেই, যাঁরা নতমস্তকে সেই চরণামৃত পান না করবেন–
অপঃ শালগ্রামাপ্লবন-গরিমোদগার-সরসাঃ
সুধীঃ কো বা কৌপীরপি নমিতমূর্ধা ন পিবতি।
আমি সেই ভরসাতেই চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন-কথা কিয়ৎ-কিঞ্চিৎ বলতে আরম্ভ করেছি। একই সঙ্গে এটাও খুব ঠিক কথা, চৈতন্যের কথা শুনলে পরে স্বাভাবিক যে ফলটা হয়, যেমনটা বৈষ্ণব কবিরা বলে থাকেন– শুনিলে চৈতন্য কতা ভক্তি লভ্য হয় ঠিক তেমনটা যে আমার চৈতন্য-কথা শুনলে হবে না, সেটা আমি হলফ করেই বলতে পারি।
‘তবু লিখি এ বড়ো বিস্ময়। অন্তত এই বইটা যে লিখেছি, তার একটা বড়ো কারণ নিজেকে পরীক্ষা করা। পরীক্ষা করে দেখলাম আমার কথকতায় মানুষ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন আস্বাদন করে কিনা? সম্ভবত এই পরীক্ষায় আমি পাশ করেছি কেননা এই বইটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল গুণেন শীলের ‘পত্রলেখা’ প্রকাশন-সংস্থা থেকে। বহু মানুষ, আমার বহু সহৃদয় পাঠক এই গ্রন্থসঙ্গ করেছেন এবং এখনও এই গ্রন্থ অনেকেই পড়তে চায়। ফলে গ্রন্থরূপী মহাপ্রভু ‘পত্রলেখা’র কর্ণধারের ওপর কৃপা-কণা বর্ষণ করে নতুন গৃহে এলেন দীপ্তাংশুকে কৃপা করার জন্য।
আমি শুধু এইটুকু জানি আমি নিজেই তাঁর কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছি। তা নাহলে আমি যে। ভেবেছিলাম– আমি সমস্ত অবান্তর কর্ম ছেড়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিয়ে একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করবো, আমি সেই শক্তি এখনও লাভ করিনি কেন। তবে এত জানি, আমার এই আশা ব্যর্থ হবে না। আমি বৈষ্ণব বাড়িতে জন্মেছি, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্যদের সঙ্গ করেছি এককালে, তাঁদের কৃপা-করুণাও লাভ করেছি অপার। ফলত অবান্তর বিচিত্র যত লেখা আমি লিখেছি, তা সবই সেই অনাস্বাদিত মধু লাভ করার জন্য চরৈবেতি-র সাধন। আমার প্রস্তুতির পদচারণা। চৈতন্য মহাপ্রভু যবন হরিদাসকে বলেছিলেন—
প্রভু কহে হরিদাস যে তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে।।
আমি সেই কৃপার অপেক্ষায় বসে আছি আমি জানি, অচিরেই সেই কৃপা আমি লাভ করবো।
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
.
গৌরচন্দ্রিকা
মহাপ্রভুর জন্মলীলা পাঁচশো বছর পূর্তি হয়ে গেছে এবং সেই উপলক্ষ্যে উৎসব, পদযাত্রা, স্মৃতিসভা যথারীতি চলেছে। আমরা জানি বঙ্গদেশের চৌহদ্দির মধ্যে ভগবান বলেই তাঁর প্রতিষ্ঠা বেশি। চৈতন্যপন্থীদের ভক্তিমিশ্রিত আদর্শে তাঁর রূপ–রাই-কানু একীভূত– ‘রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ।’ আজ চৈতন্যজন্মের পাঁচশো বছর পরে একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় বসে উৎসব-স্মৃতিসভার ধূপের ধোঁয়ায় সত্যি করে তাঁর চরণ ছোঁয়ার সময় পাই না, যেখানেই যাই, কেবলই সেই বহিরঙ্গ অনুভূতি, তাঁর বিচিত্র ধর্মজীবনের উপরিকাঠামো নিয়ে উচ্চগ্রাম প্রশস্তি, কিন্তু এসব কিছুর মধ্য থেকে আসল মানুষটিকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করার সময় কি এখনও আসেনি? তিনি যে কত বড় মানুষ ছিলেন তার প্রমাণ সামান্য জগাই মাধাই, আর চাপাল-গোপাল উদ্ধার কাহিনিতে নয়, কিংবা নয় তাঁর ঐশীশক্তিতে, যাতে করে ব্যারিখণ্ডের পথে তাঁর কৃষ্ণনামের ধ্বনিতে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ব্যাঘ্ৰ নাচিতে লাগিল।’ ভক্ত বৈষ্ণব সম্মেলনে এসব কথা শুনি, আবার এক প্রস্থ বৈদগ্ধ্যের প্রলেপ-মাখানো বাণী শুনতে পাই বুদ্ধিজীবীদের সভায়, যেখানে মহাপ্রভুর গায়ে লাগে সাম্যবাদের ফুরফুরে হাওয়া। কেমন করে সমগ্র ভক্তসঙ্গে মিছিলে শামিল করে কাজিদলন করেছিলেন প্রভু, কেমন করেই বা সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে ডেকে এনেছিলেন তাঁর নামসংকীর্তনের ছত্রছায়াতলে।
এ সবকিছুই সত্যি, কিন্তু এই ছোট ছোট সত্যের তলায় চৈতন্যসত্তার আসল স্বরূপটি গেছে হারিয়ে, যা পাঁচশো বছরের নিকষে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। চৈতন্যদেবের প্রধান পরিচয়–তিনি একটি বিশেষ ধর্মের প্রবক্তা এবং সেই ধর্মের সাহসের পরিচয় যেখানে দিতে হয়েছিল–সেখানে তিনি একা। মানুষ হিসেবে চৈতন্যদেব কত বড়ো কিংবা তাঁর ব্যক্তিত্ব কত অসামান্য–তা যদি খুঁজে বার করতেই হয়, তবে তা দেখতে হবে তাঁর ধর্মীয় মতবাদের মধ্যেই, কেননা প্রধানত তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণপুরুষ, তারপরে অন্যকিছু। মনে রাখা দরকার–অন্যান্য ধর্মীয় প্রবক্তাদের মতো বেদ-বেদান্তের অবলম্বন খোঁজার জন্য প্রথমেই তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেননি। এটি তাঁর দুঃসাহস। চৈতন্যপন্থীরা যতই বলুন যে, শ্ৰীমদভাগবতই তাঁর কাছে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের মতো, কিন্তু এ কোনো অজুহাত নয়, আসল কথা চৈতন্যদেব এমনই বড়ো মাপের পুরুষ, এমনই তাঁর ব্যক্তিত্ব যে, তিনি যা বিশ্বাস করেন না, তার ওপরে তিনি ভাষ্য লিখতে যাবেন কেন?
দুঃখের বিষয়, ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য কেন, চৈতন্যদেব কিছুই লিখে যাননি। সারা জীবন ভাবে বিভোর, তিনি তাঁর অনুগামীদের দিয়ে গেছেন তাঁর চিরবিশ্বস্ত তত্ত্বপ্রচারের উত্তরাধিকার; কাজেই তাঁর একান্ত অনুগামীদের ধারণাতেই প্রভুকে খুঁজে পেতে হবে। চৈতন্যের সমকালীন তথ্য পরবর্তী সাহিত্যে এবং ইতিহাসে চৈতন্যদেবকে আমরা পাই এক উদার ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে। তাঁর ধর্মমতের ওপর বেদ-বেদান্ত-পুরাণ কোনটির প্রভাব বেশি, সেটা আমাদের বিচার্য বিষয় হলেও এ সত্য অনস্বীকার্য যে, চৈতন্যদেবের ধর্মমত একান্তভাবেই তাঁরই। তাঁর ধর্মীয় মতবাদের বিষয়গুলো অন্য জায়গা থেকে সংকলিত হলেও, সেগুলোকে আত্মসাৎ করে একটি নবরূপ দান করা–এটি চৈতন্যদেব না হলে হত না।
একথা বলতে অসুবিধা নেই যে, প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যত অস্তিবাদী ধর্মমত আমাদের দেশে চালু আছে, তাদের প্রত্যেকটিই বেদ এবং উপনিষদকে মেনে নিয়েছে মৌলিক ভিত্তিতে। এই ধর্মগুলোর প্রভাবে আমাদের দর্শন এবং ধর্মের মধ্যে প্রভেদ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। যুগে যুগে যখনই কোনো মহাত্মা পুরুষ নতুন কোনো ধর্মমত প্রচার করতে চেয়েছেন তখনই তিনি বলেছেন তাঁর ধর্ম বেদানুগ, অন্যথায় জনসাধারণ–যাঁরা কোনোকালেই বেদ-বেদান্তের বেশি খবর রাখেন না–তাঁকে মেনে নিত না। ফলে বেদ-বেদান্তকে শিখণ্ডীর মতো ব্যবহার করা হয়েছে বার বার, প্রতিপক্ষের ভীষণ আক্রমণ রোধ করার জন্য। বেদ এবং উপনিষদের ব্যাখ্যা হয়েছে নব নবতর, শুধু তাই নয়, কখনওবা বিকৃত। চরম ব্যাখ্যানের এমন একটা পদ্ধতি প্রত্যেকেই বেছে নিয়েছেন, যাতে আসলটি হারিয়ে গেছে। একথা যেমন শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে বলা চলে, তেমনি চলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধেও। যেরকম আমরা জানি উপনিষদের মধ্যেও নিগুণ নির্বিশেষে ব্রহ্মের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে স্বগুণ সবিশেষ ব্রহ্মের কথাও। শঙ্করাচার্য নিজেও একথা স্বীকার করেছেন–সন্তি উভয়লিঙ্গাঃ তয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ –এসব কথা বলে। তা সত্ত্বেও কিন্তু প্রকৃতস্থলে যখন স্পষ্ট নির্দিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্মের টীকা করবার সময় এসেছে, তখন হয় তিনি এড়িয়ে গেছেন, অথবা খুব সাবলীল হতে পারেননি তিনি। ঠিক এসব দুর্বল জায়গাগুলোতেই তাঁকে চেপে ধরেছেন প্রতিপক্ষ দার্শনিকেরা। অন্যদিকে একেবারে আধুনিক দৃষ্টান্তে আসি, আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মারকগ্রন্থে (পৃ. ৫-১৫) শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত মহাশয় ‘বেদে ব্রকথা’ বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বেদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার সুরটি ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন লেখক এবং লেখাটির মধ্যে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য থাকলেও তীক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বেদের মধ্যে পরব্রহ্মস্বরূপ নলীলা কৃষ্ণকে আবিষ্কার করা এখনও সম্ভব হবে কি? বৈদিক সাহিত্যের কিছু বিখ্যাত স্থানে কতগুলি গোরু চরতে দেখা গেছে বলেই এবং সেইসব গোরুর বেদে উল্লেখ আছে বলেই গোকুল-বৃন্দাবনের স্মরণ হওয়াটা অতি-ভাবালুতা মনে হয় আমার।
আমাদের মনে হয়–বেদ এবং উপনিষদের আক্ষরিক এবং নিজস্ব অর্থের একটি ধারা আছে নিশ্চয়ই, যা একান্তভাবে বেদের কিংবা উপনিষদের। কিন্তু টীকা-টপ্পনির অন্তরালে সেগুলো হারিয়ে গেল, ক্ষুরধার পাণ্ডিত্যের সূক্ষ্ম প্রলেপে স্থান করে নিলেন শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাদ্বাাচার্য ইত্যাদি, যার শেষে আছেন বলদেব বিদ্যাভূষণ, যিনি ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করলেন চৈতন্য-ধারায়। আমি বলছি না যে, টীকা ভাষ্যের প্রয়োজন নেই, কিন্তু মূল অর্থসঙ্গতির প্রয়োজন বোধহয় তার থেকেও বেশি। শঙ্করাচার্য প্রভৃতি প্রত্যেকেই মহাপণ্ডিত, যাঁদের নিজস্ব দর্শনও পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু অনর্থক কষ্টকল্পনা যেখানে, সেখানে বেদ উপনিষদের সোজাসুজি অর্থটা ধরলে ক্ষতি কী?
চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ একজায়গায় বলেছেন– ‘বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্ধেক বেদ মুখে মানে’, অর্থাৎ অনেক ধর্মতত্ত্বই নিজের সুবিধার জন্য বেদকে ব্যবহার করে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অতি পণ্ডিত গ্রন্থকার, তিনি নিজেও যে এ তথ্যটি জানতেন, তাতে আমাদের সুবিধেই হল। তাত্ত্বিক দিক থেকে বেদ-বেদান্তের সঙ্গে কোনো ধর্মীয় মতবাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে কি না তা বোঝা যাবে সেই বিশেষ মতবাদের মৌলিক বিষয়গুলো পর্যালোচনার মাধ্যমে।
জীবগোস্বামী–যাঁকে চৈতন্যদর্শন-শাখায় এক স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয়–তিনি তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে প্রথমেই বেদকে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাস (রামায়ণ-মহাভারত) এবং পুরাণগুলোকে তিনি বেদের সমমর্যাদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। এমনকী তিনি এ কথাও বলেছেন যে, বেদের মতো ইতিহাস-পুরাণগুলোও পুরুষরচিত নয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ। মহাভারতের কথা উদ্ধৃত করে জীব বললেন–ইতিহাস এবং পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ পরিপূরণ করতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাস-পুরাণই হল বেদোপনিষদের ভাষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের কথাও উদ্ধৃত করেছেন জীবগোস্বামী। এখানে নারদের জবানিতে বলা হয়েছে–আমি ঋগবেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ এবং ইতিহাস-পুরাণ নামক পঞ্চম বেদও পড়েছি। এই প্রমাণবলে জীব বললেন, ইতিহাস-পুরাণ তা হলে বেদ বটেই।
জীবগোস্বামী যেসব যুক্তি দিয়েছেন, সম্প্রদায়গত কারণে তার প্রয়োজন ছিল হয়তো, কিন্তু এইসব যুক্তিতে ইতিহাস-পুরাণকে বেদের সমমর্যাদায় স্থাপন করা যাবে কি? প্রথমত, বেদের পয়লা নম্বর দেবতা যাঁরা– সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র–এঁদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বৈষ্ণবমতে সমান আসনে বসানো যাবে কি? চৈতন্য-দর্শনে এবং ধর্মে কৃষ্ণের তুলনা কৃষ্ণ নিজেই। সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি তাঁর আজ্ঞাবাহী কিঙ্করমাত্র। তা ছাড়া চৈতন্যদেবের মনোভূমিতে শ্রীকৃষ্ণকে যে চেহারায় আমরা পাই, বেদের মধ্যে তার কোনো আভাস পাই না। ছান্দোগ্য উপনিষদে কৃষ্ণের নাম করা হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক কৃষ্ণ। যাকে আমরা বাসুদেব কৃষ্ণ বলে জানি, পরবর্তীকালে তিনিই মহাভারতের সূত্রধার।
চৈতন্যদেবের মানসপটে কৃষ্ণের যে ছবি ছিল, তাতে শাস্ত্রবচনের পটভূমিতে মিশেছিল তাঁর আপন মনের মাধুরী। চৈতন্যধর্মের কৃষ্ণ নিজের মাধুর্য আস্বাদনের জন্য নেমে এসেছেন জগতে, ভু-ভার-হরণ ইত্যাদি তাঁর আনুষঙ্গিক কাজ। তিনি নন্দ-যশোদার স্নেহের বাঁধনে বাঁধা, গোপবালকের খেলার সাথী এবং তাঁর সব থেকে বড়ো পরিচয় তিনি গোপীচিত্তচোর। শ্রীকৃষ্ণের এই রূপের সঙ্গে বৈদিক দেবতার কোনো ছবিই মেলে না। উপনিষদের ব্রহ্ম চৈতন্যমতাবলম্বীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তিমাত্র। (‘যদ অদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তপস্য তনুভা’–চৈতন্যচরিতামৃত ১.১.৩ ‘যস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞং ক্বচিদপি নিগমে যাতি চিন্মাত্রসত্তাহ’–জীবগোস্বামীকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ) বিশেষ করে গীতার মধ্যে “ব্রহ্ম আমাতেই (কৃষ্ণ মধ্যে) প্রতিষ্ঠিত’’–এইসব কথায় গীতার মহিমা উপনিষদের থেকেও গ্রাহ্য হয়েছে বেশি। কেউ কেউ বলেন বৈদিক বিষ্ণুই হলেন কৃষ্ণের আদিরূপ। সত্যি কথা বলতে কী, বিষ্ণুর ক্ষমতা, গুণাবলি এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-কর্মের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিল ছিল বোধহয় সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তবু তো গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বৈদিক বিষ্ণু স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। বিষ্ণু সেখানে স্থিতিকর্তা মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের বিভূতি। তাঁর কাজ অসুর সংহার ইত্যাদি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করার সময় বিষ্ণু তাঁর শরীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য। (চৈতন্যচরিতামৃত, ১.৪.১৩) কাজেই দেখা যাচ্ছে, বৈদিক বিষ্ণু কিংবা অন্যান্য দেবতা, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম–কেউ কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ওপরে নন। স্বাভাবিক কারণেই বেদ-উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে পুরাণগুলির প্রতিপাদ্য বিষয়ের মৌলিক পার্থক্য আছে। পুরাণগুলিকে সে অবস্থায় বেদের সমভূমিতে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। সময়ের হিসেব ধরলেও তা একেবারেই অসম্ভব।
দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত গ্রন্থকে মূল গ্রন্থের পরিপূরক ভাষ্য হিসেবে মনে করা যায়, তাদের কি মূলের সমমর্যাদা দেওয়া যাবে? অথচ ‘ইতিহাস-পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ পরিপূরণ করবে’–মহাভারতের এই কথাটির ওপর ভরসা করে জীব গোস্বামী ইতিহাস-পুরাণকেই বেদ বলে মেনে নিলেন। আমাদের জিজ্ঞাসা– নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়া ম্যাথেমেটিকা’র সমতুল্য মর্যাদা কি অন্যকৃত পরিপূরক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থগুলোকে দেওয়া যাবে?
তৃতীয়ত, আমরা জানি–বেদ ছাড়া আর যা কিছু মানুষের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তাকেই পঞ্চম বেদ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে আমাদের দেশে। যেমন নাট্যশাস্ত্র (নাটকং পঞ্চম বেদং সেতিহাসং করোম্যহম–ভরতকৃত নাট্যশাস্ত্র ১.১৫) আয়ুর্বেদ ইত্যাদি। তার মানে এই নয় যে, নাট্যশাস্ত্রকে আমরা বেদ বলে মনে করব, যেমন আমরা পুরাণগুলিকে তা মনে করব না। বেদ-উপনিষদের পরবর্তী যুগে ইতিহাস-পুরাণের জনপ্রিয়তা বোধহয় তাদের দার্শনিক মুলাধার বেদ-উপনিষদকেও অতিক্রম করেছিল। ইতিহাস-পুরাণের মর্যাদা সেইটুকুই, কিন্তু তবুও এগুলো বেদ-উপনিষদ নয়।
চতুর্থত, যেসব যুক্তিতে প্রাচীনপন্থীরা বেদকে অপৌরুষেয় বলেছেন (সায়নাচার্যের ঋগভাষ্যোপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য) সেইসব যুক্তিতে কখনোই ইতিহাস-পুরাণকে বেদ বলে মানা যায় না। বিশেষ করে পুরাণগুলোর মধ্যে অনেক জায়গায়ই পুরাণকর্তাদের নাম আছে। বেদের মন্ত্রের ক্ষেত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকে পাওয়া যাবে, কিন্তু মন্ত্রকর্তা পাওয়া যাবে না।
পরিশেষে বলি, ইতিহাস-পুরাণকে বেদ বলে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না জীব গোস্বামীর। পুরাণগুলোকে প্রায় বেদের মর্যাদা দেওয়ার রেওয়াজ আরম্ভ হয়েছে যামুনাচার্য, রামানুজের সময় থেকেই। রামানুজের লেখার মধ্যে ভূরিভূরি পাওয়া যাবে বিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ। পরবর্তীকালে জীব গোস্বামী সম্পূর্ণ বৈদিক মর্যাদায় স্থাপন করেছেন ভাগবত পুরাণকে, কারণ ভাগবতের মধ্যে চৈতন্যপ্রবর্তিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্যদেব বুঝেছিলেন–পুরাণগুলোকে দিয়েই লীলাময় এবং মধুর রসের রসিক কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। চৈতন্যদেবের যেহেতু কোনো ‘প্রিটেনশন’ ছিল না, তাই সনাতন শিক্ষায় তাঁর নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী বলেছেন সোজাসুজি–’সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন’ (চৈতন্যচরিতামৃত ২.২৪.২৫৬)। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পুরাণগুলি যত সুবিধাজনকই হোক না কেন, কোনো মতের প্রামাণিকতা স্থাপনের জন্য উপনিষদ এবং ব্রহ্মসুত্রের ভিত্তি না হলে কোনো ধর্মেরই চলেনি–তাই বৈষ্ণবমতাবলম্বী পণ্ডিতেরাও চেষ্টা করেছেন সেই মর্মে এবং এইখানেই বোঝা যাবে বেদ-বেদান্তের সঙ্গে চৈতন্যধর্মের আত্মিক যোগাযোগ কতটা।
কৃষ্ণতত্ত্বের কথা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে যাই হোক না কেন, দার্শনিক দিক থেকে তার একটা প্রতিষ্ঠা চাই– যা খুব ভালোভাবে ধরা হয়েছে ভাগবতের একটি শ্লোক (১.২.১১) তত্ত্ববিদেরা তত্ত্ব বলেন তাকেই যা দ্বিতীয় জ্ঞানের সূচনা করে না অর্থাৎ যেটি অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব বলেন তাকেই ঔপনিষদিকেরা বলেছেন ‘ব্রহ্ম, যোগমার্গের উপাসকেরা বলেন পরমাত্মা, ভক্তেরা বলেন ভগবান’, (১.২.১১ শ্লোকে শ্রীধরস্বামীর টীকা দ্রষ্টব্য)। ভাগবতের মূল শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় একই তত্ত্বকে তিনটি পৃথক নামে ডাকা হয়েছে মাত্র। শ্লোকটি উল্লেখ করার কারণ হল–ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান–এঁরা একই তত্ত্বে পর্যবসিত হলেও শ্লোকটির মূল এবং সাধারণ অর্থের অপেক্ষা করেননি বৈষ্ণব দার্শনিকেরা, (ব্যাকরণে যাঁদের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে তাঁরা এই শ্লোকে তিনবার পৃথকভাবে ‘ইতি’ অব্যয়টির ব্যবহার খেয়াল করবেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে স্বর্গীয় রাধাগোবিন্দনাথ মহাশয়ের লেখায় পাই–’’এই শ্লোকে ইহাও জানা গেল–নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং জীবান্তর্যামী পরমাত্মা জিজ্ঞাসা তত্ত্ব নহেন। কেননা নির্বিশেষ ব্ৰহ্ম এবং জীবান্তর্যামী পরমাত্মা চরম এবং পরম তত্ত্ব নহেন।’
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনেক আলোচনা এবং প্রবন্ধে ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির ব্যাপারে একটা অহেতুক আতঙ্ক প্রকট হয়ে ওঠে। এই শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করাচার্যের নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম তাঁদের মন জুড়ে বসে। কিন্তু উপনিষদের নিজস্ব দর্শন আর শঙ্করাচার্যের দর্শন তো এক নয়। ভাগবতের শ্লোকটির মধ্যে কোথাও কি এঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্ম বলা হয়েছে? শুধু বলা হয়েছে এঁকে ব্রহ্মা বলে ডাকা হয়, ব্রহ্মেতি…শব্দতে। সে ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলে ব্যাখ্যা করা এবং উপনিষদের পরম তত্ত্বকে জিজ্ঞাস্য তত্ত্ব নহেন’ এমন কথা বলা সঙ্গত নয়। আসল কথা ভাগবত পুরাণের মধ্যেও ব্রহ্মতত্ত্বের যতখানি সঙ্গতি ছিল চৈতন্যপরবর্তীযুগে তার থেকে দূরে সরে এসেছেন বৈষ্ণব দার্শনিকেরা; অথচ উপনিষদের ব্রহ্ম থেকেই ভগবৎ প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁরা এবং এই ভগবত্তত্ত্ব থেকেই কৃষ্ণের দার্শনিক প্রতিষ্ঠা। এ বিষয়ে তাঁদের আনুক্রমিক পদ্ধতিটি এইরকম—
প্রথমেই শঙ্করের নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে ধূলিসাৎ করে, তাঁকে সবিশেষ, নির্মল-গুণযুক্ত, অশেষ শক্তিমান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ব্যাপারে উপনিষদের সেই শ্লোকগুলোই বেছে নেওয়া হয় প্রমাণ বলে, যেগুলো ব্রহ্মের রূপ, গুণ, শক্তি ইত্যাদির কথা বলেছে।
জীবগোস্বামী তাঁর ভগবৎসন্দর্ভের প্রথমেই ব্ৰহ্মকে ভগবান বলা যায় কিনা সেইটে চেষ্টা করেছেন। এই বিচারে উপনিষদের সাহায্য পাওয়া মুশকিল তাই প্রমাণগুলো প্রধানত এসেছে পুরাণ থেকে। বাস্তবিকপক্ষে পুরাণের মধ্যে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানকে সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। এখানেই ব্রহ্মের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, শক্তিমত্তা শেষ পর্যন্ত পর্যবসিত হয়েছে ভগবানে। ভগবান বলতে আমরা একটা ব্যক্তিক রূপ (personalised form) বুঝি যাঁর অসীম শক্তি, অনন্ত লীলা এবং বিচিত্র মহিমা। কিন্তু ভগবানকে ব্রহ্মের সঙ্গে এক করে ফেলার ব্যাপারটা উপনিষদ-পরবর্তী গ্রন্থগুলোতে বিশেষত পুরাণগুলোতে যে রকম আছে। তেমনটি কোথাও নেই, যদিও অহিবুন্ধ্যাসংহিতা ইত্যাদি পাঞ্চরাত্ৰ-সাহিত্যও আর একটি বড় উপাদান।
উপনিষদের মধ্যে যেসব জায়গায় ব্রহ্মকে পুরুষ, অক্ষর পুরুষ ইত্যাদি বলা হয়েছে সেইসব জায়গাগুলো ব্যক্তিক রূপ প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে সুবিধা দিয়েছে বেশি। কোনো কোনো বৈষ্ণব মহাজনেরা আবার ব্রহ্মের বৃহত্ত্ব, স্বপ্রকাশ, জ্ঞানস্বরূপত্ব, শক্তিবিকাশ বৈচিত্র্য, রসবৈচিত্র্য–এসব বিষয়ে উপনিষদের যত প্রমাণ আছে। তার সবকিছুরই পর্যবসান করেছেন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণে। এতে আপত্তিরও কিছু আছে বলে মনে হয় না। কেননা ব্রহ্মের সবিশেষ, সগুণ, সশক্তিক রূপটির সঙ্গে ভগবানের ব্যক্তিক রূপের খুব একটা পার্থক্য নেই, যেমন পার্থক্য নেই কৃষ্ণের সঙ্গেও। কিন্তু অদ্ভুত লাগে তখনই, যখন দেখি উপনিষদের যে সমস্ত ব্রহ্মসম্বন্ধী শ্লোকগুলি দিয়ে কৃষ্ণের মর্যাদা প্রতিস্থাপিত করা হল সেই ব্রহ্মই কৃষ্ণের অঙ্গক্লান্তিতে পরিণত হলেন। এ যেন ডাল বেয়ে গাছের মগডালে উঠে ডাল কাটতে কাটতে নামা। বিশেষ করে ভাগবতের যে শ্লোকটিতে ব্রহ্মা, পরমাত্মা এবং ভগবানের সমত্ব দেখানো হয়েছে সেখানে ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা–এই দুটি তত্ত্বের লঘুত্ব দেখানো মূল শ্লোকের অর্থহানি করে। জীব গোস্বামী তাঁর দার্শনিক নিপুণতা দিয়ে ভগবৎসন্দর্ভে ব্রহ্মকে ভগবান বলা যায় কি না সেই নিয়ে নিপুণ বিচার করার পর কৃষ্ণসন্দর্ভে এসে বললেন–যিনি ভগবান তিনি যে কৃষ্ণ হয়েছেন তা নয়। যদি ভগবান কৃষ্ণ হয়েছেন এমন বলা হয়, তবে কৃষ্ণের অবতারী মূলস্বরূপ প্রমাণ করার জন্য অন্য ভগবান কল্পনা করতে হয়, কিন্তু তা হতে পারে না, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন একটি নিরপেক্ষ তত্ত্ব, কাজেই ভগবানের তত্ত্ব থেকেই কৃষ্ণের তত্ত্ব প্রতিপাদন করা যেতে পারে না, বরং কৃষ্ণের। থেকেই ভগবানের তত্ত্ব প্রতিপাদন করা যেতে পারে–কৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণো ধর্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এর প্রতিধ্বনি করে বলেছেন–
যাঁহার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা
স্বয়ং ভগবান শব্দের তাঁহাতেই সত্তা।।
জীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কিংবা আজকের ড. রাধাগোবিন্দ নাথ যা করেছেন বা যতটুকু করেছেন। তার পদ্ধতিটি কিছু নতুন নয়, তবে নতুন এইটুকু যে কৃষ্ণের সার্বিক প্রতিষ্ঠার পর দার্শনিক পরম তত্ত্ব হিসেবে ব্রহ্মা কিংবা পরমাত্মা, এমনকী ভগবানও তাঁর পূর্বস্বীকৃত গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছেন। অপ্রিয় সত্য হলেও বলতে হয়–বেদ-বেদান্তের সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিপাদিত ভগবৎ-তত্ত্বের কোনো মৌলিক যোগ নেই, যোগ যতটুকু আছে তা পুরাণের সঙ্গে। যেমন বিষ্ণুপুরাণে অব্যক্ত, অজড়, অচিন্ত্য, অব্যয়, অনির্দেশ্য, ব্রহ্মের কথা (যা নাকি শুনতে অনেকটা অদ্বৈতবাদী শঙ্করের ব্রহ্মের মতো) বলতে বলতে হঠাৎ বলা হল–এই ব্রহ্মই হলেন ‘তদ বিষ্ণোঃ পরমং পদম’ অর্থাৎ একটা ব্যক্তিক (Personalised) রূপের স্পষ্ট আভাস পেয়ে গেলাম আমরা। ঠিক তারপরই বিষ্ণুপুরাণ বললেন–এই কথাগুলো ‘ভগবান’ শব্দের দ্বারাই বোঝানো সম্ভব অর্থাৎ অব্যক্ত অজড়, ব্রহ্ম এবং ‘তদ বিষ্ণোঃ পরমং পদম’–এগুলো ভগবৎ শব্দবাচ্য। তারপর বললেন, এটিই হল পরমাত্মার স্বরূপ। অর্থাৎ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান–এদের সমভুমিতে নিয়ে আসা হলেও ভগবানের গুরুত্ব বেশি থাকল, কেননা ‘ভগবান’ এই মহাশব্দটি পরমব্রহ্মভূত বাসুদেবের ক্ষেত্রেই একমাত্র প্রযোজ্য, অন্যত্র কোথাও নয় (বিষ্ণুপুরাণ ৫.৬.৬৭-৭৬)। তা ছাড়া স্বয়ং ব্রহ্ম কৃষ্ণের রূপ ধারণ করেছেন–’ইচ্ছা গৃহীতো ভিমতোরুদেহঃ’ কিংবা সোজাসুজি ‘কৃষ্ণাখ্যাং পরব্রহ্ম পরাকৃতিঃ’ এসব কথা প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণেই আছে, ভাগবতের কথা তো ছেড়েই দিলাম–কারণ সেখানে কৃষ্ণই প্রথম এবং শেষ কথা। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ–এগুলো ভাগবতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে মাত্র।
কৃষ্ণের মতো চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের আরেকটি মূল বিষয় হল ভক্তি অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে ভক্তি কথাটি যথেষ্ট পুরোনো। পাণিনির সূত্রে কিংবা পতঞ্জলির মহাভাষ্যে ‘ভক্তি’ শব্দ পাই বটে এবং বাসুদেবভক্তের প্রসঙ্গটিও সেখানে অনিবার্য কারণে এসেছে বটে, কিন্তু তবুও সেই ভক্তির সঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের আকাশ-পাতাল তফাত আছে। উপনিষদগুলির মধ্যে ভক্তির কথা পাই একমাত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ৬.১৮ শ্লোকে এবং তাও রুদ্রশিব এবং গুরুভক্তির প্রসঙ্গে। চৈতন্যদেব যে শ্রদ্ধাভক্তির পুনরুজ্জীবন করেছেন, গীতা এবং পুরাণগুলির মাধ্যমে বহুপূর্বেই তা শুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছেছিল। তার আগে এটি অশুদ্ধ ছিল তা নয়, তবে জ্ঞান, যোগ, কর্ম এগুলোর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় ছিল।
চৈতন্যদেবের অব্যবহিত পূর্বযুগ পর্যন্ত ভক্তিকে ব্যবহার করা হত মুক্তির সাধক হিসেবে। এমনকি গীতা, যে গীতাকে আমরা ভক্তিধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর বলে মনে করি–তার মধ্যেও অনেক জায়গাতেই মনে হয় ভক্তি যেন মুক্তির অন্যতম সাধন (১৪-২৬)। আর এই মুক্তির সঙ্গেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সম্পর্ক কিছু তিক্তরসাশ্রিত। মুক্তি ছাড়াও ভক্তিকে যে বিভিন্ন বৈষয়িক প্রয়োজনেও ব্যবহার করা হত তার প্রমাণ আমরা ভাগবত পুরাণেই পাই। স্বার্থসিদ্ধি, যশ, শক্তি অথবা কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি–এইসব নানা কারণে ভক্তির সহায়তা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এই ভক্তির নাম সগুণাভক্তি, অর্থাৎ এটি শুদ্ধা ভক্তি নয়। ভক্তি নিজে ভগবানের স্বরূপাশক্তির অন্তর্ভুক্ত বলে সব সময়েই শুদ্ধা বা গুণাতীত, তবু যে একে সগুণা বলা হচ্ছে তার কারণ জীবজগতের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ইত্যাদি মায়িক গুণের সংস্পর্শে ভক্তির এই আপাত রূপান্তর। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা–যে মুক্তির জন্য উপনিষদের ঋষিরা বহু তপস্যা করেছেন, সেই মুক্তির জন্য ভক্তিকে যদি ব্যবহার করা হয় তবে তাও কিন্তু জীব গোস্বামীর মতে সগুণ ভক্তি। খুব বেশি হলে সেটি সত্ত্বগুণজাত। কাজেই ভক্তি শব্দটি প্রাচীন হলেও চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের সঙ্গে ঔপনিষদিক ভক্তিধর্মের মৌলিক পার্থক্য আছে।
গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের অব্যবহিত পূর্বযুগে রামানুজ প্রভৃতি অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও মুক্তির সাধক হিসেবেই ভক্তিকে বেছে নিয়েছে। রামানুজ তাঁর শ্ৰীভাষ্যে ব্রহ্মবিজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হলেই মোক্ষ হতে পারে–এ ব্যাপারে শঙ্করাচার্যের সঙ্গে একমত হয়েছেন, কিন্তু কীভাবে সেটা হতে পারে, অর্থাৎ সাধনের ব্যাপারে তিনি বলেছেন উপাসনার কথা, যে উপাসনা অবশ্য ভক্তি বা ‘ধ্রুবানুস্মৃতির’ একটি নামান্তর মাত্র উপাসনা-পর্যায়ত্বৎ ভক্তিশব্দস্য)। আমাদের মনে হয় এই সম্প্রদায়গুলো তবুও ভক্তির সঙ্গে মুক্তির কিছু যোগসূত্র রাখার চেষ্টা করেছে, যেমন মাধবাচার্যের কথাও বলা যায়। মাধবাচার্যের দর্শনের সঙ্গে চৈতন্যদর্শনের মিল আছে বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু তিনিও অনেক জায়গাতেই ভক্তিকে ব্যবহার করেছেন মুক্তির জন্য, তা ছাড়া মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ হিসেবেও বেছে নিয়েছেন মাধবাচার্য।
মুক্তি পরম পুরুষার্থ–একথা চৈতন্যপন্থীরা কখনোই বলবেন না, অথচ উপনিষদের প্রতিপাদ্য ছিল তাই। অন্যদিকে মুক্তিকামীর ভক্তি সগুণা–একথা আবার উপনিষদ বলবে না, কেননা গুণাতীত অবস্থা না হলে ব্রহ্মজ্ঞানও হতে পারে না, মুক্তিও হতে পারে না, অন্তত উপনিষদ কিংবা বেদান্তের অভিমত তাই, সে অবস্থায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বেদ-বেদাঙ্গের যোগ কতটুকু?
একথা অনস্বীকার্য, মুক্তির ওপরে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের একটা অসাধারণ বিরক্তি আছে। এ যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় আধুনিক অনেক বৈষ্ণবের মুখে মুখে। আমি অনেক বৈষ্ণবকে (যে বৈষ্ণবদের বেদ বেদান্ত, উপনিষদ, এমনকী নিজস্ব সাম্প্রদায়িক গ্রন্থগুলোও ভালো অধিগত নয়) শুধুমাত্র গুরুমুখোদগীৰ্ণবাণী সহায় করে বলতে শুনেছি–’ও তো ব্রক্ষবাদী, মুক্তিকামী” কিংবা ‘ব্রহ্মবাদীরা এমন কথা বলে’–যেন ধর্মতত্ত্বে ব্রহ্মবাদীর মতো অকুলীন, বোকা আর কোথাও নেই। তবে একথা সত্য, মুক্ত কিংবা পরিষ্কার করে বলাই ভালো যে, ব্রহ্মের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের যে এই অদ্ভুত অসহযোগ দেখা যায়, তার মূল কিন্তু চৈতন্যযুগেই নয়, এর প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে পুরাণগুলির যোগাযোগই প্রধান, বেদবেদান্তের ওপর গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকদের শ্রদ্ধা অনেকটাই পরম্পরাগত দার্শনিক প্রয়োজনে আচরিত।
আমরা জানি গীতার মধ্যে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি–এই তিন ধারার ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছে। কর্মের মধ্যে সকাম কর্ম বাসনার পরিপূর্তি করে বলে দার্শনিকদের মন স্পর্শ করে না; আর নিষ্কাম কর্মের অবসান যেহেতু জ্ঞানে (গীতা ৪.৩৩), তাই সাধন হিসাবে আমাদের পথ দুটি–জ্ঞান এবং ভক্তি। সাধারণ মতে জ্ঞানের ফল ব্ৰহ্মদর্শন, মুক্তি; ভক্তির ফল ভগবানের সেবা লাভ করা। গীতার মধ্যে জ্ঞান এবং ভক্তি–এই শব্দ দুটি অনেক জায়গায় এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যে সেখানে এই দুইয়ের মধ্যে কোনটি গীতাকারের অভিপ্রেত তা বোঝা মুশকিল হয়ে পড়ে। অবশ্য বোঝানোর জন্য যুক্তিনিষ্ঠ টীকাকারেরা আছেন, তাঁরা যেমন বোঝান মনের সঙ্গে মিলে গেলে আমরাও তেমনি বুঝি, একটি পক্ষ নিয়ে নিই।
বাস্তবিকপক্ষে গীতার মধ্যে ভক্তির ওপর দুর্বলতা কিছু বেশি আছে একথা অনস্বীকার্য। কেননা গীতা বললেন “বহু জন্ম-জন্মান্তরের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আত্মাকে (কৃষ্ণকে) আশ্রয় করে” (৭.১১)–এক কথায় জ্ঞানমার্গের খানিকটা প্রমাণিত হয় বইকি। ঠিক তারপরেই ‘এমন মহাত্মা দুর্লভ, যিনি মনে করেন ভগবান বাসুদেবই সব’ গীতার এই শ্লোকে কৃষ্ণভক্তির প্রাধান্য সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া এমন শ্লোকও রয়েছে যাতে করে বোঝা যায়–ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে ভক্তি অনেক বেশি সুবিধাজনক এবং সর্বজনীনতাও অনেক বেশি। ভক্তির ওপর গীতাকারের একটা সূক্ষ্ম পক্ষপাত যে আছেই, সেকথা অন্য প্রসঙ্গেও আমাদের বলতে হবে, এখন এটুকু বললেই যথেষ্ট যে গীতার ভক্তিমূলক সাধনই পরিণতি লাভ করেছে পুরাণে।
একথা স্বীকার করতেই হবে যে, পুরাণগুলির মধ্যে ভক্তির মাহাত্ম্য যতই পল্লবিত হোক না কেন, উপনিষদ-বেদান্তের মৌলিক প্রতিপাদ্য জ্ঞানমার্গ কিন্তু ভক্তির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে এখানে। আসল কথা উপনিষদ-বেদান্তের বস্তু বলেই হোক অথবা তকালীন সমাজের শিরোমণি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দ্বারা অভ্যস্ত বলেই হোক–জ্ঞানমার্গের অসারতা সোজাসুজি প্রতিপাদন করা সম্ভব হয়নি পুরাণগুলির মধ্যে। বিশেষ করে প্রাচীন পুরাণগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বোধহয় বিষ্ণুপুরাণ। এই পুরাণের মধ্যেও বাসুদেব-স্মরণ কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর স্মরণ, মনন ইত্যাদি ভক্তির মাহাত্ম্য যেমন কীর্তন করা হয়েছে, তেমনি একই সময়ে পরমবস্তুকে পাওয়ার জন্য জ্ঞানের মহিমাও খ্যাপন করা হয়েছে বারবার। (দ্র. ২, ৬, ৩৯, ৪০, ২, ৬, ৪৫-৪৬ ২, ১২, ৪৩, ৬, ৫, ৮৭)
আমাদের মনে হয়, এইসব সময় জ্ঞান এবং ভক্তির কোনো পরিষ্কার বিভেদরেখা ছিল না, যেমনটি ছিল না ব্রহ্ম এবং ভগবানের মধ্যেও। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, নারায়ণ, হরি, বাসুদেব–এঁরা একই তত্ত্ব হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন ততদিন এবং এইসব নাম যেহেতু ব্রহ্মের মূর্ত স্বরূপ বলে মনে করা হত, ভক্তি আর জ্ঞানের মধ্যেও তাই বিরোধ ছিল না কোনো। প্রকৃতপক্ষে জনপ্রিয়তার প্রথম অবস্থায় ভক্তিকে জ্ঞানের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়েছিল, কেননা তখন পর্যন্ত জ্ঞানের আভিজাত্য ছিল অটুট। কিন্তু বেদ বেদান্ত এবং পরোক্ষভাবে জ্ঞানও যেহেতু অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ভক্তির পথ প্রশস্ত হয়েছিল। সমাজের সুবৃহৎ অংশ, যার মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরা ছিলেন না, তাঁরা ধর্মীয় দিক দিয়ে সমাজে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন এই ভক্তিধর্মের মধ্য দিয়ে, কেননা জ্ঞানমার্গ ছিল তাঁদের কাছে অনেক দূরের জিনিস, প্রায় ধারণার অতীত।
পুরাণকারেরা ভক্তির জনপ্রিয়তা লক্ষ করে অতি মহিমান্বিত করেছেন ভক্তির পথ, তবুও প্রথমেই জ্ঞানের পথকে সোজাসুজি নস্যাৎ করেননি তাঁরা। কেননা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাহলে ধর্মীয় আঙ্গিকের মধ্যে ভক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে দিত না। ঠিক এই কারণেই পুরাণকারেরা জ্ঞান ও ভক্তির যুগপৎ প্রশংসা শুরু করলেন। এমনকী ভাগবতপুরাণ, যেটিকে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের বেদ বলা হয় এবং যার মধ্যে ভক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট পক্ষপাত দেখা যায়, সেটিও সাধনের প্রথম পর্যায়ে গীতার মতো কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির ত্রৈবিধ বিধান করেছে। (১১.২.৬)। তাছাড়া চিরায়ত জ্ঞানযোগের পথে ভক্তি যে একটি নতুন প্রকল্পও একথা স্বীকার করেছে ভাগবতই। উদ্ধব সেখানে ভগবানকে বলেছেন, ‘‘আমি বহু পুরাতন জ্ঞানমার্গের কথা শুনেছি, এখন আপনি মহাত্মাদের জিজ্ঞাস্য ভক্তিযোগের কথা বলুন।’ অন্যত্র এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পুরাণটির মধ্যে জ্ঞানযোগের সঙ্গে সইয়ে সইয়ে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ভক্তিযোগকে, যেমন– জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ভজ মাং ভক্তিভাবিতঃ ১১.১৯.৫), আর-এক জায়গায় পরমপ্রাপ্তি হিসেবে জ্ঞান ও ভক্তির বৈকল্পিক প্রাধান্য দেখতে পাই–জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদভক্তিং বা যদৃচ্ছায়া (১১.২০.১১)।
ভাগবতের মধ্যে ব্রাহ্মণ সমাজের চক্ষু ধৌত করবার জন্য জ্ঞানের কথা যত নিপুণভাবেই বলা হোক না কেন, ঐতিহাসিক বিচারে তার কিছু মূল্য থাকলেও সেটা ভাগবতের মমার্থ নয়, কেননা ভাগবতকার প্রধানত জ্ঞানের অসারতার কথা বারবার বলেছেন, আরও বলেছেন ভক্তিমার্গের সুবিধার কথা। কর্ম, তপস্যা, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম এগুলোর যা ফল, ভক্তি তা সবই দিতে পারে। তাছাড়া, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি, যা নাকি এককালে সাধনের অন্যতম উপায় ছিল, তা ভগবানকে তুষ্ট করতে পারে না, আর তুষ্ট না হলে (ভাগবতের মতে) বৃথা পরিশ্রমে ধান ভেঙে চালের বদলে তুষ পাওয়ার মতো শুধু পরিশ্রমই সার (৭.৯.৯)। জ্ঞান-বৈরাগ্য ভাগবত পুরাণে শেষপর্যন্ত ভক্তিরই by product হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, জ্ঞান সম্পর্কে নির্ভর করতে হয়েছে ভক্তির ওপর। জ্ঞানের ফল হিসেবে মুক্তির অবস্থাও হয়ে উঠেছে করুণ। ভাগবতের সবচেয়ে প্রাচীন টীকাকার শ্রীধরস্বামী তো ভাগবতের প্রারম্ভিক শ্লোকগুলির মধ্যে বলে দিলেন যে, ভাগবতে এমন একটি ধর্মের কথা বলা হয়েছে যার মধ্যে মুক্তির কোনো ‘অভিসন্ধান নেই। রূপ গোস্বামী, যিনি চৈতন্যদেবের কথা জানতেন বলে ধরা হয়, তিনি তো মুক্তির নামকরণ করলেন ‘পিশাচী’। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ আরও একধাপ এগিয়ে বললেন–অজ্ঞানই হচ্ছে অন্ধকার, একে এককথায় বলে ‘কৈতব’। সাধকের সাধনপথে যত ‘কৈতব’ আছে তার মধ্যে মোক্ষস্থা কৈতবপ্রধান”। জানি না এর পরেও বলা যায় কি না– বেদ-উপনিষদের সঙ্গে চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মের কোনো সংযোগ আছে।
আমাদের বক্তব্য হল চৈতন্যদেবের ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে বেদ-বেদান্তের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকলেই তবে সেটা ধর্ম হবে, না হলে সেটা ধর্ম হবে না–এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। চৈতন্যের এই বিরাট ধর্মান্দোলনের মধ্যে যেখানে ‘পাত্ৰাপাত্র বিচার নাহি নাহি স্থানাস্থান’–সেই নির্বিচার ভালোবাসা, যা নাকি ‘স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সবারে ডুবায়’, সেখানে প্রথাগত সংরক্ষণশীলতা এবং নবদ্বীপের তৎকালীন বেদান্ত ন্যায়াধ্যুষিত পরিমণ্ডল–ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, অধ্যাপক, পড়য়া–এঁরা মহাপ্রভুর সংগৃহীত এই হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধনকে গ্রহণ করতে পারছিলেন না ভালো মনে। অথচ চৈতন্যের কারণেই বঙ্গদেশে ধর্মের যে আলোড়ন তৈরি হয়েছিল, তা চালিয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছিল সাধারণ মানুষের সমাগ্রহে, কিন্তু তঙ্কালীন ব্রাহ্মণ্য এবং বিদ্যাভিজাত্যের প্রতিস্রোতে।
কী ভীষণ এবং কঠিন ছিল এই প্রতিপক্ষতা, যা নৈয়ায়িক-কুলের চেয়েও বেশি অদ্বৈত বেদান্তীদের কাছ থেকে এসেছিল। সেই প্রতিপক্ষতার সঙ্গে লড়াই করার জন্য মহাপ্রভুর একমাত্র উপজীব্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সর্বসাধারণ বঞ্চিত মানুষের জন্য তাঁর ভাবনা। একজন কালচারাল স্পেশালিস্ট’ বা ‘কালাচারাল মিডিয়েটর’-এর যে দায়িত্ব থাকে–সেই ‘গ্রেট ট্র্যাডিশন এবং ‘লিটল ট্র্যাডিশন’- কে মিলিয়ে দেওয়া চৈতন্যদেবের দায়িত্ব ছিল তার চেয়েও বেশি। দার্শনিক জগতে তিনি যেমন বুদ্ধিমানের সাধন জ্ঞানমার্গকে ভক্তিমার্গের অধীনে টেনে এনেছিলেন, তেমনই ধর্মসাধনের ক্ষেত্রেও পরম জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্মের পরিবর্তে অখিলরসামৃত মূর্তি কৃষ্ণের আরাধ্যতা প্রতিষ্ঠা করে ধর্মকে এমন একটা ‘ডোমিস্টিসিটি-র মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন, যাতে সাধারণ মানুষ তার নিত্যকর্মের মধ্যে ভগবানকে নিয়ে আসতে পেরেছে। ভগবানের সর্বত্রতার ভূমিকাটা তাতে গৌণ হয়ে নিত্যদিন ভালোবাসার জায়গায় এসে পৌঁছেছে। চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য এইখানেই। তাঁর জয় হোক–জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
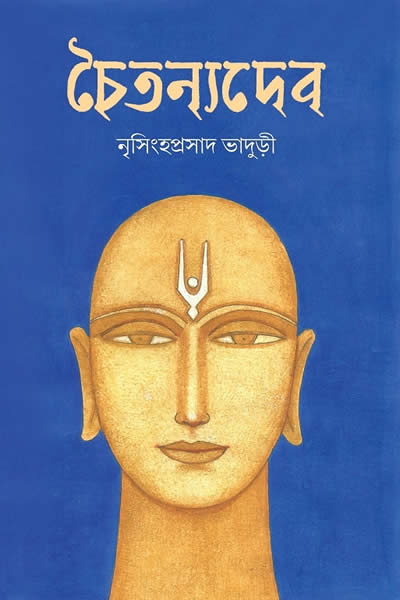

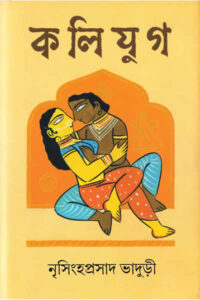



Leave a Reply